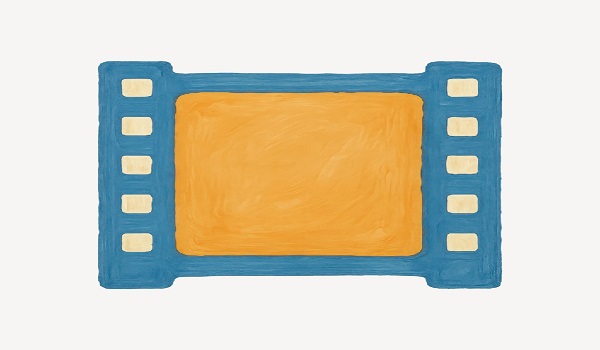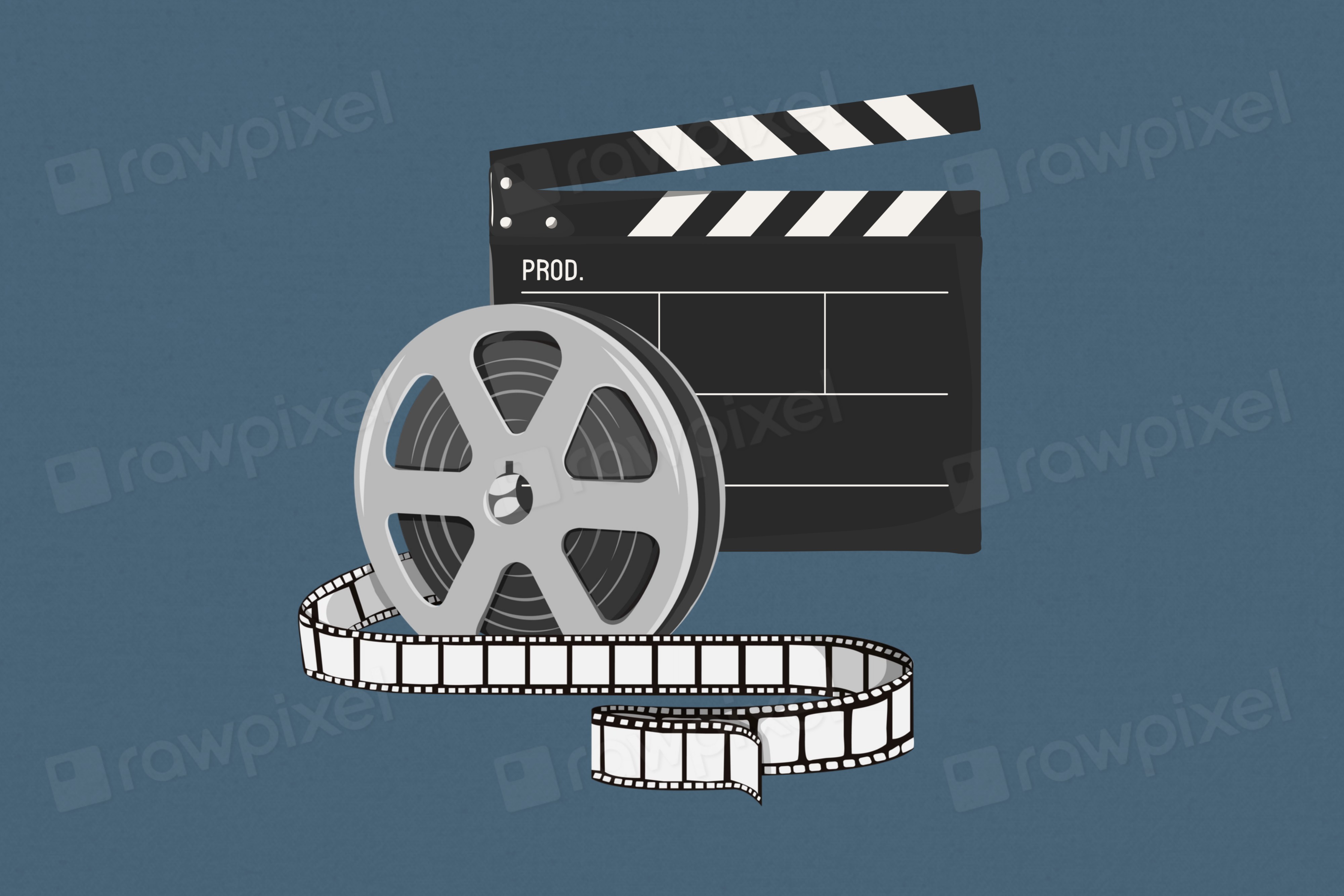সেখ আশরাফ আলি ও একতা গাঙ্গুলী
প্রকাশিত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৫৫-১৯৮০) : পরিপ্রেক্ষিত নকশালবাড়ি
সেখ আশরাফ আলি ও একতা গাঙ্গুলী
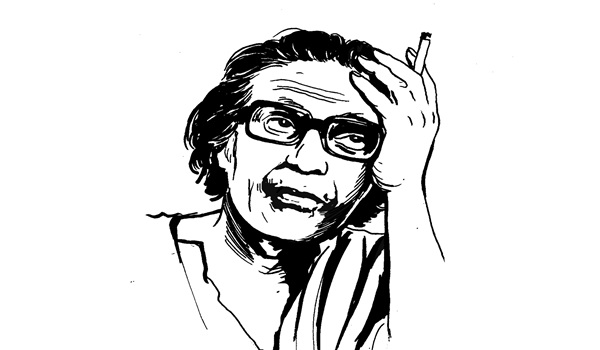
মৃণাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আদ্যোপান্ত নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, সর্বোপরি লেখক। মৃণাল বাংলা চলচ্চিত্রে একদিকে যেমন আধুনিকতার প্রতীক, অন্যদিকে ভারতের সমান্তরাল চলচ্চিত্রের (parallel Cinema) জনক।১ গণনাট্য আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করা মৃণাল পাশ্চাত্য নতুন ধারার চলচ্চিত্র দর্শনে সমৃদ্ধ হয়ে চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন সমাজজীবন সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা প্রকাশের সৃজনশীল মাধ্যম হিসেবে। বিংশ শতকের ৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ৭০ দশক অবধি সমগ্র বাংলা যে উত্তাল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে-সেখানেই তার সৃষ্টির মৃগয়াভূমি। একজন যথার্থ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মৃণাল তার নির্মিত চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তৎকালীন অস্থির পরিস্থিতির চক্রব্যূহ থেকে। তাই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে নির্মিত তার চলচ্চিত্রগুলোর ভাষা রাজনৈতিক। এহেন চলচ্চিত্রে ধরা দিয়েছে সাধারণ মানুষের কাহিনি, তাদের জীবনযন্ত্রণা, সম্পর্কের টানাপড়েন, মূল্যবোধের সঙ্কট, মানসিক দ্বন্দ্ব, হতাশা আর নতুন প্রভাতের আর্তি। প্রথাগত নিয়ম বর্জন করে, গতানুগতিক কাহিনি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তার সৃষ্টিতে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনন্য সংযোজন সাধন করেছেন তা আপামর দর্শকের মনকে আলোড়িত করেছে। আন্দোলিত করেছে সমাজের প্রান্তিক মানুষের বোধকে। এখানেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সনাতন চলচ্চিত্রের ধারা, ব্যাকরণ ও গতিপ্রকৃতি।২
এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা যায়, মৃণাল সেনের ৬০-৭০ দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রে সমকালীন সময়পর্বে গড়ে ওঠা নকশালবাড়ি আন্দোলনের কীরূপ প্রভাব পড়েছিলো তা অনুসন্ধান করা। এর পাশাপাশি তার সৃষ্টিতে কীভাবে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটগুলো প্রতিভাত হয়েছে তাও খুঁজে দেখা। সংক্ষেপে বলা যায়, মৃণালের রাজনৈতিক চলচ্চিত্র দর্শনকে যথার্থভাবে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।
দুই.
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে মৃণাল সেন জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরের লেখাপড়া সমাপ্ত করে ১৯৪০ নাগাদ স্নাতক হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন কলকাতায়। ভর্তি হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ স্কটিশ চার্চ কলেজে। পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। এক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় ৪০-এর দশক ছিলো ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের উন্মেষপর্ব। নব্য প্রতিষ্ঠিত ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ -এর নেতৃত্বে ভারতজুড়ে শুরু হয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কর্মকাণ্ডের পথচলা শুরু হয় দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।৩ সংঘের প্রধান লক্ষ্য ছিলো বৃটিশ বিরোধিতা ও সমাজের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের দুর্দশা তুলে ধরা এবং নাটক, গান, কবিতা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা বামপন্থি ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক অধিকারের পক্ষে সামিল হয়। তাই বলা যায়, সংস্কৃতিকে নিপীড়িত মানুষের জীবনসংগ্রাম ও মানব-মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছিলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।৪
চিন্তার এই নবতরঙ্গ থেকে মৃণালও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি, ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। নিকট বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, বংশীচন্দ্র গুপ্তের মতো ব্যক্তিত্বদের। ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী প্রমুখরা পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদ নিলেও তিনি কখনো পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেননি।৫ সাংস্কৃতিক জগতে পা রেখেছিলেন নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে। হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া শহরে অবস্থিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা ‘ভদ্রকালী নাট্যচক্র’-এ যোগ দিয়েছিলেন ৬০-এর দশকের গোড়ায়। এই সংগঠন প্রথম থেকেই বামপন্থি আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো। মৃণাল ‘ভদ্রকালী নাট্যচক্র’ থেকে পরিচালনা করেছিলেন দুটি নাটক-‘মশাল’ ও ‘শহীদের ডাক’।৬ ‘মশাল’ নাটকটি দিগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, অন্যদিকে ‘শহীদের ডাক’ ছায়ানাটকের উদাহরণ। আশ্চর্য সমাপতন যে বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-খ্যাত হীরালাল সেনও আলোছায়ার জগতে অভ্যস্ত হয়েই আলোকচিত্রের জগতে পদার্পণ করেছিলেন। মৃণাল অবশ্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাপস সেনের কাছ থেকে।
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মৃণাল মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল আত্মনিবেদনের কাহিনি ‘শহীদের ডাক’-এ মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।৭ ছুটে গিয়েছিলেন বাঁকুড়া ও বিহারের দুমকা এলাকায়। যদিও নাটকের ওপর পুলিশি সুনজর না থাকায় তা মঞ্চস্থ করার অনুমতি পাওয়া যায়নি। তবে দুমকার পৌরপ্রধান শেষ পর্যন্ত সহৃদয় হয়ে নিজের বাসভবনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য সেখানে ‘মশাল’ মঞ্চস্থ হলেও বিদ্যুতের অভাবে ‘শহীদের ডাক’ মঞ্চস্থ হয়নি।৮ জীবনের প্রথমপর্বে চলচ্চিত্রের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। তবে এ কথা ঠিক যে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র দেখে তিনি ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন। জীবিকার কারণে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েও ছেড়ে দেন এই উৎসাহের বশবর্তী হয়ে। অডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে যোগ দেন কলকাতা ফিল্ম স্টুডিওতে। পদার্থবিদ্যার ছাত্র হওয়ায় প্রথম থেকেই সাউন্ডের প্রতি তার আগ্রহ ছিলো।৯ মৃণাল সম্পূর্ণভাবে চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশের আগে চলচ্চিত্র নিয়ে তাত্ত্বিক পড়াশোনা ও লেখালেখি শুরু করেছিলেন। নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকেন তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অর্থাৎ আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।১০ এ সময়েই লিখে ফেলেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে আস্ত একটি বই, যা এখন অবধি বাংলা ভাষায় রচিত চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কিত অন্যতম আকরগ্রন্থ। গ্রন্থাগারে নিত্যনতুন বই পড়ার মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন বিশ্ববন্দিত সব চলচ্চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্রের ব্যবহারিক কৌশলের সঙ্গে। রুডলফ আর্নহেইম-এর ‘ফিল্ম এসথেটিকস’, নীলসন-এর ‘সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট’-এর মতো বই তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখতে চলে যেতেন ফিল্ম সোসাইটিতে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারাকে যথার্থ পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি চলচ্চিত্র দর্শন আত্তীকরণ করেন। তবে তার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সম্ভবত ছিলো ৬০-এর দশকের ফরাসি চলচ্চিত্রের নিউ ওয়েভ ধারার। চলচ্চিত্রে নিউ ওয়েভ ধারাটি ছিলো ৪০-এর দশকের নিউরিয়ালিজমের পরবর্তী একটি স্রোত। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে কীভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন, সেই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন-
সেই সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরির নাম ছিল ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি। ... লিটারেচার, ফিলোসফি, সোশিওলজি, পলিটিক্স, কবিতা, নাটক- সবই পড়তাম। ... তারপর পড়ি আইজেনস্টাইনের ছাত্র নীলসেনের লেখা ‘The cinema as a graphic Art’। এই বইয়ের মুখবন্ধ আইজেনস্টাইন নিজে লিখেছিলেন, ... এই বইটি যখন প্রথম পড়ি, তখনই আমি আইজেনস্টাইনের নাম শুনি এবং তখন আমি আইজেনস্টাইনকে আইনস্টাইন বলে মনে করতাম। এই বইটি ছিল টেকনিক্যাল বই; পড়ে খানিকটা বুঝলাম খানিকটা বুঝলাম না। মন্তাজ সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের থিওরি, তাঁর চিন্তাভাবনার ব্যাখ্যা এই বইতে আছে। এই বইতে মস্ত একটা ব্যাপার আছে যা আমাকে খুব টেনেছিল। পুশকিনের বিখ্যাত লম্বা কবিতা ‘The bronze Horseman’| সেটা আমার পড়া ছিল। আইজেনস্টাইন ক্লাসে বলেছিলেন কিভাবে এই কবিতাকে ফিল্ম-স্ক্রিপ্ট করতে হবে। এই বইতে সেই কবিতার স্ক্রিপ্ট আছে। যা নীলসেন করেছিলেন। অসাধারণ সেই স্ক্রিপ্ট খানিকটা বুঝেছিলাম, খানিকটা বুঝিনি। সেই থেকে ফিল্ম সংক্রান্ত যা-কিছু বই পেয়েছি, পড়েছি। সেই থেকে আমার সিনেমার প্রতি ইন্টারেস্ট, সিনেমার জন্য প্যাশন ডেভলপ করে।১১
চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে মৃণালের কাজের প্রসার ছিলো প্রায় পাঁচ দশকের। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাত-ভোর চলচ্চিত্র দিয়ে যাত্রা শুরু করে অবসর নিয়েছিলেন ২০০২-এ নির্মিত আমার ভুবন-এর মধ্য দিয়ে। সমগ্র জীবনে নির্মাণ করেছিলেন ২৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্যরে চলচ্চিত্র, চারটি তথ্যচিত্র, একটি দূরদর্শনচিত্র, ১৩টি দূরদর্শন ধারাবাহিক, চারটি চিত্রনাট্য। মৃণাল সেনের কাজের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত-প্রারম্ভিক, রূপান্তর ও পরিণত পর্যায়। প্রারম্ভিক পর্যায়ের (১৯৫৫-১৯৬৩) শুরু রাত-ভোর দিয়ে, শেষ হয়েছে অবশেষে (১৯৬৩) দিয়ে। অবশেষের পর থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের চরিত্রে তার পরিবর্তনের সূচনা ঘটতে থাকে। যেখানে তার সামাজিক সক্রিয়তা ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। এটাকে ‘ট্রানজিশন পিরিয়ড’ বলে অভিহিত করা যায়। ‘ট্রানজিশন পিরিয়ড’ (১৯৬৪-১৯৬৯) এর প্রথম চলচ্চিত্র প্রতিনিধি (১৯৬৪) আর শেষ ভুবন সোম (১৯৬৯)।
শেষের পর্যায়ে মৃণাল আধা-সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় মধ্যবিত্ত পরিবারের আধা সামাজিক সঙ্কটের নানা বিষয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের বিষয়টি একের পর এক চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন। ভুবন সোম থেকে আমার ভুবন-এ তিনি শুধু পরিণত হয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং বাগ্মী, একরোখা জেদি, বেনিয়মের কারবারি মৃণাল বস্তুত চেতনার চৌকিদার হিসেবে হাজির হয়েছেন। তাই বলা যায়, মৃণালের প্রথম দিককার চলচ্চিত্রে আখ্যানের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিলো, পরে সেখান থেকে তিনি সচেতনভাবে খানিকটা সরে আসেন; প্রবেশ করেন নিগূঢ় রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায়। এ কারণেই ৬০-৭০ দশকে নকশাল কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্কট, সম্ভাবনা ও বিপর্যয় ঘনীভূত হয় তা জ্যঁ লুক গদার-এর চলচ্চিত্রের মতোই মৃণালের ৭০-এর দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে ন্যারেটিভের ভাঙচুর পরিলক্ষিত। ৭০-এর উত্তাল দিনগুলোর সঙ্গে এই চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশল একে অন্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে মৃণালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সরাসরি পলিটিকাল (রাজনৈতিক) চলচ্চিত্র নির্মাণের অদম্য-আপসহীন সাহস এবং চলচ্চিত্র প্রকরণ নিয়ে অজস্র পরীক্ষানিরীক্ষা। চলচ্চিত্র ও নিজের তাগিদ সম্পর্কে মৃণাল সেন বলেছিলেন, ‘As a social being I need to express myself. I need to convey to others Ges †mw`K †_‡K I want to share my own opinion with others or I want to provoke a controversy which is also very important’.১২
তিন.
৬০-এর দশকের শেষ দিকে ভারতীয় সমাজ এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা বজায় রেখে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করে, সীমিত পুঁজিবাদ বিকাশের যে নীতি নেহেরুর সময় গ্রহণ করা হয়, তারই বিষময় পরিণতিতে সেসময় ভারতীয় অর্থনীতিতে দেখা দেয় চরম বিপর্যয়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন নেমে গিয়েছিলো যথাক্রমে ছয় কোটি ৩৩ লাখ এবং ছয় কোটি ৪৯ লাখ টনে। পর পর দুই বছরে পর্যায়ক্রমে এক কোটি এবং ৮৬ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করেও মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যশস্যের জোগান ওই দুই বছর ৪০৮ দশমিক দুই গ্রাম এবং ৪০১ দশমিক চার গ্রামের ঊর্ধ্বে তোলা যায়নি। ৫০ ও ৬০-এর দশকের গোড়ায় খাদ্য পরিস্থিতি এতোটা ভয়াবহ ছিলো না; এমনকি তখনো খাদ্যশস্যের মাথাপিছু জোগান ছিলো দৈনিক ৪৫০ গ্রামের কাছাকাছি। বলা বাহুল্য, খাদ্য সঙ্কট তথা কৃষির সঙ্কট বহুবার মুলতবি রাখা কৃষি প্রশ্নটিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে; কৃষির প্রশ্নে শাসকদলের অনুসৃত নীতির ওপর জনগণের আস্থার অভাব দেখা দেয়। গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে সমগ্র ভারতবর্ষে গণআন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। অসম্ভব হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণির পক্ষে পুরনো সংসদীয় শাসন পার্টির সাহায্যে শাসন চালিয়ে যাওয়া। জনগণও পুরনো ধরনের শাসন মানতে অস্বীকার করে।১৩
এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নকশালবাড়ির প্রসাদুজোত এলাকায় কৃষক বিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ ১১ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এদের মধ্যে আটজন নারী, একজন বালক ও দুই শিশু ছিলো। প্রকাশে অত্যুক্তি হবে না, এই হত্যাকাণ্ডই সশস্ত্র নকশালবাড়ি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় কৃষকের আন্দোলন। গড়ে ওঠে ‘কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি’। আন্দোলনটি সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কমিউনিস্টদের সংগঠিত করে সশস্ত্র কৃষক বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে ‘অল ইন্ডিয়া কো অর্ডিনেশন কমিটি অব দি কমিউনিস্ট রেভেলিউশনারি’ (AICCR) গঠন করে। এই সংগঠনের সদস্যরা পরবর্তীকালে সি পি আই (এম এল) নামক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলে, যার নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বিষয় হিসেবে স্থির হয় কৃষি বিদ্রোহ। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার জন্য গ্রামভিত্তিক সংগ্রাম ও অপ্রকাশ্য কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।১৪ সংসদীয় পথকে অগ্রাহ্য করা হয়। এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উৎখাত ও সামন্ততান্ত্রিক জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেওয়া হয় সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। নব্য প্রতিষ্ঠিত পার্টি ধীরে ধীরে চিনের বিপ্লবী মাও সে-তুং-এর চিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকে। পার্টির সদস্যদের মধ্যে থেকে স্লোগান ওঠে ‘চিনের পথ আমাদের পথ’ ও ‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’।১৫
শুধু কৃষি সঙ্কট নয়, জাতপাতগত এবং সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার ও শোষণ, সরকারি অফিসের দুর্নীতি, পুলিশের অপরাধীকরণ এবং ভূস্বামীদের অনুগত সরকারি আধিকারিকদের অনৈতিকতার কারণে ভূমিসংস্কারের ব্যর্থতা, পুঁজিবাদী শক্তি ও সমাজবিরোধীদের বাড়বাড়ন্ত সমাজে বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে; কারণ তারাই সবচেয়ে বেশি শোষিত।১৬ সুতরাং ১৯৬০-এর দশকের মধ্য পর্বে ভারত যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয় তা মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে, যারা সবকিছুর জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে দায়ী করে। হতাশ যুবকেরা মনে করে, সমস্যাগুলো রয়ে যাচ্ছে কারণ রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের হাতে এবং জনগণকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় সশস্ত্র বিপ্লব এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এছাড়া সি পি আই ও সি পি আই (এম) এর সংসদীয় রাজনীতির প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া এবং চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব কৃষক বিদ্রোহে নব্য এই মাওপন্থিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নকশাল মতাদর্শ গঠনের পশ্চাতে ছিলো ১৯৬৫-৬৭ সময় পর্বে রচিত চারু মজুমদারের রচনাবলী, বিপ্লবী মার্কসবাদীদের দ্বারা আন্দোলনের শুরুর সময় প্রচারিত নিবন্ধ, প্রচারপত্র, সার্কুলার ও প্রতিবেদন। সি পি আই (এম এল) এর মুখপত্র লিবারেশনে প্রকাশিত রচনাগুলো, মাও সে-তুং ও চিনা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রাক্কালে তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদারের রচিত ‘আটটি দলিল’ ছিলো বিপ্লবের বাইবেল।
নকশালবাড়ি আন্দোলনে শহুরে ছাত্র-যুব সমাজের অংশগ্রহণ ছিলো উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। কলকাতাও এই উত্তাপ বৃত্তের বাইরে ছিলো না। প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ কলেজ ও গুরুদাস কলেজের ছাত্র-যুব সম্প্রদায় নকশাল আদর্শ, মাও সে-তুং ও বিপ্লবকে সামনে রেখে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। বলা যায়, ১৯৬০-এর দশকে শিক্ষাব্যবস্থার ভেঙে পড়া ছিলো কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের যুবকদের ক্ষোভের প্রধান কারণ। ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করা হয়েছিলো। বাস্তবতা বর্জিত একঘেয়ে ক্লাস-বক্তৃতা, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার অভাব, দুর্নীতিগ্রস্ত পরীক্ষকদের দ্বারা উত্তরপত্রে নম্বরের কারচুপি প্রভৃতি কারণে ক্যাম্পাসের মধ্যে বাঙালি যুবরা ছিলো ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। এমনকি স্নাতক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার পর তারা এক আশাহীন ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়। মধ্যবিত্তের চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছিলো কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা ছাত্রদের জন্য চাকরির সুযোগ কমে গিয়েছিলো। ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে শিল্পে মন্দা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর থেকে পাশ করে আসা হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির সুযোগকে অনেকখানি নষ্ট করেছিলো। এর ফলে হতাশ যুবকদের গোটা প্রজন্মটাই তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের উপযুক্ত পরিস্থিতির অনুসন্ধান করে। এই চরম সঙ্কটকালে ‘দেশব্রতী’ পত্রিকায় ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে লেখা হয়,
দুশো বছরের পরাধীন ও শোষিত ভারতবর্ষে ছাত্র ও যুবকরাই হচ্ছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যাপক জনতাকে অশিক্ষিত ও অন্ধ করে রেখে দিয়েছে। তাই বিপ্লবী আন্দোলনে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্র যুবক শুধু শিক্ষিতই নন, তাদের আছে বিরাট উৎসাহ, ত্যাগ স্বীকারের শক্তি এবং যেকোনো অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই তাঁরাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হয়ে ব্যাপক জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক জনতার মধ্যে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কৃষকের বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরীর কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা শিক্ষিত, তাই দেশের অশিক্ষিত মানুষের কাছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার শিক্ষা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তাদের সবচেয়ে বেশি।১৭
বিপ্লবের নেতৃত্বে থেকে চারু মজুমদার ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে বলেন,
এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরিব কৃষক শ্রমিক জনগণকে হেও চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সব কিছুরই ওপর তার আর শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে তাদেরই সেবা দাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তাছাড়া ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স থাকতে মানুষ সারা জীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বয়সটাতে যুব ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন : যত বেশি পড়াশোনা করবে, তত বেশি মুর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। চীনের যুব ছাত্র-সমাজও মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুতে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দু-বছর বাদে-১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।১৮
১৯৭০-র দশকের সূচনাপর্বে কলকাতার ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায় বিপ্লবের ডাকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরে ও রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন সরোজ দত্ত। এই সময় বহু ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে নিজেদের মতো করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক এই ব্যবস্থার পতন আসন্ন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের উৎসাহে বিপ্লবী যুব এবং ছাত্ররা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করে। দলে দলে যুবক স্কুল-কলেজে ঢুকে সেখানকার অফিসের ক্লাসরুমের ল্যাবরেটরি এবং গ্রন্থাগারে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এমনকি তারা পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বই পুড়িয়ে নষ্ট করে; কোথাও কোথাও আবার এই সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীরা স্কুলে ঢুকে বোমা ছুড়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে বিপুল সংখ্যক বই নিয়ে গিয়ে পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেয়। ক্রমে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় ধ্বংসাত্মক মূর্তি ধারণ করে।
প্রথমে আক্রমণের লক্ষ্য হন গান্ধী ও নেহেরু এবং তারপরে বাংলার ‘নবজাগরণের’ নেতৃবৃন্দ-রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ। তাদের প্রতিকৃতিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় ও মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলের যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, ছাত্র-যুবসম্প্রদায় তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার করতে থাকে। বিপ্লবীরা এদের বিচার করতে চায় একটি মাপকাঠিতে, ব্যারিকেডের কোন দিকে এদের অবস্থান?১৯ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নকশালবাড়ি কৃষকসংগ্রামে অনুপ্রাণিত ছাত্ররা শুধু রাজনীতিতে নয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেও বিদ্রোহী গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করে। মূর্তি ভাঙার স্বপক্ষে কলম ধরে ছিলেন সরোজ দত্ত। তিনি শশাঙ্ক ছদ্মনামে ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে কৃতকর্মের সমর্থন জানিয়েছিলেন। যদিও মধ্যবিত্ত জনগণ ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।
সরকারের পক্ষ থেকে নকশালপন্থিদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়। এবং আন্দোলন দমনের জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মারাত্মক রূপ ধারণ করে। পুলিশ হেফাজতে হত্যা, সংঘর্ষে হত্যা, বেআইনি আটক, জেলখানায় নিরস্ত্র রাজবন্দিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ এ সময় দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছিলো। মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কার্যত তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিলো। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে কলকাতায় পাঠায়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্বাচিত হলে বাংলায় নকশালপন্থিদের ওপর বীভৎস ও নির্মম গণহত্যা চালানো হয়।২০
১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের বারাসাত গণহত্যার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যে ঘটনায় বারাসাতের আমডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১১ যুবক ও কৃষকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে এদের দেহ শনাক্ত করে জানানো হয় এদের কেউ কারখানা শ্রমিক কেউ বা কলেজ ছাত্র। এরা নকশালপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিহতরা প্রায় সবাই আড়িয়াদহ দক্ষিণেশ্বর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ কলকাতার ময়দান এলাকায় হত্যা করে তাদের দেহ বারাসাতে ফেলে রেখে যায়।২১ কয়েকদিন পর ১৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুর কারাগার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু নকশালপন্থি বন্দিকে পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, তাদের মুক্তির নির্দেশ এসে গেছে; তাই তাদের জেলের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কারাগারের অন্যান্য বন্ধুরা বুঝতে পারে, পুলিশ ভুয়া সংঘর্ষে এদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তারা তীব্র প্রতিবাদ জানালে সি আর পি এফ বা কেন্দ্রীয় পুলিশ কারাগারে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সেদিন শতাধিক রাজনৈতিক বন্দি মেদিনীপুরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়; যদিও সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিলো মাত্র নয়। এমনকি নিহত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে সরকার অস্বীকার করে।২২
বারাসাত গণহত্যার মাত্র দুই মাসের মধ্যে আরো একটি পৈশাচিক গণহত্যার সাক্ষী হয়ে রইলো ডায়মন্ডহারবার। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবারে গঙ্গার তীরে ছয়টি মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, নিহতরা ডাকাতি করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু একটি বাংলা দৈনিক জানিয়েছিলো, নিহতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি বা ফৌজদারি অপরাধের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিহতদের রাজনৈতিক বিশ্বাস কাজ করেছিলো বলেই সবার অনুমান।২৩ তেমনই আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় ১ জুন কোন্নগর হত্যাকাণ্ড, যেখানে নয় জনের মৃত্যু প্রকাশ্যে আসে।২৪ তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের বরানগর কাশিপুর গণহত্যা। কংগ্রেসী গুন্ডারা পুলিশের সাহায্য নিয়ে নকশালপন্থিদের ওপর নারকীয় গণহত্যা চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। গণহত্যার এই বীভৎস প্রক্রিয়া শুরু হয় ১২ আগস্ট এবং তা ১৪ আগস্ট সকাল পর্যন্ত চলেছিলো। একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক জানিয়েছিলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর বলি হয়ে দেড়শো জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। এই গণহত্যার পেছনে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এম-এর ভূমিকাও ছিলো নিন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে ‘Frontier’ সাপ্তাহিক লিখেছিলো,
the Baranagar people know that the CPM cadres who had in the past made and strategic retreat from the area of operation, presumably due to Congress threat where allowed to come back and they held the Congress (R) killers to flush out the extremists.25
বরানগর-কাশিপুর গণহত্যা সম্পর্কে একটি বাংলা দৈনিক তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছিলো এভাবে-‘মোট কতজন যে খুন হয়েছে তার কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবই নেই। তবে অনেকগুলি লাশ যে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সংবাদ পুলিশের কাছে আছে।’২৬ নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের উদ্ভব, বিকাশ এমনকি চরম পরিণতি মৃণাল প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক উপলব্ধি থেকে ধরতে চেয়েছেন শ্রেণিসংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও পরিণতির পরিবর্তনশীল চরিত্রকে, যা থেকেই ১৯৬০-৭০ এর দশকে তার নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো ছিলো সংগ্রাম ও শিল্পের যৌথ বহিঃপ্রকাশ।
চার.
১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী মুক্তি পায়, সেই বছরের ২১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছিলো মৃণাল সেনের প্রথম চলচ্চিত্র রাত-ভোর। রাত-ভোর গাঢ় আবেগঘন এক সামাজিক চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের কাহিনি এক তরুণের আর্থ-সামাজিক লড়াই ও বাস্তব জীবনের কঠিন পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম, প্রেম, হতাশা এবং নতুন জীবনের সন্ধান করার প্রচেষ্টাই এর বিষয়বস্তু। পিতৃহারা লোটন মাকে নিয়ে থাকে কাকার সংসারে। নিকট আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে দিনযাপন করলেও অভাব-অবহেলা সর্বস্ব জীবনে লোটন একদিকে প্রাণবন্ত, অন্যদিকে লাঞ্ছিত শ্রেণির প্রতিচ্ছবি। ঘটনাক্রমে জমিদার বাড়িতে যাত্রাপালার দিন চোর ধরা পড়লে, জমিদারের হুকুমে তাকে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু চোরের দুঃখময় দারিদ্র্য জীবনের সহজসরল স্বীকারোক্তি লোটনের কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই জমিদারের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই তিনি চোরকে ছেড়ে দেন। ন্যায়-অন্যায় যাইহোক, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদারের হুকুম যে গ্রামের আইন তা বিস্মৃত হননি নির্মাতা, তাই জমিদারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে লোটনের গ্রাম ছাড়ার ঘটনাকে তুলে ধরেন পর্দায়।
ঘটনা পরম্পরায় লোটনের কলকাতা শহরে আসা এবং যুবকের আশ্রয়দাতার পরিবার কর্তৃক ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা ও অসম্মান তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে তিনি ফিরে যেতে চান পুরনো ঠিকানায়। কিন্তু মালিকের নিষেধ ও আর্থিক শূন্যতা সে পথের বিরাট বাধা। তবে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন জীবনের স্পৃহা সমস্ত শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে মায়ের কোলে ফিরে আসার জন্য সামান্য অর্থ জোগানের লক্ষ্যে চৌর্য পথ বেছে নেন লোটন। চলচ্চিত্রের শেষে সব বিষয় জানাজানি হলে খোঁজ পড়ে লোটনের, ততোক্ষণে তিনি জ্ঞাত পরিসরের বাইরে। মৃণাল রাত-ভোর চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্কট, শ্রেণি বৈষম্য এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের গল্প তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটিতে ইতালীয় নব্য-বাস্তববাদের ধারণা ও প্রভাব পরিলক্ষিত, যা পরবর্তী সময়ে মৃণালের চলচ্চিত্রে গভীরভাবে প্রতিফলিত।
যদিও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এই চলচ্চিত্র দর্শকমহলে সাড়া তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে মৃণালও এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘রাত-ভোর খুবই খারাপ ছবি। এইটি ছবিই নয়। এ যেন মোটামুটি ভদ্রজীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং করতে চান এমন একজন লোক কোনো এক বেয়াড়া সময় যদি কুখ্যাতপল্লীতে চলে যান, তাহলে সেটা যেমন তিনি ভুলতে চান, আমার কাছে এই ছবিটির ব্যাপারও সেরকম’।২৭
প্রথম চলচ্চিত্রে তেমন সাড়া ফেলতে না পারায় অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন মৃণাল। পরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের২৮ হাত ধরে ফিরে এসেছিলেন নীল আকাশের নীচে চলচ্চিত্রে। এক আন্তর্জাতিক আত্মীয়তাবোধ এই চলচ্চিত্রের মূল প্রেরণা। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসন্তী নামের এক নারী ও চিনা ফেরিওয়ালা ওয়াং লু। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতে চিনা সিল্কের কাপড় বিক্রি করতে আসা এই চিনা ফেরিওয়ালা গল্পের কোনো এক মোড়ে বাসন্তীর মধ্যে খুঁজে পান নিজের দিদিকে। ভিনদেশি যুবক ধীরে ধীরে এদেশের সঙ্গে, এদেশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। যার চরম পরিণতি নেমে আসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক হওয়ার মধ্য দিয়ে। গল্পের বিষয়কে নির্মাতা অবশ্য ‘মেমোয়ারস’ অর্থাৎ স্মৃতিকথা বলেছিলেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নীল আকাশের নীচের চিত্রনাট্য যখন তিনি লিখেছেন, তখন খুব সচেতন হয়েই লিখেছেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষ তথা কলকাতার সামাজিক চিত্র, লবণ সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ। এই রকম প্রেক্ষাপটে চিনা ফেরিওয়ালার সঙ্গে এক ভারতীয় নারীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানেই নাটকের আখ্যান আরম্ভ। দেশে তখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে। চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যে ধ্বনিত হয়-‘১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মুক্তি উন্মুখ অশান্ত কলকাতা। সারাদেশে তখন শিকল ভাঙা পথ। দিনগুলো ভোলবার নয়, আর ভোলবার নয় চিন দেশের এক অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষ শহরের রাস্তায় যার পায়ের চিহ্ন কবে হারিয়ে গেছে। ইতিহাসের নায়ক না হয়েও যার জীবন সুতোয় জড়িয়ে গেছে সেদিনের সেই অস্থির দামাল দিনগুলো’।
সংলাপে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ-রাজনৈতিক ভাষা। মনে রাখার বিষয়, চলচ্চিত্রটি যখন মুক্তি পায়, তার কয়েক বছর আগেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ ভারত-চিন ‘পঞ্চশীল চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিব্বতকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে দুই দেশের তরজা। চিনা আক্রমণে তিব্বত থেকে দালাইলামা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, ভারত-চিন সম্পর্ক এ সময় অন্য ইতিহাস লিখছে। এই সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে চিনা ফেরিওয়ালা ওয়াং-লুকে কেন্দ্র করে নীল আকাশের নীচে মুক্তি দেওয়াকে ভালোভাবে নেয়নি ভারত সরকার। বেঁধে দেওয়া হয় নিষিদ্ধতার বলয়ে। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিলো। এহেন পরিস্থিতিতে এমন চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে মৃণালের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ। মৃণাল স্বয়ং স্বীকার করেন,
ছবিটি সেন্টিমেন্টাল। ছবির কাঠামোতেও অনেক গণ্ডগোল আছে, কিন্তু এর রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে তিনি এখনও একমত। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মূলত এক। আমার এখনও মনে হয় আমার চিন্তাধারা ভুল ছিল না।২৯
পাঁচ.
১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃণাল নির্মিত তৃতীয় চলচ্চিত্র বাইশে শ্রাবণ। এখানেই ছকভাঙা মৃণালকে পাওয়া গেলো প্রথমবার। বাইশে শ্রাবণ-এ দ্বিতীয় চলচ্চিত্রের চিনা ফেরিওয়ালার চরিত্র ফিরে এলো দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙালি যুবকের মধ্য দিয়ে। সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রটি একটি পারিবারিক গল্প-স্বামী-স্ত্রীর জীবনসংগ্রামের গল্প। ৫০-এর মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত বাইশে শ্রাবণ। মন্বন্তর পরিস্থিতিতে মানুষের ব্যক্তিজীবনে সম্পর্কের ভাঙাগড়া, তার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব, ন্যায়-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দোলাচল অবস্থা এবং সর্বোপরি মানবতাবাদের অনিশ্চিত নবজাগরণ এই চলচ্চিত্রের মূল প্রতিপাদ্য। রেলগাড়িতে প্রসাধনী পণ্য ফেরি করে ফেরা মাঝবয়সি সরল চরিত্রের প্রিয়নাথ সাংসারিক কর্তব্য পালনের তাগিদে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে স্বল্পবয়সি তরুণী মালতীর সঙ্গে। অসম বয়সি সুখী দাম্পত্য জীবনে দুঃসময় নেমে আসে জীবনের ভার ও মাতৃহারা শোকের ব্যাকুলতা থেকে। বয়সের ভারে কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় পিছু হঠতে থাকা প্রিয়নাথ যখন আরেক আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিজের একটি পা খুইয়ে কর্মহীন হয়ে গৃহে ফিরে আসেন, ঠিক তখনই জীবন পরীক্ষা নিতে চায় মন্বন্তরের সঙ্কটে। অনাহার এবং অবসাদে বিষণ্ন হয়ে পড়ে সম্পর্কের উচ্ছ্বাস, গতি হারিয়ে ফেলে দাম্পত্য জীবনের প্রাণময়তা। তিন দিন অনাহারে থাকার পর প্রিয়নাথ একটু চাল জোগাড় করে আনে কোনোমতে। ভাত রেঁধে মালতী একটু একটু করে প্রায় সবটুকুই তুলে দেন প্রিয়নাথের পাতে। প্রাণপণে ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত প্রিয়নাথ স্মরণে রাখতে ব্যর্থ হন স্ত্রীর জন্য কিছু ভাত অবশিষ্ট রইলো কিনা! স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকা নীরব মালতীর তীক্ষè দৃষ্টিতে বোধহয় ক্ষোভ আর ঘেন্না ছাড়া কিছুই ছিলো না। তাই তো যেটুকু ভাত হাঁড়ির তলায় পড়েছিলো সেটুকু পাতে নিয়েও মুখে ওঠেনি তার; আবার হাঁড়িতে নামিয়ে জল দিয়ে রেখে দেন প্রিয়নাথের জন্য। অনাহার নয়, দারিদ্র্যও নয়, প্রিয়নাথের এই বদলে যাওয়া, এই স্বার্থপর হয়ে ওঠাই ব্যথিত করে মালতীকে। স্বামীর থেকে কিছু না পাওয়া মালতীর আফসোস এক বিশেষ মুহূর্তে প্রকাশ পায় চরম সত্য হয়ে। এই সত্যের উপলব্ধিই তাকে নিঃসঙ্গ করে, হতাশ করে, ঠেলে দেয় আত্মহত্যার পথে। ইতিহাসকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে নির্মাতা মৃণাল মন্বন্তরকালীন মনুষ্য জীবনে যে বিপর্যয়ের ছবি অঙ্কন করেন তা আদতেই জ্বলন্ত ইতিহাস। তবে ইতিহাসকারের ভূমিকা পালন করতে তিনি চাননি। তার সৃষ্টি এখানে রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক পরিহাস। বাইশে শ্রাবণ সম্পর্কে মৃণাল সেন বলেন,
বাইশে শ্রাবণ করতে গিয়ে গ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্য আমাকে একেবারেই টানেনি ... মানুষের উপরেই ফোকাস রাখা হয়েছে। ... মহিলা এবং একজন পুরুষের সম্পর্ক এই পুরুষশাসিত সমাজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এই সম্পর্কটা আরও ইন্টারেস্টিং হয় যদি তারা বিবাহিত হয় কেননা আমাদের সমাজে এত ট্যাবু এত লিমিটেশন সেখানে প্রি-ম্যারিটাল সম্পর্ক কখনো একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে পারে না, কোন ডাইমেনশন আনতে পারেনা অন্তত সে যুগে তো নয়ই তাই পোস্ট ম্যারিটাল সম্পর্ক ধরেছি। সে কারণেই আমি এক বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এক্সামেন করতে গেলাম কোন সোসাইটিতে না পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে মেয়েরা কমোডিটি ছাড়া কিছু নয়। সেখানে মেয়েরা পারসিকিউটেড সেটাকে আরো আন্ডারলাইন করার জন্য আরও একটু ইন্টারেস্টিং করবার জন্য আমরা বয়সের ডিফারেন্স বাড়িয়ে দিলাম। তাদের এই সম্পর্ককে নতুন আর এক ডাইমেনশন দেবার জন্য তাদের এনে ফেললাম এক ভয়ঙ্কর অবস্থায়, দুর্ভিক্ষের সময়ে। এই সম্পর্ক কি এক্সামেন করতে গিয়ে আমি তারা যে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, সমাজের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার সম্পর্ককেও কতকগুলি কমেন্ট রাখার চেষ্টা করেছি। বাইশে শ্রাবণ সম্পর্কে আমি যখন নতুন করে ভাবি, ভাবতে চেষ্টা করি ,তখন আমি পার্টিকুলারলি এই ছবিটি সম্পর্কে বেশ উৎসাহিত বোধ করি।৩০
নির্মাতার রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের দক্ষতা এখানেই-অতিসাধারণ প্রণয়োপাখ্যানটিতে ইতিহাসের অমঙ্গলকে পারিবারিক বিস্তারের মধ্যে উৎকীর্ণ করেছেন। স্পেক্টাকেলের বিরুদ্ধে দৈনন্দিনকতা আধুনিক চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এটা। একটি তুচ্ছ দম্পতির তুচ্ছতর মিলনরজনী কীভাবে পরিবার, প্রেম বা দাম্পত্য জাতীয় ধারণাগুলোকেই আপেক্ষিক প্রমাণ করলো, তার অন্যতম নিদর্শন এই চলচ্চিত্র।
দ্বিতীয় পর্ব.
ছয়.
মৃণাল সেন তার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ‘ক্যালকাটা ট্রিলজি’ বা কলকাতা ত্রয়ীর চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করেন ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই ত্রয়ীর চলচ্চিত্রগুলো হলো-ইন্টারভিউ (১৯৭১), কলকাতা ৭১ (১৯৭২) ও পদাতিক (১৯৭৩)। এই তিনটি চলচ্চিত্রের মধ্যে রাজনৈতিক ভাষা স্পষ্ট। প্রতিটিতেই দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইন্টারভিউ ক্যালকাটা ট্রিলজির প্রথম চলচ্চিত্র। বেকারত্বের সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই চলচ্চিত্রের পথ চলা। নির্মাতা এতে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভঙ্গির দিকে দিক নির্দেশিত করেন। চলচ্চিত্রটিকে দেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করার অন্যতম প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ইন্টারভিউকে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বলার মূল কারণ হলো, এর চরিত্ররা নিছক ব্যক্তি চরিত্র নয়, তারা সমাজের বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধি। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রঞ্জিত মধ্যবিত্ত যুবকের প্রতিনিধি, তার ওপর অর্পিত পরিবারের দায়িত্ব।
ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য চরিত্রটির বাস্তব সংগ্রামকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে; পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে ক্ষমতাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ। অন্যভাবে বললে সমাজে উপরের দিকে আসীন ব্যক্তিদের পুরুষালি মানসিকতার ছবি। এ কথা ঠিক যে, ’৬০-এর দশকের শেষের দিকে কলকাতা শহর থেকে বৃটিশ আমলের নানা কলা সামগ্রী নিজেদের অস্তিত্ব হারাচ্ছিলো, অথচ শহরের এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের চলনে-বলনে ও রুচিতে আরো বেশি করে সাহেব হয়ে উঠতে তৎপর ছিলো। ক্রমশ সমাজে ঔপনিবেশিক মানসিকতার মোহভঙ্গের ছবি ফুটে উঠতে থাকে। ইন্টারভিউ-এ দেখা যায়, তরুণ রঞ্জিতকে চাকরির ইন্টারভিউয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটা স্যুট জোগাড় করতে হবে এবং সেই স্যুটটি তার চাকরি পাকা করে দেবে। কিন্তু ব্যান্ডবক্সে পরিষ্কার করতে দেওয়া স্যুটটি তরুণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়, কারণ ইন্টারভিউয়ের দিন তিনি জানতে পারেন ব্যান্ডবক্স লকআউট করেছে মালিকরা। কবে খুলবে ঠিক নেই। তখন রঞ্জিত বিহ্বল! হতাশা নিয়ে তিনি প্রথাগত বাঙালি পোশাকে (ধুতি-পাঞ্জাবি) ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হলে, চাকরিটি হাতছাড়া হয়ে যায়। স্যুটের পেছনে ছুটতে ছুটতে দিশেহারা হতাশাগ্রস্ত তরুণ একদিন প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন।
এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে মৃণাল ধীর ভঙ্গিতে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব সমকালীন ভারতবর্ষ থেকেই মুছে যায়নি এবং তা দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য ও উন্নয়নের পথে বিরাট এক বাধা। স্বাধীন ভারতের নয়া শাসনও যে আধা ঔপনিবেশিকতা পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে আছে, সেই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন নির্মাতা। তিনি এমন একটা সময়ের কথা বলছেন, যখন সমাজ নষ্ট মানুষের কুক্ষিগত, যখন যোগ্যতার চেয়ে বাহ্যিক চাকচিক্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর দরকার ক্ষমতাশীলদের লেজুড়বৃত্তি। মৃণালের বামপন্থি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, যখন ব্যান্ডবক্স কোম্পানি বন্ধ হওয়ার খবর দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে কাট করে মৃণাল এক নতুন ব্যাপার দেখান-গল্প চলে যায় ডকুমেন্টারিতে কাল্পনিক দৃশ্য-দেখা যায় মোটাসোটা মালিকরা পথে মিছিল করছে। স্যুট-টাই পড়ে তারা বলছে- Capitalist of the world, unite!! কাল মার্কস-এর কথাটি উল্টে মালিকদের নিয়ে এই দৃশ্য কল্পনার অভিনবত্বকে প্রকাশ করে। ৭০-এর দশকে শিক্ষিত সমাজের বেকারত্ব, সামাজিক টানাপড়েন, হতাশা, দারিদ্র্য সর্বোপরি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভয়াবহতাকে চলচ্চিত্রের পর্দায় মৃণাল ফুটিয়ে তোলেন। তবে শেষে চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতার সঞ্চার করে ইতিহাসের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন নির্মাতা, এখানেই তার সৃষ্টির অভিনবত্ব! এই পাথর ছোড়ার কাজটি হয়ে ওঠে বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের প্রতীক। চলচ্চিত্রের এই শেষাংশটিতে মৃণাল সংক্ষেপে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনকে ছুঁয়ে গেছেন।
ইন্টারভিউ তার বিষয়বস্তু ও শৈলী দুইয়ের জন্যই সমাদৃত হয়েছে। এর আগে কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রে চরিত্রকে সরাসরি দর্শকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়নি। এই প্রথম মৃণাল মঞ্চের দেয়াল ভেঙে দর্শকের সঙ্গে কথা বলার ব্রেখটিয় তত্ত্বকে হাতেকলমে প্রয়োগ করলেন। ফলত দর্শকের ‘কল কর্নার’ দেয়ালও বাস্তবতই ভেঙে পড়ে। শেষ দৃশ্যে পাথর দিয়ে ম্যানিকুইন ভাঙার দৃশ্য নিঃসন্দেহে ৭০-এর বিপ্লবের আগুনের আঁচ। তাই তো মূর্তি ভাঙার পরেই ধ্বনিত হয় ‘ইনকিলাব’ এবং দৃশ্য চলে যায় কোনো আন্দোলনের উত্তাল অংশে। ইন্টারভিউ অনন্য এখানেই যে, সেদিনের চলচ্চিত্রটি সেদিনের কথাই বলেছিলো। নির্মাতার নিজের কথায়, ‘... আজকে বুদ্ধি বেড়েছে, সময় অনেক জটিল হয়েছে এবং ইন্টারভিউ এ যে প্রশ্নগুলি এসেছে সেগুলো জরুরী হয়ে উঠেছে। সময়ের ধাক্কায় এবং সে কারণেই মনে হয় ইন্টারভিউ ছবিটি যে সময় করা উচিত ছিল, সেই সময়টাতে আমি ইন্টারভিউ করেছি’।৩১
সাত.
১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় কলকাতা ৭১। ইন্টারভিউ-এর ঠিক পরের চলচ্চিত্র। এ কথা নির্মাতা নিজেও স্বীকার করেন-ইন্টারভিউ যেখানে শেষ সেখানেই প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয় কলকাতা ৭১-এর।৩২ ইন্টারভিউ-এর ব্যক্তি সমস্যা এখানে সাধারণ সমস্যায় উপনীত হয়। চলচ্চিত্রে অসহনীয় দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহাসিক চিত্র প্রতিফলন হয়। কিন্তু ভঙ্গির আঙ্গিকে তা আগের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে কলকাতার পাঁচ দশকের খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে পাঁচটি ভাগে। শুরু হয় ’৪৩-এ আর শেষ হয় ১৯৭১-এ। গত পাঁচ দশকের সমগ্র কলকাতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বাস্তব চিত্রকল্পের ছোটো ছোটো অংশ দর্শকের সামনে উঠে আসে। নির্মাতা আখ্যান ভেঙে সময়ের টুকরো টুকরো অংশের মধ্য দিয়ে সমগ্রতায় পৌঁছে যান। একটি ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে দর্শক ক্রমাগত আরেকটি ঘটনার সম্মুখীন হয়। দর্শকের চেতনা-চিন্তনে আঘাত হানতে থাকেন মৃণাল।
চলচ্চিত্রের শুরুতে এক কথকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, আর দেখা যায় কিছু মন্তাজ; তারপর চিত্রিত হয় তিন বাঙালি সাহিত্যিকের তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের গল্প। গল্পগুলোর সময় কাল আলাদা-১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩। নিজের আগেরকার সমস্ত ছবির থেকে ভিন্ন পথে হেঁটে মৃণাল এই চলচ্চিত্রে এক তরুণ কথকের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেন। তিনি কথা বলে চলেছেন দারিদ্র্য, শোষণ ও মৃত্যু নিয়ে, কিন্তু বিশেষ কোনো সময়ের উল্লেখ ছাড়াই। এই বিশেষ পদ্ধতিটির মাধ্যমে মৃণাল চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুকে সময়ের বন্ধন থেকে ছিন্ন করে তাকে করে তুলেছেন সর্বকালীন ও সর্বজনীন। এই চলচ্চিত্রে তিনি সংবাদচিত্র বা নিউজ গোত্রের বিভিন্ন ফুটেজ ব্যবহার করেছেন এবং তার ফলে এতে তথ্যচিত্রের আদল ফুটে উঠেছে। মৃণাল একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, সামাজিক ক্রোধ কী করে এই পর্যায়ে পৌঁছলো, তার কারণ বোঝা প্রয়োজন। যে সামাজিক ক্রোধ ও বিক্ষোভ কলকাতা শহরকে অধিকৃত করে ফেলেছিলো তার একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে। এ ঘটনা নিছক একদিনে ঘটেনি। তাই সেই ক্রোধের শিকড় সন্ধানের জন্য এই চলচ্চিত্রে মৃণাল দশকের পর দশক পিছিয়ে গিয়ে পথ পরিক্রমা করেছেন। একদিকে ক্রোধান্ধ নৈরাজ্য আর বিপ্লবী আবেগ, অন্যদিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব-এই দুইয়ের ওপর ভর করে চলচ্চিত্রটির সমালোচনা চলতে থাকে। তিলোত্তমার বুকে তখন ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব, শহরের অলিগলিতে তখন বিপ্লবী রাজনীতির দারুণ দাপাদাপি। সমাজ পরিবর্তনে উৎসর্গীকৃত তাজা ফুসফুসগুলোতে বেয়োনেট বৃদ্ধি করতে পথে-রাজপথে চলছে কম্বিন অপারেশন। আতঙ্কিত শহর আবার রক্তাক্ত পরিবর্তনের আনন্দে।
ইন্টারভিউ চলচ্চিত্রের শেষে কাচের দেয়াল ভেঙে ফেলার দৃশ্যটির সূত্র ধরে শুরু হয় কলকাতা ৭১। এর প্রথম গল্পের বিষয় বর্ষার দুটি রাত এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের কাহিনি। চলচ্চিত্রের এই অংশে নির্মাতা আর্থিক অবস্থার সঙ্গে অসহায়ত্বের যোগসূত্রের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। নীলমণি (পরিবারের কর্তা) হতাশা ও বিরক্তির দোলাচলের মধ্যে একটি কুকুরকে তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন। অবশেষে পরিবারটি উদ্বাস্তুর মতো অন্য এক আশ্রয়ে উঠে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে নীলমণি দেখে কুকুরটি আগে থেকে সেখানে খানিকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। অতএব এবার কুকুরের সঙ্গে অবস্থান পরিবর্তন করে নতুন আশ্রয় খোঁজা ছাড়া নীলমণির আর কোনো উপায় নেই। এ কাহিনিতে মৃণাল নিষ্ঠুরতা, মানবিকতার অবক্ষয় ও গরিব মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের প্রতি নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত ও নৈতিক, খানিকটা স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের ক্রোধী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়; সমবেদনা যুক্তিসঙ্গতভাবেই শ্রেণিগত জোটে পরিণত হয়। আর এই অর্থেই চলচ্চিত্রটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক।
দ্বিতীয় কাহিনিতে দারিদ্র্যের চিত্রায়ণ ঘটেছে, কিন্তু এই গল্পটির মূল বিষয়বস্তু দারিদ্র্যের ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই গল্পটিতে মৃণাল দিল্লিবাসী একটি চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন, বহু বছর ধরে তিনি বাংলা ছাড়া। বাংলাদেশে ফিরে তার আত্মীয়ের বাড়িতে দেখা করতে এসে তিনি বঙ্গ জীবনের প্রবল দারিদ্র্য ও কঠোর দুর্দশার কথা উপলব্ধি করেন। দারিদ্র্য যে মানুষের মনুষ্যত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে অসহায় করে তোলে, সেই নিষ্ঠুর ও পরীক্ষিত সত্যই তিনি নতুন করে উপলব্ধি করেন। এহেন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ব্যক্তিমানুষের সামনে খোলা থাকে না-এমন বক্তব্যই প্রকাশ করা হয়েছে।
চলচ্চিত্রের তৃতীয় কাহিনিটি গৌরাঙ্গ নামে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ১৫ বছরের এক কিশোরের। সে নিজেই তার পরিবার চালায়। প্রথম দুটি গল্পের চরিত্ররা পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করলেও গৌরাঙ্গ কিন্তু তা করে না। ট্রেনের কামড়ায় এক স্বাস্থ্যবান যাত্রীর হাতে বেধড়ক মার খেয়েও সে হার স্বীকার করে না এবং অবশেষে প্রতিশোধ নেয়।
এই গল্পটির পর মৃণাল দর্শককে নিয়ে যান ১৯৭১-এর কলকাতায় উচ্চবর্গের এক পার্টিতে। যেখানে psychedelic আলো এবং আনন্দ শংকরের pop music চমৎকার স্থানিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এরপরই পার্টিতে নেশাগ্রস্ত এক রাজনীতিবিদ তার বংশধরদের সামনে দারিদ্র্যের ফলাফল নিয়ে বক্তৃতারত-এই কথোপকথনস সঙ্গে দুর্ভিক্ষের ছবির দ্বান্দ্বিক অবস্থান। ব্যাপারটা ভিজ্যুয়ালি খানিকটা ইন্টারেস্টিং, মেয়েদের আইসক্রিম খেতে চাওয়ার সঙ্গে কাট করে রিফিউজিদের অমানসিক দুর্দশার দৃশ্যের দ্রুত ট্র্যাকিং বেশ কার্যকরী। চলচ্চিত্রের এই অংশটি দর্শককে সব থেকে বেশি নাড়া দেয় এবং অস্বস্তির সম্মুখীন করে। এই অংশটি টুকরো টুকরো এবং বার বার বাধাগ্রস্ত-রাজনীতিবিদের বক্তৃতাটি প্রায় স্বাগত সংলাপ, তার পাশাপাশি পর্দায় ভেসে ওঠে ক্ষুধার শিকার কঙ্কালসার মানুষের ছবি; তাই জনতার আক্রমণাত্মক বিক্ষোভ ও পুলিশী দমন পীড়নের নিউজ রিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপ্লবী আন্দোলনবিষয়ক তথ্যচিত্রের ফুটেজ, হত্যার রাজনীতি ঘোষণা করে রাজনৈতিক দেয়াল লিখন-এমনকি ইন্টারভিউ চলচ্চিত্রের সেই ম্যানিকুইন ভাঙার দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্য।
বিভিন্ন দৃশ্যবস্তুর এই কোলাজ করে প্রকৃতপক্ষে দর্শককে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকাতে বাধ্য করা হয়েছে। যে ইতিহাস দারিদ্র্যের, বঞ্চনার ও শোষণের। চলচ্চিত্রের শেষে দেখা যায় বিক্ষোভস্থলে পুলিশের হাতে নিহত কুড়ি বছরের তরুণটির মুখে রক্ত। মৃণাল এই গোটা অংশটিকে সাজিয়েছেন থিয়েটারের মতো করে। তরুণটি এখানে সরাসরি দর্শকের সঙ্গে কথা বলে এবং গোটা পর্দাজুড়ে কালো পটভূমিকায় শুধু তার মুখটি দেখতে পাওয়া যায়। ওই তরুণ স্পেকটেটরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে-‘আমাকে কে গুলি করেছে আমি জানি কিন্তু বলবো না, আপনারা সাফার করুন যতোদিন না আপনারা তাকে খুঁজে বের করতে পারেন’। এ যেনো দর্শকের কাছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার আহ্বান। দর্শকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, নির্মাতা শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু সরাসরি চিনিয়ে দিতে চাইছেন না। এখানে মৃণালের বক্তব্য পরিষ্কার। সত্যকে চিনতে হবে আপনার চোখ দিয়েই এবং সেই চেনাটা হবে চেতনার চোখ দিয়ে। অর্থাৎ মানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করবে তার শত্রুকে। নির্মাতার কাজ হচ্ছে এই যোগাযোগটা করিয়ে দেওয়া।৩৩ মূল চরিত্রের স্বীকারোক্তির ফাঁকে ফাঁকে নির্মাতা আবারও তথ্যচিত্রের ঢঙে গণপ্রতিবাদ, হত্যা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ছবি দেখাতে থাকেন। কলকাতা ৭১-এ তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন দশকব্যাপী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখানে তিনি শত্রুকে চিহ্নিত করতে এবং শোষণ অত্যাচারের হাতিয়ারগুলোর বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম। আলোচ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ প্রসঙ্গে মৃণালের নিজের ভাষ্য এমন-
... সেদিক থেকে film is more of list of kind of an essayসেখানে আমার যেমন তিনটি মোদ্দা গল্প আছে, একেবারে পরিষ্কার গল্প সেখানে আবার আমি essayist -এর মেজাজে এই মিডিয়ামকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছি। এবং সে দিক থেকে কারুর ভালো লাগতে পারে, কারোর খারাপ লাগতে পারে। সেটা আলাদা কথা কিন্তু এটা করে আমি খুব মজা পেয়েছি। এবং ছবিটির সেই লাস্ট সিকুয়েন্সে ১৯৭১ এর সেই সিকুয়েন্সে যখন ফিরে আসছি, তখন আমি ফিজিক্যাল রিয়েলিটিকে রিডিং করতে পারিনি এবং চাইনি। Redemption of physical realityফিল্মের একমাত্র দায়িত্ব নয়। fragments of physical realityকে নিয়ে আমি আমার ইচ্ছামত একটা shape দিয়েছি আমার মানসিকতায় জমে এ রকম একটা shape দিয়েছি অর্থাৎ ফিজিকাল রিয়েলিটি থেকে খুচরো উপাদান সংগ্রহ করেছি টুকরো টুকরো অনেক বাচ্চাদের খেলনা যেমন পাওয়া যায় টুকরো টুকরো অনেক ব্লক যা দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে পারা যায় নানান ডিজাইনের বাড়ি অনেকটা সেই রকম কাজ। তাই করেছি এখানে, টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি ও শব্দ জোগাড় করেছি জুড়েছি নিজের ইচ্ছামত নিজের ইচ্ছামত একটা পৃথিবী তৈরি করেছি। তারপর নিজস্ব লজিক আমদানি করেছি পৃথিবীটাকে বাঁধতে অর্গানাইজড করতে কনভেন্সিং করে তুলতে বক্তব্যকে শক্ত করতে। এবং সবশেষে জেনেশুনেই খানিকটা ভেনজিন্স নিয়েও নেগেটিভ স্টাইলে ট্র্যাডিশন ভাঙতে। এই ব্যাপারটা আমি খানিকটা প্রচলিত ফর্ম ভাঙ্গার চেষ্টা থেকেও করেছি এবং আমি বিশেষ করে মনে করেছি যে, এভাবেই আমার বক্তব্যটাকে আমি অনেক powerfully বলতে পারব এটাই হচ্ছে কলকাতা একাত্তরের structural দিক সম্পর্কে আমার বক্তব্য।৩৪
মৃণাল সেনের কলকাতা ত্রয়ীর শেষ চলচ্চিত্র পদাতিক (১৯৭৩)। তখন নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রথম পর্ব আঘাত পেয়েছে। সেই পর্বেই বেরিয়ে এলো মৃণালের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। পদাতিক-এ নির্মাতা শোনালেন দারিদ্র্য, মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে চিৎকার করে ওঠা ‘আমি পথ চলেছি হাজার বছর ধরে, হাজার বছর ধরে দেখেছি শোষণের ইতিহাস’। বহুকাল ধরে অটল দাঁড়িয়ে থাকা শোষণের দেয়াল গুঁড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিচ্ছিলো তখনই বিপ্লব পথভ্রষ্ট হলো। সমাজটাকে কীভাবে বাসযোগ্য করা যাবে এবং সেটা করতে গেলে যে সামাজিক শোষণ, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজন, সেটা সবাই উপলব্ধি করলেও সঠিক পথ নির্দেশের জায়গাটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। অস্পষ্টতা, সম্ভাবনা ও ব্যর্থতার দোলাচলের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যে ফুটে উঠলো রাজনৈতিকতা ও শিল্পকর্মের অসাধারণ মেলবন্ধন। মধ্যবিত্ত চেতনাকে জাগানোর যে প্রয়াস মৃণালবাবুর ইন্টারভিউ ও কলকাতা ৭১-এ দেখা যায়, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো ৭০ দশকের কলকাতার রাজনীতির তরুণ বিপ্লবীদের এক প্রতীকী মূর্তি। ওই দুটি চলচ্চিত্র ধরেই কুড়ি বছর বয়সি যে তরুণটি দর্শককে প্রত্যক্ষ প্রশ্নে তাড়িত করে, পুলিশের তাড়ায় সরু গলি দিয়ে ছোটে, ময়দানে সুন্দর সকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে; পদাতিক-এ এই তরুণ বিপ্লবী তার দ্বিধা সংশয় নিয়ে কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। তার প্রতীকী নিবাস্তবতা ছেড়ে একেবারেই বাস্তবের জটিলতার আবর্তে এসে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক চলচ্চিত্র যখন এই জটিলতায় প্রবেশ করে, তখন তা থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়। রাজনীতি থেকে সরে থাকা মানুষদেরই কেবল লক্ষ না করে রাজনৈতিক কর্মীদেরও লক্ষ করে। সক্রিয় বিপ্লবী পালাচ্ছে বন্দুক হাতে পুলিশ তাকে বিনা বিচারে হত্যা করতে চায়। তখন পর্দায় খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা বিদীর্ণ করে হঠাৎ বেরিয়ে আসে বিপ্লবীর মুখ। সেই বিপ্লবী কোনোমতে ঢুকে পড়ে এক ফ্ল্যাটে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে। সেই ফ্ল্যাট একেবারেই যে বাস্তবতা থেকে এসে পড়েছিলো তার বিপরীত-অতি ভদ্র সুন্দর দামি আসবাবে সাজানো এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের যিনি মালিক তিনি নারী, তার ছোটোভাই কেরলে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রাণ দেয়। তার স্মৃতি ওই নারীর কাছে খুব পুণ্যের। ফলে পলাতক বিপ্লবী নায়ক সহানুভূতিশীল দিদির মতো একজনকে পায়। স্পষ্টই বোঝা যায়, বিপ্লবী ছেলেটি নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং পুলিশের গুলি থেকে বাঁচতে তিনি ওই অবাঙালি নারীর বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী।
তবে চলচ্চিত্রটি নৈরাশ্যবোধে শেষ হয়নি; ছেলেটির বাবাও বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে শরিক ছিলেন। একসময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে ছেলেকে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে বাবাকে দেখতে যেতে হয়। ছেলের আন্দোলনের কিছু সমালোচনা করলেও বাবা শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ করে বলেন, সাহসী হও। দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার মধ্যে নির্মাতা কতকগুলো প্রশ্নের সামনে দর্শককে দাঁড় করান, যা আজও প্রাসঙ্গিক। এই প্রাসঙ্গিকতাই ঠিক করে দেয় চলচ্চিত্রটির মূল কাঠামো। উত্তাল সময়ের জরুরি কিছু প্রশ্ন যেনো তাকে অস্থির করে তোলে। তিনি সবকিছুই ছুঁড়ে দিতে চান দর্শকের দিকে-
... আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম, যেভাবে এগোচ্ছি, সেটা বিচ্ছিন্নতার পথ। সে পথে আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। জনসাধারণের সমর্থন পাচ্ছি না। জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি আমরা পাচ্ছি না। জনগণকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলতে পারছি না। আমরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি, এ পথ মারাত্মক হয়ে পড়েছে, ক্ষতিকারক হচ্ছে এবং যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আরো জোরদার হয়ে উঠছে, এই পথে চললে আমরা শেষ হয়ে যাবো। সুতরাং এটা এখনই মেরামত করা দরকার। এই বিচ্ছিন্নতামুখী আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে হবে, আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে এবং এভাবে নিজেদের সমস্ত ভুলত্রুটি মেরামত করে আবার ঠিক পথে এগোতে হবে।
এটাই হচ্ছে গল্পের মূল কাঠামো। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, যারা সর্বহারা শ্রেণির জন্য লড়ছিলো তাদের হাত রক্তে লিপ্ত হলেও তাদের দেহ ও মন ছিলো মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে জারিত। সেই মূল্যবোধে বেশ বুর্জোয়া গন্ধও ছিলো। বিশেষ করে অনর্থক রক্তপাত, হত্যা-এমন সব মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, যারা সঠিক অর্থে শ্রেণি শত্রু ছিলো না। অন্যদিকে আসল পুঁজিপতি প্রায় নিধন হয়নি। পদাতিক-এর মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের মূলগত সেইসব সমস্যার কথা নির্মাতা নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন।
চলচ্চিত্রটি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থক। এক্ষেত্রে তা দুনিয়াজুড়ে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি ও সমর্থন দেয়। জনগণের বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতিগত পার্থক্যের মধ্যে সেতু নির্মাণের জন্য নির্মাতা এখানে জনতার যৌথ সংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্তের শট্কে পাশাপাশি সাজিয়েছেন। তাই কলকাতার রাস্তায় তরুণ ছাত্রদের প্রতিবাদের দৃশ্যের পরেই চলে আসে মার্কিন বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে এশীয় যুব সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের দৃশ্য। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামের উল্লেখ মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রজুড়ে বিভিন্ন মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদদের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়।
আট.
আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য শুধু জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান নেওয়াই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা পরস্পরের থেকে দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন পরিসরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার প্রয়াসী। এবং এই বন্ধুত্বের ভিত্তি অবশ্যই দরিদ্র ও শোষিত মানুষের অধিকার এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।
পদাতিক-এর নারী চরিত্রটির মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নারীদের একটি সমীক্ষা হাজির করা হয়েছে এবং লিঙ্গ সাম্য, মেয়েদের অধিকার ও ন্যায় বিচারের প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। সংহতি বলতে এখানে নির্বিচারে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সংহতির কথা বলা হচ্ছে না। তাছাড়া বিশ্বস্তরের চিন্তা কোনোভাবেই স্থানীয় সমস্যাগুলোর গুরুত্বকে খাটো করে দেবে না। আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তা বরং এমন একটি পরিবেশের জোগান দেবে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিষয় ও পরিস্থিতি হিসেবে দেখা সম্ভব। যেমন এই চলচ্চিত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম নারী-পুরুষের লিঙ্গ সাম্য ও তাদের আপেক্ষিক সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন। এর সঙ্গে জড়িত নারীর ওপর পুরুষের হিংসা এবং পুরুষ যেখানে নারীদের জীবন, উপার্জন ও শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে সে প্রশ্ন। বর্তমানের সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে চলচ্চিত্রে কলকাতা শহরের রাস্তায় যেসব প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও শিক্ষার্থীদের দেখা যায়, তারা প্রায় সবাই পুরুষ। এর থেকে ধারণা করা যায়, আলোচ্য পরিস্থিতিতে বিপ্লবী শ্রেণিটি গড়ে উঠেছিলো একচেটিয়াভাবে পুরুষদের নিয়েই-এখানেও প্রশ্ন তুলতে সক্ষম পদাতিক। পদাতিক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মৃণাল স্বয়ং বলেন এভাবে-‘পদাতিক সবচেয়ে বেশি পলিটিকাল ফিল্ম বলে আমার কাছে মনে হয় সে দিক থেকে। কারণ সেখানে কিন্তু আমি পদাতিকের কথা বলতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির যে দুটো ভাগ, তারপর আরেকটা ভাগ হল, সেই প্রশ্নগুলো এসে গেছে। সেগুলো নিয়ে বেশ কিছু রসঢ়ড়ৎঃধহঃ কথা আমি বলেছি’।৩৫
নয়.
পদাতিক-এর পরবর্তী চলচ্চিত্র কোরাস (১৯৭৪)। কলকাতা ত্রয়ীকে মোটাদাগে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ত্রয়ী বলা হলেও কোরাসকে বাদ দিলে আগের তিনটি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। আসলে তিনি চৌকো চলচ্চিত্র বানিয়েছেন, যেটার শেষ বিন্দুটির নাম কোরাস। এই চলচ্চিত্রেই তিনি নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়া পেশ করেছেন। এতে চলচ্চিত্র নির্মাণের টেকনিক নিয়ে অনেক অভিনব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। নিউরিয়ালিজম ও ডকুমেন্টারি ধারার আঙ্গিকে মেলাতে চেয়েছেন তার সৃষ্টিকে।৩৬ কোরাস শুরু হয় কীর্তন দিয়ে। ছড়াগুলো রূপকাশ্রিত। সেই রূপকে আছে দারিদ্র্যকে আড়াল করতে ধর্মের দোহাই দেওয়ার কথা বা অন্যভাবে বললে, দারিদ্র্যের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপের ছলনা। কীর্তনের মধ্য দিয়েই দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় একটি দুর্গের সঙ্গে। যেখানে চেয়ারম্যান আছেন, আর আছে তার বোর্ড অব ডিরেক্টর্স। প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০০ জন লোক দরকার। এজন্য দরখাস্ত পড়েছে ৩০,০০০। এখন এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে কোন উপায়ে নিয়োগ দেওয়া হবে, নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করার পদ্ধতিইবা কী হবে, এটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান চেয়ারম্যান ও বোর্ডের সদস্যরা।
এরই মধ্যে দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ সারি পড়ে যায় দুর্গের বাইরে। চাপের ভেতর পড়ে যায় কর্তৃপক্ষ। হিমশিম খায় নিরাপত্তাকর্মীরা। বেলা যতো গড়াতে থাকে ততোই চাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু এতো লোককে কী করে সামলানো যাবে, সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করতে না পারায়, দরখাস্ত জমা নেওয়া মুলতবি রাখা হয়। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে দরখাস্ত জমা দিতে আসা অজ্ঞাত মানুষের ভিড়। অপেক্ষারতদের ক্ষোভ প্রশমন করতে ফাটানো হয় কয়েকটি বোমা, প্রহরীরা চালায় লাঠি, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে সবাই। সাংবাদিক ছুটে আসে। তার দরকার খবর। কে পড়লো, কে মরলো, কে বাঁচলো, সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো ধরনের একটা ‘গণ্ডগোল’ হচ্ছে, সেটাই বড়ো ব্যাপার। কারণ পত্রিকার সম্পাদকও মনে করেন তাদের দরকার ‘সেনসেশন’। বেকারত্বের কারণে মর্মন্তুদ এই ঘটনার খবরটি যেনো লোকে খায়, সেজন্য আবেদনকারীদের আলাদা আলাদা করে সাক্ষাৎকার নেয় সাংবাদিক। সুনিপুণভাবে ওই দশকে বেকারত্ব, হাহাকার, হতাশা, দুর্দশার পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভয়াবহতাকে তুলে ধরা হয় চলচ্চিত্রে।
এই সাক্ষাৎকারের হাত ধরেই দর্শক প্রবেশ করে নিষ্ঠুর বাস্তবতায়। অপেক্ষারত বাদল নামে একজনকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সঙ্কট, রাজনৈতিক বিপথগামিতা সর্বোপরি বেকারত্বকে তুলে ধরা হয়। আরেকজনের কাহিনি দেখা যায়, যার বাবা একজন শ্রমিক, নাম মুখুজ্যে। এই মুখুজ্যে একসময় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তখন তার কণ্ঠে গান ভাসতো ‘আজাদি কা ডাংকা বাজা’। কিন্তু দেখা গেলো এই শ্রমিক একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি তার কারখানায় যখন ধর্মঘট শুরু হয়, তখন তিনি মালিকের কাছে মুচলেকা দিয়ে কারখানায় কাজ করতে থাকেন। ধর্মঘটে সামিল হন না তিনি। এক সতীর্থ এর কারণ জানতে চাইলে মুখুজ্যে ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, ‘একটা কারখানা, তিনটা ইউনিয়ন, ইউনিয়নবাজি করো, ঝগড়া করো, কাটাকাটি করো। আমি নিজে লিখবো নিজের ডিমান্ড।’ এই কথা যেনো মৃণালের সেই কথার প্রতিধ্বনি, যেখানে তিনি সমালোচনা করছেন বাম দলগুলোর ভেতরকার বিভেদকে।
এরপর মৃণাল শোনান মা ও মেয়ের সংসারের গল্প। যেখানে মা অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। প্রতিদিন কতো মাছ-মাংস রান্না করেন, কিন্তু নিজের সন্তানের মুখে সেগুলো তুলে দিতে পারেন না। ঘর ভাড়া বাকি পাঁচ মাসের। পাড়াটাও ভালো নয়, বখাটেদের উৎপাত। প্রত্যহ প্রতিবেশী স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, কারণ স্বামীটি বেকার। এই অসুস্থ পরিবেশে থাকতে চায় না মেয়ে; অথচ সহসা এই পরিবেশ থেকে যে মুক্তি মিলবে, সেই সম্ভাবনাও নেই। এইসব টুকরো টুকরো কাহিনির পাশাপাশি ওদিকে জমাট বাঁধতে থাকে ক্ষোভ। চাকরির আশ্বাস দিয়ে, দরখাস্ত জমা না নেওয়ার ক্ষোভ। ৩০,০০০ দরখাস্তকারী জোট বাঁধে। চিন্তার ভাঁজ পড়ে চেয়ারম্যানের কপালে। বোর্ডের সদস্যদের তিনি বলেন, ‘দেশটা একটা ভলকানোর উপরে দাঁড়িয়ে আছে, যেকোনো সময় এক্সপ্লোর করতে পারে।’ ভূমিকম্প শুরু হয়, যখন চেয়ারম্যান ও বোর্ডের সদস্যরা রাতের একটায় ফোনে হুমকি পান। থরহরি কম্প শুরু হয়ে যায় তাদের ভেতর। দূরবীন দিয়ে এই দাবিদারদের পর্যবেক্ষণ করেন চেয়ারম্যান। বলেন, এরা আমাদের চেনা। চেয়ারম্যান ভাবেন, বৈঠক করে মীমাংসা করা যাবে। এখানে যা বলা দরকার সেটা হলো, দূরবীন ব্যবহার করে মৃণাল যে মালিক ও শ্রমিকের দূরত্ব মেপে দেখিয়ে দিয়েছেন তা এককথায় অসাধারণ এবং ইন্টেলেকচ্যুয়াল মন্তাজ সৃষ্টির চমৎকার উদাহরণ। এটা সত্যজিৎ রায়-এর চারুলতার চোখে লাগানো থিয়েটার গ্লাসের ‘গেইজ’ নয়, এটা দুই শ্রেণির মধ্যকার দূরত্ব। এই দূরত্ব বৈঠক করে দূর করা যাবে না, সেটা চেয়ারম্যান ভালো করেই জানেন। তাই নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বসেন তিনি। এদের চিহ্ন আবার কঙ্কাল! এর মধ্য দিয়ে মালিক ও প্রশাসনকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যঙ্গ করেন মৃণাল!
আর চুপ করে থাকা যায় না, মালিকপক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে। এতোদিন প্রশাসন তাদের সঙ্গ দিলেও এবার জুটে যায় গণমাধ্যম। নিরপেক্ষতার ঘোমটা খুলে নগ্নভাবেই বেতারে প্রচার করা হয়,
আজ কয়েকদিন হলো কিছু হুজুগসর্বস্ব ব্যক্তি দেশে উদ্বেগ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে, এইসব কুচক্রীর দল জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করছে। দেশ যখন নানাবিধ সঙ্কট মোচনে বদ্ধপরিকর, দেশের মানুষ যখন দারিদ্র্য দূরীকরণে কৃতসংকল্প, দেশের আপামর জনসাধারণ যখন অগ্রগতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সমাজদ্রোহী জনগণকে উত্তেজিত করবার নাশকতামূলক প্রয়াস চালাচ্ছে। এই অন্তঃসারশূন্য ৩০ হাজারি হুজুগের সমূলে উৎপাটন একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সফল রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে হলে, আগামীদিনের বংশধরদের সামনে এক উজ্জ্বল স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে, এই সর্বনাশা হুজুগের মূল উচ্ছেদ আজ অপরিহার্য। এই দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্ত ...।
এমন প্রচার ও প্রোপাগান্ডায় চায়ের কাপে ঝড় ওঠে, সাংবাদিকের ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায়। পথেঘাটে, শহরে, গ্রামেগঞ্জে কে বা কারা শুধু ‘ত্রিশ হাজার’ লিখে সেঁটে দেয়। দরখাস্তকারীদের এই আন্দোলনে সামিল হতে থাকে শ্রমিক ও কৃষক। এদিকে প্রশাসনের লোক ধরপাকড় শুরু করে। চলে জিজ্ঞাসাবাদ। গোপন দল আছে কি? পেছনে নেতা কারা? ইত্যাদি। দেড়শো থেকে আড়াইশো, গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সমান অনুপাতে বাড়তে থাকে আন্দোলন। ‘লাঙল যার জমি তার/ সঙ্গে আছে তিরিশ হাজার’ স্লোগান নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে কৃষকরা। তারাও চায় প্রহসন বন্ধ হোক। মনে রাখা দরকার, উপরের স্লোগানের দাবিটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।
যাইহোক, শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান বলতে বাধ্য হন, আমরা এখন বিপন্ন। দেখা যায় সব জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। বানের জলের মতো মানুষ ছুটে আসছে। ‘কন্ট্রোল’ নামে একজনকে ডেকে সাহায্য চান চেয়ারম্যান, কিন্তু নিরুপায় হয়ে গেছে খোদ ‘কন্ট্রোল’। এই ‘কন্ট্রোল’ চেয়ারম্যানকে বলতে থাকে, আন্দোলনকারীরা স্বপ্নের মুখোমুখি, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, সমাজবিরোধী স্বপ্ন। এই ‘কন্ট্রোল’ যেনো বুর্জোয়াদের সরকার বাহাদুর। সর্বহারা শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র-জনতার উত্থানে ভীত; তাই সহযোগিতা করতে অপারগ। চেয়ারম্যান তখন চিৎকার করে বলতে থাকেন, কন্ট্রোল ইঁদুরের গর্তে লুকাবেন না। অ্যাটাক করুন; কাউন্টার অ্যাটাক। এসব বলে চেয়ারম্যান নিজেই কাঁটাতার ঘেরা নো ম্যানস ল্যান্ডে আত্মগোপন করেন। বাকিরা লাপাত্তা। গ্রামের সেই মহাজন, যিনি ধান মজুদ করে রেখেছিলেন চোরাকারবারের উদ্দেশে, তার বাড়িতেও হামলা চালায় জাগ্রত জনতা। হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষকে তখন ছুটে আসতে দেখা যায় রাজপথে, ফসলের মাঠ পেরিয়ে, দর্শকের দিকে তারা ছুটে আসছে বাঁধ ভাঙা ঢেউয়ের মতো-প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, সংগ্রামের প্রতিধ্বনি। এখানেই শেষ হয় মৃণালের কোরাস।
দশ.
উত্তাল ৭০-এর ঝড়ো হাওয়া স্তিমিত হয়ে আসে একদিন প্রতিদিন (১৯৭৯) এর মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের অফিস থেকে সময়ে বাড়ি না ফেরা নিয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার প্রেক্ষাপটে নির্মিত। তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেমেছে, কিন্তু অনিশ্চয়তা দুর্ভাবনার রেশ থেকে গেছে। তার সঙ্গেই জড়িয়ে থেকেছে মানসিকতার ক্ষুদ্রতা, অসহায়ত্ব ও স্বার্থপরতা-এই সবকিছুই মৃণাল সেনের বিষয়বস্তু।
১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের আকালের সন্ধানে হলো চলচ্চিত্র কলাকুশলী এক দলের কোনো গ্রামে গিয়ে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণের কাহিনি নিয়ে। কীভাবে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কাল্পনিক কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেই গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এই ছিলো চলচ্চিত্রটির মর্মকথা। আকালের সন্ধানে প্রসঙ্গে মৃণাল নিজেই বলেন, আমরা বুদ্ধিজীবীরা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে ভয় পাই। মূলত এই বিষয়টাকে মূল ধরে তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। তার ভাষায়, ‘ইটস আ ফিল্ম উইদইন আ ফিল্ম’। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। এখন প্রশ্ন, কেনো মৃণাল ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষকেই বেছে নিলেন? এর উত্তর মৃণাল দিয়েছেন এভাবে-‘সব দুর্ভিক্ষই ম্যানমেড, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সৃষ্টি’।
এগারো.
বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেনের অনন্যতা বিচার করা যায় নির্মাণে তার নিজস্ব ভাষা, ব্যাকরণ ও পরিবেশন ভঙ্গিমার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিষয় ছিলো তার চলচ্চিত্রগুলোর মূল পটভূমি। একটানা গল্প বলার নেগেটিভ টেকনিকের পরিবর্তে ভিন্ন ভাষায় প্রদর্শনীর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তিনি। বামপন্থি ভাবনাচিন্তায় বিশ্বাস রেখে তিনি নানা প্রশ্নে নিরন্তর খোঁজ চালিয়ে গিয়েছেন তার চলচ্চিত্রে। ৭০-এর কলকাতা ত্রয়ীতে সময়ের যথার্থ প্রতিচ্ছবি যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি ভুবন সোম-এ সচেতনভাবে অ্যারিস্টোক্র্যাট বুরোক্রেসির চকচকে আদালতটিকে ভেঙে ফেলতেও দ্বিধা করেননি। আবার একদিন প্রতিদিন-এ এক প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বাড়ি না ফেরা নিয়ে নানাভাবে কথা ভাবনার সূত্রে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সমস্যাগুলোকে তিনি উন্নীত করেছেন অনায়াস দক্ষতায়।
পরিশেষে বলা যায়, একজন নির্মাতা হিসেবে মৃণাল তার সৃষ্টিতে কোনো কৃত্রিম কল্পনার অকারণ স্থান দিতে চাননি। জীবন অভিজ্ঞতায় যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাকেই চলচ্চিত্রের উপজীব্য বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। একজন সৎ শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকে আজীবন মৃণাল মানুষের জন্য মানুষের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে গেছেন।
লেখক : সেখ আসরাফ আলি ও একতা গাঙ্গুলী, যথাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ ডি ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন।
ekataganguly0090@gmail.com
তথ্যসূত্র ও টীকা
১. হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (২০১৯ : ৮০); ‘পরিশিষ্ট’; মৃণাল সেন : সত্তা ও সৃষ্টি; অনীশ ঘোষ (সম্পা); বোধিসত্ত্ব, কলকাতা।
২. প্রাগুক্ত; হোসেন (২০১৯ : ৮০)।
৩. দাশ, সুস্নাত (১৯৬১ : ১৭৫); ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা।
৪. প্রাগুক্ত; দাশ (১৯৬১ : ১৭৬)।
৫. Sen, Mrinal; https:/www.mrinalsen.org/,2022; retrieved on: 15.05.2025
৬.মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয়; ‘নগর পরিক্রমা: মৃণাল সে’ ; লিঙ্ক দেখুন: https://nagorik.net/culture/cinema/sanjay-uvacha-2mrinalsen-exploring -the-city/; retrieved on: 14.05.2025
৭. সেন, মৃণাল (২০০২ : ১); অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত; থিমা প্রকাশনি, কলকাতা।
৮. প্রাগুক্ত; মুখোপাধ্যায়; ‘নগর পরিক্রমা: মৃণাল সেন’।
৯. সেন, মৃণাল (২০২৩ : ১৭); মৃণাল সেন; পরিমল মুখাজ্জী (সম্পা.); সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা।
১০. প্রাগুক্ত; সেন (২০২৩ : ১৮)।
১১. সেন, মৃণাল; ‘মৃণাল সেনের মুখোমুখি’; চিত্রবীক্ষণ (মৃণাল সেন সংখ্যা); কলকাতা, এপ্রিল-মে ১৯৯৩, পৃ.
১২. প্রাগুক্ত; সেন, পৃ. ৯।
১৩. বসু, সৌরেন (২০১৭ : ৯); চারু মজুমদারের কথা; পিপিলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।
১৪. Ghosh, Sankar (1974: 59Ñ133); The Naxalite Movement: A Maoist Experiment, Firma k.l Mukhopadhyay, Kolkata.
১৫. মৌলিক, সুমন কল্যাণ (ভাষান্তর) (২০১৩ : ১০১); নকশালবাড়ি থেকে লালগড়; সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।
১৬. প্রাগুক্ত; মৌলিক (ভাষান্তর), (২০১৩ : ১০১-১০৩)।
১৭. মজুমদার, চারু; ‘এ ফিউ ওয়ার্ডস টু দি রেভলিউশনারি স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথস’; লিবারেশন, মার্চ ১৯৭০, পৃ.১৩।
১৮. মজুমদার, চারু (২০২৩ : ২০৩); চারু মজুমদার রচনা সমগ্র : প্রথম খণ্ড; মনজুরুল হক (সম্পা.), ঐতিহ্য, ঢাকা।
১৯. ঘোষ, সুনীতি কুমার (২০২২ : ২৬৪-২৬৫), নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন; পিপিলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।
২০. রায়, সিদ্ধার্থ গুহ রায় (২০২৪ : ১২৮); স্বাধীনতা উত্তর ভারত (১৯৪৭-২০২২); সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।
২১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ নভেম্বর ১৯৭০।
২২. স্বপনকান্তি ঘোষ (সম্পা.) (২০১১ : ৪০); রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: নকশালবাড়ি থেকে নেতাইগ্রাম, কলকাতা।
২৩. যুগান্তর, ২৮-৩০ জানুয়ারি ১৯৭১, কলকাতা, পৃ.১।
২৪. যুগান্তর, ২ জুন ১৯৭১, কলকাতা, পৃ.১।
২৫. Frontier, 18th September 1971, Kolkata, p.10.
২৬. যুগান্তর, ১৫ অগাস্ট ১৯৭১, কলকাতা, পৃ.৩-৪।
২৭. চিত্রবীক্ষণ, দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭২, কলকাতা, পৃ.৪১।
২৮. গুপ্ত, বিক্রমজিৎ (২০১৯ : ২৭); ‘প্রসঙ্গ আকাশ কুসুম’; মৃণাল সেন : সত্তা ও সৃষ্টি; অনীশ ঘোষ (সম্পা); বোধিসত্ত্ব, কলকাতা।
২৯. প্রাগুক্ত; সেন (২০২৩ : ৭৩)।
৩০. চিত্রবীক্ষণ, দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭২, কলকাতা,
পৃ.৪২-৪৩।
৩১. চিত্রবীক্ষণ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ১৮।
৩২. চিত্রবীক্ষণ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ১৯।
৩৩. মুখার্জি, পরিমল (সম্পা.) (২০২৩ : ৯১); মৃণাল সেন, সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা।
৩৪. চিত্রবীক্ষণ; দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৩৫. ঘোষ, অনীশ (সম্পা) (২০১৯ : ২৯); মৃণাল সেন : সত্তা ও সৃষ্টি, বোধিসত্ত্ব, কলকাতা।
৩৬. ঘোষাল, সৌভিক; ‘মৃণাল সেনের সিনেমা’; নবান্ন; কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যা, পৃ. ১৪৪।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন