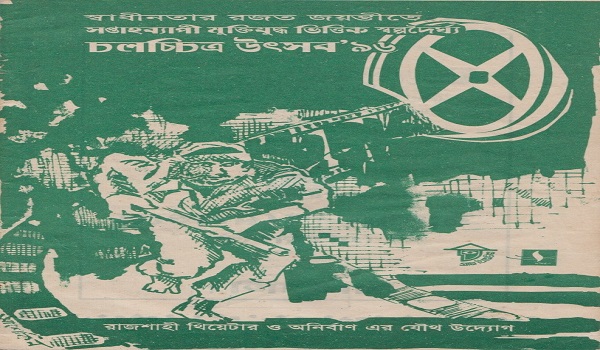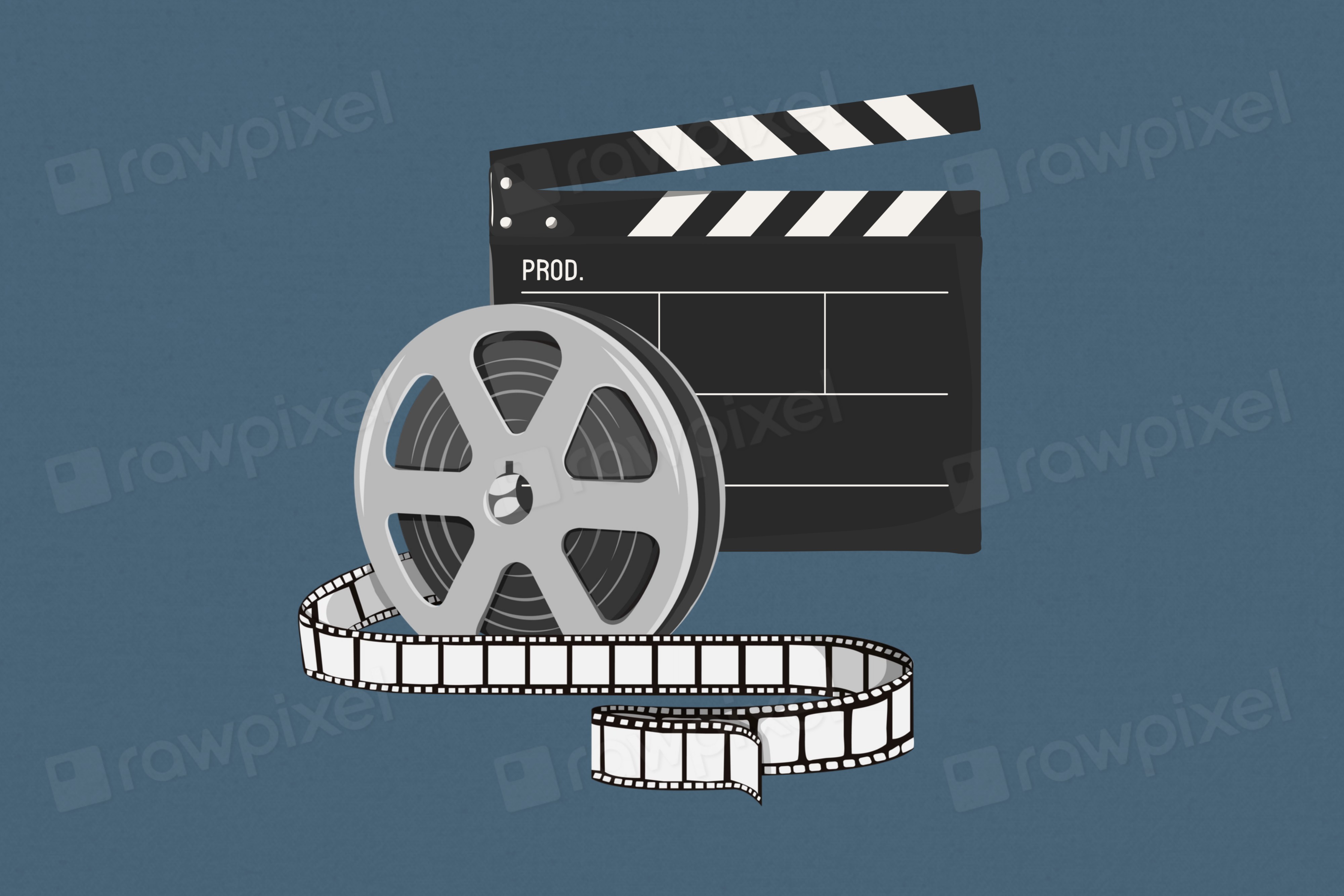মাহামুদ সেতু
প্রকাশিত ০১ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
প্রসঙ্গ অস্কারের রাজনীতি
মাহামুদ সেতু

পুরস্কার, তিরস্কার ও অন্যান্য
স্বীকৃত ইতিহাস অনুসারে ঠিক কবে থেকে মানবসমাজে পুরস্কারের প্রবর্তন শুরু হয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় মিথ থেকে জানা যায়, সৃষ্টির শুরু থেকেই এর প্রচলন রয়েছে। স্রষ্টা তার সৃষ্টির উপাসনায় খুশি হয়ে বিভিন্ন সময়ে অনন্ত সুখের জীবনের নিশ্চয়তাসহ নানা পুরস্কার দেওয়ার কথা শুনিয়েছেন তার ‘প্রতিনিধি’দের মুখে। তারই ধারাবাহিকতায় হয়তো মানবসমাজেও শুরু হয়েছে পুরস্কার ব্যবস্থার। তাই কেউ কোনো ‘ভালো’কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার সবসময় ক্ষমতাবানরাই দিয়ে এসেছেন। ফলে সেই ‘ভালো’কাজটিও আদৌ ভালো কি না, তা নির্ধারণ করেছে তারাই।
এই যেমন ধরুন, নবাব আব্দুল লতিফের কথা। তাকে ব্রিটিশ ভারতের পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ‘আধুনিক’শিক্ষার প্রসারের জন্য পুরস্কৃত করে তৎকালীন সরকার। তাকে পর্যায়ক্রমে খান বাহাদুর, নবাব ও সবশেষে সর্বোচ্চ মুসলিম খেতাব নবাব বাহাদুরে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি কি আসলেই পুরোপুরি বাঙালি মুসলমানদের জন্য কাজ করে গেছেন? নবাব আব্দুল লতিফের ভাষ্য মতে, ‘বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রধানত উর্দু। তবে নিম্নশ্রেণির বাঙালি মুসলমানরাই শুধু বাংলায় কথা বলে। তাদেরকেও ধীরে ধীরে উর্দু শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।’১ অর্থাৎ, তার এই শিক্ষা প্রসারের ‘দরদি’প্রচেষ্টার পিছনে ভিন্ন কোনো রাজনীতি থাকলেও থাকতে পারে। আর যাইহোক সেই রাজনীতি কিন্তু ব্রিটিশদের অনুকূলেই গেছে। যেজন্য তাকে এতো এতো সম্মানে ভূষিত করেছে তারা। অন্যদিকে মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের মতো যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, তাদেরকে সন্ত্রাসী উপাধি দিয়েছে তারা। আসলে এটা তো জানা কথাই যে, আপনি তাকেই কাছে টানবেন, যে আপনাকে ভালো বলবে, আপনাকে মেনে চলবে। পুরস্কারটা তো তাকেই দিবেন, আর তিরস্কারটা রইবে অবাধ্যদের জন্যই!
এই পুরস্কার নামে মহার্ঘ্য বস্তুটি আজ জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা কারণেই একজন অন্যজনকে দিয়ে থাকে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা, বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, পড়াশোনা এহেন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে কোনো পুরস্কার নেই। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ‘কৃতিত্ব’দেখাতে পারলেই পুরস্কার দেওয়া হয় সেই কৃতিমানকে। কিন্তু সবসময় কি সেই কৃতিত্ব বিচার করার মাপকাঠি যথার্থ থাকে, নাকি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত শর্ত পালনের পরও আরো কিছু দিক বাকি থেকে যায়? বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার অস্কার’কে কেন্দ্র করে সেটাই খুঁজে দেখা হবে এই আলোচনায়।
অস্কারের আদ্যোপান্ত
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। আমেরিকায় চলচ্চিত্র ব্যবসা তখন তুঙ্গে। আসলে ১৯২০-এর দশকে গড়ে ওঠা ‘কনজ্যুমার সোসাইটি’র কারণে গোটা আমেরিকার অর্থনীতিতে সুবাতাস বইছে। ওই দশকেই গোটা দেশের জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ ফার্ম হাউজের পরিবর্তে শহরে বসবাস শুরু করে।২ যার কারণেই বিনোদন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র এতোটা প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সেসময়ে। তখনকার স্টুডিও-নির্ভর এই চলচ্চিত্রশিল্পে নির্মাতা, কলাকুশলী সবাই স্টুডিওর সঙ্গে মাসিক বা বাৎসরিক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ ছিলো। যতো চলচ্চিত্রই নির্মাণ হোক না কেনো, কলাকুশলীরা তাদের বেতনের বাইরে কোনো টাকা পেতো না। ফলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিলো কেবল স্টুডিও মালিকেরা। তেমনই একজন লুই বি মেয়ার, হলিউডের অন্যতম স্টুডিও মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার-এর (এম জি এম) সহ-প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ে ইরিন-এর ইচ্ছা পূরণে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্টা মনিকা সমুদ্র সৈকতের পাশে একটি বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেন তিনি। অঢেল টাকার মালিক হলেও মেয়ার বেশ হিসাবি ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, বাড়ি বানাতে হলে ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, মিস্ত্রি, কনট্রাক্টরসহ অনেক লোক লাগাতে হবে, সময়ও লাগবে অনেক। আর এসব করতে খরচও হবে প্রচুর। অথচ স্টুডিওতে কম খরচে রাতারাতি তারা অনেক বড়ো বড়ো বাড়ি বানিয়ে ফেলেন, সপ্তাহের মধ্যেই শহর-বন্দর নির্মাণ করেন। তাহলে বাড়ি বানাতে শুধু শুধু এতো খরচের দরকার কি!
ভাবনা অনুযায়ী তিনি কথা বলেন, তার স্টুডিওর প্রধান ডিজাইনার কেড্রিক গিবন্স (Cedric Gibbons) ও প্রোডাকশন ম্যানেজার জো কন-এর সঙ্গে। তারা মেয়ার’কে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দিতে পারবেন বলে জানায়। আর এ কাজের জন্য তাদের তিন শিফটে দিনের ২৪ ঘণ্টাই কাজ চালাতে হবে। সবকিছু চূড়ান্তের পর নতুন এক সমস্যা দেখা দেয়। সেসময় শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে স্টুডিওগুলোর চুক্তি ছিলো। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে কর্মীদের বেতন, ওভারটাইম ও অন্যান্য সুবিধা দিতে হতো ইউনিয়নকে। কিন্তু এভাবে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করালে বাড়ি নির্মাণে খরচ অনেক বেশি পড়বে বলে মেয়ার’কে জানান জো কন। ফলে তিনি মেয়ার’কে পরামর্শ দেন, স্টুডিও থেকে দক্ষ কয়েকজন নিয়ে বাকি শ্রমিক বাহির থেকে নেওয়ার। এতে করে কম খরচে, অল্প সময়েই রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়ে যায়।
বাড়ির কাজ শেষ হলেও মেয়ার-এর চিন্তা শেষ হয় না। শ্রমিক ইউনিয়নের মতো করে যদি অভিনয়শিল্পী, নির্মাতারাও ইউনিয়ন তৈরি করে পেনশন, আবাসনসহ অন্যান্য ভাতা কিংবা চলচ্চিত্রের লভ্যাংশ দাবি করে বসে, তবে কী হবে, সে চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো তার মাথায়। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানও করে ফেলেন মেয়ার। কলাকুশলী ও নির্মাতারা যাতে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত না হয়, সেজন্য তিনি তার কয়েক বন্ধু মিলে আলোচনায় বসেন। আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী ১১ জানুয়ারি ১৯২৭ যাত্রা শুরু করে ‘দ্য অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস’(এ এম পি এ এস)। যে সংগঠন স্টুডিওর পক্ষ থেকেই কলাকুশলীদের সব সমস্যার সমাধান করে দিবে। পাশাপাশি হলিউডের চলমান স্টুডিও ব্যবস্থা যে খুবই কার্যকর ও যথাযথ, এই সংগঠন সেটাও তুলে ধরবে।৩
এ এম পি এ এস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ‘শ্রম শোষণের’ নতুন এক অধ্যায় শুরু করেন মেয়ার’রা। এতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে নিজেরা ইউনিয়ন গড়ে এসেছে, কিন্তু এবার মালিকরাই তাদের জন্য ইউনিয়ন তৈরি করে দেয়। কিন্তু শুধু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেই তো চলবে না, সেখানে সদস্যও থাকতে হবে। সেজন্য ওই সংগঠনে অভিনয়শিল্পী, নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক ও কুশলীদের পাঁচটি আলাদা ভাগে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়। তারপর তাদেরকে ‘নিয়ন্ত্রণে’রাখতেই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করা হয় অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বা অস্কার। মেয়ার নিজেই বলেছেন, ‘I found that the best way to handle [filmmakers] was to hang medals all over them ... If I got them cups and awards they'd kill them to produce what I wanted. That's why the Academy Award was created.’৪
মেয়ার-এর এই কথায় এটা স্পষ্ট হয় যে, স্টুডিও মালিকরা পুরস্কারের মুলা ঝুলিয়ে চলচ্চিত্রকর্মীদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল ছাড়া ভিন্ন কোনো চিন্তা থেকে এই অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করেনি। এখনো অবশ্য তেমনটাই হয়ে আসছে। অভিযোগ রয়েছে, শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অ্যাকাডেমি কমিটি, পুরস্কারের জন্য কালোদের পরিবর্তে শ্বেতাঙ্গদেরই বেশি মনোনয়ন দিয়ে এসেছে। ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে টানা দুই বারই পুরস্কারের জন্য কোনো অ-শ্বেতাঙ্গ অভিনয়শিল্পী মনোনয়ন পায়নি। যা নিয়ে সেসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে #OscarsSoWhite নামে আন্দোলন গড়ে ওঠে। আসলে এ এম পি এ এস-এর পাঁচ হাজার সাতশো ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ হাজার একশো জনের তালিকা বিশ্লেষণ করে জানা যায়, সেখানে ৯৪ শতাংশই শ্বেতাঙ্গ এবং ৭৭ শতাংশ পুরুষ।৫ আর সেই আন্দোলনের ফলে অ্যাকাডেমি ২০১৬-তে নতুন সদস্য হিসেবে নারী ও অ-শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য দেয় এবং বর্তমানে অ্যাকাডেমিতে অ-শ্বেতাঙ্গদের অংশগ্রহণ বেড়ে ৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
তার মানে, অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর জন্মই হয়েছিলো মালিকের স্বার্থরক্ষায়। ফলে তাদের প্রবর্তিত পুরস্কারও যে মালিকের স্বার্থরক্ষার বিনিময়েই পাওয়া যাবে, সেটা বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়। শুরুতে আউটস্ট্যান্ডিং পিকচার, ইউনিক অ্যান্ড আর্টিস্টিক পিকচার, বেস্ট ডিরেক্টর কমেডি পিকচার, বেস্ট ডিরেক্টর ড্রামাটিক পিকচার, বেস্ট অ্যাক্টর, বেস্ট অ্যাক্ট্রেস, বেস্ট রাইটিং অরিজিনাল স্টোরি, বেস্ট রাইটিং অ্যাডাপ্টেড স্টোরি, বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি, বেস্ট আর্ট ডিরেকশন, বেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইফেক্ট, বেস্ট রাইটিং : টাইটেল রাইটিং- এই ১২টি শাখায় পুরস্কার দেওয়া হতো। সেসময় কোনো ব্যক্তি তাদের একাধিক চলচ্চিত্রের জন্য একটি পুরস্কার পেতেন। পরবর্তী সময়ে একজন ব্যক্তি বছরে একটি চলচ্চিত্রে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন। বর্তমানে মোট ২৫টি বিভাগে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।
প্রাতিষ্ঠানিক নাম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট হলেও সেটি অবশ্য অস্কার নামেই বেশি পরিচিত। তবে এটাকে কেনো অস্কার বলা হয়, তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রচলিত যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা হলো, পুরস্কারের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাচু বা মানব প্রতিকৃতিটি তৈরি হওয়ার পর তা প্রথমবার দেখেন অ্যাকাডেমির তৎকালীন গ্রন্থাগারিক ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মার্গারেট হেরিক (Margaret Herrick)। এ সময় তিনি সেই প্রতিকৃতিটির সঙ্গে তার চাচার চেহারার মিল পান। তার সেই চাচার নাম ছিলো অস্কার। যদিও ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ অস্কার নামটি কোথাও ব্যবহার করতো না। কিন্তু ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অভিনয়শিল্পী ক্যাথরিন হেপবার্ন-এর প্রথম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড লাভের সংবাদে হলিউড কলামিস্ট সিডসি স্কোলস্কি ব্যবহার করেন অস্কার শব্দটি। তারপর থেকেই মানুষের মধ্যে অস্কার হিসেবেই বেশি পরিচিতি লাভ করে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষও নামটি দাপ্তরিকভাবে গ্রহণ করে।৬
শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট তিন হাজার ৪৮টি অস্কার প্রদান করা হয়েছে। প্রথম থেকেই পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে একজন নাইট বা যোদ্ধার প্রতিকৃতিকে। সেই নাইট ক্রুসেডের তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফিল্ম রিলের উপর। সেটাতে আবার পাঁচটি স্পোক আছে, যেগুলো অ্যাকাডেমির প্রধান পাঁচটি শাখা- অভিনয়, পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, প্রযোজনা ও টেকনিশিয়ান’কে নির্দেশ করে।৭ অস্কারের এই স্ট্যাচুটি দেখার পর থেকেই একটি প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খায়, জানি না সেটা কতোখানি প্রাসঙ্গিক হবে এই আলোচনায়। চলচ্চিত্রশিল্পের সবচেয়ে সম্মানের এই পুরস্কার হিসেবে কেনো একজন ‘ক্ষমতাবান পুরুষ যোদ্ধা’-এর প্রতিকৃতি প্রদান করা হয়? আর তার পায়ের নিচে থাকে অভিনয়, পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, প্রযোজনা ও টেকনিশিয়ান! এমন একটি ক্রেস্ট তৈরির পিছনে এর নকশাকার কেড্রিক গিবনসের (Cedric Gibbons) আসলে কী উদ্দেশ্য ছিলো? অবশ্য তা আজ জানার উপায় নেই। কিন্তু এমন কি হতে পারে, অন্য অনেক কিছুর মতো অস্কার পুরস্কারেও পুরুষ প্রাধান্যশীলতা ঘেরাটোপের বাইরে যেতে পারেননি কেড্রিক গিবনস!
অস্কার নিয়ে ব্যবসার যতো ফন্দি
চলচ্চিত্রবিশ্বের সবচেয়ে দামি পুরস্কার অস্কার- অর্থমান ও সম্মান উভয় দিক থেকেই। এর সঙ্গে আবার যোগ হয় ব্যবসা। পুরস্কার নয়, শুধু অস্কার মনোনয়ন পেলেই কোনো চলচ্চিত্রের ব্যবসা তিন- চার গুণ বেড়ে যায়! যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার (ইউ সি এল এ) দুই গবেষক, গ্যাব্রিয়েল রসম্যান (Gabriel Rossman) ও অলিভার সিল্ক (Oliver Schilke) তাদের এক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, অস্কার মনোনয়ন না পাওয়া কোনো চলচ্চিত্র যদি ২৪ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করে, তবে একটি শাখায় অস্কার মনোনয়ন পেলে সেই চলচ্চিত্রই ৪০ মিলিয়ন ডলার আয় করবে। আর সেটি যদি পাঁচটি শাখায় মনোনয়ন পায়, তবে এই ব্যবসা ৯২ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।৮ কিন্তু এসব চলচ্চিত্রের নির্মাণ ব্যয়ও খুব বেশি হয় না। তাই কম বিনিয়োগে অধিক মুনাফা ঘরে তুলতে চাইলে নির্মাতা-প্রযোজকদের অস্কার মনোনয়ন পাওয়াটা খুবই জরুরি।
আর অস্কার মনোনয়ন পেতে হলে কোন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে সেটাও গবেষণায় বের করেছেন রসম্যান ও সিল্ক। তারা ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার অস্কার মনোনয়ন পাওয়া চলচ্চিত্রের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, নির্দিষ্ট কয়েকটি জেনারের চলচ্চিত্রই মূলত অস্কারের জন্য মনোনীত হয়। এগুলোর মধ্যে ড্রামা, ইতিহাস, যুদ্ধ ও জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র সবচেয়ে বেশি মনোনীত হতে দেখা গেছে। আর এসব চলচ্চিত্রের কাহিনিতে রাজনৈতিক কূটকৌশল, অক্ষমতা, যুদ্ধাপরাধ ও সংস্কৃতি ব্যবসার উপস্থিতি সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে নির্মাতারা বছরের পর বছর ধরে সেই একই ধারার চলচ্চিত্র বানায় অস্কারকে টার্গেট করে। আর নির্মাতাদের এই কৌশলকে রসম্যান ও সিল্ক আখ্যায়িত করেছেন ‘অস্কার বেইট’(Oscar Bait) বা ‘অস্কার টোপ’ হিসেবে। ইতিহাস বলছে, অ্যাকাডেমি কমিটিও সেই টোপ নিয়মিতই গিলে চলছে।
কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, অস্কার পুরস্কার পাওয়া সেরা চলচ্চিত্রের তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে হলিউডের বড়ো ছয়টি স্টুডিওর নামই বেশি জ্বলজ্বল করে। পুরস্কার পাওয়া অধিকাংশ চলচ্চিত্রই ফক্স, প্যারামাউন্ট, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ডিজনি, ইউনিভার্সাল ও কলাম্বিয়া প্রযোজনা কোম্পানির। অবশ্য সবসময় এরা নিজ নামেই যে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে তা নয়, অনেক সময়ই তাদের সাবসিডিয়ারি স্বাধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এসব ‘শিল্পমান’ সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বাজারজাত করে। যেমন ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৭৩তম অস্কারের সেরা চলচ্চিত্র গ্ল্যাডিয়েটর (২০০০) প্রযোজনা করেছে ইউনিভার্সাল ও তার অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ড্রিমওয়ার্কস। আর সেই আসরে সেরা চলচ্চিত্র শাখায় মনোনয়ন পাওয়া বাকি চারটি চলচ্চিত্রের দুটি ইউনিভার্সালের, একটি সনি’র ও অন্যটি ওয়াল্ট ডিজনি’র সাবসিডিয়ারি মিরাম্যাক্স-এর প্রযোজিত ছিলো। একইভাবে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে অস্কার পাওয়া অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড-এর পিছনে রয়েছে ইউনিভার্সাল। সে বছর মনোনয়ন পাওয়া বাকি চারটির মধ্যে ইউনিভার্সালের সাবসিডিয়ারি ইউএসএ-এর একটি, ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর সাবসিডিয়ারি ‘নিউ লাইন সিনেমা’র একটি, ফক্স-এর একটি এবং ইউনিভার্সাল ও ওয়াল্ট ডিজনির যৌথ প্রযোজনার ছিলো একটি। ২০০২-এ সেরা চলচ্চিত্র মিরাম্যাক্স-এর, মনোনয়ন পাওয়া বাকি চারটির একটি ‘মিরাম্যাক্স’, একটি ‘নিউ লাইন সিনেমা’, একটি ইউনিভার্সালের সাবসিডিয়ারি ‘ফোকাস ফিচারস’-এর এবং আরেকটি মিরাম্যাক্স ও প্যারামাউন্ট-এর যৌথ প্রযোজনার।
বছরভিত্তিক অস্কার মনোনয়ন পাওয়া প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের তালিকা৯
|
প্রযোজনা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান |
২০০০ |
২০০১ |
২০০২ |
২০০৩ |
২০০৪ |
২০০৫ |
২০০৬ |
২০০৭ |
২০০৮ |
মোট |
|
ইউনিভার্সাল |
৩ |
২ |
১ |
২ |
১ |
২ |
|
১ |
২ |
১৪ |
|
ওয়ার্নার ব্রাদাস |
|
১ |
১ |
২ |
২ |
১ |
১ |
১ |
|
৯ |
|
ওয়াল্ট ডিজনি |
১ |
|
২ |
|
১ |
|
১ |
|
|
৫ |
|
সনি |
১ |
|
|
|
|
১ |
|
|
|
২ |
|
প্যারামাউন্ট |
|
|
|
|
|
|
১ |
১ |
|
২ |
|
টুয়েন্টি সেঞ্চুরি ফক্স |
|
১ |
|
১ |
১ |
|
১ |
১ |
|
৫ |
|
যৌথ প্রযোজনা |
|
১ |
১ |
|
|
|
১ |
১ |
২ |
৬ |
|
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
১ |
|
|
১ |
২ |
একই পরিস্থিতি দেখা যায় পরের বছরগুলোতেও। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত অস্কার পুরস্কার বিজয়ী ও মনোনয়ন পাওয়া ৩০টি চলচ্চিত্রের তালিকায় দেখা যায়, এগুলোর মধ্যে সাতটি ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও তাদের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের, আটটি ইউনিভার্সাল ও তাদের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের, ফক্সের তিনটি, ডিজনি’র দুটি এবং সনি ও প্যারামাউন্ট-এর একটি করে প্রযোজনা রয়েছে। পাশাপাশি ওয়ার্নার-ডিজনি যৌথ প্রযোজনা একটি, ওয়ার্নার-ইউনিভার্সাল একটি, ওয়ার্নার-প্যারামাউন্ট একটি, ডিজনি-প্যারামাউন্ট দুটি এবং ফক্স-ইউনিভার্সাল-ডিজনি’র যৌথ প্রযোজনায় রয়েছে একটি। অবশ্য বড়ো স্টুডিওগুলোর একক প্রযোজনার সঙ্গেও কিন্তু ছোটো ছোটো এক বা একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে। তার পরও এই ৩০টি চলচ্চিত্রের মধ্যে আলাদাভাবে অন্যান্য ছোটো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের চলচ্চিত্র রয়েছে মাত্র দুইটি। যার মানেটা হলো অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস যারা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার প্রবর্তিত পুরস্কারও তারাই ঘরে তুলছে। বলে নেওয়া দরকার, এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ২০০০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত অস্কার বিজয়ী ও মনোনয়ন পাওয়া চলচ্চিত্রের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এর কারণ হলো, ২০০৮ অবধি সেরা চলচ্চিত্রের জন্য পাঁচটি করে চলচ্চিত্রকে মনোনয়ন দেওয়া হতো এবং তা থেকে একটি অস্কারে ভূষিত হতো। কিন্তু ২০০৯ থেকে পাঁচটির পরিবর্তে ৯-১০টি করে চলচ্চিত্রকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। তাই হিসাবটা সহজ করার জন্যই ২০০৮ পর্যন্ত তালিকা নিয়ে কথা বলা হয়েছে।
যাহোক, মনোনয়ন ও পুরস্কার পাওয়ার এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো এতে করে দুই দিক থেকেই লাভবান হচ্ছে। একদিকে পুরস্কার পেয়ে নিজেদের কাজের স্বীকৃতি আদায় করে নেয় তারা, সঙ্গে ব্যবসায়িক লাভ তো রয়েছেই। আবার অস্কারকে উদ্দেশ্য করে নির্মাণ করা চলচ্চিত্র ছাড়াও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্র তো রয়েছেই। এভাবে গোটা হলিউড চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিটাকেই নিয়ন্ত্রণ করছে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো।
হে অস্কার, তুমি কার?
যেকোনো চলচ্চিত্রনির্মাতার স্বপ্ন থাকে তার নিজস্ব স্বপ্ন-কল্পনার চিত্র বা ইমেজকে জনসমক্ষে তুলে ধরে স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই স্বীকৃতির সবচেয়ে সম্মানজনক রূপ অস্কার। কিন্তু সবসময় কি শুধু নির্মাতার মেধার মূল্যায়ন করেই অস্কার দেওয়া হয়, নাকি এর পিছনে অন্য কোনো ভিন্ন রাজনীতিও থাকে? ২০০৯-এ দ্য হার্ট লকার কিংবা ২০১৩-তে টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর মতো চলচ্চিত্রের অস্কার লাভ সেই সংশয় বাড়িয়েই দেয় শুধু। দ্য হার্ট লকার-এ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনীর জনদরদি উপস্থাপন এবং টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এ এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির দাস হওয়া ও তা থেকে পরিত্রাণের পিছনে ত্রাতা শ্বেতাঙ্গের অবদানকে তুলে ধরা হয়। ফলে এখানে গল্প বয়ানে নির্মাতার নৈপুণ্যের বিপরীতে অস্কার লাভের পিছনে ভিন্ন কোনো রাজনীতির ‘গন্ধ’পেলে সেটাকে নেহাত দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দুই চলচ্চিত্রেই ক্ষমতাবান শ্বেতাঙ্গকে ‘দেবতা’র আসনে বসানো হয়। সেজন্য সাদা চোখে যাই দেখা যাক না কেনো, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এই ধরনের রাজনৈতিক ‘নৈকট্য’থাকাটা অস্কার পাওয়ার পিছনে বড়ো কোনো ভূমিকা সবসময়ই রাখে কি না তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই বিশ্লেষণের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্কার বিজয়ী তিনটি চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করলেই হয়তো মনের ভিতর তৈরি হওয়া খচখচানি কিছুটা দূর করা সম্ভব। তাই এখনকার আলোচনা জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র দ্য কিংস স্পিচ (২০১০), হিস্টোরিকাল ড্রামা আরগো (২০১২) ও ড্রামা চলচ্চিত্র মুনলাইট (২০১৬) নিয়ে এগিয়ে যাবে। মূলত রসম্যান ও সিল্কের গবেষণায় উঠে আসা চারটি জেনার থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্প্রতিকতার ভিত্তিতে এই চলচ্চিত্রগুলোকে বাছাই করা হয়েছে।
ক. দ্য কিংস স্পিচ : বন্ধুর বিজয় তো নিজেরও!
ব্রিটেনের বর্তমান রানি এলিজাবেথ টু-এর বাবা রাজা আলবার্ট ফ্রেডরিক আর্থার জর্জ- যিনি জর্জ সিক্স নামেই বেশি পরিচিত- তরুণ বয়সে অস্ট্রেলিয় বাক চিকিৎসক লাইওনেল লগ-এর (Lionel Logue) কাছে তোতলামির চিকিৎসা করতে যান। একপর্যায়ে তাদের দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এমনই ‘সত্য’ঘটনা নিয়ে নির্মিত দ্য কিংস স্পিচ। একশো ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রটি তিন হাজার তিনশো ২১ কোটি টাকা আয় করে। সেই সঙ্গে ১২টি শাখায় অস্কার মনোনয়ন পাওয়া চলচ্চিত্রটি সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনয়শিল্পী, সেরা নির্মাতা ও সেরা চিত্রনাট্য শাখায় বিজয়ী হয়। অস্কার ছাড়াও দ্য কিংস স্পিচ সেরা চলচ্চিত্রসহ সাতটি শাখায় ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা) পুরস্কার, টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড, সেরা অভিনয়শিল্পী হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার, সেরা নির্মাতা শাখায় ডিরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা অ্যাওয়ার্ডসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।
যুদ্ধের মাঠে যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন সম্পর্ক বেশ পুরনো। গত শতকের বিশ্বযুদ্ধগুলোর পর থেকে সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলন হয়ে বর্তমানের ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’ ময়দানেও দেশ দুটি ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। যুক্তরাষ্ট্রের সেই বন্ধু রাষ্ট্রের রাজপরিবার নিয়েই নির্মিত দ্য কিংস স্পিচ। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা জর্জ ফিফথ-এর মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব পান জর্জ সিক্স-এর বড়ো ভাই অ্যাডওয়ার্ড ডেভিড। কিন্তু ব্রিটেনের রাজা পদাধিকারবলে চার্চেরও প্রধান। আর চার্চের প্রধান কোনো বিবাহিত, বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করতে পারবেন না। কিন্তু রাজা হওয়ার পর ডেভিড ভালোবেসে দুই বার তালাকপ্রাপ্ত ওয়ালিস সিম্পসন’কে বিয়ে করতে চান। ওয়ালিসকে আবার হিটলারের গুপ্তচর হিসেবেও সন্দেহ করা হতো।
সেই সূত্রে হিটলারের সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রজুড়ে অস্পৃশ্যই থেকে যান জর্জ সিক্সের বড়ো ভাই ও সিংহাসনের ‘প্রকৃত’ দাবিদার অ্যাডওয়ার্ড ডেভিড। যিনি সিংহাসনের পরিবর্তে নিজের ভালোবাসাকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। চলচ্চিত্রে তাকে রাজকীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি হিসেবেই তুলে ধরা হয়। অবশ্য আইনি দিক থেকে ‘সত্য’ঘটনা সেটাই। তার পরও প্রেমের কারণে সিংহাসন ত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে কিন্তু বিরলই! সেদিক থেকে বিচার করলে, চলচ্চিত্রে তার সেই প্রেমকে ‘নোংরামি’হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। দ্য কিংস স্পিচ-এর ৩১ মিনিটের দিকে রাজা জর্জ ফিফথ, তার ছোটো ছেলে জর্জ সিক্সকে বলেন, ‘আমি তাকে (এডওয়ার্ড) সরাসরি বলেছি, অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোর্ট তা মেনে নেবে না। কিন্তু সে নাকি এতেই খুশি! নিশ্চয় ওই মেয়েটা তার সঙ্গে শোয় বলেই হয়তো সে এতো খুশি!’ শেষ পর্যন্ত বিবাহিত নারীকে বিয়ের ‘অপরাধে’ অ্যাডওয়ার্ড ডেভিডকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। সেই জায়গায় দায়িত্ব পান জর্জ সিক্স। কিন্তু তার তোতলামির সমস্যা থাকায় জনসমক্ষে ও বেতারে ভাষণ দিতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই চিকিৎসক লগ-এর শরণাপন্ন হন তিনি।
চলচ্চিত্রে বলা হয়, রাজা কোনো সাধারণ মানুষ নন। তাকে অন্যদের মন জয় করে নিতে হয়। আর অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারলে, সেটা সম্ভব নয়। এই প্রভাব ফেলতে হবে নিজের কাজ ও কথা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত রাজা জর্জ সিক্স সফল হন মানুষের মন জয় করতে। অবশ্য শুধু মনই নয়, তিনি ‘যুদ্ধ’ও জয় করেন। হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাষণ দেন জর্জ সিক্স। সেই ভাষণের সময়ও তাকে সহায়তা করেন লগ। শুধু বিশ্বযুদ্ধেই নয়, বরং তার জীবদ্দশায় প্রতিটি যুদ্ধের ভাষণেই তিনি জনগণের আস্থা অর্জন করেন। যেজন্য কিংস স্পিচ-এর শেষের প্রোলগে বলা হয়, ‘জর্জ তার জোরালো ভাষণের মধ্য দিয়েই জাতীয় সহনশীলতার প্রতীকে পরিণত হন।’আর তার এই কৃতিত্বের পিছনে অবদান রাখায় চিকিৎসক লাইওনেল লগ’কে এক রাজকীয় আদেশে কমান্ডার পদবিতে ভূষিত করা হয়। অন্যদিকে জোরালো ভাষণ দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই কাতারে থাকা জর্জ সিক্স-এর মতো ‘বন্ধু’র এমন সফলতার গল্পকে পুরস্কার দিয়ে হয়তো বন্ধুত্বটাকে আরো একটু গাঢ় করে নেয় অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ।
খ. মহৎ রাষ্ট্রের বীরত্বের গল্প আরগো
১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানে বিপ্লবের সময় শিক্ষার্থীরা তেহরানের আমেরিকান দূতাবাসে হামলা চালিয়ে সেখানকার ৬০ জনকে জিম্মি করে। কিন্তু সেসময় ছয় আমেরিকান দূতাবাস থেকে পালিয়ে কানাডার রাষ্ট্রদূত কেন টেলরের (Ken Taylor) বাসায় আশ্রয় নেয়। পালিয়ে বাঁচা ওই ছয় নাগরিককে গোপনে দেশে ফেরত নিতে ইরানে ‘সি আই এ’র একটি দল পাঠায় আমেরিকা। আর তারা সফলভাবেই তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নেয়। সেই ঘটনারই চিত্রায়ণ করা হয়েছে আরগোতে। চলচ্চিত্রটি সেরা চলচ্চিত্র, সেরা চিত্রনাট্য (অ্যাডাপ্টেড) ও সম্পাদনা শাখায় অস্কার পায়। সেই সঙ্গে সেরা চলচ্চিত্রসহ তিনটি বাফটা পুরস্কার, ডিরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা পুরস্কার, সেরা পরিচালক হিসেবে গোল্ডেন গ্লোবস অ্যাওয়ার্ডসহ বেশকিছু পুরস্কার লাভ করে। তবে শুধু পুরস্কারই নয়, ব্যবসাতেও সফল আরগো। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৪৪ মিলিয়ন ডলার এবং সেটি বিশ্বব্যাপী দুইশো ৩২ মিলিয়ন ডলার আয় করে।
অন্যদিকে ইরান বিপ্লবের পর থেকে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কটা সাপে নেউলে পর্যায়ে চলে যায়। আর সেই বিপ্লবকালীন ইরানই আরগোর পটভূমি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, চলচ্চিত্রটিতে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কথা সরাসরি স্বীকার করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির প্রোলগেই বলে দেওয়া হয়,
১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইরানের জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রপন্থি মোহাম্মদ মোসাদ্দি’কে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। তিনি ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলোকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে ইরানের তেল ইরানিদের হাতে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ক্যু ঘটিয়ে মোসাদ্দিকে ক্ষমতাচ্যুত করে রেজা শাহ্ পাহলভিকে ক্ষমতায় বসায়। তরুণ শাহ খুব বিলাসী জীবন যাপন করতেন ... সুপারসনিক বিমানে করে প্যারিস থেকে তার দুপুরের খাবার আনা হতো। কিন্তু ইরানের সাধারণ মানুষ তখন অনাহারে দিন কাটাতো। ... সূত্রপাত হয় নিপীড়ন ও শঙ্কাপূর্ণ একটি যুগের। অবশ্য এ সময় তিনি ইরানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচলন শুরু করতে একটি ক্যাম্পেইন আয়োজন করেন। এতে করে শিয়ারা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানের জনগণ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ... এরপর শুরু হয় প্রতিশোধের বন্যা, বিরোধী দলীয়দের হত্যা ও বিশৃঙ্খলা। ...
প্রোলগ থেকেই বোঝা যায়, নির্মাতা ‘সত্য ইতিহাস’ তুলে ধরতে চেয়েছেন তার চলচ্চিত্রে। যে ইরানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘হুমকি’ (শত্রু!) হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এককালে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে-ব্যাপারটা স্বীকার করে নেওয়া যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার। তাছাড়া চলচ্চিত্রের একাধিক জায়গায় শাহকে অত্যাচারী ও দুর্নীতিবাজ প্রমাণ করা হয়েছে; হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে তাকে- এর সবই হয়তো নিজেদের গা বাঁচাতে করেছেন নির্মাতা! কারণ, শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিলো তারাই। আর সেই ঘটনার ৩৩ বছর পর ২০১২-তে এসে আরগোর নির্মাতা নিজেদের ‘ভুল’টা স্বীকার করে নেওয়ার ‘মহত্ত্ব’ দেখান এভাবে- শাহের মতো শোষককে সমর্থন করাটা ঠিক হয়নি। তিনি হয়তো বোঝাতে চান, ভুল স্বীকার করার মতো মহত্ত্ব সবাই দেখাতে পারে না! আর এর সবই বোধহয় তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এর পরের বছরই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ওবামা-রুহানি ফোনালাপের১০ ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের বরফ গলতে শুরু করেছে তখন। এর বাইরে আরেকটি ব্যাপারও রয়েছে। দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক, যতো প্রতিকূল পরিবেশই হোক, যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের নাগরিকের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। তার জীবন রক্ষার কার্যকরী মোড়লীয় ক্ষমতা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই সংরক্ষণ করে। নাগরিকের প্রাণরক্ষার রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চ সফলতা এবং কোনো বিষয়ে ভুল স্বীকার করে নেওয়ার মহত্ত্ব- দুইয়ে মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেরই জয়জয়কার ধ্বনিত হয় নির্মাতা বেন অ্যাফ্লেকের ইমেজে ইমেজে।
গ. মুনলাইট নয়, সোডিয়াম আলোয় সাদা-কালোর তফাৎ বোঝা দায়
‘অস্কার সো হোয়াইট’ বিতর্কের পর অস্কারের ৯০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে নির্মিত কোনো চলচ্চিত্র অস্কার পেয়েছে। মুনলাইট-এর সব চরিত্রেই কৃষ্ণাঙ্গ অভিনয়শিল্পী কাজ করেছেন। একজন মানুষের জীবনের তিনটি পর্যায়ে তার আত্মপরিচয়, যৌনতা ও এসব নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি। তিনটি শাখায় অস্কারসহ গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড ছাড়া ‘শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে’তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পায়নি মুনলাইট। ‘শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে’, বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে চলচ্চিত্রটি অ-শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান-আমেরিকান ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাসোসিয়েশন-এর পাঁচটি শাখার সবগুলোতেই বিজয়ী হয়েছে। তাছাড়া সেরা চলচ্চিত্রসহ সাতটি শাখায় ব্ল্যাক রিল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এটি। অবশ্য বাফটা বা অন্য কোনো বড়ো মাপের পুরস্কার এর ভাগ্যে জোটেনি! আর পুরস্কারের পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও এটি অন্য অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। দেড় মিলিয়ন ডলারে নির্মিত চলচ্চিত্রটি মোটে ৫৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রের তালিকায় মুনলাইট দ্বিতীয় সর্বনিম্ন আয় করা চলচ্চিত্র।
এর মানে দাঁড়ায়, মুনলাইট তেমন একটা দর্শকপ্রিয়তা পায়নি। যদিও কোনো চলচ্চিত্রের পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে দর্শকপ্রিয়তা কখনোই বিবেচ্য নয়। সেখানে বিবেচ্য নির্মাণশৈলী, বক্তব্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতি। সেদিক থেকে মুনলাইট ‘উৎকৃষ্ট’ মানের চলচ্চিত্র। এতে লিটল নামের এক নিগ্রো তরুণের জীবনের নানা পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে। তার সেই জীবনে মাদকাসক্ত যৌনকর্র্মী মা, পালক পিতা মাদক ব্যবসায়ী উয়ান, উয়ানের স্ত্রী টেরেসা, শত্রু-মিত্র সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। লিটল তাদের এক পক্ষের হাতে মার খায়, আবার অন্য পক্ষের কাছে পায় আশ্রয়! বোঝা যায়, কৃষ্ণাঙ্গরা নিজেরাই নিজেদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। তার মানেটা দাঁড়ায়, শ্বেতাঙ্গরা না থাকলেও কালোরা অশান্তিতেই থাকবে। কারণ তারা এখনো ‘বর্বরতা’ ও ‘অপরাধ’ প্রবণতা ছাড়তে পারেনি। তাই এতদিন ধরে বলে আসা বর্ণবৈষম্য ইস্যুটাকে এতো গুরুত্ব না দিলেও চলবে! কারণ সাদাদের করা বৈষম্য না থাকলেও যে কালোরা দুর্দশাতেই থাকবে, তা একদিক দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন নির্মাতা। যে জন্যই হয়তো সাদাদের দেখানোর দরকার হয়নি মুনলাইট-এ। কিন্তু বাস্তবতা বলে, সুযোগ পেলেই শ্বেতাঙ্গরা সবসময়ই কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর চড়াও হয়েছে। এমনকি অস্কারের ইতিহাসেও এই বর্ণবৈষম্য প্রবল। যার কারণে গত বছর ‘অস্কার সো হোয়াইট’ আন্দোলনও করে কৃষ্ণাঙ্গ নির্মাতা-অভিনয়শিল্পীরা। আর এমন এক পরিস্থিতিতে মুনলাইট-এর অস্কারপ্রাপ্তি সেই বিতর্কে পানি ঢেলে দেয়। এতে একদিকে অস্কারের ‘মর্যাদা’ও রক্ষা পায়, আবার চলচ্চিত্রটিতে শ্বেতাঙ্গদের উপস্থিতি না থাকায় ‘গণতান্ত্রিক’ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্য আড়ালেই থেকে যায়।
অবশ্য অস্কারের রাজনীতি বুঝতে সেরা চলচ্চিত্র মুনলাইট-এর সঙ্গে তার নিকটতম প্রতিযোগী লা লা ল্যান্ড-এর তুলনা করলেও হয়তো কিছুটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। এবারের অস্কারে সবচেয়ে বেশি শাখায় পুরস্কার পেয়েছে লা লা ল্যান্ড- ছয়টি। সেই সঙ্গে এটি সেরা চলচ্চিত্রসহ পাঁচটি শাখায় বাফটা পুরস্কার, সাতটিতে মনোনয়ন পেয়ে সাতটিতেই গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। তাছাড়া অন্যান্য আরো জাতীয়-আন্তর্জাতিক পুরস্কার তো রয়েছেই। সেদিক বিবেচনায় ও অতীত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায়, লা লা ল্যান্ড-এরই অস্কারে সেরা চলচ্চিত্র হওয়া উচিত ছিলো। কারণ এর আগে প্রায় প্রতিবারই বাফটা, গোল্ডেন গ্লোব-এর মতো বড়ো বড়ো পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রকেই অস্কার পেতে দেখা গেছে। দ্য কিংস স্পিচ ও আরগোর পুরস্কারের তালিকা দেখলেও সেটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু এবারই প্রথম সেই ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটে। অবশ্য প্রথমে ‘ভুলক্রমে’লা লা ল্যান্ড-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছিলো এবারের পুরস্কার প্রদান আসরে। পরে সেটা সংশোধন করে মুনলাইটকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। আর সেই ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটায়, প্রশ্ন তো উঠতেই পারে ‘ভুল’টা কি আসলেই ভুল ছিলো!
প্রথমেই বলেছিলাম, অস্কার পুরস্কার লাভের সঙ্গে সাদা-কালোর রাজনীতি আছে কি না খতিয়ে দেখা দরকার। অস্কারের ৮৯টি সেরা চলচ্চিত্র ধরে আলোচনা করলে হয়তো পরিষ্কার একটি চিত্র পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক কারণেই সেটা করা সম্ভব নয়। তার পরও তিনটি চলচ্চিত্র থেকেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, পুরস্কার পাওয়ার জন্য শুধু নির্মাণশৈলীই যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে ক্ষমতবানদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও জড়িত।
ভিনদেশের অস্কার, স্বার্থের হাতিয়ার?
প্রতিবছর যে ২৪টি শাখায় অস্কার দেওয়া হয়, তার মধ্যে মাত্র একটি হলিউডের বাইরের চলচ্চিত্রের জন্য বরাদ্দ। আর এই একটি পুরস্কারের জন্য বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র শাখায় সারাবিশ্বের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা করে। অস্কারের শুরু থেকে অবশ্য এই শাখায় পুরস্কার দেওয়া হতো না। মূলত ১৯৪৭-৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হতো। এই সময় বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রগুলোকে প্রতিযোগিতা করতে হতো না। বরং অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো চলচ্চিত্রকে এই পুরস্কারটি দিতো। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিদেশি ভাষার সেরা চলচ্চিত্র বাছাই শুরু হয়। তখন থেকে এ পর্যন্ত দেওয়া ৬৮টি পুরস্কারের মধ্যে ৫৬টিই গেছে ইউরোপের দেশগুলোতে। বাকি ১২টির মধ্যে ছয়টি এশিয়া, তিনটি করে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো পেয়েছে।
হলিউডের চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণমান ছাড়াও বিশেষ কিছু কারণের বদৌলতে অস্কারে ভূষিত হয়, তা আগের আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়েছে। এবার দেখা দরকার কোন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দেশের চলচ্চিত্রকে বিদেশি ভাষার সেরা চলচ্চিত্র শাখায় বাছাই করেছে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ। এজন্য গত তিন বছরের বিজয়ী চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই হয়তো ‘সত্য’টা সামনে আসবে। চলচ্চিত্র তিনটি হলো পোল্যান্ডের ইডা (২০১৩), হাঙ্গেরির সন অব সাউল (২০১৫) ও ইরানের দ্য সেলসম্যান (২০১৬)।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনে বাবা-মা হারানো অ্যানা বেড়ে ওঠেন ক্যাথলিক কনভেন্টে। তরুণ বয়সে তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্ন্যাসিনী (Catholic Nun) হওয়ার। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের আগে নিয়মানুযায়ী তাকে জীবিত আত্মীয়দের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে হবে। সেই শর্ত পূরণে আন্না তার খালা উয়ান্ডা গ্রুজ-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, তার আসল নাম ইডা লেবেনেস্টেইন এবং তিনি একজন ইহুদি। এরপর তিনি তার মৃত বাবা-মা’র কবরের সন্ধানে বের হন। ইহুদিবিদ্বেষী এক পোলিশ খ্রিস্টান তার বাবা-মা’কে হত্যা করে তাদের সহায়-সম্পদ দখল করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ইডা তার বাবা-মার কবরের সন্ধান দেওয়ার বিনিময়ে সেই লোককে সম্পদের দাবি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন।
অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হলোকাস্ট বা ইহুদি নিধনযজ্ঞ নিয়ে নির্মাণ হয়েছে সন অব সাউল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বার থেকে মৃতদেহ বের করে নিয়ে যাওয়া ‘সন্ডারকমান্ডো’ দলের সদস্য সাউল অসল্যান্ডার। একদিন গ্যাস চেম্বার থেকে মৃতদেহ বের করার সময় এক শিশুর দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখতে পান তিনি। কিন্তু সেখানে কর্মরত নাজি চিকিৎসক ওই শিশুকে দমবন্ধ করে খুন করেন। এরপর সেই শিশুকে ইহুদি রীতি অনুযায়ী কবর দিতে চান সাউল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও ‘ব্যর্থ’ হন তিনি।
ইরানের থিয়েটারকর্মী দম্পতি এমাদ ও রানার জীবনে ঘটে যাওয়া ‘দুর্ঘটনা’কে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে দ্য সেলসম্যান-এর গল্প। তাদের বাড়িটি ধসে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, তারা অন্য এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এক রাতে নতুন বাসায় ফিরে এমাদ দেখতে পান তার স্ত্রী রানা নিখোঁজ এবং বাথরুম রক্তে সয়লাব হয়ে রয়েছে। পরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পেরে তিনি হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীকে দেখতে পান। জানতে পারেন, বাসায় ঢুকে রানাকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হয়েছে। মূলত তারা নতুন যে বাসায় উঠেছেন, সেখানে আগে এক যৌনকর্মী থাকতেন। কিন্তু তার বাসা ছাড়া ও নতুন ভাড়াটিয়া আসার বিষয়টি যৌনকর্মীর খদ্দেররা জানতেন না। ফলে এমনই এক খদ্দের এসে রানার ওপর চড়াও হন। একসময় রানা সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেও ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেন না এবং তারা পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগও দায়ের করান না। শেষ পর্যন্ত এমাদ তার স্ত্রীর ওপর চড়াও হওয়া ব্যক্তির খোঁজ পান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সেই ব্যক্তিকে থাপ্পড় দিয়ে চলে আসেন। এরপর তিনি ও তার স্ত্রী পুনরায় থিয়েটারে কাজ করতে চলে যান।
এই তিনটি চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ, ইডা ও সন অব সউল স্পষ্টতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষের চোখে দেখা ‘ইতিহাস’ বর্ণনা করে। যে ইতিহাসের রচয়িতা স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রও। তাছাড়া ইডা নিয়ে খোদ পোল্যান্ডেই বিতর্ক হয়েছে যে, সেটা পোলিশ খ্রিস্টানদের হেয় করেছে। তাদের দাবি, শুধু ইহুদিপন্থি গল্প হওয়ার কারণেই ইডাকে অস্কার দেওয়া হয়েছে।১১ আর সন অব সাউল তো পুরোপুরিই যুদ্ধে জার্মানদের নৃশংসতাকে তুলে ধরেছে। তাদের হাত থেকে একজন শিশুও নিরাপদ নয়, সেটাই দেখানো হয়েছে। যার ফলে আরো একবার সেই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ হয়। যে ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্র বলতে চায়, বলে, ইডা ও সন অব সাউল সেটাই প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্রের সুরেই সুর মিলিয়েছে চলচ্চিত্র দুটি। যার জন্য যথাযথ পুরস্কারও জুটেছে তাদের ভাগ্যে।
অন্যদিকে ইরানি নির্মাতা আসগর ফরহাদি’র দ্য সেলসম্যান দেখিয়েছে, ইরানের সামাজিক অবক্ষয়, জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, মানসিক টানাপড়েন, মানবিকতার সঙ্কট। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার টানাপড়েন ছাপিয়ে ‘শত্রু’কে পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে হয়তো অস্কার কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করতে চায়, তাদের কাছে ‘মেধা’র মূল্যই সর্বাধিক। তাছাড়া এমন এক সময়ে দ্য সেলসম্যানকে অস্কার দেওয়া হয়েছে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন। আর এর প্রতিবাদে স্বয়ং ফরহাদি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বর্জন করেন। এমন পরিস্থিতিতে এই পুরস্কার হয়তো ‘গণতান্ত্রিক’যুক্তরাষ্ট্রের ইমেজ রক্ষার কাজে লেগেছে। তাছাড়া চলচ্চিত্রটিতে যুক্তরাষ্ট্রের লাল তালিকার শীর্ষে থাকা ইরানকে রাষ্ট্র হিসেবে একপ্রকার ব্যর্থভাবে তুলে ধরা হয়। এজন্য ফরহাদিকে নিজ দেশে সরকারের রোষানলে পড়তে হয়।১২ সেদিক থেকে দেখলে, এক সেলসম্যানকে (ফরহাদিকে) কৃতিত্বের সঙ্গে ‘দেশের ইমেজ বিক্রি’র সফলতায় পুরস্কৃত করে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইমেজও রক্ষা করার সুযোগ হাতছাড়া করে না!
‘এই অস্কার লইয়া আমরা কী করিবো’
আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে ‘মানবতাবাদী’যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে সেখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের লাশের ওপর- এ ব্যাপারে সবাই অল্পবিস্তর অবগত। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। প্রথমে তাদেরকে তামাক, অস্ত্র, পোশাকসহ নানাধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে ‘বন্ধুত্ব’ গড়ে তুলে ‘সভ্যতা’র শিক্ষা দিতে চায় ইংরেজ, স্পেনিশ ও ফরাসিরা। অনেকে সেই উপহার সামগ্রী নিয়ে বন্ধুত্বও করেছিলো। সেই সুযোগে আসলে তারা আমেরিকা থেকে আদিবাসীদের নিজ দেশে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি শুরু করে। তাই পরবর্তী সময়ে যখন আর ‘বর্বর’ রেড ইন্ডিয়ানরা ‘সভ্য’ হতে চাইলো না, তখনই শুরু হলো অস্ত্রের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া। আর শেষ পর্যন্ত ১৯ শতকের শেষ দিকে এসে গোটা আমেরিকাই দখল করে নেয় ‘সভ্য’ ইংরেজরা।
‘বর্বর’রেড ইন্ডিয়ানদের অস্তিত্ব কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও, আধুনিক ‘সভ্য’ আমেরিকানদের উপহার-উপঢৌকনের বন্ধুত্ব গড়ার ধারা আজও অব্যাহতই রয়েছে। আজকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বড়ো পুরস্কারগুলোর অধিকাংশ তারাই দিয়ে থাকে। বিশ্বের কে কেমন কতোখানি ‘ভালো’কাজ করলো, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড তাই তাদের হাতেই থাকে! ফলে যারা তাদের ‘বন্ধু’হয়, পুরস্কারটাও তো তাদেরই পাওয়ার কথা। অন্যদের জন্য তিরস্কারটাই তুলে রাখে আমেরিকা। এজন্য আসগর ফরহাদি অস্কার পেলেও, তার নিজ দেশের মানুষেরই আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার থাকে না। ইরানের চলচ্চিত্র আমেরিকায় সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলেও, ইরান কিন্তু লাল তালিকার শীর্ষেই থেকে যায়। বিষয়টি এমন যে, ইরান শত্রু হলেও, সেখানকার গুণীর কদর করতে জানে যুক্তরাষ্ট্র! আবার হলিউডের যে চলচ্চিত্র রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত শক্তিশালী করে, পুরস্কার থাকে তার জন্যও।
আসলে ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত সবকিছুই তো আপেক্ষিক। পুঁজিপতির কাছে যা ভালো, সমাজতন্ত্রে তা গর্হিত। আবার মালিকের লাভ মানেই তো অন্যদিকে শ্রমিকের শোষিত হওয়া, যতো শোষণ ততো লাভ। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, একজনের কাছ থেকে পুরস্কার পেলেও, অন্যজনের কাছ থেকে তিরস্কার কপালে জুটতেই পারে। তাই পুরস্কার-তিরস্কারের পাকে-চক্রে না পড়ে, শিল্পী হিসেবে নির্মাতার ‘উচিত’ এক শতাংশ নয়, ৯৯ শতাংশের পক্ষে কথা বলা।
লেখক : মাহামুদ সেতু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন।
msetu.mcj@gmail.com
তথ্যসূত্র
1. https://web.archive.org/web/20150204080757/; retrieved on 25.04.2017
http://www.bangladesh-web.com/view.php?hidRecord=44486; retrieved on 25.04.2017
2. http://www.history.com/topics/roaring-twenties; retrieved on 05.03.2017
3. http://www.vanityfair.com/hollywood/2014/02/secret-oscar-history; retrieved on 22.02.2017
4. https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Academy_Awards#cite_note-6; retrieved on 25.02.2017
5. http://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html; retrieved on 25.02.2017
6. http://www.oscars.org/oscars/statuette; retrieved on 13.03.2017
7. http://www.oscars.org/oscars/statuette; retrieved on 13.03.2017
8. https://www.universityofcalifornia.edu/news/oscar-bait-or-pandering-audience; retrieved on 25.02.217
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Picture#Winners_and_nominees; retrieved on 25.04.2017
১০. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ তিন দশক পর কোনো ইরানি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের সরাসরি যোগাযোগের ঘটনা ঘটে। সেসময়ে নবনির্বাচিত ইরানি রাষ্ট্রপতি ড. হাসান রুহানি সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এতে করে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশ দুটির মধ্যে চলা দীর্ঘদিনের টানাপড়েন নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যদিও পরে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। সূত্র : http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-iran-idUSBRE98Q16S20130928; retrieved on 25.04.2017
11. http://www.buenosairesherald.com/article/182771/why-is-ida-controversial-in-its-homeland; retrieved on 25.04.2017
12. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/asghar-farhadi-the-salesman-forooshandeh-criticism-iran.html; retrieved on 25.04.2017
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন