কাজী মামুন হায়দার
প্রকাশিত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
দেখা না-দেখা, ভিন্ন ভিন্ন দেখা নিয়ে ‘দেখা’
কাজী মামুন হায়দার
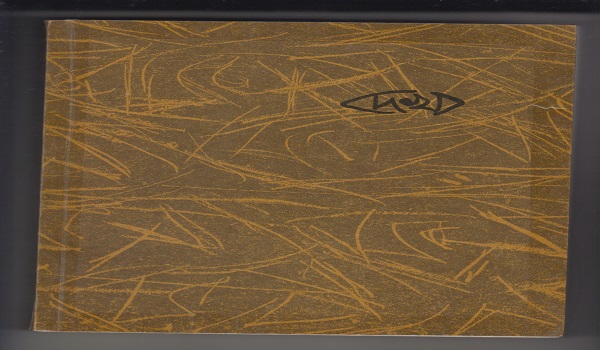
দেখা বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হলেই কেনো জানি গৌতম ঘোষের দেখা১ চলচ্চিত্রটির কথা মনে পড়ে যায়। তাই এই আলোচনাও দেখা দিয়েই শুরু করতে একরকম বাধ্যই হচ্ছি। গৌতম খুব যত্ন নিয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন, কখনো মনে হয় নির্মাতা হিসেবে এটিই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর সংলাপ, নির্মাণশৈলী, ক্যামেরা-ভাষা প্রতিটি পর্যায়ে দেখা, না-দেখার যে বোঝাপড়া তা রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। পঞ্চাশোর্ধ্ব কবি শশীভূষণ মধ্য বয়সের কিছু পরে দৃষ্টিশক্তি হারান। তার কাছে এক সময়ের দেখা পৃথিবী এখন অন্যরকম না-দেখা। শশীর বাড়িতে আশ্রিত স্বামী পরিত্যক্তা শরমা ও তার ছেলে সুমন।
অন্যদিকে আছেন বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে সৃষ্ট দাঙ্গায় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ থেকে ভারতে পালিয়ে আসা জন্মান্ধ গগণ চন্দ্র; যিনি কেবল শব্দ আর গন্ধ নিয়ে বেঁচে আছেন। যার কণ্ঠে সুর আছে কিন্তু চোখে দৃষ্টি নেই। তার কাছে লাল, নীল কিংবা সবুজ কোনো পার্থক্য তৈরি করে না; নদী আর সমুদ্রও হয়তো একই রকম! পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ এসবের কোনো মানে নেই এই মানুষটির কাছেদৃশ্যহীন এক না-দেখা জগতের মানুষ তিনি। তাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগে আসলেই কি কিছুই দেখেননি তিনি? তাহলে তার দেখা কী রকম? তার সুরে ভালোবাসার যে রঙ, সাগরের যে উত্তালতা সেটা আসে কীভাবে? তার কাছে পাখিই বা কী রকম; যে পাখির ডাক শুনে তিনি কণ্ঠে সুর তুলেছেন!
শশী, শরমা, সুমন, গগণ এদের প্রত্যেকের দেখা তাহলে কেমন? একজনের দেখার পর না-দেখা; একজনের একেবারেই না-দেখা; আর অন্যদের অব্যাহত দেখা। সবই কি একই, নাকি ভিন্ন? সমাজে অবশ্য শরমা, সুমনদের সংখ্যাই বেশি। তাই বেশি কথা হয় তাদের এই ‘দেখা’ নিয়েই। আর শশী বাবুর অতীত দেখা, বর্তমান দেখা, ভবিষ্যৎ দেখা—এসবই তিনি দেখেন তার মতো করে। তাইতো সুমনের ‘জ্যাঠু তুমি দেখতে পাও’ প্রশ্নের জবাবে শশী বলেন, ‘দেখতে পাই, তবে তোমার মতো করে নয়।’ আমরা হয়তো কেউই কারো মতো করে দেখি না।
এবার কথা বলতে ইচ্ছে করছে আকিরা কুরোসাওয়ার রাশোমন২-এর দেখা নিয়ে। একই ঘটনা সেখানে অনেকে দেখেন অনেকভাবে। আপাত চলচ্চিত্রের গল্পটি খুবই সাধারণ। বনের মধ্যে দস্যুর হাতে এক নারী ধর্ষিত এবং তার সামুরাই স্বামী খুন হন। কিন্তু বিচারকার্যের সময় এ ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের ভাষ্য আলাদা। দস্যু তাজোমারু, ধর্ষিতা, নিহত স্বামী (চলচ্চিত্রে অবশ্য তার আত্মা আরেকজনের মাধ্যমে কথা বলে), বৌদ্ধ ভিক্ষু ও কাঠুরিয়া প্রত্যেকেই পুরো ঘটনাটিকে যার যার মতো করে বর্ণনা করেন; অর্থাৎ ঘটনাটি তারা যার যার মতো করে দেখেছেন। মানে তাদের প্রত্যেকের দেখা আলাদা। যে কাঠুরিয়া, ভিক্ষু দূর থেকে ঘটনা দেখেন, তাদের সত্য এক; আবার যারা (দস্যু তাজোমারু, ধর্ষিতা, নিহত স্বামী) ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাদের কাছে সত্য আরেক ধরনের। তাহলে কোন দেখাটি সত্য?
আবার গীতিকবির কথায়, `Close your eyes and try to see'; চোখ বন্ধ করে দেখা। এই লাইন শুনেই নাকি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ আগ্রহী হয়েছিলেন তার মিসির আলি চরিত্র সৃষ্টিতে। তার বয়ানে বিষয়টি এ রকম—‘মিসির আলি এমন একজন মানুষ যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। যে পৃথিবীতে চোখ খুলেই কেউ দেখে না, সেখানে চোখ বন্ধ করে দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।’৩ তার মানে দাঁড়ায় দেখতে সক্ষম মানুষও চোখ বন্ধ করে দেখতে পারে। হুমায়ূনের যুক্তিতে চোখ বন্ধ করে সেই দেখা সাধারণ দেখার চেয়ে অনেক বেশি-ই শক্তিশালী।
তাহলে দেখা নিয়ে কথা বলায় খানিকটা জটিলতা আছে। দেখার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়তো আরো কঠিন। কিংবা কোন দেখাটা ঠিক কিংবা কোনটা বেঠিক—সেটাও অনেকক্ষেত্রে মূল্যায়নের অতীত। সেই দেখা নিয়েই কথা বলতে আজকের এই অবতারণা। আগেই বলেছি এটা কষ্টকর। মাহমুদুল হোসেনের সম্পাদনায় সংকলন `দেখা'; নাম নির্বাচনটি অসাধারণ। দেখার সব বস্তু—চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, স্থাপত্য—নিয়ে এই সংকলন বলেই হয়তো এমন নাম। সংকলনটি দেখেই আগের এই ধরনের আরেকটি সংকলনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। যারা এ ধরনের সংকলনের খোঁজ রাখেন তাদের নিশ্চয় মনে আছে `দৃশ্যরূপ'-এর কথা। বাংলা ১৪১০ বঙ্গাব্দে বের হওয়া সংকলনটির দুটি ইস্যু প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সেটার সম্পাদকও ছিলেন মাহমুদুল হোসেন। আমরা পাঠকরা অবশ্য এখনো উন্মুখ হয়ে আছি ওই রকম আরেকটি সংকলনের জন্য। কিন্তু আজও সেই আশা পূর্ণতা পায়নি। তবে সে স্থান দখল করে নিয়েছে দেখা। অবশ্য ভূমিকায় `দেখা'র সম্পাদকও (মাহমুদুল হোসেন) পরবর্তী সংকলন নিয়ে পাঠকদের খুব বেশি আশাবাদী করে তুলতে পারেননি। যাক এ নিয়ে পরে কথা বলবো। এখন `দেখা'কে দেখা যাক।
এক.
চলচ্চিত্র, চারুকলা, আলোকচিত্র ও স্থাপত্য চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে `দেখা' পাঠকদের পথ দেখিয়েছে। চলচ্চিত্র অংশের অর্ধেকটা জুড়েই তারেক মাসুদের অবস্থান। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। পুরো সংকলনটি তারেককে নিয়ে হলেও খারাপ হতো না। কারণ তারেক বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য কী ছিলেন, সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তারেক তো আসলে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া একটা লাল ফানুস; এখন যেটা থাকছে সেটা তার কাজ, স্বপ্ন। সেই কাজ নিয়ে লিখেছেন জাকির হোসেন রাজু `সিনেমার গল্প বলা ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ : প্রসঙ্গ মুক্তির গান' শিরোনামে। রাজু মূলত দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন ইতিহাস নির্মাণ নিয়ে। তিনি চলচ্চিত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী গবেষক। তাই তার লেখায় ইতিহাস উপস্থাপনের একটা ঝোঁক থাকে। সাধারণত সেই উপস্থাপনা অত্যন্ত যৌক্তিকও হয়। এ লেখার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটিই হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র ও কাহিনিচিত্র নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে তিনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের যে ইতিহাস নির্মাণ করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। পঞ্চদশ শতকে গণমাধ্যমের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীতে চলচ্চিত্রের বাঁধভাঙা বাণিজ্যিকীকরণের যে ছোঁয়া তিনি লেখায় দিয়েছেন, তা অনন্য।
ফ্রান্সে লুমিয়েরদের হাতে সৃষ্টি চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমিক রূপ পেয়েছিলো রাশিয়ায়; তারপর তা ইতালি, জার্মানি হয়ে আমেরিকায় গিয়ে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আজকের অবস্থানে এসেছে। যখন ভাবি ঝিগা ভের্তভের সেই কিনো-আই আন্দোলন আজ ক্যাটরিনা কিংবা মল্লিকা শেরওয়াতের শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, তখন চলচ্চিত্রের দর্শক হিসেবে নিজেকে খুব বেশি অসহায় মনে হয়। যখন দেখি পাওলি দাম কিংবা সানি লিওনিরা চলচ্চিত্র নয়, অন্য কারণে চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন—তখন অন্যদের কী হয় জানি না, আমি ভীত, শঙ্কিত হয়ে উঠি। সেই শঙ্কা থেকে দর্শককে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিলেন তারেক। এক্ষেত্রে তারেকের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সেটা নিয়ে নির্মিত তার চলচ্চিত্রগুলো। প্রামাণ্যচিত্র মুক্তির গান ও তার নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্লেষণী এই লেখা চলচ্চিত্রের অনেক কিছুর সন্ধান দেয়।
প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে মাহমুদুল হোসেনের লেখালেখি আগে থেকেই। তার ‘সিনেমা’৪ নামের পুস্তকটিতে ‘প্রামাণ্যচিত্র : সত্যবিষয়ক সমস্যা ও কিছু বিবেচনা’ শিরোনামে লেখাটি প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এই প্রযুক্তির যুগে তরুণ প্রামাণ্যচিত্রনির্মাতাদের জন্য লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্যচিত্রে সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে যে খেলা হয়, তা বোঝা খুব জরুরি। বিখ্যাত নানুক অব দ্য নর্থ-এর বিপরীতে গিয়ে লুই বুনুয়েলে’র ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড বা হ্যান্স জারগেন সাইবারবার্গের হিটলার, অ্যা ফিল্ম ফ্রম জার্মানি দেখিয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তার সমাধানও জরুরি। এবারেও তিনি লিখলেন বাংলাদেশের অন্যতম নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে। শিরোনামটি ভালো লেগেছে‘তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যছবি : স্বদেশের সত্য-কোষ’। স্বপ্নভূমি, বনযাত্রী ও তাজউদ্দিন আহমেদ : নিঃসঙ্গ সারথি নামে তিনটি প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে স্বদেশের সত্য-কোষ অনুসন্ধান করেছেন মাহমুদুল। দেশহীন, পরিচয়হীন কিছু মানুষের চলচ্চিত্র স্বপ্নভূমি। মাহমুদুলের ভাষায়, ‘বিচ্ছিন্ন পরিবারের কান্না, আশাভঙ্গের বেদনা, মানুষ নিয়ে রাজনীতির নিষ্ঠুর খেলা এবং শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গের ইঙ্গিত এসব কিছু স্থান পেয়েছে ছবিতে।’ সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে যে প্রশ্ন মাহমুদুল তার আগের লেখায় তুলেছিলেন, সেটা প্রয়োগ করেছেন প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আলোচিত এই লেখায়। প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে প্রজেক্টের ধারণা, তহবিল, গবেষণা, ভিজ্যুয়াল রিয়ালাইজেশন এবং আবেগজাত সাবজেক্টিজমের বাইরে গিয়ে তানভীর কীভাবে কাজ করেছেন তা দেখার চেষ্টা এই প্রবন্ধ।
বনযাত্রী নিয়ে মাহমুদুলের নিজের বক্তব্য অনেকটা এ রকম—‘সত্য নির্মাতার কাছে পূর্বনির্ধারিত নয়; বনযাত্রাকালে যাপিত জীবন, বনযাত্রীদের বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং জীবনের কথা নির্বাচিত কিন্তু স্বতস্ফূর্ত, যেন অনায়োজিত। ... বনযাত্রী এইসব মানুষের জীবন ভাগ্যের বিষয়ে কোনো অনুযোগ নেই। দারিদ্র্যকে তারা ক্যামেরার সামনে একটা ইস্যু করে তুলতে ব্যস্ত নন।’ প্রামাণ্যচিত্রের সত্য যে আপেক্ষিক ও নির্মাতার নিজস্ব সত্য, সেটা এই প্রবন্ধে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আর একজন তাজউদ্দিনের মধ্য দিয়ে একটি দেশের সূর্যোদয়ের ইতিহাস তুলে ধরা চলচ্চিত্র হলো তাজউদ্দিন আহমেদ : নিঃসঙ্গ সারথি। তানভীরের এক অসাধারণ উদ্যোগ। মোটকথা, বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের অবস্থা এবং তার মূল্যায়নের একটি বড়ো পথ এই প্রবন্ধটি খুলে দিয়েছে।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় প্রজন্মের নায়কদের একজন মোরশেদুল ইসলাম ‘দেখেছেন’ অকালপ্রয়াত আরেক নায়ক তারেক মাসুদকে। স্মৃতিকথামূলক এই লেখায় মোরশেদুল তার দেখা তারেককে তুলে ধরেছেন। কেনো জানি যতোটা আগ্রহ নিয়ে এই দেখা পড়তে শুরু করেছিলাম, তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি। একই ধরনের কথা বলতে হয়, শাহাদুজ্জামানের লেখাটি নিয়েও। আগেই বলেছি ‘দেখা’ নিয়ে কথা বলার কিছু সমস্যা আছে। সেই সমস্যা মাথায় রেখেই এমন কথা বলার সাহস করছি।
ভারতের যে কজন নির্মাতা ‘বলিউডি সিনেমা’র ধারণা থেকে বের হয়ে এসে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তাদের অন্যতম মণি কাউল। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে চলে যাওয়া এই নির্মাতাকে দেখার চেষ্টা ছিলো ‘দেখা’য়। মণি কাউলকে নিয়ে খুব বেশি লেখালেখি বাংলাদেশে হয়েছে বলে জানা নেই। তাই ‘দেখা’র এই দেখার চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ধ্রুপদ গাইয়ে মণি কাউল পুনেতে ঋত্বিকের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তার প্রথম চলচ্চিত্র উস্কি রোটি দেখেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখেছি সিদ্ধেশ্বরী। মনে হয়েছে, মণি কাউলকে নির্দ্বিধায় আলাদা করা যায়, বলিউডের শরীরী ভাঁজ থেকে, পাওলির খোলা পিঠ থেকে। মণি অনন্য হয়ে ওঠেন তার ‘পাগল’ গুরুর মতো। চে হুসাইন ভালো লিখেছেন, কিন্তু ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য : মনি কাউল’ শিরোনামে লেখাটির মধ্যে কিছু দূর পরপর বড়ো বড়ো ইংরেজি উদ্ধৃতির ব্যবহার এর ছন্দপতন করেছে। ভাবানুবাদ করে মণি’র এসব কথা মূল লেখায় দিয়ে end note-এ মূল ইংরেজিটা দিলে মনে হয় ভালো হতো।
এছাড়া ফৌজিয়া খানের প্রামাণ্যছবি আমাকে বলতে দাও নিয়ে আলোচনা ভালো লেগেছে। আজ এই সময়ে এসে চলচ্চিত্রের যে ডিসকোর্স দাঁড়িয়েছে, সেখানে শৈশব পেরিয়ে আসা বধূশাহনাজ, আয়েশা, নার্গিসরা প্রায় উপেক্ষিত। আর যদি তারা চলচ্চিত্রে আসেও সেটা ব্যবসার নানা উপকরণ হয়ে। মাতৃত্ব বুঝে উঠার আগেই মা হওয়া আয়েশাদের বন্দিত্বের কথা যেনো কেউ বলে না। যেমন স্বামী বা বিয়ে কী বস্তু বোঝেনি দীপা মেহতার ওয়াটার-এর সেই শিশুটি; যে কিনা মরণাপন্ন বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুশয্যায় বসে নিজের মনে আখ চিবোচ্ছিলো। আয়েশা, নার্গিসরা হয়তো এমনটা করে না, কিন্তু মুক্ত থেকেও পুরো দুনিয়াটাকে তাদের কাছে কেবল কারাগার মনে হয়। আলোচনাটি আমাকে বলতে দাও দেখতে আগ্রহী করে তোলে। চলচ্চিত্রটি যদিও দেখা হয়নি। অবশ্য ঢাকার বাইরে থেকে কারো জন্য এসব চলচ্চিত্র দেখতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়; তার পরও ফৌজিয়া খান হয়ে লেখক তপন কুমার পালের চোখ দিয়ে এ দেখা ভালো লেগেছে।
দুই.
দীর্ঘকাল ধরে মানুষের ইতিহাস প্রবাহিত হয়েছে মুখে মুখে, সেটা ছিলো oral tradition-এর যুগ। মানুষ অনেক আগেই সেসময় পেরিয়ে এসেছে। তারা প্রতিদিন জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নথি উৎপাদন করছে। সময়ের প্রবাহে এই নথিই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা নির্মাণ করে। গবেষকরা সেই নথি বিশ্লেষণ করে, সেখান থেকে নির্যাসটুকু সংগ্রহ করে নেন। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। মনসুর উল করিম, মারজারেহাসীন মুরাদ, আল মনসুর, ঢালী আল মামুন ও মাহমুদুল হোসেনের কথোপকথন পড়তে পড়তে আবার যেনো সেই oral tradition-এর যুগে ফিরে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিলো আদিবাসী কোনো এক বৃদ্ধ যেনো তার প্রজন্মকে পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে বিগতের কথা শোনাচ্ছেন, অতীতের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছেন।
মনে হয়েছে পড়ছি, আবার একই সঙ্গে আড্ডাও দিচ্ছি। পাঠক হিসেবে নিজেকে ওই আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে হয়েছে। আসলে ইতিহাসটা, অতীতটা মনে হয় এভাবেই জানতে হয়, শিখতে হয়। চারকোণা বইয়ের পাতার পর পাতায় ‘বাবরের পুত্র হুমায়ূন’ মুখস্থ করে আর যাই হোক ইতিহাস জানা যায় না। পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিতে হয় ইতিহাসের কাছাকাছি। এমন আয়োজনের জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আড্ডার ছলে, গল্পের ছলে বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাস (আসলে একধরনের দেখা) জানানোর জন্য। রশীদ চৌধুরী ও চারুকলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান—এগুলো জানাও ছিলো জরুরি। এছাড়া একজন ব্যক্তি মনসুর উল করিম ও শিল্পী মনসুর উল করিমের বোঝাপড়া, বেড়ে উঠা, ইতিহাসের অংশ হওয়া ইত্যাদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা দেখার সেই জন্মান্ধ গায়ক গগণের মতো কোনো কিছু না-দেখেই অনেক কিছুকে দেখার প্রয়োজন মেটায়।
মোহাম্মদ কিবরিয়া ও আমিনুল ইসলামকে নিয়ে দুটো প্রবন্ধ আছে এই সংকলনে। দুটো লেখাতেই দেখার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে এসেছে। তৈয়বা বেগম লিপি ‘সোনালি সময়’ শিরোনামে আমিনুলকে নিয়ে লিখেছেন; সেখানে ব্যক্তি আমিনুল শিল্পী আমিনুলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তি, একজন শিল্পীকে কিন্তু এ দুভাবেই দেখা যায়। লিপির এ দেখা ভালো লেগেছে। শিল্পের বর্ণনা তো সবাই করে, কিন্তু শিল্পের পাশাপাশি ব্যক্তির স্বরূপ অনেককে অনুপ্রাণিত করে, স্বপ্ন দেখায়। আসলে সবকিছুর শেষে তো কেবল স্বপ্নই থেকে যায়, তাই না? অন্যদিকে শামীম ইমতিয়াজ লিখেছেন কিবরিয়াকে নিয়ে। সেটা ব্যক্তি কিবরিয়াকে ছুঁয়ে শিল্পী কিবরিয়ার কাছে যাওয়া—সেটাও একধরনের দেখা। সেখানে কিবরিয়া আছেন, আছে ইতিহাস—আছে শিল্পের বর্ণন। এ বর্ণন কেবল শিল্পের নয়, একজন ব্যক্তিকে দেখা। তবে দেখার এই নানা রূপ পাঠকদের নিঃসন্দেহে ভাবিয়েছে, ব্যক্তির বোঝাপড়ার জায়গাগুলো পরিষ্কার করেছে।
ডিজিটাল আর্ট নিয়ে আজকের বিশ্বে যতো বিতর্ক হচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ফিরে যেতে হয় প্রাচীন গ্রিসে। সেখানে শিল্পের পুনরুৎপাদন হতো দুটি প্রক্রিয়ায়—কোনো শিল্প কর্ম হুবহু নতুন করে তৈরি করা, না হয় ছাপ দেওয়া। তবে এই পুনরুৎপাদন তারা মূলত করতো ব্রোঞ্জের কাজ, টেরাকোটা ও মুদ্রা উৎপাদনের জন্য। তবে এর বাইরে শিল্পের অন্যান্য শাখায় পুনরুৎপাদন অনুপযোগী ছিলো। মধ্যযুগে পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত হতো কাঠখোদাই, পরে যুক্ত হয় এচিং। আর ১৯ শতকের শুরুতে আবির্ভাব লিথোগ্রাফির। লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের কয়েক দশকের মধ্যে এলো আলোকচিত্র, তা লিথোগ্রাফিকেও ছাড়িয়ে গেলো। আলোকচিত্র মূলত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় শৈল্পিক ক্রিয়াকর্মে হাতের ব্যবহার লোপ করে দেয়। আর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রযুক্তির অগ্রসরতায় যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন মোটামুটি সম্পূর্ণতা অর্জন করে।
প্রযুক্তির এই উত্তরোত্তর উন্নতির ফসল আজকের প্রকাশনা শিল্প। যেখানে যেকোনো শিল্পের পুনরুৎপাদন কেবল ইশারার বিষয়। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ‘দেখা’য় কথা হয়েছে ডিজিটাল শিল্পকর্ম নিয়ে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটারে তৈরি আর্টের শিল্পগুণ নিয়ে। অবশ্য এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারাই, যারা শিল্পের ঘাটে নৌকা বেঁধে নিজেদেরকে আভিজাত্যের আসনে বসাতে চান; শিল্পকে কেবল লক্ষ টাকায় কিনে নিজেদের জন্য ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখতে চান। অনেকে বলছেন, হাতের ছোঁয়া নেই, সেটা শিল্প হয় কীভাবে? আবার অন্য দলের প্রশ্ন এখানে তো কাজ করে কম্পিউটার। অন্যদিকে ডিজিটাল আর্টের পক্ষের লোকজন সবকিছু খারিজ করে মানুষের জয়গান তুলে বলছেন, কম্পিউটারের সহায়তা নিলেও কাজ করে তো মানুষেরই মস্তিষ্ক।
বিতর্ক যা-ই থাক, প্রযুক্তির বিকাশ আজ এই মুহূর্তে যেখানে ঠেকেছে, সেখানে ডিজিটাল আর্টের ব্যবহারকে দাবিয়ে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই লিওনার্দোর ছবি কেবল আপনি একা ল্যুভর মিউজিয়ামে রাখবেন, আর বাকিরা এর পুনরুৎপাদন দেখে দুধের সাধ ঘোলে মেটাবে, সেদিন শেষ। উড়োজাহাজের মডেল আঁকা লিওনার্দো যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও হয়তো মোনালিসাকে এঁকে ইন্টারনেটের গ্যালারিতেই রেখে দিতেন। কারণ মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁচিয়ে রাখার যে কাজ শিল্পীরা যুগে যুগে করেছেন, সেখানে সবসময়ই সাধারণ মানুষই প্রথম সারিতে ছিলো। লক্ষ টাকায় চিত্রকর্ম কিনে মানুষ ড্রয়িং-রুম বন্দি করে রাখবে সেই স্বপ্ন প্রকৃত শিল্পী দেখেনি। তাই ডিজিটাল আর্ট নিয়ে যতো বিতর্কই থাক, তা এগিয়ে যাবে স্বমহিমায়; শিল্পের মহিমা নষ্ট না করে। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এ ধরনের বয়ান জরুরি।
এছাড়া ‘স্বদেশ, ব্যক্তি ও বিমূর্ত শিল্প’ শিরোনামে দীর্ঘ লেখাটি শিল্পকলা নিয়ে অনেক অজানা প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে। ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে শিল্পের যে বিরোধ, নিয়ন্ত্রণের যে তীব্র আকাক্সক্ষা তা যুগে যুগে ছিলো, আছে। রাষ্ট্র সবসময় শিল্পের বিমূর্ততাকে অবজ্ঞা করেছে। হয়তো বোঝেনি, না হয় বোঝার চেষ্টাই করেনি। কিন্তু রাষ্ট্র গড়ে উঠার অনেক আগেই শিল্পে বিমূর্ততা, তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তাই রাষ্ট্র, শিল্প ও বিমূর্ততার দ্বন্দ্ব, তার ইতিহাস নিয়ে এই আলোচনা সমঝদার পাঠককে আরো সমঝদার করেছে। পুরো সংকলন জুড়ে এই বিভাগটির আলোচনার গভীরতা ও বৈচিত্র্য পাঠকদের চারুকলা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।
তিন.
আলোকচিত্র অধ্যায়ে কোনো মৌলিক লেখা না থাকায় কিছুটা হতাশ হতে হলো। সুসান সনটাগের ‘অন ফটোগ্রাফি’ পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ‘ইন প্লেটোস কেইভ’ অনুবাদ দিয়ে অধ্যায়ের শুরু। শান্ত সায়ন্তের অনুবাদ করা লেখাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কয়েকটি লাইন দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি। লেখকের ভাষ্যমতে, ‘আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যেন বিশ্বকেই সংগ্রহ করা। সিনেমা এবং টেলিভিশন দেয়াল আলোকিত করে তোলে, জ্বলে উঠে এবং নিভে যায়। কিন্তু স্থিরচিত্রের ছবি একটি বস্তুও বটে, হালকা সস্তায় তৈরি করা যায়, সহজে বহন এবং সংরক্ষণ করা যায়।’
১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা বইয়ের এই কথাগুলো নিয়ে আজ ২১ শতকে এসে কিছু কথা না বললেই নয়। আলোকচিত্রকে আসমানে তুলে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রকে খারিজ করে দেওয়ার যে মনোভাব সুসান দেখিয়েছেন তা আজকের সময়ে এসে আর খাটে না। প্রযুক্তির বিকাশ আজ যেখানে দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে কেবল চলচ্চিত্র আর টেলিভিশন এখন হঠাৎ দেয়াল আলোকিত করে না। প্রতিক্ষণ মানুষের পকেটে পকেটে ঘোরে, ঘোরে মানুষের মস্তিষ্কে। ইন্টারনেট নামক কল্পনাতীত প্রযুক্তিটির আবিষ্কার মানুষকে কোথায় নিয়ে গেছে কিংবা প্রতিদিন নিয়ে যাচ্ছে তা এখন কল্পনা করতে ভয় হয়। তাই এই সময়ে চলচ্চিত্র কিংবা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানকে সংগ্রহের তকমা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ আর নেই। পকেটে থাকা থার্ড জেনারেশন মুঠোফোনটিতে সারা পৃথিবীকে সংগ্রহে রাখতে এখন খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। টিভি-অনুষ্ঠান আর সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রের আর্কাইভকে পকেটে নিয়ে ঘুরতে, দেখতে এখন আর কাড়িকাড়ি টাকাও খরচ করতে হয় না। কয়েকটা বাটন নিমিষেই ঘুরিয়ে নিয়ে আসে নতুন সেই আশ্চর্য সাইবার দুনিয়ায়।
এসব কথা দিয়ে আমি মোটেও আলোকচিত্রের মহিমাকে ঋণাত্মক জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করছি না। কেবল বলছি, সংরক্ষণ কিংবা সস্তায় তৈরির ধুয়াতুলে টেলিভিশন, চলচ্চিত্রকে এখন আর পিছিয়ে রাখা যাবে না। এছাড়া আলোকচিত্রের উপযোগিতা নিয়ে যেসব কথা এই লেখায় বলা হয়েছে, তার অনেকগুলোই আজ আর হালে টেকে না। বাস্তবতা নির্মাণ, সত্য বলার যে গুণ আলোকচিত্র এক সময় ধারণ করতো, প্রযুক্তির বদৌলতে তা আজ প্রতি মুহূর্তে প্রশ্নবিদ্ধ। তাই সত্য, বাস্তব নিয়ে বর্তমানে আলোকচিত্রের এতো বেশি উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। এছাড়াও মুভি ক্যামেরা ও ফিল্মের দাম বর্তমানে কলম ও কাগজের দামের পর্যায়ে হওয়ায় ভিজ্যুয়াল বাস্তবতা নির্মাণ ও সংরক্ষণের কথা উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। তার পরও আলোকচিত্র নিয়ে এমন তাত্ত্বিক লেখার প্রয়োজন আছে। তবে তা মৌলিক হলে আরো ভালো হতো; হয়তো সুসানের চিন্তাকে আর একটু এগিয়ে নেওয়া যেতো।
আর ফটোফিচার সবসময়ই চলচ্চিত্রের মতো গল্প বলে। এক সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেম আর একটি ফ্রেমের পার্থক্য ঘুচিয়ে চিত্রকে চোখের সামনে গতিময় করে তোলে। ফটোফিচার বা হালের প্রামাণ্য-আলোকচিত্রে উঠে আসে কখনো নিম্নবর্গের অসহায় চোখ, নাগরিক অস্থির জীবন, নদীর তপ্ত বালুর কান্না কিংবা ভারতের আসামে পুলিশের ক্রসফায়ারের নামে গুলিতে হত্যা করা অসহায় যুবকের শরীর৫। ‘টোবাকো টেইল’ নামের এই প্রামাণ্য-আলোকচিত্রে কিছু নিম্নবর্গের মানুষের ধীরে ধীরে মৃত্যুর কাছে এগিয়ে যাওয়ার ছবি এসেছে। লক্ষ্যহীন ওই মানুষগুলোর জীবনে আলো, রঙের উপস্থিতি নেই বলেই হয়তো আলোকচিত্রী তাদের দেখেছেন সাদা-কালো ফ্রেমে। প্রতিটি ছবির ডেপথ্ অব ফিল্ড, ডিটেইল অসাধারণ। প্রামাণ্য-আলোকচিত্রে থাকা তামাকের তামাটে কালোয় রাঙানো এক নারীর চোখ যেনো অনেক গল্পের কথা বলে; যে গল্প কেবল মরে বেঁচে থাকার।
চার.
রাষ্ট্র, ক্ষমতা সবসময়ই সাধারণকে আরো বেশি সাধারণ করে তুলতে কাজ করে। কোথাকার একজন স্পার্টাকাস ‘অসাধারণ’ হয়েছিলেন, আর তা নিয়েই বেঁধেছিলো যতো গণ্ডগোল। কিংবা একজন মার্টিন লুথার কিং চিৎকার করে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন; আবার মহামতি লেলিন বলেছিলেন সাধারণের কথা অসাধারণ হয়ে। রাষ্ট্র কোনোটিই ভালোভাবে নেয়নি। কারণ এই ‘অসাধারণরা’ই বেশিরভাগ সময় শাসকদের টেনে নামিয়ে সাধারণ করে তোলে। তাই অসাধারণদের সংখ্যা কম হয়। তার পরও চাঁপাইনবাবগঞ্জের কার্তিক পরামানিকরা রাস্তার ধারে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগান, পলান সরকার পথে পথে ঘুরে বই বিলান আর নওগাঁর বৃদ্ধ ভিক্ষুক গহের আলী কুড়িয়ে আনা তালের বীজ দিয়ে গড়েন তাল-সাম্রাজ্য। এই অসাধারণরা ছিলেন বলেই হয়তো আজকের প্রজন্ম স্বপ্ন দেখে এগিয়ে যাওয়ার।
‘আরবান স্টাডি গ্রুপ’-এর স্থপতিদের তেমনই মনে হয়েছে। উন্নত দেশগুলো যখন তাদের সামান্য সামান্য পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্যগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, বিপরীতে আমরা আমাদের সোনার খনি পুড়িয়ে কয়লা করছি। চারশো বছরের পুরোনো নগরী ঢাকার বেশিরভাগ স্থাপনাকে যখন ধ্বংস করা হচ্ছে, তখন এই প্রাণহীন কীর্তিগুলোর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন তারা। তারা পুরান ঢাকার দুই হাজার ভবন ও অসংখ্য রাস্তাকে হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ এর বিপরীতে সরকার মাত্র ৫৭টি ভবন ও নয়টি রাস্তাকে হেরিটেজ তালিকায় তুলেছে। আরবান স্টাডি গ্রুপের তালিকা তো নস্যি, সরকারের তালিকাভুক্ত ভবনের অনেকগুলোও নাকি ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এমতাবস্থায় বিশাল এই স্বর্ণখনিকে বাঁচাতে, নিজেদের দখলে নিতে হীরক রাজার দেশ-এর মতো দড়ি ধরে টান মেরে রাজাকে খান খান করতে হবে। রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এ খনি সাধারণের, এই খনি সাধারণের স্মৃতি হয়েই থাকবে। এজন্য চাই জনসচেতনতা, চাই সাধারণের অসাধারণ হয়ে এগিয়ে আসা। সেই কাজটি করেছে আরবান স্টাডি গ্রুপ। একই সঙ্গে তারা অমূল্য স্থাপনাগুলো রিস্টোরেশন করলে তার রূপ কী হবে তাও তুলে ধরেছেন।
আমরা হয়তো জানি না, নষ্ট-অস্থির এই সময়ে অসাধারণ এই গ্রুপটির লড়াই নতুন কোনো সূর্যের উদয় করবে কি না; তবে এ কথা ঠিক, যদি কখনো এই সম্পদ লুটও (!) হয়ে যায়, তাদের এই অসাধারণ ডকুমেন্টেশন শাসককে দেশের সমান সময় ধরে ধিক্কার পাওয়ার সুযোগ করে দেবে।
পাঁচ.
এই পর্যায়ে একেবারেই ভিন্ন কিছু দেখা দিয়ে শেষ করবো। আগেই বলেছি, সংকলনটির ধারাবাহিকতা নিয়ে পাঠককে খুব বেশি আশাবাদী করতে পারেননি সম্পাদক। তার পরও আশা থাকবে, এই সংকলনটি ‘দৃশ্যরূপ’-এর মতো দুটি সংখ্যা বের হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না। প্রকাশনার মান যদি একটু খারাপও হয়, এতো দামি কাগজ যদি ব্যবহার করা নাও যায়, ছবিগুলো যদি গ্লোসি কাগজ ছেড়ে ৮০ গ্রাম অফসেটে ছাপানো হয়তার পরও যেনো এর ধারাবাহিকতা থাকে। কারণ শিল্পের এই শাখাগুলো নিয়ে মাতৃভাষায় লেখালেখি অনেক কম। আর যে দু-চারটি হয়, তার প্রকাশনার ধারাবাহিকতা নেই বললেই চলে। তাই গুণগত মান একটু ছাড় দিয়েও এ ধরনের বই, সংকলন পাঠক চায়।
প্রবন্ধগুলোর এক অনুচ্ছেদ থেকে আরেক অনুচ্ছেদের ফাঁক এতো বেশি দেওয়ার মনে হয় প্রয়োজন ছিলো না। অপ্রয়োজনীয় এই ফাঁক কমিয়ে দিলে বেশকিছু কাগজের সাশ্রয় হতো। সাধারণ পাঠক ও বইয়ের নিয়মিত ক্রেতা হিসেবে আর একটা কথা না বলে পারছি না; দেখুন, এই প্রজন্মের বিশাল একটা অংশ এখন চলচ্চিত্র, চারুকলা, আলোকচিত্র, স্থাপত্য এসব শাখায় ভিড় করছে। স্বপ্নবান, সৃষ্টিশীল এই তরুণদের বেশিরভাগই অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয়। বিশেষ করে শিল্প অনুরাগী বেশিরভাগ তরুণই বৈষয়িক বিষয়ে উদাসীন হয়—তাদের পক্ষে এতো টাকায় এই সংকলন কেনা একটু কঠিনই। তাই দাম কমিয়ে স্বপ্নবান বেশিকিছু মানুষের হাতে এই সংকলনটি পৌঁছানো গেলে ভালো হতো। তার পরও নিশ্চয় ক্ষুদ্র সংখ্যক কিছু স্বপ্নবান এই সংকলনের স্পর্শ পেয়েছেন। আগামী দিন নিশ্চয় আরো বেশি বেশি স্বপ্নবানের বৃহৎ স্বপ্ন সৃষ্টিতে এই সংকলনটি এগিয়ে আসবে এই প্রত্যাশায় দেখাকে দেখার ইতি টানছি; নিশ্চয় অচিরেই আগামী সংখ্যায় দেখা হবে।
বইয়ের নাম : দেখা
সম্পাদক : মাহমুদুল হোসেন
প্রকাশক : মাহমুদুল হোসেন, ধানমণ্ডি, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪১৮, ডিসেম্বর ২০১১
প্রচ্ছদ : মিতু হক
মূল্য : ৫২০ টাকা
লেখক : কাজী মামুন হায়দার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ান।
kmhaiderru@yahoo.com
তথ্যসূত্র
১. গৌতম ঘোষ পরিচালিত দেখা ২০০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। দেখা ওই বছর সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
২. আকিরা কুরোসাওয়ার ৮৮ মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি সাদাকালোয় নির্মিত। রাশোমন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন লায়ন, ডিরেক্টর গিল্ড অ্যাওয়ার্ড, ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ডসহ ২৪তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে সম্মাননা পুরস্কার পায়।
৩. আহমেদ, হুমায়ূন (১৯৯০ : ভূমিকা); সাইন্স ফিকশন সমগ্র; প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
৪. হোসেন, মাহমুদুল (২০১০); সিনেমা; ফ্ল্যাট ১/বি, বাড়ি ২৮, সড়ক ১৫ (নতুন), ধানধণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৫. মণিপুরের স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করা সংগঠন ‘পিপলস লিবারেশন আর্মি’র এক সময়কার সৈনিক সঞ্জিৎ স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে সংগঠন ছেড়ে চলে আসেন। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সাধারণ জীবনযাপনে। পরিবারের সঙ্গে তিনি বসবাস করতে শুরু করেন। চাকরিও নিয়েছিলেন স্থানীয় একটি হাসপাতালে। মৃত্যুর গন্ধমাখা জীবন ছাড়লেও, মৃত্যু তার পিছু ছাড়েনি। একদিন দিনে-দুপুরে তাকে ঘিরে ফেলে স্পেশাল ফোর্স মণিপুর র্যাপিড অ্যাকশন পুলিশ। সঞ্জিৎকে গ্রেপ্তারের পর ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হয়। বিচারবহির্ভূত এই হত্যার পুরো প্রক্রিয়াটি ক্যামেরায় বন্দি করেন মণিপুরের স্থানীয় এক আলোকচিত্রী। ভারতের স্বনামধন্য সাপ্তাহিক তেহেলকা ডট কম সেই আলোকচিত্রগুলো সংগ্রহ করে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন


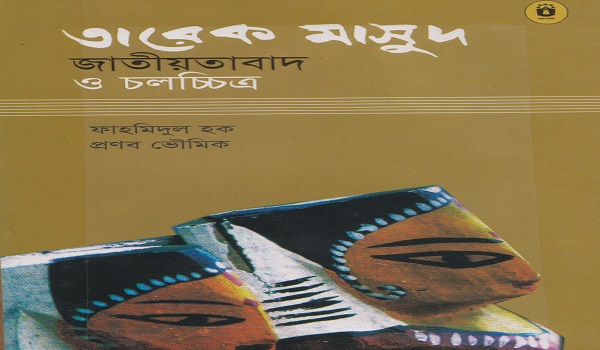
1735263359.jpg)




