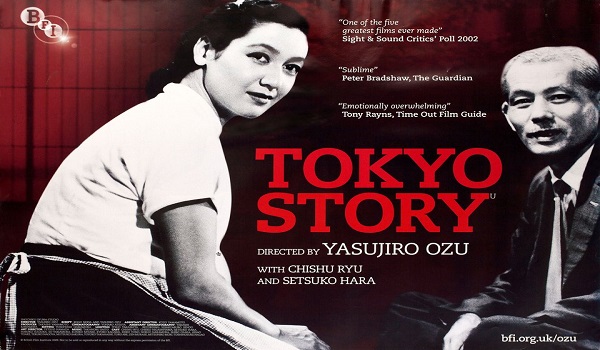মো. হারুন-অর-রশিদ
প্রকাশিত ২২ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
'দ্য সেভেন্থ সিল'-এ ঈশ্বর ও জীবনের মেলবন্ধন
মো. হারুন-অর-রশিদ
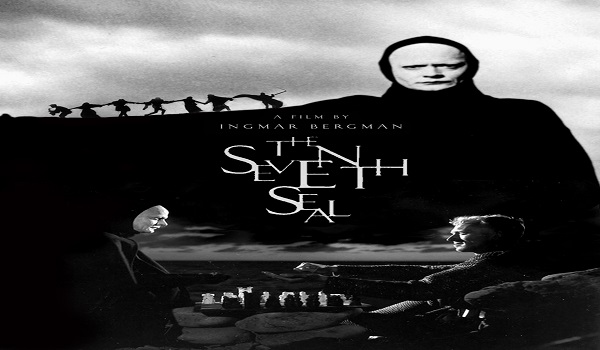
শুধু বিশ্বাসই কি মুক্তির পথ
যেখানে নিজেকেই বিশ্বাস করি না
প্রতিটি সত্তায় মিশে থাকে দুইটি বৈশিষ্ট্য—ধ্বংস ও সৃষ্টি। কেউ মেতে থাকে ধ্বংসলীলায়; কেউবা সৃষ্টির নেশায়; দৃঢ় প্রত্যয়ে এঁকে যায় পৃথিবীর বুকে আপন পদচিহ্ন। সৃষ্টিশীল এই মানুষগুলোর সৃষ্টি বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, যার ফল বর্তমান সভ্যতা। সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সৃষ্টিগুলো অন্যতম, তার একটি চলচ্চিত্র। যার বদৌলতে মানুষ নিজেকে, চারপাশকে চলমান ও জীবন্ত দেখতে পায়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে চলচ্চিত্র পূর্ণাঙ্গভাবে পথ চলতে শুরু করলেও, পরবর্তী সময়ে অনেক মনীষীর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় সমৃদ্ধ হয় এই মাধ্যম। কথা, শব্দ, আবহসঙ্গীত, আলো, নানান ঘরানার শট্, সম্পাদনা, অ্যাঙ্গেল প্রভৃতি নতুন নতুন সব সংযোজন। এই সমৃদ্ধকরণের পিছনে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরই একজন ইঙ্গমার বার্গম্যান।
বার্গম্যান চলচ্চিত্রকে কেবল প্রাযুক্তিক বিষয় হিসেবে নেননি। তিনি চিন্তা-চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন চলচ্চিত্রকে; অর্থাৎ চলচ্চিত্র পায় দার্শনিক রূপ। যদিও বিষয়টি শুরু থেকেই কোনো না কোনোভাবে ছিলো। প্রথম থেকেই শাসকশ্রেণি শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে চলচ্চিত্রকে। আর এই উপনিবেশ ও শোষণকে বৈধতা দিতে তারা আফ্রিকা, এশিয়ার ভয়ঙ্কর সব চিত্র তুলে তা সারাবিশ্বে প্রদর্শন করতো। অন্য একটা শ্রেণি ঠিক উল্টোভাবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করেছে শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে। চলচ্চিত্র এভাবেই তার দার্শনিক ভূমিকা পালন করে আসছে। যা মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণকেও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। বার্গম্যান দ্য সেভেন্থ সিল-এ এই দর্শনের প্রয়োগ আরো সফলভাবে করেন; নিয়ে আসেন জীবন-মৃত্যু, নাস্তিক্য-আস্তিক্য প্রসঙ্গ।
আজকে যে দর্শন শাশ্বত-চিরন্তন, সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, কালই হয়তো এর শাশ্বত-চিরন্তনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। চলতে চলতে সেই প্রশ্নগুলোই দানা বাঁধবে, বাধা পাবে, ঘটবে পরিবর্তন; প্রতিষ্ঠা পাবে নতুন দর্শন। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা, নিয়ম-অনিয়ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস জগতের সবকিছুর মতোই দর্শনও সদা পরিবর্তনশীল। তবে দর্শন নিয়ে অনেকের মধ্যেই একটা ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। অনেকে মনে করে, জ্ঞানী-গুণীরাই বোধ হয় দার্শনিক। তাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই দর্শন। যারা নানা তত্ত্ব, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ কখনোবা হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা বলবে। দর্শন, দার্শনিক নিয়ে সমাজে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, একজন সাধারণ মানুষ তার জীবনকে যেভাবে দেখে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাও একটা দর্শন।
তাবৎ দুনিয়ার মানুষকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোটাদাগে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায়— আস্তিক ও নাস্তিক। যেখানে আস্তিকরা সৃষ্টিকর্তার ভয়ে সদা কাতর, সুখ-দুঃখ, অবহেলা-অনাচার সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার বিধান বলেই জ্ঞান করে। আর নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, ব্যক্তি-ক্ষমতায় বিশ্বাসী। বার্গম্যানের মধ্যেও হয়তো বিষয়টি নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতো, যা ফুটে ওঠে তার চলচ্চিত্রে। তার ভাষায়, ‘সেভেন্থ সিল করে দুটো জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। মৃত্যুর ভয়, এখন আমি আর মৃত্যুর ভয়টা পাই না, আর ঈশ্বর সম্পর্কিত আমার ধ্যান-ধর্ম নিয়ে আমি বড় বেশি আচ্ছন্ন ছিলাম এখন মনে হয়, বস্তুবাদী হও, সব কিছু স্বচ্ছভাবে দেখ।’১
মানব সভ্যতার শুরুতে ছিলো শুধু বেঁচে থাকার লড়াই, নিত্যদিনের খাদ্যান্বেষণ। সময়ের পরিবর্তনে দেখা দিয়েছে নানা সঙ্কট, সমাধানে এসেছে নানা দর্শন, ধর্ম। পরবর্তী সময়ে সেই ধর্মকেই ব্যবহার করে একশ্রেণি ব্যবসা করে চলেছে। ঈশ্বরের বুলি আওড়ালেও তারা তাকে মানে না, তবে সাধারণের মধ্যে একটা ভয় তারা ঢুকিয়ে দেয়। তারা বোঝাতে সক্ষম হয়, জীবন-মৃত্যু যে নিয়মে চলে তার পিছনে কাজ করে ঈশ্বর বা অদৃশ্য এক শক্তি। যে শক্তির আঁতুড়ঘর হয়তো দায়বোধ, অপরাধবোধ বা নিয়ম বর্জিত কর্মের ভয়াবহ শাস্তি। এই শাস্তি বিশ্বাসীদের মনে জন্ম দেয় এক ভয়ের, আর এই ‘ভয়’ বিশ্বাসের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই এই ভীতি সৃষ্টিকারী শক্তি এবং ভীতি বা ঈশ্বরের মধ্যে হয়তো কোনো ফারাক দেখেন না বার্গম্যান, কাজ করে গেছেন এর বিরুদ্ধে। তার ভাষায়, ‘‘বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে আমার এই যুদ্ধ আসলে প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।’২
তবে এই দর্শনের বিপরীতে নাস্তিকরা বিশ্বাস করে, জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হবে, এটা স্বাভাবিক। মৃত্যু ব্যতীত জীবনের স্বাদ শূন্য। মৃত্যুই জীবনকে পূর্ণতা দেয়। তাই মৃত্যুর ভয়ে, স্বর্গ হারানোর ভয়ে কাতর হয়ে থাকার কোনো অর্থই নেই। কোনো কিছুর ভয়ে মানুষকে অবহেলা করার কোনো উপায় নেই, মানুষে মানুষে সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এটাই কাম্য। বার্গম্যানও হয়তো এমনটাই বিশ্বাস করতেন। তাই হয়তো তিনি বলতেন, ‘‘আমার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ঈশ্বর আছেন, নাকি ঈশ্বর নেই? ... তার অস্তিত্ব ...? শুধুই বিশ্বাস কি কোনো মুক্তির পথ হতে পারে, যেখানে আমরা নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারি না?’৩
কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেন, ‘‘আমি জন্মের প্রয়োজনে ছোট হয়েছিলাম, এখন মৃত্যুর প্রয়োজনে বড় হচ্ছি।’’৪ গুণের মতো জীবন-মৃত্যু নিয়ে রয়েছে নানা জনের নানা মত। ধর্ম বলে মৃত্যুর পরেই জীবন; বস্তুবাদ বলে জীবনের পরে মৃত্যু; হতাশাগ্রস্ত বলে জীবন-মৃত্যু বলতে কিছুই নেই; শিশু মানে জীবনের কাছাকাছি, বৃদ্ধ মানে মৃত্যুর কাছাকাছি। জীবন-মৃত্যু, আবর্তন-বিবর্তন সবকিছুই একটা গণ্ডি মাত্র। মৃত্যুহীন জীবন কিংবা জীবনহীন মৃত্যু কোথাও নেই। তবে এটা বলা যায়, জীবন-মৃত্যু, ঈশ্বর-ঈশ্বরহীনতা প্রপঞ্চগুলো অন্ধভাবে না বিশ্বাস করে প্রত্যেকের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে বিবেচনা করাই শ্রেয়।
মানুষ বার্গম্যান, স্রষ্টা বার্গম্যান
১৪ জুলাই, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ। দিনটি রবিবার। সুইডেনের উপসালা’য় এক অভিজাত ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা বার্গম্যান। পুরো নাম আর্নোস্ত ইঙ্গমার বার্গম্যান। বাবা এরিক বার্গম্যান ও মা ক্যারিন বার্গম্যানের তিন সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। এরিক লুথারান ধর্মযাজক হওয়ায় ছোটোবেলা থেকেই ধর্মীয় চর্চা আর সংস্কারের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন বার্গম্যান। এর বাইরেও বার্গম্যান পেয়েছেন সংস্কৃতিমনা নানির সান্নিধ্য।
তাই তার বেড়ে ওঠায় ধর্মীয় অনুশাসন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সমপ্রভাব ছিলো। তার বাবা ধর্মযাজক হলেও থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের প্রতি কট্টর ছিলেন না। তিনি ছোটোবেলায় বার্গম্যানকে রাসুন্ডা স্টুডিও নামে এক ফিল্মসিটিতে বেড়াতে নিয়ে যান। বড়োদিনে পারিবারিক বাইবেল পাঠের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঘনঘটায় কেচ্ছা শোনার আসরের আয়োজন করতেন। বড়ো ভাই ড্যাগ ও নানির সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে গিয়েও চলচ্চিত্র দেখতেন বার্গম্যান।
বার্গম্যানের বয়স যখন ১০, তখন বড়োদিন উপলক্ষ্যে তার বড়ো ভাইকে কেরোসিন তেল চালিত একটি ১৬ মি মি প্রজেক্টর উপহার দিয়েছিলেন এক আত্মীয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিজের উপহারটি ভাইকে দিয়ে প্রজেক্টরটি নিজের করে নেন বার্গম্যান। নিজের অজান্তেই প্রক্ষেপণকে ধারণ করা বার্গম্যান ছোটোবেলায় দুই বন্ধু ও ছোটো বোন মার্গারিটাকে নিয়ে টেবিলে চাদর বিছিয়ে পাপেট থিয়েটার করতেন। একদিকে প্রক্ষেপণ-থিয়েটার, অন্যদিকে ঈশ্বর চিন্তা; সবকিছু মিলেই অতিবাহিত হতে থাকে বার্গম্যানের শৈশব।
তার শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি সুইডিশ মিশন সোসাইটি পরিচালিত স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তবে ছোটোবেলা থেকে চলচ্চিত্র-থিয়েটার তাকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, সেই ঘোর তিনি আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মাধ্যমিকে এসে বার্গম্যান নিজের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন। তাই ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্গম্যান আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার-এ স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তা শেষ করতে পারেননি। এ বিষয়ে তার বক্তব্য, ‘‘যতদূর মনে পড়ে, থিয়েটার ও ফিল্ম ডিরেক্টর হয়ে ওঠার ব্যাপারে কোনোদিনই দ্বিধায় ভুগিনি আমি। ধারণা করি, আমার বাবা-মা এই বিষয়টি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। শুরুতে তারা ভেবেছিলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলেই ব্যাপারটি শিথিল হয়ে আসবে। কিন্তু আমি তা করিনি।’৫ পড়াশোনা চলার সময় তিনি যুক্ত হন গ্রুপ থিয়েটারে। সেখানেই তিনি নাটক লেখা, অভিনয় শুরু করেন, নির্দেশনা দিতেন স্টুডেন্ট প্রোডাকশনের।
২২ বছর বয়সে ‘‘ম্যাকবেথ’’-এর নির্দেশনা দিয়ে সফলতা লাভ করেন বার্গম্যান। তবে এই নাটকের নির্দেশনা দেওয়ার আগেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এতে সুইডেন নিরপেক্ষ দেশের ভূমিকা পালন করলে বার্গম্যানও রাষ্ট্রের পক্ষেই অবস্থান নেন। ১৯৪৪ খিস্টাব্দে তিনি মাস্টার অলফস গার্ডেন থিয়েটার ও সাগাস থিয়েটারে শিক্ষানবিস নির্দেশক হিসেবে নিয়োগ পান। এর কিছুদিনের মধ্যেই বার্গম্যান হেলসিংবার্গ থিয়েটারে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেসময় থিয়েটারটির অবস্থা ছিলো বেশ শোচনীয়। তিনি সেখানে মাত্র দুই বছর কাজ করে অবস্থার পরিবর্তন আনেন।
বার্গম্যান ইতোমধ্যেই উপলব্ধি করেন, শুধু নাটকে নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারছেন না। তাই ধীরে ধীরে মনোনিবেশ করতে থাকেন চলচ্চিত্রে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দেই তিনি চলচ্চিত্রের জন্য টুকটাক চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেন, যদিও সেগুলোর হদিস পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে হেলসিংবার্গ থিয়েটারে কাজের সুবাদে সভেন্সক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রধান কার্ল অ্যান্ডার্স ডিমলিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মেলে বার্গম্যানের। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বার্গম্যানের চিত্রনাট্যে সেসময়ের সুইডিশ খ্যাতিমান পরিচালক আলফ সজবার্গ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে টরমেন্ট নির্মাণ করেন। যা দেশ-বিদেশে ভালো সাড়া ফেলে। এই চলচ্চিত্রে তার সহকারী-পরিচালক হিসেবে কাজ করা, এর আন্তর্জাতিক সফলতা এবং তার কর্মোদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়ে বার্গম্যানকে নিজের চিত্রনাট্যে চলচ্চিত্র-নির্মাণের সুযোগ দেন কার্ল অ্যান্ডার্স। এরই ফলে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বার্গম্যান নির্মাণ করেন ক্রাইসিস। এ দিয়ে তার হাতেখড়ি হলেও এটি সমসাময়িক সুইডিশ চলচ্চিত্রে নতুন কিছু যোগ করেনি। তবে দমে যাননি বার্গম্যান। এরপর ১৯৪৭-এ অ্যা শিপ বাউন্ড ফর ইন্ডিয়া, ১৯৪৮-এ নির্মাণ করেন মিউজিক ইন ডার্কনেস ও পোর্ট অব কল।
প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লরেন্স মার্মস্টেট-এর প্রযোজনায় বার্গম্যান ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন প্রিজন, পরের বছর টু জয়। তবে এ দুটির একটিও ভালো সাড়া ফেলতে পারেনি। এদিকে ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে বিনোদন কর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে সুইডেনের প্রধান চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। সঙ্কটে পড়ে যান বার্গম্যান। ইতোমধ্যে তিনি নাটকও ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তার সংসার চালানোও কষ্টকর হয়ে যায়। তিনি বাধ্য হন সোভেনস্ক চলচ্চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিতে। বিনিময়ে বার্গম্যানকে এমন চুক্তিবদ্ধ হতে হয়, তিনি নির্মাতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবে যতো সম্মানী পেতেন তার দুই-তৃতীয়াংশ টাকায় তাকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দিতে হতো। এভাবে তিনি পাঁচটি চলচ্চিত্র নির্মাণের চুক্তি করেন।৬
এমন দুরবস্থার মধ্যে সানলাই করপোরেশনের একটি পণ্যের জন্য বেশ কয়েকটি রম্য বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেন বার্গম্যান। মার্মস্টেট ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে স্টকহোমে ‘‘ইন্টিমা থিয়েটার’’ চালু করেন লরেন্স। সেখানে বার্গম্যান নির্দেশক পদে যোগ দেন। এতে আর্থিক দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেলেও ইন্টিমা থিয়েটারে জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হন তিনি। এতে বার্গম্যান হতাশ হয়ে পড়েন।
হতাশার মধ্যে ১৯৫২-তে স্টকহোম ছেড়ে তিনি সুইডেনের মালমো’’তে চলে যান। ওই বছরই তিনি সিক্রেট অব উইমেন ও সামার উইথ মনিকা চলচ্চিত্র দুটি নির্মাণ করে আলোচনায় আসেন। সমালোচকদের মতে, এই চলচ্চিত্র দুটিই তার নির্মিত প্রথম পরিপক্ক কাজ। বার্গম্যানের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফলতা আসে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত স্মাইলস অব অ্যা সামার নাইট-এর মাধ্যমে। তবে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের দ্য সেভেন্থ সিল ও ওয়াইল্ড স্ট্রোবেরিজ তাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান করে তোলে। মালমোতে ছয় বছর কাটানোর পর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে স্টকহোমে ফিরে আসেন বার্গম্যান। দেশে ফিরে মধ্যযুগীয় সমাজে খ্রিস্টধর্মের রূপান্তরকে ধারণ করে তিনি দ্য ভার্জিন স্প্রিং (১৯৫৯) নির্মাণ করেন, যেটি বিদেশি ভাষা চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে অস্কার জিতে নেয়। চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে এ সময় বার্গম্যান খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলেন, পরিচিতি পান ‘‘অথর দু সিনেমা’’ নামে।
৬০ দশকে বার্গম্যান দুটি ট্রিলজি নির্মাণ করেন থ্রো অ্যা গ্লাস ডার্কলি (১৯৬২), উইন্টার লাইট (১৯৬৩), দ্য সাইলেন্স (১৯৬৩) ও পারসোনা (১৯৬৬), আওয়ার অব দ্য উলফ ও শেইম (১৯৬৬)। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বার্গম্যান নির্মাণ করেন তার প্রথম টেলিভিশন চিত্রনাট্য ‘‘দ্য রিচ্যুয়াল’’। তবে ১৯৭১-এ ক্রাইজ অ্যান্ড উইস্পার্স নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি এতোটাই আর্থিক সঙ্কটে পড়েন, অভিনেতারা চলচ্চিত্রের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাকে টাকা দেন। চলচ্চিত্রটি তিনি মাত্র ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারে (ডাউন পেমেন্ট) প্রদর্শনের অনুরোধ করলেও অ্যামেরিকান প্রধান প্রধান স্টুডিও তা প্রদর্শন করেনি। অবশেষে ইন্ডিপেনডেন্ট প্রোডাকশন নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তার এই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের দায়িত্ব নেয়। ক্রাইজ অ্যান্ড উইস্পার্স পরবর্তীতে অবশ্য ন্যাশনাল সোসাইটি অব ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড, নিউ ইয়র্ক ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ডসহ শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফিতে অস্কার জিতে নেয়।
‘‘সিনেমাটোগ্রাফ’’ নামে বার্গম্যান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে একটি চলচ্চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছিলেন তার নিজের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমেরিকান কোনো প্রতিষ্ঠানের চুক্তি করে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে। খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করলেও চুক্তি স্বাক্ষর করতে তাকে ১৯৭৫-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর আগে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত তার ‘‘সিন ফ্রম অ্যা ম্যারিজ’’ সোপ অপেরাটি বেশ হইচই ফেলে দেয়। সোপ অপেরাটি সেসময় সুইডেনের দম্পতিদের ওপর এতোটাই প্রভাব ফেলেছিলো যে, তারা সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এজেন্সিগুলোতে ভিড় করতো। এর প্রভাবে সুইডেন ও জার্মানিতে বিয়ের হ্যান্ডবুক লেখা শুরু হয়।
১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কর ফাঁকির অভিযোগে আটক হন বার্গম্যান। যদিও কর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিলো ‘‘পারসোনাফিল্ম’’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কর ফাঁকির বিষয়টি তুলে আনা। বার্গম্যানের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র-নির্মাণের অর্থদাতা এই প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তিনি এর লক্ষ্যবস্তুর শিকার হন। বিষয়টি এতোটাই খারাপ আকার ধারণ করে, গণমাধ্যম থেকে সাধারণ মানুষও তাকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে। এমনকি সরকার তার পাসপোর্টও জব্দ করে।
দীর্ঘদিন বার্গম্যানকে এই আইনি জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পরে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলে অনেকটা অপমান-অভিমানে সেই বছরই আবার স্টকহোম ত্যাগ করেন তিনি। এরপর প্যারিস হয়ে লস অ্যাঞ্জেলসে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি জার্মানির মিউনিখে স্থায়ী হন। প্রায় আট বছর পর তিনি নিজ দেশে ফেরেন। তবে এর মধ্যে তার চলচ্চিত্র-নির্মাণ বন্ধ ছিলো না। এ সময় তিনি নির্মাণ করেন অটাম সোনাটা (১৯৭৮), ফানি অ্যান্ড আলেক্সান্ডার (১৯৮২), অ্যা স্কুল ফর ওয়াইভ’স (১৯৮৩) ও আফটার দ্য রিহার্সেল (১৯৮৪)। দেশে ফিরে ওই বছরই বার্গম্যান শেক্সপিয়রের ‘‘কিং লিয়ার’’ নাটকের নির্দেশনা দেন। তিনি নাটকের নির্দেশনা দিলেও সচরাচর মঞ্চে আসতেন না। কিন্তু ‘‘কিং লিয়ার’’-এর ক্ষেত্রে তিনি মঞ্চে আসেন, এ সময় লিয়ার চরিত্রে অভিনয়কারী তাকে ‘‘ওয়েলকাম হোম’’ বলে সম্ভাষণ জানায়।
এর পর তিনি নির্মাণ করেন ওয়ানস (১৯৮৬), ম্যাডাম দু সাদ (১৯৯২), দ্য বাচ্চে (১৯৯৩), দ্য লাস্ট গ্যাস্প (১৯৯৫), ইন দ্য প্রেজেন্স অব অ্যা ক্লাউন (১৯৯৭), দ্য ইমেজ মেকার (২০০০) প্রভৃতি। দীর্ঘ ৬০ বছরের কর্মজীবনে বার্গম্যান ৬০টির মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যার মধ্যে আরো রয়েছে অ্যা শিপ বাউন্ড ফর ইন্ডিয়া, মিউজিক ইন ডার্কনেস, সামার ইন্টারলুড (১৯৫১), অ্যা লেসন ইন লাভ (১৯৫৪), ড্রিমস (১৯৫৫), দ্য ম্যাজিশিয়ান (১৯৫৮), দ্য ডেভিল’স আই (১৯৬০), অল দিজ ওমেন (১৯৬৪), আওয়ার অব দ্য ওল্ফ (১৯৬৮), দ্য টাচ (১৯৭১), দ্য ম্যাজিক ফ্লুইট (১৯৭৫), ফেস টু ফেস (১৯৭৬) প্রভৃতি। এই সময়ে তিনি প্রায় ১২৫টি চিত্রনাট্য লিখেন এবং ২০টির মতো প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সারা ব্যান্ড নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণের ইতি টানেন।
বার্গম্যান তার এই কর্মজীবনে অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা লাভ করেন। তার ভার্জিন স্প্রিং (১৯৬০), থ্রো অ্যা গ্লাস ডার্কলি (১৯৬১) ও ফানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার (১৯৮৩) বিদেশি ভাষার বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিস (১৯৫৭) ও থ্রো অ্যা গ্লাস ডার্কলি। দ্য সেভেন্থ সিল, ব্রিংক অব লাইফসহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায়।
বার্গম্যান তার চলচ্চিত্রে দু’টি বিষয় স্পষ্টভাবে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করতেন ভালোবাসার শিকড় যৌনতায়। সামার উইথ মনিকা (১৯৫৩), সিক্রেটস অব ওম্যান (১৯৫২), দ্য ভার্জিন স্প্রিং এর ভালো উদাহরণ। নারীদের নিয়ে বার্গম্যানের বেশকিছু কাজ থাকায় অনেকেই তাকে নারীবাদী নির্মাতাও মনে করেন। অবশ্য বার্গম্যানের গুরুত্বের জায়গাটা হলো ‘তার ‘নারীচরিত্র পুরুষের তুলনায় যৌনস্পর্শকাতর এবং নারীরা তা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না।’৭ বিষয়টি বার্গম্যান ব্যাখ্যা করেন এভাবে—‘‘যৌনতার স্পষ্ট বহিপ্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে আমার কাছে। আমি তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল ছবি বানাতে চাইনা। আমি চাই দর্শক আমার ছবি অনুভব করুক, ধারণ করুক, সবাই আমার ছবি বুঝতে পারল এটাই আমার আগ্রহের বিষয়।’’৮ দ্বিতীয়ত, রাজনীতি বা সামাজিক অবক্ষয়ের চেয়ে ধর্মীয় ভাবধারা বেশি ভাবাতো বার্গম্যানকে। হয়তো তার ছোটোবেলায় সেই ধর্মীয় আবহই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তার অনেক চলচ্চিত্রেই সেই দিক দেখতে পাওয়া যায়; দ্য সেভেন্থ সিল যার মধ্যে অন্যতম।
বার্গম্যানের বৈবাহিক জীবনের ইতিহাসও বেশ দীর্ঘ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বিয়ে করেন ইলস ফিসার’’কে। ফিসার ছিলেন কোরিওগ্রাফার ও নৃত্যশিল্পী। মাত্র দুই বছরের মাথায়ই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই ঘটনার পর পরই আরেক নৃত্যশিল্পী ও চলচ্চিত্রনির্মাতা ইলেন লুন্ডস্ট্রোম’’কে বিয়ে করেন বার্গম্যান। লুন্ডস্ট্রোমের সঙ্গেও সম্পর্ক খুব বেশিদিন টিকেনি তার। ১৯৫০-এ বিচ্ছেদ ঘটলে পরের বছরই বার্গম্যান বিয়ে করেন সাংবাদিক গান গ্রান্ট’কে। এই বিয়ের পর হ্যারিয়েট অ্যান্ডারসন (৫২-৫৯), বিবি অ্যান্ডারসন (৫৫-৫৯) সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান বার্গম্যান। তাই হয়তো এই সম্পর্কটিও ১৯৫৯-এ এসে থেমে যায়। ওই বছরই বার্গম্যান আবারও বিয়ে করেন পিয়ানিস্ট কাবি লরেত্য’’কে। এই বিয়েও টিকে না। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে, ১৯৭১-এ ইংরিদ ভন রোসেন’’কে তিনি বিয়ে করেন। ভন রোসেন অবশ্য বার্গম্যানের নয় সন্তানকে একত্র করেছিলেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান ভন, আমৃত্যু তিনি বার্গম্যানের সঙ্গেই ছিলেন। বার্গম্যান ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই ৮৯ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।
দ্য সেভেন্থ সিল-এর কথা
পরিষ্কার আকাশে একটি চিল উড়ছে। আবহসঙ্গীতে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। এক দশকের ক্রুসেড শেষে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ প্লেগের থাবা। এ যেনো এক মৃত্যুপুরী। চারদিকে লাশ আর মৃতপ্রায় মানুষের ঢল। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে মানুষ। এমন অবস্থায় সমুদ্র তীরে বিস্তৃত পাথরের বুকে শুয়ে ক্রুসেড ফেরত যোদ্ধা অ্যান্টোনিয়াস ব্লক, অন্যদিকে ছুরি হাতে শুয়ে অনুচর জনস। এমন সময় ব্লকের সামনে এসে দাঁড়ায় কালো কোর্তাধারী এক সত্তা। ব্লক জানতে চান, ‘‘কে তুমি, কী চাও?’’ উত্তরে সত্তা বলে, ‘‘আমি মৃত্যু, তোমায় নিতে এসেছি। তুমি কি প্রস্তুত?’’ ‘‘আমার শরীর ভয় পেতে পারে, আমি না’—’ ব্লকের জবাব। মৃত্যুদূত জীবন নিতে উদ্যত হতেই ব্লক তাকে থামিয়ে প্রস্তাব দেন দাবা খেলার। খেলায় পরাজিত হলে ব্লককে মৃত্যুবরণ করতে হবে—এমন শর্তে রাজি হয় মৃত্যুদূত।
এভাবেই শুরু হয় দ্য সেভেন্থ সিল-এর গল্প। আপন গৃহে ফেরার পথে ব্লক ও জনস এক চার্চে যান। চার্চের ভিতরে গিয়ে অঙ্কনরত একজনকে এসব কী আঁকছে জনস জিজ্ঞেস করলে, তার সহজ উত্তর মৃত্যুনৃত্য। মানুষকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিতেই এসব আঁকা। মৃত্যু নিয়ে এতো সব আয়োজন দেখে ব্লক এ বিষয়ে যাজকের সঙ্গে আলোচনায় মাতেন। আলোচনা শেষে ব্লক আবিষ্কার করেন, যাজক ভেবে তিনি এতোক্ষণ মৃত্যুদূতের সঙ্গেই কথা বলছিলেন! চার্চের বাইরে এসে তারা দেখেন, অচেতন অবস্থায় বাঁধা এক মেয়ে। চারদিকে জনরব এই মেয়ে ডাইনি!
এভাবে তারা চলতে থাকেন কিন্তু মৃত্যুদূত তাদের পিছু ছাড়ে না, তারা সাক্ষী হতে থাকেন এ রকম নানা ঘটনার। সেই সঙ্গে উঠে আসতে থাকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, মৃত্যু, রোগে-শোকে, কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত জনজীবন। খাবার নেই, ওষুধ নেই, জীবনের নিশ্চয়তা নেই; এগুলোর জন্য খুনখারাপি, পতিতাবৃত্তিসহ নানাধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জর্জরিত দেশ।
অবশেষে নিজের বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সঙ্গীদের বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দেন ব্লক। তবে শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, মৃত্যুদূত তাদের সবাইকে পাহাড়ের ওপরে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুদূতের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে থাকলেও ব্লক বাঁচতে পারেন না। ধর্মের নামে, মানুষের মঙ্গলের নামে যুদ্ধবাজরা যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, তার হাত থেকে রেহাই পায় না ব্লকের মতো কেউই। তবে ব্লকরা বাঁচার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, প্রশ্ন তোলে ঈশ্বরের নামে মৃত্যু মৃত্যু খেলা নিয়ে।
লেখক : মো. হারুন-অর-রশিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।
harunmcj25@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. রহমান, মুম (২০১২ : ৭৪); বিশ্বসেরা ৫০ চলচ্চিত্র; ভাষাচিত্র, ঢাকা।
২. ফেরদৌস, ফাহিম; ‘‘ইঙ্গমার বার্গম্যান : সিনেমাটিক জীবন ও বার্গম্যানের সিনেমা’’; ম্যুভিয়ানা; সম্পাদনা: বেলায়েত হোসেন মামুন; ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশনা, ঢাকা, ১ম সংকলন মার্চ ২০০৯, পৃ. ৫৩।
৩. প্রাগুক্ত; ফেরদৌস (২০০৯ : ৫৩)।
৪. নির্মলেন্দু গুণের ‘‘স্ববিরোধী’’ কবিতা থেকে নেওয়া।
৫. স্তিন, বির্গিতা (২০১৫ : ৯৭, ৯৮); ‘‘ইংমার বারিমন’; সিনেঅলা-২; গ্রন্থনা ও অনুবাদ : রুদ্র আরিফ; ভাষাচিত্র, ঢাকা।
৬. প্রাগুক্ত; বির্গিতা (২০১৫ : ১১৪)।
৭. প্রাগুক্ত; ফেরদৌস (২০০৯ : ৫৭)।
৮. প্রাগুক্ত; ফেরদৌস (২০০৯ : ৫৭)।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন