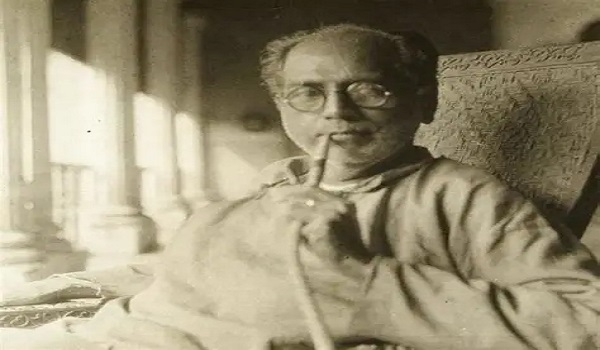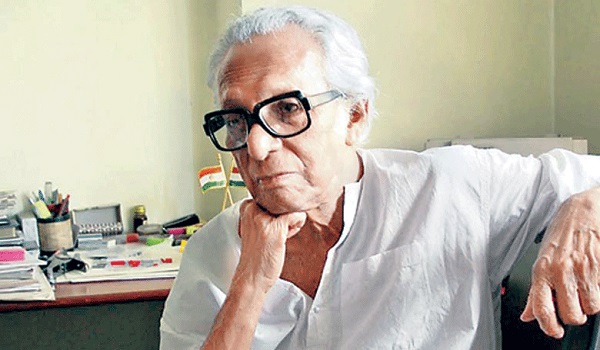জাহিদ হাসান মাহমুদ
প্রকাশিত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র
জাহিদ হাসান মাহমুদ
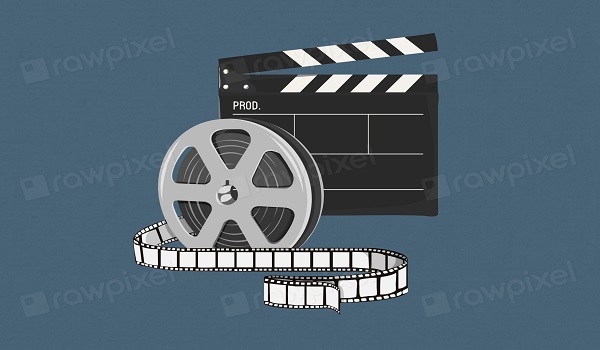
বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ষাট দশকের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা অনুধাবন এবং পূর্ণ জাগরণের বিশাল ব্যাপ্তিতে যে তৎপরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা শুধু ষাট দশকের সামগ্রিক এবং পর্যায়ক্রমিক অগ্রসরমানতার কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতা শব্দটির গভীর আলোড়ন একটি জাতিকে আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছিল এই ষাট দশক। বাঙালি জাতি মনস্তাত্বিক দেউলিয়াপনাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ভূখণ্ডকে চিনে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় যখনই সক্রিয় হলো তখনই সে আন্তর্জাতিক এবং পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতির রূপরেখাটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো এবং ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে ঠিক এই দশকের পরই বাঙালির প্রথম স্বাধীন শাসক এবং প্রথম স্বাধীনতা লাভ।
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশে ঘটে যাচ্ছে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। পাশাপাশি ভারতে নক্সাল আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি। ভিয়েতনামের যুদ্ধ। আটষট্টিতে ফ্রান্সের যুব বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশে সরকারী বাধার মুখে সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী পালন। রবীন্দ্র চর্চা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে দশক ব্যাপী সরব আন্দোলন। সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার অনুভবে ছায়ানটের জন্ম। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন। বাষট্টির ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের অর্থ সংগ্রহ অভিযান। চৌষট্টিতে সরকারী নির্দেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো এবং দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন। পঁয়ষট্টিতে সরকারী আদেশে সরকারী সম্প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ। ছেষট্টিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন। আটষট্টি-ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান। গণসঙ্গীতের তথা গণমানুষের সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে উদীচীর জন্ম। জাগো আর্ট সেন্টার এবং বুলবুল ললিত একাডেমী নৃত্য কলায় এ দশকের ধারাবাহিক সৃজনশীলতায় সাফল্য লাভ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি চর্চার মূল কেন্দ্রটি ছিল সংস্কৃতি সংসদ। চৌষট্টি সালে স্থাপিত হলো টেলিভিশন। বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্তের অবসর বিনোদনের জন্য অন্তঃসারশূন্য এক ইলেকট্রনিক মাধ্যম। এতো কিছুর মাঝে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৃষ্টি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে প্রতিভাবান কয়েকজন সাহিত্যিক তাঁদের মেধার অনুশীলনে গতিশীল রেখেছেন সাহিত্য চর্চার বলয়টিকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন অবশ্য ধণাত্মক ক্যাটালিস্ট হিশেবে কাজ করেছে এ ক্ষেত্রে। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে ষাট দশকে আমরা পেয়েছি ‘সমকাল’ এবং ‘কণ্ঠস্বর’-এর মতো প্রতিনিধিত্বমূলক পত্রিকা—যেগুলোকে আশ্রয় করে প্রবাহমান ছিল তখনকার সাহিত্যের ধারাটি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, হাফিজুর রহমান প্রমুখ গণমানুষের বাস্তবতাকে আন্তর্জাতিক এবং আধুনিক নিরীক্ষায় তুলে ধরেছিলেন সাহিত্যকর্মের বিস্তৃতিতে।
ষাট দশকের প্রথম ভাগেই এ দেশের তরুণেরা আধুনিক শিল্পের সবচে শক্তিধর মাধ্যম হিশেবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন এবং বোধ করি এ কারণেই তারা মিলিত উদ্যোগে তৈরি করলেন তেষট্টি সালে চলচ্চিত্র সংসদ। জন্ম হলো সংস্কৃতির অঙ্গনে আরেকটি আন্দোলন—চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন। মোটা দাগে, এই হচ্ছে এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ষাট দশকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।
লক্ষণীয় যে সংস্কৃতির অন্যান্য, এবং আপাত তুলনায় চলচ্চিত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল অন্যান্য মাধ্যমগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে পেরেছিল এবং যার কারণে আধুনিকও বটে। অথচ দুর্ভাগ্য যে, চলচ্চিত্র মাধ্যমটি এদেশে আধুনিক হয়ে উঠেনি। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল পার্লামেন্টে তখনকার মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত বিল পাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হলো চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন। নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এ দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এফ. ডি. সি.-তে বসে উর্দু ছবি নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে উঠে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর এ দেশে পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম স্টুডিও তৈরীর দাবীটা অত্যন্ত দৃঢ়তা লাভ করে। সে সময় অবাঙালী কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং প্রযোজক তখন এ দাবীর বিরোধিতা করলেও শেষ অবধি এফ. ডি. সি. নির্মিত হয়। এফ. ডি. সি.-র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৫৬ সালে নির্মিত হয় পাকিস্তানের প্রথম বাংলা ছবি “মুখ ও মুখোশ”। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ডাকাতির একটি বাস্তব ঘটনাকে উপজীব্য করে এ ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মাতারা সৎ ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটাও তারা উপেক্ষা করেননি আদৌ।
শিল্প বনাম ব্যবসার দ্বন্দ্বের মধ্যেও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র তখন নির্মাণ করেছিলেন তখনকার নির্মাতারা। কিন্তু অধিকাংশ চিত্রব্যবসায়ীর কাছে চলচ্চিত্র টাকা বানানোর কারখানা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। ফতেহ লোহানীর “আসিয়া” মুক্তি পায় ষাট সালের নভেম্বরে। সত্যজিৎ রায়ের “পথের পাঁচালী” থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফতেহ লোহানী তৈরী করলেন “আসিয়া”। শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিশেবে ষাট সালেই “আসিয়া” প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করে। “মুখ ও মুখোশ”, “আসিয়া”র ধারায় পরবর্তী সময়ে অল্প কিছু সামাজিক ছবি আমরা পেয়েছি যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য “আকাশ আর মাটি”, “মাটির পাহাড়”, “রাজধানীর বুকে”, “এদেশ তোমার আমার”, “সূর্যস্নান”, “কাঁচের দেয়াল”, “কখনো আসেনি”, “ধারাপাত”, “সুতরাং”, “নদী ও নারী” প্রভৃতি। এই ছবিগুলোতে সামাজিক মূল্যবোধটি তুলে ধরার একটা চেষ্টা ছিল। সমাজচিত্রের প্রকৃত বাস্তবতাটাকে কিছুটা উপেক্ষা করে বানানো হয়েছিল বলেই পরবর্তী সময়ে ছবিগুলো দিক নির্দেশনার বর্তিকা হিশেবে স্বীকৃতি পায়নি। একথা সত্যি যে, এ ছবিগুলোর বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন চলচিত্র উৎসবে ঈর্ষাজনক মানে পুরস্কৃত হয়। কিন্তু মাধ্যম হিশেবে এগুলোর কোনটিই চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেনি। কেননা চলচ্চিত্রিক গতিশীলতা এবং ক্যামেরার কাজের বৈচিত্র্য ছবিগুলোতে অনুপস্থিত বরঞ্চ কিছু মেলোড্রামা এবং সামাজিক নাটকের চলচ্চিত্রায়ণই ছিল ছবিগুলোর মূল ধারা। যে কারণে অশিক্ষিত চিত্রনির্মাতারা উর্দু ছবির অস্বাভাবিক ব্যবসায়িক সাফল্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে এদেশের স্টুডিও এফ. ডি. সি.-র সকল কারিগরি সুবিধা এক্সপ্লয়েট করে পুরোপুরি পাঞ্জাবী মহাজনদের চরিত্রে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়ে এক অসীমিত মাপের সম্ভবনাকে কবর দিল। এবং এই চিত্রনির্মাতাদের একজন অজুহাত দেখালেন এই বলে যে, “উর্দুতে ছবি করতে বাধ্য হচ্ছি ... বাংলা ছবির ব্যবসায়িক দিকটা নিতান্তই ভয়াবহ। তবু কিছুটা পাগলামী আর গোয়ার্তুমীর বশে বাংলাতেই ছবি শুরু করেছিলাম। ... সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস হচ্ছে আগ্রহ যেন কমে এসেছে বাংলা ছবির প্রতি। ... বেশির ভাগ দর্শক চায়—অবাস্তব এবং আজগুবি—যা জীবনে ঘটে না এমন ঘটনা সিনেমায় দেখতে—আর সে সব সস্তা চটকদার ব্যাপার উর্দু ভাষার যেন আরো জমে।” এধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে দর্শকের রুচির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে চলচ্চিত্রের শিল্পমূল্যকে ধ্বংস করার যজ্ঞে এরা কেউ কেউ মেতে উঠেছিলেন। এমনিভাবেই চলচ্চিত্রকে সুকৌশলে এবং সার্থকতার সাথে সামাজিক বাস্তবতার থেকে দূরে সরিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্যের চাবিকাঠিতে রূপান্তরিত করতে এদের আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।
আর এই পরিস্থিতির কেন্দ্রস্থলে বসে কেউ কেউ কমিটমেন্টের কথা বলেছিলেন—কিন্তু কার্যত প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকারের ভূমিকায় আমরা কাউকে পাইনি। প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকার ক্যামেরা ছেড়ে রাইফেল হাতে তুলে নেবেন—ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। তার নিজস্ব ব্যাকরণ এবং ফর্ম, কারিগরি কুশলতার মধ্যেই মূল কনটেন্টের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে চলচ্চিত্রের কাছে দায়ী থাকাই হচ্ছে প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকারের দায়িত্ব। কেউ কেউ হয়তো তখন সামাজিক দায়বদ্ধতার শ্লোগান তুলে ছবি তৈরীতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু মূলত ঘটনাটি হলো এই শ্লোগান কিংবা এই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে কালো টাকাকে সাদা টাকায় রঙিন করতে কিছু নির্মাতা কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের কাছে আপাদমস্তক মেধা মননসহ আত্মসমর্পণ করলেন। সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার জন্য তারা চলচ্চিত্র ব্যবসাকে তীর্থস্থান বানালেন। চলচ্চিত্র জগতের কেউকেটা হিশেবে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ত্বরান্বিত হলো অথচ চলচ্চিত্রের ঘটতে শুরু করলো তিলে তিলে ক্ষয়িষ্ণু মৃত্যু। এফ. ডি. সি.র সূচনা এদেশে ব্যবসায়ীদের রমরমা অবস্থায় নৃত্যরত করে দিল। একটি শিল্পমাধ্যমকে কিভাবে চরিত্র হনন করে বিনষ্টের পথে প্রক্ষেপ করা যায় তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মহাজনেরা। উর্দু ছবি নির্মাণে সাফল্যের সূত্র কিন্তু ছিল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত এ জে কারদার পরিচালিত “জাগো হুয়া সাভেরা”। “পদ্মা নদীর মাঝি” উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয় এ ছবিটি। ১৯৫৯ সালের ৮ই মে তারিখে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবিটি ১৯৫৯ সালের মস্কোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার সহ মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কাহিনী অনুকরণের অভিযোগ রয়েছে এ ছবির পরিচালক সম্পর্কে। ছবিটি আমার দেখা নেই। কেবল বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সংকলন গ্রন্থ-সমূহের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এটুকু বলতে পারি উপন্যাসের মূল স্রোত এবং দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও নির্মাণ কুশলতার জন্য ছবিটি একটি ভালো এবং সৎ চলচ্চিত্রের অভিধা পেয়েছে। ষাটের শুরুতেই এমনিভাবে উর্দু ছবির অস্বাভাবিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এর বাণিজ্যিক উপাদানগুলোকেই কেবল আঁকড়ে ধরলো তখনকার বেশ কয়েকজন চিত্র নির্মাতা এবং নিজের সংষ্কৃতি এবং মাটির সাথে করলো বিশ্বাসঘাতকতা। উর্দু ছবির বাজারলাভ বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে উঠলো। ঠিক এমন অবস্থা চলতে থাকে ষাট দশকের মাঝামাঝি। অপর একটি বিবেচনাযোগ্য উর্দু ছবি হচ্ছে বেবী ইসলাম পরিচালিত “তানহা”। বাষট্টিতে বৈরুত চিত্রমেলায় ছবিটি প্রদর্শিত হয়।
অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে উর্দু ছবি ব্যতীত চলচ্চিত্রের ভবিষ্যত অন্ধকার। কিন্তু পাশাপাশি কিছু বাংলা ছবিও আমরা পেয়েছি। জহির রায়হানের “কাঁচের দেয়াল” ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালনা, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ, সংলাপ এবং অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করে। ঐ একই উৎসবে সালাউদ্দিনের “সূর্যস্নান” লাভ করে দুটি পুরস্কার। কাঁচের দেয়ালের কাহিনীতে রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ এবং অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগত বিদ্রোহীপনার অবসাদগ্রস্থতা। সূর্যস্নানে রয়েছে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব। মূল দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে এ ছবিতেও চিত্রিত হয়েছে শ্রমিকের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে শ্রমিকের অসহায়ত্ব, পরাজয় এবং পরিণতিতে মৃত্যু। শ্রেণী সংঘাতের সম্ভাবনাময় দ্বান্দ্বিক সত্যটিকে উপজীব্য করে এ ছবি দৃঢ়তা পেতে পারতো। কাহিনীতে শ্রেণী চরিত্রের মূল উপাদান শাণিত হয়নি। ১৯৬১ তে জহির রায়হান তৈরী করেন “কখনো আসেনি” পরিচালক হিশেবে তার প্রথম ছবি। ছবির প্রচারে অতিরঞ্জিত ভাবে লেখা হয়েছিলে “দেশের জনসাধারণ বিশ বছর পরে যে ছবি দেখবে বলে আশা করেছিল বিশ বছর আগেই তরুণরা সে ছবি তাদের উপহার দিল।” অতিশোয়ক্তি ছিল এ প্রচারে। এ ছবির টাইটেল সঙ্গীতেই বাণিজ্যিক চেষ্টা ছিল সুস্পষ্ট। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে সাংস্কৃতিক উত্থানকে বন্ধ করে রাখবার স্বৈর শাসকের চেষ্টাকে প্রতীকী রূপায়ণে দেখানো হয়। শেষ পর্যায়ে নায়কের পরাজয় এবং নায়িকার গতানুগতিক জীবনধারায় আত্মসমর্পণ ছবিটির শৈল্পিক সম্ভাবনাকে সীমিত করে। উর্দু এবং ভারতীয় বাংলা ছবির সাথে প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সুভাষ দত্তের “সুতরাং” ১৯৬৪তে ফ্রাংকফুর্ট এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করে। ছবিটি ব্যবসাসফল ছিল। ১৯৬৭ তে নজিবর রহমানের উপন্যাস অবলম্বনে জহির রায়হান তৈরী করেন “আনোয়ারা”। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলিম সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে এই ছবিতে। “নদী ও নারী” ছবিটি ছিল “আসিয়া” ও “জাগো হুয়া সাভেরার” পর গ্রাম বাংলা নির্ভর একটি সৎ ছবি। চলচ্চিত্রের ছাত্রদের জন্যে “নদী ও নারী” একটা টেক্সট ফিল্ম হিশেবে বিবেচিত হয়েছে। মূলত আলোচিত এবং উল্লিখিত চলচ্চিত্রগুলো ছিল ষাট দশকে সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত ছবি।
উর্দু ছবির ব্যবসায়িক কূপমণ্ডুকতার পর পরই এলো দ্বিতীয় আঘাত। লোকগাঁথা নির্ভর ছবির মাতলামি। প্রথমে লোকগাঁথার কাছে ফিরে যাওয়ার একটা সৎ প্রচেষ্টা অনুমিত হলেও মূলত ব্যবসায়িক লাভই এ পর্বেও চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ীদের পথকেই কুসুমাস্তীর্ণ করে। ৬৫ সালে “রূপবান” দিয়ে শুরু হলো যাত্রা। ফলে বিরাট এক ক্ষতি হলো সংস্কৃতির জগতে। ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্প দু’ভাবে ধ্বংস হতে থাকলো। এক, যাত্রা শিল্পের ব্যাপক দর্শক চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলো। যাত্রার মূলসুরেও ঘটলো দ্বিতীয় বিপর্যয়। চলচ্চিত্রায়নের ফলে পরবর্তী সময়ে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যাত্রামঞ্চেও চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক এবং সংস্কৃতির জন্য ঋণাত্মক উপাদান সমূহ যুক্ত হতে থাকলো। ব্যাপক গণমানুষ যাত্রাশিল্পের পরিবেশিত সত্য তথ্য এবং ইতিহাস ভুলে সেলুলয়েডের রূপালি চমকে অপরিণত আধুনিকায়নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদের দাসশ্রেণীতে নিগড়াবদ্ধ হলো। রূপবান প্রদর্শনীর জন্যে গ্রামবাংলায় রাতারাতি গড়ে উঠলো শত শত প্রেক্ষাগৃহ। ঘরের কাছে পৌঁছে গেল এফ. ডি. সি. রোপিত বিষবৃক্ষটির গভীর শেকড়। সুস্থ দর্শকশ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথাকথিত লোকগাঁথাভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো এমনিভাবেই অন্তরায় হয়ে উঠলো। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই প্রপঞ্চটি ছিল বিরাট আঘাত। সামাজিক উর্দু ছবি, লোকগাঁথাভিত্তিক ছবির পর ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।
“নবাব সিরাজউদ্দৌলা” (১৯৬৭) এবং “তীতুমীর” (১৯৬৮) ছবি দুটো এ ধারায় উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের পর্দায় স্বাধিকার ও মুক্তির আকাংখা ধীরে ধীরে প্রবেশ শুরু করলো। এর পর পরই ষাটের দশকের শেষপ্রান্তে এসে জহির রায়হান তৈরী করলেন “জীবন থেকে নেয়া”। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির গণআন্দোলন এবং স্বাধিকারের আন্দোলনটি সেলুলয়েডে তুলে ধরলেন প্রথম বারের মতো জাহির রায়হান। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি একটি পরিবারের প্রতিবাদমুখরতার মধ্যে প্রতীকী উপমায় এ ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একুশের মিছিলের দৃশ্য রয়েছে ব্যবহৃত ফুটেজে। বাঙালির সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের নিকটবর্তী ছিল পুরো ষাট দশকের কেবল এই ছবিটিই।
জহির রায়হানের “জীবন থেকে নেয়া” ছবিটিতে রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং তথ্যের পরিবেশনা ছিল ঠিকই, কিন্তু চলচ্চিত্রিক ভাষায় এটি প্রায় অসম্পূর্ণ ছবিই কেননা পরবর্তী পর্যায়ে এই জহির রায়হানের কাছ থেকেই আমরা অনেক প্রতিভাদীপ্ত “স্টপ জেনোসাইড” পেয়েছি।
মোটামুটিভাবে ষাট দশকের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক নির্মিত চলচ্চিত্র সমূহের একটা আলোচনা করা হয়েছে এ পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কোনো ছবিই চলচ্চিত্রিক ভাষায় তেমন সমৃদ্ধ নয়। পুরো দশক জুড়ে শিল্পের অন্যান্য সকল মাধ্যমে কাজ হয়েছে বেশ। প্রতিটি শিল্প-মাধ্যমে সমৃদ্ধ ফসল পাওয়া যায়। অথচ শক্তিশালী এ মাধ্যমটি প্রকরণগত ভাবে রয়ে গেছে অনাধুনিক পর্যায়ে। কারিগরি সুযোগ সুবিধা ছিল প্রয়োজনমত, কিন্তু অভাব ছিল শিক্ষার। চলচ্চিত্রের ভাষাটি তখনকার পরিচালকদের জানা ছিল কি না সন্দেহ। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি বিচার করলে দেখা যায়, বাঙালির মূল বিষয়গুলোর কোনোটিই চলচ্চিত্রের বিষয় হিশেবে বিবেচিত হয়নি। সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হয়েছে। বাংলা ভাগ হয়েছে। বাঙালী মুসলমান নতুন শহুরে প্রতিবেশে নিজেকে তৈরী করে নেয়ার পর্যায়ে সামাজিক এবং শ্রেণীগত বিভিন্ন দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষে পুঁজির বিকাশ অস্বাভাবিকভাবে একটি অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তুলে দিল ক্ষমতার বিভিন্ন কাঠামোগুলোতে। শাসন প্রক্রিয়ার নিয়মনীতি সে জানে না। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলাবিহীন চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকলো। মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় ভাষা আন্দোলনের জন্ম হলো। জহির রায়হান লিখলেন উপন্যাস “আরেক ফাল্গুন”। অথচ চলচ্চিত্রকে এগুলোর কিছুই স্পর্শ করতে পারলো না। তেষট্টি সালে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন শুরু হয়েছে। পয়ষট্টি সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলিচ্চত্র উৎসব হয়েছে। ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বের বিখ্যাত ধ্রুপদ চলচ্চিত্র সমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। ষাট দশকে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় পদচারণা ঘটে মেধাবী চলচ্চিত্রকারদের। প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলায় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন—এরাঁ সকলেই সমসাময়িক সমস্যা এবং আবহমান কালের বাংলাকে নিয়ে ধ্রুপদ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন একের পর এক। এঁদের উত্তরসূরী হয়ে এলেন অসংখ্য প্রতিভাধর চলচ্চিত্র নির্মাতা। স্বল্প খরচে, স্বল্প দৈর্ঘ্য আশ্রয় করে জীবনের বাস্তবতা, জাতীয় রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, সংস্কৃতি—সমস্যা নিয়ে এরা তৈরি করতে থাকলেন প্রচুর প্রণিধানযোগ্য চলচ্চিত্র। ব্যাপারটি এমন নয় যে, এ ভূখণ্ডের মানুষ তথ্য কিম্বা সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক আউটের মধ্যে দিনযাপন করছেন। চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে জয়নুল আবেদিনের আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠা আধুনিকায়নের সুযোগ এনে দিল। পাশ্চাত্য রীতিনীতিতে নিয়মিত শিক্ষিত হয়ে উঠলেন আর্ট কলেজ কেন্দ্রিক চিত্রশিল্পীবৃন্দ। এঁদের অনেকেই পাশ্চাত্যে বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে চারুশিল্পের উন্নয়নে ব্যাপৃত হয়েছেন। দেশের মানুষ, সংস্কৃতি, সমস্যা এবং আন্দোলনকে বিষয় নির্বাচন করে এই শিল্পীরা নির্মাণ করলেন চিত্রকর্ম। পাশাপাশি সাহিত্যিক কবিরা সমান্তরালে এগিয়েছেন। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, চৌষট্টির দাঙ্গা, ছেষটি-আটষট্টি-ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাস্তবতার থেকে দূরে থাকার ফলেই এমনটি ঘটেছে কিংবা এও বলা যেতে পারে এরা নিজেরা ছিল জ্ঞানপদবী। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণেও কেউ সচেষ্ট হননি। যদি বাধা আসতো, শিল্পমাধ্যমগুলোর অন্যান্য ধারার মতো প্রতিবাদের ঝড় তোলা এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না। কেননা পরিবেশ তৈরী ছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমির একটু আগেই উত্তপ্ত ছিল রাজনৈতিক প্রতিবেশ। ব্যর্থতা এই জন্যে যে, তারা কেউই চেষ্টাটা পর্যন্ত করেননি। পুরো ষাট দশক জুড়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর উপর এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত সমালোচনাসমূহ পাঠ করলে কেবলই কারিগরী কুশলতা এবং গ্ল্যামারাস নায়ক-নায়িকা এবং মেদবহুল নর্তক-নতর্কীর পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনাই পাওয়া যায়। ছবিগুলোর সামাজিক বাস্তবতা, শিল্পগুণ, চলচ্চিত্রিক ভাষা সম্পর্কিত কোনো প্রকার আভাস ইঙ্গিত-ধনাত্মক কিংবা ঋনাত্মক—কোনো দৃষ্টিকোণেই তেমন আলোচনা হয়নি। নিছক টাকা বানানো এবং মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো পরিশ্রমহীন বিলাসে ম্যানেজারি করে চলচ্চিত্র নির্মাতা নাম কিনেছে তখনকার ব্যবসায়ীরা। একজন অতর পরিচালকের ধারণাই তাদের ছিল না। অথচ বিষয় বস্তুর অভাব ছিল না। প্রয়োজন ছিল শিক্ষিত আধুনিক মানুষের দৃষ্টির। ’৪৭-এ নতুন দেশ হলো। বাস্তবতার প্রয়োজনে কারখানা গড়ে উঠে আদমজীনগরে, টঙ্গিতে শ্রমিক আন্দোলন রূপ নিল। এর পূর্বে উত্তর বঙ্গ জুড়ে ছিল তেভাগা আন্দোলন। নতুন শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের সংঘাত। আধুনিকতম এলিয়েনেশন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে একে একে ভাঙতে শুরু করেছে যৌথ পরিবারের ধারণাটি। নগর এবং গ্রামের জীবন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। বিরাট অঞ্চল জুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে হলেও দানা বাঁধছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে সাংস্কৃতিক জোয়ার। এন এস এফের বদমাইশি। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্র আন্দোলন। এর কোনো কিছু আকৃষ্ট করতে পারেনি তখনকার চলচ্চিত্রকারদের। বস্তাপচা ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী এবং বটতলার উপন্যাসগুলোকে কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের ধারায় দু’তিনটে গান দিয়ে ফর্মুলাবন্দী করে বাজারজাত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য তখনকার চলচ্চিত্রকারদের। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীরা গড়ে উঠেছিলেন যাদের অনেকেই ষাটের দশকে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে। কিন্তু কোনো এক অব্যাখ্যাত কারণে এরা কেউই চলচ্চিত্র নির্মাণের বিকল্প ধারায় এগিয়ে এলেন না। সমগ্র বিশ্বের অন্যান্য বহুদেশের আমরা দেখি চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীরা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনেই চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন। ব্যাপারটি মোটেই চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদিতা নয়, বরং প্রত্যক্ষ অঙ্গ হিশেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু বিশেষ এক স্নবারি তখনকার চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীদের চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এরা যদি সত্যজিৎ-চিদানন্দকে অনুসরণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিকল্প ধারায় এগিয়ে আসতেন তবে হয়তো এফ. ডি. সি.-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের অশুভ চক্র হতে চলচ্চিত্র শিল্পটি মুক্তি পেত। পুরো ষাট দশক জুড়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার অভাব ছিল। তদানীন্তন পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত “ধ্রুপদী”, আলমগীর কবির রচিত “সিনেমা ইন পাকিস্তান” ব্যতীত প্রকাশনার উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক চলচ্চিত্রপাতা এবং বেশ কয়েকটি সিনেমা সাপ্তাহিক ষাট দশকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সব সংবাদপত্রের পাতার মূল কাজটি ছিল হলুদ সাংবাদিকতাকে পৃষ্ঠপোষণ করা। চলচ্চিত্র শিল্পটিকে সংগঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়া কিংবা চলচ্চিত্রের পঠন-পাঠনের ফোরাম হিশেবে এ পত্রিকাগুলো ধনাত্মক ভূমিকা রাখতে পারতো। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পী-নির্মাতা কিংবা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মী কিংবা চলচ্চিত্র উৎপাদন ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা কেউই প্রকাশনার কাজে সৎ কমিটমেন্টে এগিয়ে আসেননি। ফলাফল মোটেও শুভ হয়নি। চলচ্চিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি আদৌ। এবং আজ অবধি সেই অসুস্থ হলুদ সাংবাদিকতার শিকার আমাদের চলচ্চিত্রের জগৎ।
ষাটের দশকে ফিল্ম ইনস্টিটিউট কিংবা আর্কাইভ গড়ে তোলার উদ্যোগও দেখা যায় না। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করে গ্রামে গঞ্জে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের আগ্রহর কমতি ছিল না। একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে পৃথিবীর সকল উন্নত এবং সংস্কৃতি ঋদ্ধ দেশেই ফিল্ম ইনস্টিটিউট রয়েছে। অথচ ষাট দশকে সরকারী, বেসরকারী কিংবা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীদের এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব থাকতে দেখা যায়। আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সরকারী উদ্যোগে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নিয়মিত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতের বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছে বেসরকারী আগ্রহে। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আর্কাইভের প্রয়োজনীয়তাও কেউ অনুভব করলো না। নিজেদের ইতিহাস সংরক্ষণ করার মতো জরুরী ব্যাপারটি ষাট দশকের কারু কাছে স্পষ্ট ছিল না। উদাসীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকল মহল।
ঔদাসীন্যের অন্য একটি দুঃখজনক উদাহরণ হলো চলচ্চিত্রের প্রতি অন্যান্য মাধ্যমের শিল্পীদের ইচ্ছাকৃত অনাগ্রহ। কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, শিল্পী এদের অধিকাংশই চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা দিতে চাননি এবং বরাবরই চলচ্চিত্রে তাদের ঔদাসীন্যের প্রকাশই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। মুর্তজা বশীর, কলিম শরাফী এঁরা কেউ কেউ চলচ্চিত্রে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ শিল্প মাধ্যমটিতে কেউ আর সক্রিয় ভাবে সংযুক্ত থাকেননি। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যবহারে প্রতিভার স্বাক্ষর খুঁজে পাই না। চলচ্চিত্রকারের সাথে অন্যান্য মাধ্যমের শিল্পীদের সহযোগিতা কিংবা যোগাযোগের অভাবও প্রকট ছিল।
অথচ এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরুতে দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট সকল কলাকুশলী, নেপথ্য কর্মী, অভিনেতা প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন শিল্পটির প্রতি। গোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় টিমওয়ার্ক সম্পূর্ণই তখন উপস্থিত ছিল প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণ ইউনিটে। পরিচালকের উদ্দেশ্য কিংবা চিত্রনাট্য-কাহিনীকে ধারণ করে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দায়িত্ব বোধ ছিল প্রশংসনীয়। কুশীলবরা বিশ্বাস করতেন চলচ্চিত্র একটি শিল্প। তাদের কমিটমেন্ট বিচারে অনুমান করা সম্ভব যে প্রথমযুগের শিল্পীরা চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে তখনো তেমন বিবেচনা করেননি। সিডিউলের প্রতি, নির্দেশনার প্রতি, পরিচালকের প্রতি এমনকি ইউনিটের সকল কর্মীর প্রতি তাদের আস্থা বিশ্বস্ততা ছিল উদাহরণযোগ্য। কুশীলবদের এই নিষ্ঠা অবশ্য ষাট দশকের শেষ ভাগে এসে নষ্ট হয়ে পড়ে যখন চলচ্চিত্র জগতে ধস নামতে শুরু করে উর্দু ছবির জোয়ারের ফলে। আজকের নব্বই এর দশকে আমরা দেখি যে কুশলবেরা আদৌ কমিটেড নয়। সিডিউলে কেউ নিয়মানুবর্তী নয়। অন্যান্য সকল কর্মীর মতে তাদের চরিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছে শিল্পটির প্রতি অবজ্ঞা-উদাসীনতা। ষাট দশকের শিল্পীরা পারিশ্রমিক নিয়ে চিন্তিত থাকতেন না। অথচ আজ মোটা অংকের পারিশ্রমিকই প্রধান। শিল্প নয় বরঞ্চ এখন পুরো প্রপঞ্চটি আর্থিক উদ্বৃত্তের জন্য রুচিহীন এক পরিবেশের দিকে চলেছে ক্রমাগত।
পরিসংখ্যান মতে, ষাট দশকের প্রথম ভাগে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা ছিল। প্রথম ভাগে নির্মিত এই চলচ্চিত্র সমূহের প্রায় সবকটি শিল্পোত্তীর্ণ এবং দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯৬০ সালে কেবল দুটি চলচ্চিত্র এফ. ডি. সি. থেকে নির্মিত হয়েছে—“আসিয়া” এবং “জাগো হুয়া সাভেরা” এই দুটি ছবি পুরস্কৃত এবং প্রশংসিত। পরবর্তী পর্যায়ে উর্দু ছবির ধাক্কা এবং রূপবান জাতীয় লোককাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রের জোয়ারে সৎ প্রচেষ্ট বন্ধাত্বের শিকার হতে থাকে। ’৬৪ সাল থেকেই এফ. ডি. সি.’র ফ্লোরে তৈরী হতে থাকলো অসংখ্য চলচ্চিত্র কিন্তু শিল্প সৃষ্টির উদ্যোগ পুরোপুরি নষ্ট হতে শুরু করলো। এই ভাবে সম্ভাবনাময় ধারাটিকে ব্যবসায়িক দুরভিসন্ধির অন্ধপথে বিনষ্ট করে দিল এফ. ডি. সি.-কেন্দ্রিক মুভি মোড়লরা। বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের সময়কাল ’৬৬-৬৯ পর্বেও চলচ্চিত্রের কোনো উন্নতি হয়নি।
উপসংহারে এই টুকুই বলা যায় পুরো ষাট দশক জুড়ে সৎ কলাকুশলী শিল্পী নেপথ্য কর্মীর আন্তরিক দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কেবল অপরিণামদর্শী কূপমণ্ডুক পরিচালক কিংবা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে এফ. ডি. সি. আবর্তিত এই শিল্পটি ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। শক্তিশালী এই মাধ্যমটি ষাট দশকের দিকভ্রান্তির ফলে আধুনিক হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আজকের চলচ্চিত্রের কর্মীরা উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ লাভ করেনি বরঞ্চ পূর্বসূরীদের দায়িত্বহীনতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপকর্মের খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতি মাত্রই পূর্ব সূত্র থেকে আহরণ করে বিভিন্ন উপাদান এবং ধারাবাহিক সৃজনশীলতা। অথচ আমাদের এখানে তৈরি হয়ে উঠেনি চলচ্চিত্র স্কুল, চলচ্চিত্র সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র সাহিত্য, চলচ্চিত্রিক প্রতিবেশ। অল্পকিছু সৎ প্রচেষ্টা যারা করেছিলেন তাদের অধিকাংশই পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবসায়িক সাফল্যে আত্মহারা হয়ে শিল্পটিকে ধ্বংস করেছে। এবং বাকী অনেক সৎ কর্মী শিল্পটিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চলচ্চিত্রিক নিজস্ব ভাষায় বুঝে উঠতে সক্ষম হন নি। পাশাপাশি ষাট দশকের গোড়া থেকে সূচিত হলো যে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন তারা কেউই তেমন বিকল্প ধারা নির্মাণে এগিয়ে এলেন না। স্নবারি এবং উদাসীনতায় ভেবে বসে থাকলেন চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়াটি আদৌ তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধিভুক্ত নয়। অল্প কিছু ধ্রুপদ চলচ্চিত্র নিজেরা দেখলেন, বুঝলেন এবং শিক্ষিত হলেন, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর যে কী পরিমাণ ক্ষতি করে চলেছে এফ. ডি. সি.-র মুভিমোঘলরা সে দিকে তেমন দৃকপাত করলে না তারা। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে প্রতিবাদ কিংবা বাধা দেয়ার জন্যে প্রথম দিকেই চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের উচিত ছিল এফ. ডি. সি. র কর্মযজ্ঞ নিজেদের সম্পৃক্ত করা এবং নিশ্চয়ই বিকল্প ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্রিয় হয়ে উঠা।
দায়স্বীকার : লেখাটি তানভীর মোকাম্মেল, মানজারে হাসীন, মাহমুদুল হোসেন ও জাহিদ হাসান মাহমুদ সম্পাদিত ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদের বার্ষিক সংকলন ‘মন্তাজ’ থেকে নেওয়া হয়েছে। সংকলনটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন