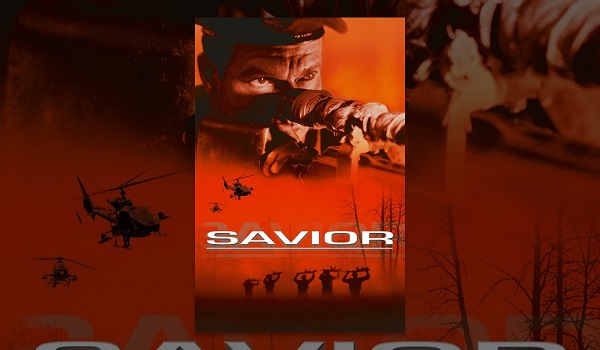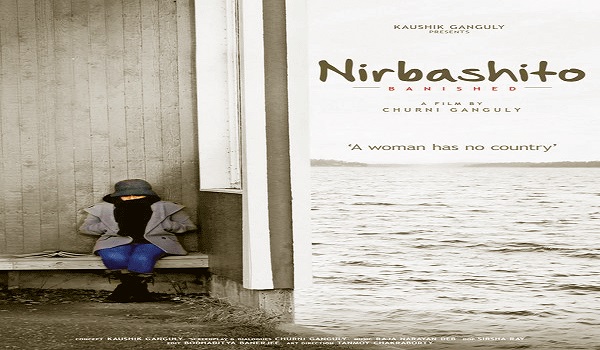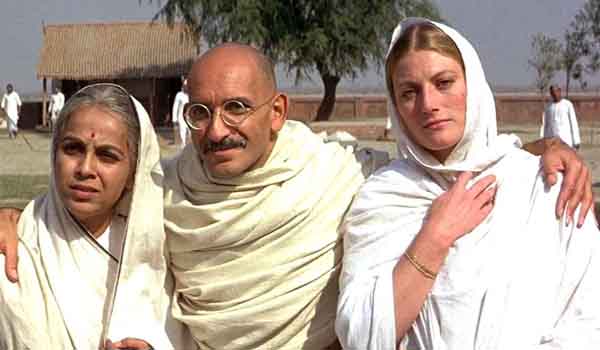মাহামুদ সেতু
প্রকাশিত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
ফারুকীর আরেক টুকরো ‘বেসামাল’ চালাকি 'পিঁপড়াবিদ্যা'
মাহামুদ সেতু

পাঠ-যুক্তি ও প্রস্তাবনা
এক টুকরো রুক্ষ, কঠিন, অনুর্বর পাথরখণ্ড কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণত হয়েছে আজকের সুজলা-সুফলা, সবুজ পৃথিবীতে। এর পিছনে প্রকৃতির যেমন হাত রয়েছে, তেমনই সব প্রাণীও অক্লান্ত শ্রম দিয়েছে। তবে অন্য অনেক প্রাণীর তুলনায়, বিজ্ঞানের ভাষ্য মতে, মানুষের আগমন অনেক পরে। তার পরও অনুর্বর শুষ্ক জমিনে প্রাণের স্পন্দন জাগাতে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে মানুষই। হয়তো তারা স্বপ্নবাজ বলেই তা করতে পেরেছে। স্বপ্ন দেখে বলেই তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস রাখে, এগিয়েও যায়। স্বপ্ন আছে বলেই টিকে আছে পৃথিবীটা।
তবে স্বপ্ন দেখা আর তার বাস্তবায়ন এক নয়। আবার অনেকে স্বপ্ন দেখতে পারলেও, অন্যকে তা দেখাতে পারে না। সেজন্যই পৃথিবীতে সবাই কবি-সাহিত্যিক, লেখক, রাজনীতিক হতে পারে না; কেউ কেউ হয়। আর অন্য সব স্বপ্নবাজদের চেয়ে চলচ্চিত্রনির্মাতারা এক ধাপ এগিয়ে থাকেন অন্যকে স্বপ্ন দেখানোর ক্ষেত্রে। তারা আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের স্বপ্ন, কল্পনা, ইমেজকে অন্যের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরতে পারে। আর যে নির্মাতা যতো জীবন্ত করে তার স্বপ্নকে পর্দায় তুলে আনতে পারে, দর্শককে দেখাতে পারে; তাকে মানুষ ততো উঁচুতে স্থান দেয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে নিরন্তর উপরে উঠতে থাকা এমনই একটি নাম মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তার নির্মিত ব্যাচেলর (২০০৩), মেইড ইন বাংলাদেশ (২০০৭), থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার (২০০৯), টেলিভিশন (২০১২) ও সর্বশেষ পিঁপড়াবিদ্যা (২০১৪) দেখে মনে হয়েছে তিনি কিছু বলতে চান। প্রতিটি চলচ্চিত্রেই তিনি হাজির হয়েছেন সমাজ-সংসারের নানা সমস্যা, বিশেষত তারুণ্যের টানাপড়েন নিয়ে। তার পিঁপড়াবিদ্যাতেও দেখা গেছে বেকারত্ব, হতাশা, সামাজিক অসঙ্গতি, প্রেম-কাম। কিন্তু সাদা চোখে সবসময় যা দেখা যায়, সেটাই সব নয়। এর বাইরেও অন্তর্নিহিত কোনো কথা হয়তো থেকে গেছে ফারুকীর। সেই পাঠোদ্ধারের চেষ্টাই এ লেখা।
এই বিদ্যায় ঘোর লাগে না
দৃশ্যপট-১
চলচ্চিত্র শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্র মিঠু দ্বিতল বাসের সামনের আসনে বসে আছেন। বাসটি ট্রাফিক সিগন্যালে অপেক্ষা করছে। মিঠুর পিছন থেকে ক্যামেরা ধরা। তিনি মুঠোফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছেন—‘আমার ওই ছয় কোটি টাকার কী অবস্থা? আপনি এতিমখানাকে বলেন, আমি এক কোটি টাকা ডনেশন দিবো। এর বেশি পারবো না; বুঝছেন? আপনে প্লিজ আমাকে আর রিকোয়েস্ট কইরেন না। আমি আর পারবো না। রাখেন।’ ফোন রেখে মিঠু তার বাম দিকের আসনে বসা নারী সহযাত্রীর দিকে তাকান। কাট টু’তে নামলিপি দেখানো হয়।
দৃশ্যপট-২
চলচ্চিত্রের তিন মিনিট ২০ সেকেন্ডে মিঠু একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যান। সেখানে নিয়োগদাতা তাকে বলেন—‘তোমার তো এই পোশাকে আসলে হবে না। তোমার পোশাক-আশাক, কথাবার্তা আরো ফিটফাট হইতে হবে। কারণ ডেইলি তোমাকে বিচ (২০) জনের ওপর, মিনিমাম বিচ জনের ওপর সার্ভে করতে হবে। বুঝছো? এহন তুমি নিজেই যদি ফিটফাট, ইস্মাট না থাকো, মানুষ তো তোমার কথা শুনবে না ...।’ কথা শেষে মিঠুকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘ঠিক আছে?’ জবাবে মিঠু শুধু মাথা উপরনীচ করেন।
নিয়োগদাতা আবারও বলেন, ‘ওই মিয়া এমনে কথা কও ক্যা? মিন মিন কইরা কথা বললে হইবো না তো। শামুকের মতো লজ্জায় জড়সড় হইয়া থাকলে হইবো না। ... ঢাকা শহরে চলতে হইলে তোমার একহাতে পাঁচটা ঢাল থাকতে হইবো। আরেক হাতে পাঁচটা তরবারি রাখবা মিয়া। একবারে সাঁই সাঁই কইরা শুয়াইয়া ফালাইবা। ঠিক আছে? (মিঠু আবারো মাথা নাড়াতে থাকেন) পারবা? পারবা?’
মিঠু কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ানোয় বিরক্ত হয়ে নিয়োগদাতা বলেন, ‘কী হইলো এভাবে আস্তে কথা কও ক্যান? জোরে বলো মিয়া যে, জি পারবো।’ শেষমেষ মিঠু বলে ওঠেন, ‘এনায়েত ভাই, কালকে বলি?’
দৃশ্যপট-৩
লাকি সেভেন এম এল এম কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার পর মিঠু পুরনো মুঠোফোনের দোকানে গিয়ে ফোন দেখতে থাকেন। চলচ্চিত্রের তখন নয় মিনিট ২০ সেকেন্ড চলছে। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে ডেকে নেন। ওই ব্যক্তির অভিব্যক্তি দেখেই দর্শক বুঝতে পারে, ‘ডাল মে কুছ কালা’। এরপর মিঠু যখন জিজ্ঞেস করেন কেনো তাকে ডাকা হলো, তখন ওই ব্যক্তির উত্তর—‘আরে ভাই, আপনি দোকানের থে পুরনো মোবাইল কিনতে আসছেন না? দোকানের থে যে মোবাইল আট-দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন, আমি তার থেকে খুব অল্প দামে ভালো মোবাইল দেবো আপনাকে।’ দর্শকের আর বুঝতে বাকি থাকে না, ওই ব্যক্তির পেশা কী। কিন্তু পরক্ষণেই মিঠু ফোনটি দেখতে চাইলে লোকটি বলে ওঠেন, ‘আরে ভাই কেনবেন তো। মাত্রই তো চুরি করে নিয়ে আসছি। সিমটা আমারে খুলতি দেন।’
দৃশ্যপট-৪
মিঠুর সদ্য কেনা চোরাই ফোনটিতে একটি কল আসে। কল ধরামাত্রই অন্য পাশ থেকে এক নারীকে বলতে শোনা যায়—‘হ্যালো, মিস্টার নূরে ইমরান বলছেন?’
মিঠু বলেন, ‘হ্যাঁ, নূরে ইমরান মিঠু বলছি। আপনি কে বলছেন?’
ফোনকারী বলেন, ‘লিসেন মিস্টার মিঠু, আমি অ্যাক্ট্রেস রিমা বলছি। আপনি যে মোবাইলটি ইউজ করছেন, দ্যাট ইজ মাই মোবাইল। আমি পুলিশ দিয়ে মোবাইল ট্র্যাকিং করে আপনার সব ডিটেইল আর বায়োডাটা জানতে পেরেছি। ইফ ইউ ডোন্ট কাম অ্যান্ড গিভ মি মাই মোবাইল ব্যাক বাই টুমরো মর্নিং, আই উইল হ্যাভ ইউ অ্যারেস্টেড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?‘
পিঁপড়াবিদ্যার প্রথম দৃশ্যপটটিতে ট্রাফিক সিগন্যালে আটকা পড়া বাসে বসে মিঠু এতিমখানাকে কোটি টাকা ডোনেশন দেওয়ার ‘ফাঁপা বয়ান’ দেন। আসলে এটাকে বোধ হয় ফাঁপা বয়ান বলা ঠিক হবে না। কারণ, এমন ফাঁপা বয়ান দেওয়ার সঙ্গে বিশ্বাস করাতে পারার সম্পর্ক রয়েছে। আপনি ফাঁপা কথা বললেন, কিন্তু আমার কাছে যদি তা বিশ্বাসযোগ্যতা না-ই পায়, তবে তা নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ মনে হবে। এখানে কোটি টাকার বদলে মিঠু যদি দুই-চার লক্ষ টাকা ডোনেশন দিতে চাইতেন, তাহলেও না হয় বিশ্বাস করা যেতো। কারণ, পুঁজি প্রাধান্যশীল সমাজে যার কয়েক কোটি টাকা আছে, সে আর যাই হোক অন্তত লোকাল বাসে চড়ে না। অবশ্য এমনও হতে পারে, ফারুকী চাইছিলেন দর্শক সহজেই বুঝতে পারুক মিঠু ফাঁপর মারছে। সেজন্যই হয়তো এমন আকাশপাতাল ফারাকে ফাঁপরে উপস্থাপন!
আবার দ্বিতীয় দৃশ্যে ফারুকী যে আত্মবিশ্বাসহীন মিঠুকে পরিচয় করিয়ে দেন, পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রজুড়ে সেই মিঠুকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে মিঠু মুখ ফুটে হ্যাঁ বলতে পারেন না, তিনিই কি না অত্যন্ত জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয় না। তার ভাষায়—‘ক্যান্সার? কীসের ক্যান্সার? কই আমার আব্বা তো আইজ ৪০ বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছে, কই তার তো ক্যান্সার হয়নি? ভাই এগুলো কী জানেন—ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওষুধ বিক্রি করার প্রচারণা। এসব বাজে কথা। আপনারা বিশ্বাস করবেন না এগুলো।’ তাহলে কিছু আগের মুখচোরা মিঠু, আজ কীভাবে এতো চতুর বিপণনকর্মী হয়ে গেলো তার জবাবও পাওয়া যায় না পিঁপড়াবিদ্যায়।
অন্যদিকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে সাধারণত প্রচুর কথা বলানো হয়। চোখ দিয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি, নির্মাতা তা শুনিয়েও নেন। যেমন : কেউ কারো দিকে একটা কলম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা দেখে সহজেই বোঝা যায়, তাকে কলমটা নিতে বলা হচ্ছে। অথচ, সেখানেও সংলাপ বলানো হবে, কলমটা ধরো। তার মানে যা দেখি, সেটাই আবার শুনি। একই পরিস্থিতি রয়েছে তৃতীয় দৃশ্যপটেও। সেখানে মিঠুকে ডেকে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির হাবভাব থেকে সহজেই বোঝা যায়, তিনি ‘ধান্দাবাজ’। অথচ ফারুকী তাকে দিয়ে বলিয়েও নেন, ‘আরে ভাই কেনবেন তো। মাত্রই তো চুরি করে নিয়ে আসছি।’ সত্যি কথা বলতে কী, একে তো ধান্দাবাজ তার ওপর আবার এতো সত্যবাদী (!) চোর আসলেও বিরল! তাছাড়া ওই দৃশ্যটি দেখে সেই ব্যক্তি যে চোর বা একজন ‘ধান্দাবাজ’ এতোটুকু বোঝার ক্ষমতা দর্শকের রয়েছে বলেই মনে হয়। সেদিক থেকে এই দৃশ্য ও সংলাপের এই দ্বিরুক্তি নির্মাতার বিচক্ষণতার অভাবের পরিচয় দেয়।
তবে পিঁপড়াবিদ্যার সবচেয়ে বড়ো গোঁজামিল পাওয়া যায় দৃশ্য চারে। সেখানে অ্যাক্ট্রেস রিমা চুরি যাওয়া ফোনের ক্রেতা মিঠুকে ফোন দিয়ে তা ফেরত চান। আশ্চর্যের বিষয়, কীভাবে এতো দ্রুত মিঠুর খোঁজ পেলেন রিমা, তা হয়তো ফারুকী ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। যদিও সেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে, পুলিশ দিয়ে ফোন ট্র্যাক করা হয়েছে। সেটা যদি মেনেও নিই, তাহলে পুলিশ মিঠুর নাম কী করে জানলো, কেনোইবা মিঠুকে আটক করলো না? অবশ্য পরের এক দৃশ্যে রিমার প্রেমিক যখন তাকে পুলিশের কাছে যেতে বলেন, তখন রিমা ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে ভেবে তাতে অস্বীকৃতি জানান। বোঝা যায়, তিনি পুলিশের কাছে যাননি। তাহলে মিঠুর হদিস কীভাবে পেলেন রিমা—এ প্রশ্নের উত্তর দর্শকের অজানাই রয়ে যায়!
যেকোনো নির্মাতাই তার কল্পনার ইমেজ দিয়ে দর্শকের সামনে একটি বাস্তব অবস্থা হাজির করেন। যে বাস্তবতা দর্শককে ওই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে। আর যে নির্মাতা যতো বেশি বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই বাস্তবতা হাজির করতে পারে, সে ততো সফল হিসেবে মূল্যায়ন পায়। কিন্তু পিঁপড়াবিদ্যায় ফারুকী তার দর্শককে হতাশ করেন। চলচ্চিত্রে সৃষ্ট বাস্তবতার মায়াজালে দর্শককে তিনি বিভ্রান্ত করতে পারেন না। বারবার মায়াজাল ছিন্ন হয়। দর্শকমনে প্রশ্ন জাগে, সুতাগুলো তো জোড়া লাগছে না!
প্রসঙ্গ পিঁপড়া ও তার বিদ্যা
শব্দ হিসেবে ‘পিঁপড়াবিদ্যা’কে ভাঙলে পাওয়া যাবে পিঁপড়া বিষয়ক বিদ্যা, অর্থাৎ পিঁপড়া কেমন করে জীবন চালায়, কীভাবে চলে, কী করে, কী করে না কিংবা পিঁপড়ার কাছ থেকে মানুষের জন্যইবা কী কী শিক্ষণীয় রয়েছে—সবই পিঁপড়াবিদ্যার অন্তর্গত। এখন মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দিক খুঁজতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, পিঁপড়া খুবই পরিশ্রমী প্রাণী। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণীই পরিশ্রমী। পরিশ্রম না করে কারো পক্ষেই জীবন ধারণ সম্ভব নয়। মানুষ ছাড়া প্রায় সব প্রাণীই জন্মের কিছুকাল পর থেকেই কাজ করতে শেখে, মানে শিকার করা বা অন্য উপায়ে খাবার সংগ্রহ করা, বাসস্থান নির্মাণ, এসব আর কি।
আবার সাধারণ পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, পরিশ্রমের পাশাপাশি পিঁপড়া শৃঙ্খলাও মেনে চলে। তারা পথচলার সময় সাধারণত এক সারিতে চলে এবং দলনেতার নির্দেশ মানে। এমনকি তাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থাও রয়েছে। তারা একত্রে বাস করে, যেটাকে পিঁপড়াদের ‘কলোনি’ বলা যেতে পারে। আর কলোনিতে পিঁপড়াদের আচার-আচরণে মনে হয়, তাদের সবার দায়িত্ব যেনো ভাগ করা আছে; কেউ খাবার সংগ্রহ করে, কেউ ঘর বানায়, কেউ পাহারা দেয় প্রভৃতি। তারা এসব দায়িত্ব পালনও করে যথাযথভাবে। অর্থাৎ পিঁপড়ারা একতাবদ্ধ থাকে বলা যায়। সেজন্যই দেখা যায়, কোনো একটি পিঁপড়া যদি বড়ো কোনো খাবার পায়, যেটা সে একা কলোনিতে নিতে পারে না, তখন অন্যদের ডেকে নেয়। তারপর সবাই মিলে একত্রে খাবারটি টেনে নিয়ে যায়। খাবার সংগ্রহের পাশাপাশি পিঁপড়াদের দেখা যায়, দুঃসময়ের জন্য তা সঞ্চয় করতেও। তারা গরমের সময় বেশি করে খাবার সংগ্রহ করে রাখে। কারণ, শীতকালে যেহেতু তারা গর্ত ছেড়ে বের হতে পারে না, সেজন্য তারা পর্যাপ্ত খাবার সঞ্চয় করে রাখে।
আবার লাল পিঁপড়ার আচরণ দেখে বোঝা যায়, তারা নিজেদের অধিকারের প্রতি সচেতন। সেই অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তারা প্রতিবাদ করে। তাইতো কেউ লাল পিঁপড়ার ‘কলোনি’ মাড়িয়ে দিলে অনেক পিঁপড়া একসঙ্গে আক্রমণ করে, কামড়ে দেয়। তবে এতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পিঁপড়ার কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। তার এই দুর্বলতা আগুনের প্রতি। কিছু পিঁপড়ার পাখা গজালে তারা আগুনের দিকে ছুটে যায়। আগুনের বর্ণিল শিখা তাদেরকে টেনে নেয় মৃত্যুর দিকে। সেজন্যই বলা হয়, ‘পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।’ বর্ণিল আগুনের লোভই শেষ পর্যন্ত পিঁপড়ার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই পরিস্থিতি হয়তো মানুষের জন্যও সত্য। লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
ফারুকীর পিঁপড়াবিদ্যায় মিঠু ভালো কোনো কাজ জোটাতে না পেরে অবশেষে লাকি সেভেন এম এল এম কোম্পানিতে যোগ দেন। স্বপ্ন দেখেন ধনী হওয়ার, বাড়ি-গাড়ি করার। কিন্তু এর বিপরীতে তিনি কোনো পরিশ্রম করেন না। এম এল এম কোম্পানির লোকদের অবশ্য পরিশ্রম করার দরকারই পড়তো না। কারণ বাংলাদেশে তারা কালোজিরার তেল, পাহাড়ে বনায়ন, নিজ প্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োগ প্রভৃতি ‘বায়বীয়’ পণ্য বিক্রি করে মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতো। অন্যদিকে মানুষ এভাবে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে সদস্যপদ পেতো এসব কোম্পানির। এরপর তারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে প্রতিষ্ঠানে ‘বিনিয়োগ’ করাতো। আর অন্যকে ‘বিনিয়োগ’ করানোর বিনিময়ে সেই সদস্য পেতো নির্দিষ্ট একটি লভ্যাংশ। এভাবে বিনিয়োগকারীদের একটি চেইন তৈরি হতো। সেই চেইনে যে যতো উপরের দিকে থাকতো, বিনাশ্রমে তার লাভও ততো বেশি ছিলো। মিঠুও বিভোর ছিলো একই কায়দায় বড়োলোক হওয়ার স্বপ্নে। তার বন্ধুর ভাষায়—‘আসছে কোটিপতি হইতে! মানুষ জুতার ব্যবসা, সেমাইয়ের ব্যবসা, আরো কতো কী কইরা টাকার চেহারা দ্যাহে না। উনি আসছে চাপা বিক্রি কইরা কোটিপতি হতে!’
আসলে ছোটোকাল থেকেই পিঁপড়া বা অন্য প্রাণীরা যেখানে কাজ করতে শেখে, সেখানে আমাদের সমাজে মিঠুরা পড়ালেখা শেখে। তারা ‘জ্ঞান’ কতোটুকু অর্জন করে, তা জানা না গেলেও স্নাতকোত্তর পাশের একটি সনদ ঠিকই পায়। অনেকক্ষেত্রে এই সনদ তার ন্যূনতম জীবিকানির্বাহের উপায় বাতলে দিতেও ব্যর্থ হয়। সেজন্য মিঠুর মায়ের আক্ষেপ, ‘মানুষের পোলাপান কতো কিছু করে! উনি শুধু ইন্টারভিউ দেন, ইন্টারভিউ দেন, ইন্টারভিউ দেন।’ মধ্যবিত্তের আটপৌরে জীবনে এমন আক্ষেপ নিত্যকার ঘটনা। আসলে মিঠুরা হয়তো পরিশ্রম করতে ভয় পায়। সেজন্য জ্ঞানার্জনের ‘ঝক্কি’তে না গিয়ে সহজে নোট-বই মুখস্ত করে সনদ অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সনদ যখন কোনো কাজেই লাগে না, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশার দায় আসলে কার—রাষ্ট্রের, শিক্ষা ব্যবস্থার নাকি মিঠুদের? একদিকে রাষ্ট্র যেমন তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে মিঠুরা শুধু চাকরিই খোঁজে, পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হতে চায় না।
তাছাড়া ‘শিক্ষিত’ মিঠু অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে জানেন না। চলচ্চিত্রের তিন মিনিট ৫০ সেকেন্ডে মিঠুকে বাজার জরিপের চাকরি দিতে চাওয়া এনায়েত বলেন, ‘তুমি ডেইলি একশো টাকা করে পাইবা। কিন্তু তুমি সিগনিচার দিবা, দেড়শো টাকা বুঝিয়া পাইলাম। একশো টাকা হইলো তোমার, আর ৫০ টাকা হইলো আমাদের ব্যবসার।’ এ সময় মিঠু মাথা নেড়ে তাতে সায় দেন। হয়তো বেকার মিঠুর কাছে একশো টাকাও অনেক বড়ো বিষয়। চলচ্চিত্রজুড়ে মিঠুর মধ্যে পিঁপড়ার মতো লোভই শুধু দেখা যায়। তারকা রিমার ব্যক্তিগত ভিডিওর জেরে টাকার জন্য মিঠু তাকে ব্ল্যাকমেইল করে। আবার কখনোবা সাবেক প্রেমিকার কাছে নিজের স্ট্যাটাস বজায় রাখতে, কখনোবা রিমার সান্নিধ্য পেতে তিনি ওই ভিডিওর বিনিময়ে ব্ল্যাকমেইল করেন রিমাকে। ফারুকী হয়তো বলতে চান, মিঠুরা পরিশ্রম করে নয়, অন্যায় কোনো সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এর পরিণাম সবসময় ভালো হয় না। সেজন্যই হয়তো মিঠুর মধ্যে পিঁপড়ার অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলেও ‘আগুনে ঝাঁপ’ দিতে ঠিকই দেখা যায়।
অল্প কথায় বেশি বিদ্যা
ক. আড়ালে দাঁড়ানো বিদ্যা
চলচ্চিত্রের ৪০ মিনিটের দিকে মিঠু রাতের খাবার খেতে আসলে মায়ের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এরপর মিঠু না খেয়েই নিজের ঘরে চলে যান। কাট টু’তে মিঠুর ঘরের দেয়ালে টাঙানো তার তিনটি ভিন্ন সময়ের ছবি টিল্ট ডাউনে দেখানো হয়। ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়; দেখা যায় সমুদ্রের পাড়ে বেশ কিছু মুখোশ পড়ে আছে। ঢেউ এসে মুখোশগুলো ভিজিয়ে দেয়; ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে ‘পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।’ সৈকতে দাঁড়িয়ে আপেল খেতে থাকেন রিমা। রিমার পাশে রাখা উঁচু আসনে গিয়ে বসেন মিঠু। সেখানে বসে রিমার মাথায় রাখা লবণ, জলপাইয়ে লাগিয়ে তিনি খেতে শুরু করেন।
অন্যদিকে চলচ্চিত্রের ৪৫ মিনিটে রিমার বাসায় যান মিঠু। সেখানে গিয়ে তার ফোনে কপি করা রিমার ভিডিওটি রিমাকে দিয়েই তিনি ডিলিট করিয়ে নেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি রিমাকে প্রস্তাব দেন, তার সঙ্গে এক ঘণ্টা স্বামী-স্ত্রীর মতো একান্তে সময় কাটানোর। এ সময় তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলেও, শেষ পর্যন্ত মিঠুর চাপের মুখে রাজি হন রিমা। মিঠুকে তখন ব্যাটারিচালিত পুতুল হাতে দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ৫৭ মিনিট থেকে ৫৯ মিনিট পর্যন্ত মিজ-অঁ-সেন শটে রিমা ও মিঠু অবস্থান করা শয়নকক্ষের খোলা দরজা ও তার পাশে ওয়ারড্রোভের উপরে রাখা ডানে-বামে মাথা নাড়ানো সেই পুতুলটি দেখানো হয়। শটটির শেষে মিঠুকে বাসা থেকে বের করে দেন রিমা। এরপর ঘরে সাজিয়ে রাখা বেশ কয়েকটি পুতুল, মূর্তি, মুখোশ দেখানো হয় প্যানিং ও কাট টু শটে। অন্যদিকে চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ২৮ মিনিটে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো মিঠুকে দেখা যায়, বন্ধুর কাপড়ের দোকানে ম্যানিকিন জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকতে। এ সময় দোকানে রাখা অন্য একটি ম্যানিকিন থেকে আবির্ভাব ঘটে রিমার।
মিঠু-রিমার এসব আচরণ, স্বপ্ন, বাস্তবের নানা কিছু দর্শকমনে ঘোর লাগায়। মানুষের ভিন্নতা, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নানা রূপে হাজির হয়। তার ভিতরের কাম, তার বহিঃপ্রকাশ, তাকে নিয়ে এগিয়ে চলা নানাভাবে খেলা করতে থাকে। একই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের অসহায়ত্ব, তার ভিতরের লোভ, অনুশোচনা, রাগ, ক্ষোভ কীভাবে বেরিয়ে আসে বা উল্টোভাবে চাপা পড়ে তাও পরিষ্কার হয়। তার পরও মানুষ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের সঙ্গে খেলা করে; আকাক্সিক্ষত বস্তু তার মগজে নানাভাবে, নানা রূপে ঘোরাঘুরি করে। ফারুকী ব্যক্তি মানুষের এই সীমাবদ্ধতা, অগ্রসরতার নানা দিক তুলে ধরেন। প্রতীকের এই ব্যবহার নিঃসন্দেহে নির্মাতা হিসেবে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
আবার রিমার প্রতি মিঠুর পুরুষালি আচরণ, রিমার ‘মেয়েলি অসহায়ত্ব’, সঙ্গে ব্যাটারিচালিত পুতুল, মিজ-অঁ-সেন শটে পুরো পরিস্থিতিতে সময় নিয়ে হাজির থাকা—সবই দর্শককে ভাবায়। ব্যাটারিচালিত ওই পুতুলের চেয়ে রিমা অর্থাৎ নারীর ভিন্ন কোনো রূপ ধরা পড়ে না দর্শকের কাছে। সে দেখতে পায়, ওই পুতুলের মতো রিমার ‘চাবি’ও অন্য কারো কাছে গচ্ছিত। পুঁজি ও পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে আটকে আছে রিমা। বারবি পুতুলের মতো রিমারা তাদের দেহ-মন পুঁজির মর্জি মতোই তৈরি করে নেয়। মানে রিমাদেরকে ব্যবহার করে ফায়দা লুটে নেয় পুঁজি। তাতে অবশ্য রিমাদের কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না! যেমনটা সৈকতে দাঁড়িয়ে রিমার মাথায় রাখা লবণ দিয়ে জলপাই খেতে দেখা যায় মিঠুকে। আর রিমা এ সময় আপেল খেতে থাকেন। বিষয়টি এমন যে, পুঁজির হাতে বন্দি রিমা নিজের ‘সাময়িক সুখ’ (আপেল খাওয়া!) পাওয়ার জন্য নিজেকে ব্যবহার হতে দেন। এটা আবার তিনি উপভোগও করেন! উল্টোদিকে পুরুষ মিঠুও ফায়দা লুটতে থাকে।
রিমাকে পাওয়ার আকাক্সক্ষা জাগে মিঠুর মনেও। পিঁপড়াবিদ্যায় মিঠুর নির্বান্ধব, একঘেঁয়ে জীবনে এক টুকরো রোমাঞ্চ হিসেবে রিমার আগমন। কিন্তু রিমাকে নিজের করে পাওয়ার স্বপ্ন দেখার সাধ্যও নেই তার। তবুও রিমার সঙ্গ চান তিনি। যৌনতা তো আসলেও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফ্রয়েড মানুষের জীবনচক্রকে ভাগই করেছেন যৌনতার ভিত্তিতে। মিঠুর জীবনেও রয়েছে প্রেম-কামের দ্বন্দ্ব। চলচ্চিত্রটি রিওয়াইন্ড করে ৪৬ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ফিরে গেলেই মিঠুকে বলতে শোনা যায়—‘এই ভিডিওটার সাথে, মানে এতোদিন বসবাস করতে করতে আমার ভিতরে একটা লোভ হয়ে গেছে আপা। আমার, শুধু আমি এই লোভটা করেই আপা মানে এই চ্যাপ্টারের একেবারে শেষ ইতি টেনে দিবো আপা।’ কিন্তু ওই চ্যাপ্টারটির ইতি আর টানা হয় না তার। রিমা তাকে বাসা থেকে বের করে দেন। আর তাই হয়তো সেই অবদমিত যৌনাকাক্সক্ষার বহিঃপ্রকাশ মিঠুর ম্যানিকিন নিয়ে শুয়ে থাকা।
চলচ্চিত্রে প্রতীকের কাজ হলো, আসলে যা দেখাচ্ছি তার চেয়ে বেশি কিছু দেখানো; যা শুনছি তার চেয়ে বেশি শোনানো, যা বলছি তার চেয়ে বেশি কিছু বলা। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু না বলেই অনেক কিছু বলা হয়ে যায় প্রতীকের ব্যবহারে—চলচ্চিত্রের সার্থকতা এখানেই। কিন্তু সমসাময়িক বাংলাদেশি নির্মাতাদের ক্ষেত্রে এসবের ব্যবহার দেখা যায় না একেবারেই। তারা হয়তো বেশি কিছু বলতে চান না, দেখাতে চান না, শোনাতে চান না। সাদামাটাভাবে যা দেখাতে চান, সেটুকুই দেখান। যার ফলে অনেক সময় তাদের চলচ্চিত্র আর টিভি-নাটকের পার্থক্য স্পষ্ট হয় না দর্শকের কাছে। কিন্তু ফারুকী এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি যতোটুকু দেখান, তার চেয়ে হয়তো বেশিই বলতে চান। তার সেই অব্যক্ত অনুভূতিগুলো মূর্ত-বিমূর্ত হয়ে চলচ্চিত্রে উঠে আসে প্রতীকের অন্তরালে।
খ. ঘুরে-ফিরে আসি, ফিরে ফিরে যাই
পিঁপড়াবিদ্যার ৪১ মিনিটের দিকে স্বপ্নের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, মিঠু সৈকতে শুয়ে আছেন। তার মুখে এক ঝাঁক পিঁপড়া উঠেছে। ৫১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডে রিমা যখন অন্য কারো সঙ্গে ফোনালাপ করে, তখন মিঠু তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে? পিঁপড়া ভাইয়া?’ এ কথা শুনে রিমা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, ‘ইউ রেড অল মাই ম্যাসেজেস, না? ইউ রেড অল মাই ম্যাসেজেস, তাই না?’ বোঝা যায়, রিমা তার ছেলেবন্ধুকে ভালোবেসে পিঁপড়া নামে সম্বোধন করেন।
এরপর বন্ধুর কাপড়ের দোকানে ঘুমানোর দৃশ্যটিতে (০১:২৯:৩৭) মিঠু হঠাৎ পিঁপড়া দেখতে পান। যদিও পর্দায় তা দেখা যায় না, বোঝা যায় মিঠুর কল্পনা ওই পিঁপড়া। তিনি তখন ম্যানিকিন থেকে আবির্ভূত রিমাকে ঝাড়ু এনে পিঁপড়া মারতে বলেন। নিজেও রিমার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে সেই অদৃশ্য পিঁপড়া মারতে থাকেন।
পিঁপড়াবিদ্যায় পিঁপড়া মোটিফ হিসেবে হাজির হয়। প্রথম দৃশ্যে পিঁপড়া দৃশ্যমান, দ্বিতীয় দৃশ্যে শব্দ হিসেবে পিঁপড়া এবং তৃতীয় দৃশ্যে অদৃশ্য পিঁপড়ার উপস্থিতি। চলচ্চিত্রে বারবার পিঁপড়ার এই উপস্থিতি চিন্তার উদ্রেক করে। ভাবতে হয়, কেনো নির্মাতা পিঁপড়ার ওপর এতো জোর দিলেন? আসলে প্রাণিবিজ্ঞানের তথ্যানুযায়ী, পুরুষ পিঁপড়ারা রানির সঙ্গে যৌনতায় অংশ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করে না। চলচ্চিত্রে মিঠুও সবকিছু ছেড়ে পেতে চান রিমাকে। এমনকি রিমার লোভে পড়ে তার প্রাণ নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে। পুরুষ পিঁপড়ার পাখা গজালে তারা যেমন আগুনের টানে ছুটে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, মিঠুও তেমনই রিমার পিছনে ছুটে সেই একই ভুলই করেন!
আবার দেখা যায়, স্বপ্নের মধ্যে মিঠুর মুখে পিঁপড়া উঠায় লোনা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বারবার মুখ ধুতে থাকেন তিনি। কাট টু শটে দেখানো হয়, পানির কল ছেড়ে মিঠু মুখ ধুচ্ছেন। এ সময় পরপর কয়েকটি কাট টু’তে মিঠুকে মুখ ধুতে দেখা যায়। এছাড়াও চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৫ সেকেন্ড ও এক ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ২৩ সেকেন্ডে পানি দিয়ে মুখ ধুতে থাকেন মিঠু। তিনি তার মুখ থেকে পিঁপড়া ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন বারবার। আসলে মানুষ সবসময় তার বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায়। সে যতো অন্যায়ই করুক না কেনো, তার স্বপক্ষে নিজের কাছে নিজেই যুক্তি দাঁড় করায়। কারণ, ‘সুস্থ’ভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নিজের অন্যায়কে বৈধতা দিতে হয়। তা না হলে নিরন্তর অনুশোচনার আগুন তাকে জ্বালিয়ে মারে। সেজন্যই দেখা যায়, অনেক খুনী একসময় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই হিসেবে মিঠুও হয়তো লোভ, অন্যায়, অসততা, শঠতা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন; নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার হতে চেয়েছেন। তা প্রকাশেই হয়তো ফারুকীর এই প্রয়াস।
বাংলাদেশি চলচ্চিত্র-কারখানায় প্রতীক, মোটিফের এমন ব্যবহার প্রায় বিরল। তার পরও চলচ্চিত্রের এই ক্ষয়িষ্ণুকালে একখণ্ড আশার দীপ জ্বেলে রয়েছেন ফারুকী। তার চলচ্চিত্রজুড়ে প্রতীক ও মোটিফের এই ব্যবহার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও তাকে অনন্য কারিগর করে তুলেছে নিঃসন্দেহে।
মেনে চলা, মানিয়ে চলার বিদ্যা
বেশিরভাগ মানুষ সফলতার পিছনে ছুটে চলে সারাজীবন। সবাই সফল হতে চায়, সেটা হয়তো বেঠিকও নয়। আসলে আমাদের চারপাশে গড়ে ওঠা সমাজে ব্যর্থতার কোনো মূল্য নেই। তবে সবসময় যে সফলতা ধরা দেয়, তা নয়। কখনো কখনো ব্যর্থতার কটু স্বাদও আস্বাদন করতে হয় মানুষকে। কিন্তু গোল বাঁধে তখনই যখন চলার পথে ব্যর্থ হয়ে কেউ সেটাকে মেনে নিতে পারে না। ব্যর্থতার ভয় তার মনে জেঁকে বসে, পালিয়ে বাঁচতে চায়।
মিঠুর সাবেক প্রেমিকা সাথীর বর রেদোয়ানের চাকরি চলে যায়। সাথী তখন মিঠুর সঙ্গে যোগাযোগ করে রেদোয়ানের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। কারণ সাথীর কাছে মিঠু নিজেকে ‘ক্ষমতাবান’ হিসেবেই জাহির করেছেন। কিন্তু আদতে তার নিজেরই তখন দুর্দশা চলছে। সরকার এম এল এম কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় মিঠু পাওনাদারদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সাথীর কাছে তা চেপে যান তিনি। যদিও রেদোয়ানের কাছে সত্য স্বীকার করেন এবং মিঠু নিজের মতো করে তাকেও চাকরিজীবীর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে বলেন। আসলে মিঠু তার চারপাশে মিথ্যা চৈতন্যে পরিপূর্ণ এক জগৎ গড়ে তোলেন। তার যুক্তি—এভাবে অন্তত দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকা যায়। হয়তো এভাবে বাস্তবতা থেকে পালিয়ে থাকা যায়, তবে বেঁচে থাকা যায় না।
মিঠুর মতো বিশ্বের লক্ষ-কোটি নিম্নবর্গের মানুষ ওই মিথ্যা চৈতন্যের মধ্যেই বাস করে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড়ো উৎস গার্মেন্ট শিল্পের দিকে তাকালেই অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়। দাস সমাজে দাসের সন্তানরাও দাসই হতো। দাসের গোটা পরিবারই তার মালিকের সম্পদ ছিলো। এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে বটে, তবে ফলটা পাল্টেনি। একজন গার্মেন্ট শ্রমিক আট থেকে ১৬ ঘণ্টা শ্রম দিয়ে মাস শেষে বড়োজোর ১০-১২ হাজার টাকা পান। অথচ সস্তা শ্রমের বাংলাদেশের কারখানায় ১০ ডলারে উৎপাদিত একটি পোশাক আমেরিকায় বিক্রি হয় ২৫ ডলারে!১
এখান থেকেই বোঝা যায়, এই শিল্পে শ্রম শোষণ কতো ভয়াবহ। তার পরও দিনের পর দিন এই শ্রমিকরা এসব কারখানায় কাজ করে; কম খেয়ে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থেকে টাকা জমায়; সেই টাকায় বেড়ার ঘরে টিন হয়, ডিশের সংযোগ লাগে, কেউ সামান্য জমি বন্ধক নেয়—আরো কতো কতো স্বপ্ন! স্বপ্নের বানে শোষণ ভেসে যায়, থাকে কেবল নিয়তি। ফলে যুগে যুগে তাদের শোষণ আর শেষ হয় না।
পিঁপড়াবিদ্যায় মিঠু নিজের দুরবস্থাকে মেনে নেন; হয়তো ধরে নেন, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে তার মুক্তি নেই। সেজন্য তিনি নিজেকে চাকরিদাতার ভূমিকায় কল্পনা করে মানসিক তৃপ্তি চান। রেদোয়ানের কাছে মিঠু স্বীকার করেন, সাথীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ‘সিদ্ধান্ত নিলাম, এ রকম ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা খাওয়া বেকার বিধ্বস্ত যুবকের চরিত্রে আমি আর অ্যাক্টিং করবো না। তখন আমি আমার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করলাম এবং চাকরিদাতার ভূমিকায় অ্যাক্টিং শুরু করলাম।’ এভাবে অভিনয় করে মিঠু নিশ্চয় প্রভূত আনন্দ পান। কিন্তু বাস্তবের নিম্নবর্গ চাইলেই এতো সহজে ‘ক্যারেক্টার’ পরিবর্তন করতে পারে না। তবে তারা এটা ভেবে তৃপ্তি পায় যে, ভালোই তো আছি, তিন বেলা অন্তত খেয়ে-পরে বেঁচে আছি। প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রাপ্য কী, তা নিয়ে তারা আর ভাবেন না। অন্যভাবে বললে, ভাবতে দেওয়া হয় না। তারা ধরেই নেয়, এটাই তাদের নিয়তি। কিন্তু তার পরও কথা থেকে যায়। নিম্নবিত্ত ওই মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে, মাসের পর মাস সময় মতো বেতন পায় না, তখন কখনো কখনো তারা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু পিঁপড়াবিদ্যার মিঠু বা রেদোয়ানের সে ক্ষমতাও নেই! তারা তাদের দুরবস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। বাস্তবে সরকার এম এল এম কোম্পানিগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সময় সেখানে ‘বিনিয়োগ’কারীরা বিক্ষোভ করলেও২, মিঠু কিন্তু সব মেনে নেন।
বাংলাদেশে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে এম এল এম কোম্পানির আগমন ঘটলেও, বড়ো আকারে প্রথম কাজ শুরু করে ডেসটিনি-২০০০। ওই ২০০০ খ্রিস্টাব্দেই ‘নিউওয়ে’ নামে আরেকটি এম এল এম প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। এরপর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি অনুমোদন পায় প্রায় ৭০টি প্রতিষ্ঠান।৩ রাষ্ট্রের নাকের ডগায় বসে দীর্ঘ দেড় যুগ এম এল এম-এর নামে ‘অবৈধ’ভাবে মূলধন সংগ্রহ করার অভিযোগে ২০১২-তে সরকার এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সব এম এল এম প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার ততোদিনে হয়ে গেছে! এই কয়েক বছরে প্রতারণার মাধ্যমে শুধু ডেসটিনি-২০০০’ই আত্মসাৎ করেছে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা।৪ কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীদের এসব টাকা ফেরত দিতে সরকার দৃশ্যত তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। বরং নতুন করে এম এল এম কোম্পানির পরিচালনার জন্য আইন করে সরকার। অন্যদিকে মিঠুর মতো হাজার হাজার প্রতারিত তরুণ-যুবক এখনো দেনার দায় টেনে চলেছে। কিন্তু এই পুরো অবস্থা নিয়ে পিঁপড়াবিদ্যার মিঠু উদাসীন। প্রতারণা বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেন না। মুখ বুজে সব মেনে নেন মিঠু, অন্যকেও এভাবে মেনে নিতে বলেন।
অন্যদিকে রিমা তার ব্যক্তিগত ভিডিওটিই শুধু ফেরত চান। ভিডিওটি প্রকাশ হয়ে গেলে তার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে—এই ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকেন তিনি; পুলিশের কাছে পর্যন্ত যেতে চান না। কিন্তু একই ঘটনা কোনো ‘অ-তারকা’ নারীর সঙ্গে ঘটলে কী হতো? তার তো ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা থাকতো না, বরং সমাজ হয়তো তাকে একঘরে করে দিতো। তার পরও সেই নারী হয়তো রাষ্ট্রের কাছে বিচার চাইতেন—এমন উদাহরণ সমাজে আছে। তবে রিমা কিন্তু কখনোই মিঠুর বিচার চাননি কিংবা তার প্রেমিকের, যার ‘অদূরদর্শিতা’য় ওই ভিডিও প্রকাশ হয়েছে। তিনি সবসময় মিঠুকে মানিয়ে-বুঝিয়ে চলতে চেয়েছেন। তার বাজারি ক্যারিয়ারের চিন্তাই তাকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেয়নি। কিন্তু এই মেনে নেওয়া, মানিয়ে চলার পথ অবলম্বন করে যে সমাজ-রাষ্ট্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায় না, তা কি ফারুকীর জানা নেই!
পথের শেষ কি এখানেই?
মানুষের ষড়রিপুর অন্যতম লোভ। অর্থ, সম্পদ, নাম-ডাক, ক্ষমতা, সুখ-শান্তি কতো কিছুর লোভ যে আছে মানুষের জীবনে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের স্বভাবজাত সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, নিজেকে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চায়। আর এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায় পুঁজি। পুঁজির বৈশিষ্ট্যই স্ফীতি। এই স্ফীতির জন্য দরকার ভোক্তা, আরো বেশি ভোক্তা। শিল্পবিপ্লবের পর সারাবিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। যে পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন বেড়ে যায় বহুগুণ। তখনই দরকার পড়ে আরো অধিক ভোক্তার, যারা ‘প্রয়োজনে’ কিনবে, ‘প্রয়োজন’ না থাকলেও কিনবে।
আধুনিক নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে এই সময়টাতে। সে সমাজের মানুষকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে ওঠে তার অর্থ-সম্পদ বা আরো স্পষ্ট করে বললে ক্রয়ক্ষমতা। আর এইসব মানুষকে ক্রেতায় পরিণত করতে পুঁজির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে তারকা রিমা’রা। পুঁজির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রিমাদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় মানুষ। রিমারা তাদের মধ্যে ‘অভাব’ জাগিয়ে তোলে। যে অভাব পূরণের জন্য মিঠুরা ‘ন্যায়-অন্যায়’ বিচার না করেই ছুটতে থাকে পুঁজির পিছনে। এভাবে ছুটতে ছুটতে একসময় পুঁজিই ওই মানুষের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। সে আর নিজের মধ্যে থাকে না, নিজ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, হারিয়ে ফেলে নিজের নিয়ন্ত্রণ। ঠিক যেমন হারিয়েছে মিঠুর কিংবা এম এল এম কোম্পানির লক্ষ-লক্ষ ‘বিনিয়োগকারী’র। তারা অনাগত অর্থের লোভে পড়ে যুক্তির ধার ধারেনি। গোটা প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রশ্নও জাগেনি। যার ফলে শেষ পর্যন্ত মিঠুর ভাষায় ‘ধরা খেয়েছে’ তারা।
অন্যদিকে রিমার ভিডিওর বদৌলতে তাকে ব্ল্যাকমেইল করেন মিঠু। চলচ্চিত্রের ১৩ মিনিট ২০ সেকেন্ডে তিনি কল্পনায় ভিডিওর বিনিময়ে রিমার কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। কিন্তু পরক্ষণেই হয়তো তার ক্ষমতার দৌড় স্বল্প বুঝতে পারেন মিঠু। এবার ৫০ থেকে এক লক্ষে নেমে আসে তার চাহিদা। তবে শেষ পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধের কারণেই হয়তো কোনো টাকাই চাইতে পারেন না মিঠু। বরং মোবাইলের দাম বাবদ রিমার দেওয়া অতিরিক্ত টাকা তাকে ফেরত দেন। দর্শক ধরে নেয় মিঠু ‘সৎ’, ‘নির্লোভ’, ‘পরোপকারী’, ‘সাচ্চা’ লোক; যদিও অভাবের কারণে তার মাঝেমধ্যে সামান্য মতিভ্রম হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, মিঠু ষড়রিপুর আরেক রিপু কামের ফাঁদে পড়েছেন। তিনি রিমাকে চান।
এই লোভের ফল ভালো হয় না। জীবন বাঁচাতে মিঠুকে পালাতে হয়। তার পিছনে একদিকে পাওনাদার, অন্যদিকে রিমার লাগিয়ে দেওয়া মাস্তান ঘুরতে থাকে। ছুটতে ছুটতে তিনি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন; ফিরে আসেন মায়ের কাছে, প্রতিজ্ঞা করেন ছোটোবেলার মতো ভালো হয়ে যাওয়ার। এরপর মিঠুকে স্কুলব্যাগ কাঁধে ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় দেখা যায়। আরো দেখা যায়, পাওনাদার এসে মিঠুর বাবাকে হুমকি দিচ্ছে—‘শোনেন চাচা, এতো ভাঙ-ভুঙ করার দরকার নাই। আপনার ছেলের কাছে আট লাখ ট্যাকা পাই। আট লাখ টাকাই দিতে কন—এরম পাগল-ছাগল অনেক দেখছি। পাগলামি কইরা লাভ নাই। ... আমার ট্যাকা দেন, তা নাইলে এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে লেইখা দেন।’ পর্দায় মিঠুকে দেখে মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে হয়। তার ছোটো বোন তখন জিজ্ঞেস করে, ‘ভাইয়া, তুমি কি সত্যি সত্যিই ...? নাকি অ্যাক্টিং করতেছো? বলো না ভাইয়া, প্লিজ!’ মিঠু শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন!
এই একটি সংলাপ দিয়েই হয়তো পুরো চলচ্চিত্রে যা বলতে চান, বলে দেন নির্মাতা ফারুকী। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মিঠুর হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে ব্যর্থ হওয়া; একপর্যায়ে এম এল এম কোম্পানিতে ‘চাকরি’ লাভ; ঘটনাক্রমে একজন তারকার ব্যক্তিগত ভিডিওসহ মোবাইল হাতে পাওয়া; সেই ভিডিওর বিনিময়ে তারকাকে ব্ল্যাকমেইল করা; সরকারি নির্দেশে এম এল এম কোম্পানি নিষিদ্ধ হওয়ায় টাকা লগ্নি করে ‘ধরা খাওয়া’; পাওনাদারদের চাপ; সেই তারকার লেলিয়ে দেওয়া মাস্তান; পরিবারের অভাব-অনটন সবমিলিয়ে মিঠুদের ‘সুস্থ’ থাকার মতো পরিবেশ থাকে না। কিন্তু এই অসুস্থ পরিবেশের দায় কী শুধুই মিঠুদের!
উচ্চশিক্ষা নেওয়ার পরও কেনো মিঠুকে বেকার থাকতে হয়, কেনো তার মা’কে বলতে শোনা যায়, ‘এই কালকে তুই বাচ্চুর গ্যারেজে যাবি, রিকশার রোজ কতো জিজ্ঞেস করবি। আপনে তো আবার মাস্টার ডিগ্রি পাস, ছোটো কাজ করতে পারবেন না। আমি পায়জামা পরে রিকশা চালাইতে পারবো।’ এক কথায় বলতে গেলে, এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির সমাধান এতো সহজ নয়। এই গোটা পরিস্থিতির সঙ্গেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা-পুঁজি জড়িয়ে আছে, তাদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। অথচ ফারুকী কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি সমাধানের পথ দেখান; এক. এই পরিস্থিতিতে তাকে হয় পাগল হতে হবে। দুই. তাকে পাগলের অভিনয় করে টিকে থাকতে হবে। অর্থাৎ পরিস্থিতির বয়ান দিয়েই তিনি থেমে যান। কিন্তু এই পরিস্থিতিও যে চিরন্তন নয়, তা বলতে তিনি হয়তো ভুলে গেছেন! সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ পরিবর্তনের পিছনে ছুটেছে। ফলে এককালের ‘অনুৎপাদনশীল’ আদিম সাম্যবাদী সমাজ কালের পরিক্রমায় আজকের ‘উৎপাদনির্ভর’ পুঁজিবাদী সমাজে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ফারুকী তার চলচ্চিত্রে এই বিবর্তনকে ধরতে পারেননি, তিনি স্থির হয়েছেন। তবে পিঁপড়াবিদ্যা দিয়ে তার অঁতর নির্মাতা হওয়ার সুযোগ ছিলো।
লেখক : মাহামুদ সেতু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী।
msetu.mcj@gmail.com
তথ্যসূত্র
1. https://goo.gl/Vd0Gax; retrieved on 14.10.2016
2. http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-10-10/news/296647; retrieved on 12.09.2016
3. http://www.somewhereinblog.net/blog/habib700/29597354; retrieved on 20.10.2016
4. http://www.deshebideshe.com/home/printnews/6649; retrieved on 15.10.2016
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন