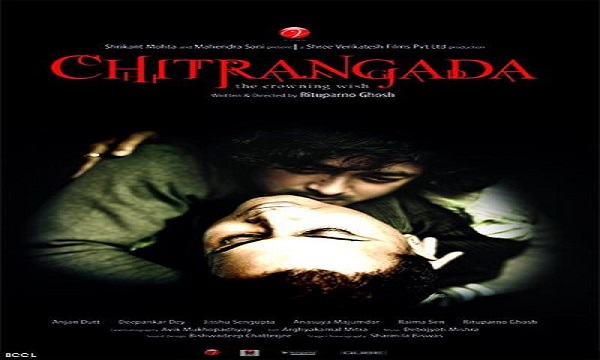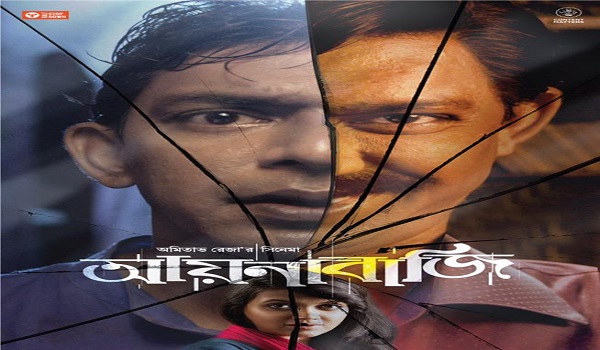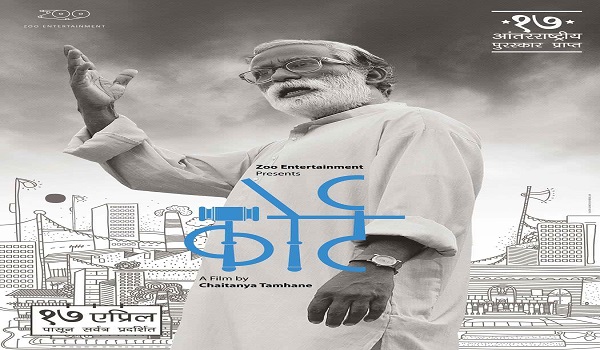পপি সরদার
প্রকাশিত ১২ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
নিজের দর্পণে দেখা 'টু অ্যান্ড টু'
পপি সরদার

চলচ্চিত্রটি মাত্র ছয় মিনিট ৫১ সেকেন্ডের। এতো ছোটো কাহিনি, অথচ রেশ থেকে গেলো সারাটি দিন। সারাজীবন ধরে মেনে নেওয়া অনেক বিষয়ই কেনো জানি মনে পড়তে লাগলো। এর অনেকগুলোই অবশ্য স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। এমন অনেক অপছন্দের কাজ করতে হয়েছে, যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে কখনো মেনে নিতে পারিনি, আজও কষ্ট হয়। সেসময় প্রচণ্ড চাপে পড়ে করতে হয়েছিলো। বিষয়গুলো আমার পছন্দ কি না, সেটা জানার প্রয়োজন মনে করেনি কেউ। অবশ্য এগুলো নিয়ে কখনো প্রতিবাদ যে করেছি, তাও নয়। কিন্তু এতোদিন পরে এসে সেসব বিষয় কেনো জানি আজ নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, জীবনের প্রতিটি ধাপে আমার অসহায়ত্বের কথা। মায়ের হাত ধরে বিদ্যালয় যাওয়া থেকে শুরু করে বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অসহায়ত্ব খুব বেশিই মনে করিয়ে দিয়েছে টু অ্যান্ড টু (২০১১) চলচ্চিত্রটি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চলচ্চিত্রের কাহিনি শুধু আমার জীবনের সঙ্গেই না, আরো অনেকের সঙ্গেই হয়তো মিলে যাবে।
ইরানি নির্মাতা বাবাক আনোয়ারি’র (Babak Anvari) টু অ্যান্ড টু-এর গল্পটা এমন—ছেলেদের স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে আছে। এমন সময় শিক্ষক ক্লাস নিতে সেখানে ঢোকেন। একটু পরেই শ্রেণিকক্ষে লাগানো সাউন্ডবক্সে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য শোনা যায়। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘স্কুলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে, শিক্ষার্থীদেরকে এসব নিয়ম মানতে হবে।’ এরপর শ্রেণিশিক্ষক ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। শুরুতেই তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখেন ২ + ২ = ৫, এটা দেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হালকা গুঞ্জন শুরু হয়।
শিক্ষক সবাইকে থামতে বলে তাদেরকে একসঙ্গে বলতে বলেন, ‘দুই যোগ দুই সমান পাঁচ।’ এ কথা শুনে এক শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলে, ‘স্যার, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, দুই যোগ দুই সমান চার।’ শিক্ষার্থীর কথা শুনে শিক্ষক বলেন, ‘তোমাকে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ বলতে বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে তোমার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।’ তখন শিক্ষার্থী বলে, ‘স্যার, আমি চিন্তা করে দেখলাম, দুই যোগ দুই সমান চার-ই।’ এ কথা শুনে এবার শিক্ষক ওই শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলেন, ‘তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। তোমার চিন্তা করার দরকার নেই। দুই যোগ দুই সমান পাঁচ।’ এরপর তিনি সব শিক্ষার্থীকে তাদের নোটবুকে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ লিখতে বলেন।
ঠিক এ সময় আরেকজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলে, ‘স্যার, দুই যোগ দুই তো সবসময়ই চার। এটা কীভাবে পাঁচ হয়?’ এ কথা শুনে শিক্ষক এবার রেগে বলেন, ‘তোমাকে কে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে? এতো সাহস তোমার, আমাকে প্রশ্ন করো!’ তার পরও ওই শিক্ষার্থী কথা মানতে চায় না। সে অন্যান্য শিক্ষার্থীকে বলে, ‘তোমরা দেখো দুই যোগ দুই সমান অবশ্যই চার।’ এরপর সে শিক্ষককে বলে, ‘স্যার, আপনি তো জানেন এটা চার। তাহলে কেনো পাঁচ বলছেন!’ এ কথা শুনে শিক্ষক প্রচণ্ড রেগে বলেন, ‘আমি যতোক্ষণ না আসবো, তুমি কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে।’
এরপর শিক্ষক ক্লাসের বাইরে গিয়ে তিন ছেলেকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে বলেন, ‘এই ছেলেটি মনে করছে সে আমার চেয়ে ভালো জানে।’ এরপর শিক্ষক ওই শিক্ষার্থীর কাছে আবার জানতে চান, ‘দুই আর দুই কতো?’ শিক্ষার্থী তখনো চার-ই বলে। শিক্ষক তখন ছেলে তিন জনকে দেখিয়ে বলেন, ‘এরা এই স্কুলের সেরা শিক্ষার্থী। তোমরা নিজেদেরকে এদের থেকেও ভালো শিক্ষার্থী ভাবছো!’ তারপর তিনি শিক্ষার্থী তিন জনের কাছে জানতে চান, দুই আর দুই কতো? উত্তরে তারা বলে, ‘স্যার, পাঁচ।’ এরপর ওই শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ লিখতে বলেন শিক্ষক। এই সময় ওই তিন শিক্ষার্থী তার দিকে বন্দুকের নল তাক করে রাখে। শিক্ষক কথা না শোনা ওই শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘এটাই তোমার শেষ সুযোগ।’ কিন্তু তার পরও ওই শিক্ষার্থী লিখে, দুই যোগ দুই সমান চার; সঙ্গে সঙ্গে গুলি এসে তার গায়ে লাগে, রক্ত ছিটকে পড়ে ব্ল্যাকবোর্ডে। শিক্ষক সেই রক্ত মুছে আবারও লেখেন ‘২ + ২ = ৫’। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের তার সঙ্গে বলতে বলেন, ‘দুই যোগ দুই সমান পাঁচ।’ শিক্ষার্থীরা তার সঙ্গে বলতে থাকে এবং খাতায়ও লিখে। কিন্তু শেষ বেঞ্চের এক শিক্ষার্থী শিক্ষকের কথায় প্রথমে পাঁচ লিখলেও তা কেটে দিয়ে লেখে চার। এর মধ্য দিয়ে টু অ্যান্ড টু শেষ হয়। আমি নির্বাক বসে থাকি। ভাবি, আমিও তো অনেক ক্ষেত্রেই শেষ বেঞ্চে বসা ওই শিক্ষার্থীর মতো শ্রেণিকক্ষে আমার মতামত জানাতে পারিনি। ওই শিক্ষার্থী তবু খাতায় প্রতিবাদ করেছিলো, আমি এবং আমার অনেক বন্ধু তো পারিনি। আজ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও যে পারছি, তা নয়।
সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারের বাইরে গিয়ে জীবনের প্রথম পথচলা শুরু হয়েছিলো আরেক প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়ে। বন্দি হলাম আরেক কাঠামোবদ্ধ জীবনে। যেখানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়াশোনা চলতো। সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যসূচিগুলো শিক্ষার্থীদের পছন্দ কি না, তারা সেগুলো পড়তে চায় কি না, সে নিয়ে শিক্ষকদের কোনো ভাবনা ছিলো না। শিক্ষকরা ক্লাসে যা পড়াতেন তার বাইরে কোনো কথা যে থাকতে পারে, তা কখনো মাথায়ই আসেনি। প্রতিদিন পড়া দেওয়া থাকতো। যেগুলো পরদিন ক্লাসে গিয়ে সঠিকভাবে বলতে না পারলে ছিলো শাস্তির ব্যবস্থা। কখনোবা বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা, কখনো বেত্রাঘাত, কখনোবা কান ধরে সম্পূর্ণ স্কুল-মাঠ দৌঁড়ানো। আমাদের কাছে এসব শাস্তি ছিলো খুবই স্বাভাবিক। এখনো অনেকেই বলতে পারে, পড়া না পারলে তো শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু সেই শাস্তি শিশুর কোমল হৃদয়ে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলো বা ফেলে, তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিলো না। আজকে এই সময়েও যে এ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা আছে, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।
যদি থাকতোই তাহলে হয়তো সাথীকে১ এভাবে জীবন দিতে হতো না। পড়াশোনা নয়, চাঁদপুরের বাগাদী গ্রামের বাগাদী গণি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাথী পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে পারেনি। তাই সাথীসহ কয়েকজনকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন তাদের শিক্ষক। অনুশাসনে আবদ্ধ সাথী তখন এর প্রতিবাদও করতে পারেনি। তখন না পারলেও সেই অপমানের প্রতিবাদ সে করেছে জীবন দিয়ে; স্থাপন করে গেছে প্রতিবাদের এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। সাথীর কথা সংবাদপত্রে পড়ে এখন মনে হয়, যেকোনো ভাবেই হোক সে তবু প্রতিবাদ করেছিলো, আমি-আমরা তো তাও পারিনি। দীর্ঘ শিক্ষাজীবনের নানা খারাপলাগা, কষ্ট সব বুকের ভিতর মাটি চাপা দিয়ে বেঁচে আছি!
বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ভর্তি হই মহাবিদ্যালয়ে। কিন্তু এখানকার পড়াশোনাও বিদ্যালয় থেকে আলাদা ছিলো না। শিক্ষকদের শেখানো বুলির বাইরে এখানেও কথা বলা ‘নিষেধ’। ‘ভালো’ শিক্ষার্থী হতে চাইলে শ্রেণিকক্ষে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন, তর্ক, প্রতিবাদ করা যেতো না। তবে মুখে প্রতিবাদ করতে না পারলেও, মনে মনে যে করতাম না, তা কিন্তু নয়। সামনে বিনয়ের অবতার হলেও, পিছনে ঠিকই তাদের সমালোচনা কম করতাম না। তবে সেগুলো শুধু নিজেদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারিনি কখনোই। কারণ আমরা ছিলাম ‘ভালো’ শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের মুখের ওপর কথা বলার মতো ‘বেয়াদব’ আমরা ছিলাম না। বিষয়টা সেলিম রেজা নিউটনের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়,
সামনে ‘সালাম’। পেছনে ‘শালা’। এই তো এক কথায়। আমার সময়েও দেখেছি, যখন আমি ছাত্র ছিলাম। টিচারদের সামনে দেখা হলে পরেই ‘সøামালেকুম স্যার’, পিছনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে। আর, সামনে থেকে গেলে পরেই ‘শালা, বদমাইশ, ক্লাস নেয় না।’ আমি বলেছি প্রচুর। আমি। মাইসেল্ফ। প্রচুর বলেছি। কেন বলব না? ছাত্ররা এখনও বলে। কেন বলবে না? অবশ্যই বলবে। সামনে বলতে পারে না বলে পেছনেও বলবে না! এ হলো সম্পর্ক।২
কলেজের পাঠ চুকিয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমার মতো অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আসে স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-কলেজে থাকতে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনেক গল্প শুনতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তচিন্তার চর্চা হয়, যেকোনো শিক্ষার্থীই এখানে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে। তাদের ভালোলাগা, মন্দলাগার বিষয়গুলো জানাতে পারে—এ রকম অনেক কিছুই। কিন্তু এখানে এসে সে ধারণা পরিবর্তন হতে বেশিদিন লাগেনি। আয়তন ও পরিসর ছাড়া স্কুল-কলেজ থেকে এটাকে পৃথক করতে পারিনি খুব বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলাম, এখানকার শিক্ষকরাও প্রশ্ন করা পছন্দ করে না। পছন্দ করে না, তাদের তৈরি চিন্তাকাঠামোর বাইরে গিয়ে কথা বলা। এখানেও সিলেবাসভুক্ত প্রশ্নহীন পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা দিন দিন উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। আর দিনের পর দিন সেই উদ্যমহীনতার জায়গা তৈরি করে দেন আমাদের শিক্ষকরাই।
পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা এত উদ্যমহীন কেনো? পড়ালেখায় আনন্দ নেই বলে। আনন্দ নাই কেনো? স্বাধীনতা নাই বলে। যেখানে যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন না সেখানে সেখানে তাঁরা নিস্তেজ, মরা, পঙ্গু, চিন্তাহীন, প্যাসিভ, অসক্রিয়, নিষ্ক্রিয়। এই জায়গাগুলো কোথায়? ক্লাসরুম। সেখানে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় কে? শিক্ষক। কারণ, তুলনামূলকভাবে তাঁর স্বাধীনতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ‘ডিপার্টমেন্ট’ বলতে শিক্ষককে বোঝায়, তাঁদের সিদ্ধান্ত আর কর্মকাণ্ডকে বোঝায়, শিক্ষার্থীরা যেগুলোতে অংশগ্রহণ করে মাত্র।৩
ফলে একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিসর হয়ে ওঠে কেবল পরীক্ষায় পাস করার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন পড়ে ঠিক ততোটুকুই। এক শিক্ষাবর্ষ থেকে আরেকটায় পদার্পণই হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে শিক্ষকরা এতোই ক্ষমতাবান যে, কোনো চিন্তা, কথা,এমনকি পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তরটি তাদের চিন্তা, মতামত, মতাদর্শের সঙ্গে না মিললে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই বেশিরভাগ সময়ই মধ্যবিত্ত ঘরের এই আমি মনের জিজ্ঞাসাকে লুকিয়ে রেখেছি; শান্ত করতে পারিনি। তাদের আচরণে মনে হয়েছে, শিক্ষকরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তবে এখানেও কিছু ‘বেয়াদব’ শিক্ষার্থী দেখেছি, যারা শিক্ষকদের সব কথা মুখ বুজে মেনে নেয়নি। নিজেদের ভিন্ন মত তুলে ধরেছে মাথা উঁচিয়ে। শিক্ষকদের কোনো অন্যায় দেখলে, সেটিকে মেনে না নিয়ে, মোসাহেবি না করে বরং তার প্রতিবাদ করেছে।
শিক্ষার্থীদের এ ধরনের ‘দুঃসাহসিক’ আচরণে কোনো কোনো শিক্ষককে প্রচণ্ড রেগে যেতে দেখেছি। কেউ কেউ তাদের এ রাগের বহিঃপ্রকাশও করেছে পরবর্তী সময়ে। তবে এর ব্যতিক্রম যে দু-একজনকে একেবারেই দেখিনি তাও কিন্তু নয়। শিক্ষকের সেই রাগের শিকার হতে দেখেছি অনেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতায়। শিক্ষকরা সেখানে প্রমাণ দিয়েছে তাদের ক্ষমতার! তাদের অনেককে এমনও বলতে শুনেছি, ‘খাতায় নয়, নম্বর থাকে শিক্ষকের মাথায়।’ ফলে ফল প্রকাশের পর ওই সব ‘বেয়াদব’ শিক্ষার্থী বুঝে যায় তাদের ‘অপরাধ’। শাস্তি পেয়ে এদের অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে ‘ভালো’ হয়ে যায়। তবে সবাই যে ‘ভালো’ হয়, এমন নয়। আর সে কারণেই হয়তো এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা কিছুটা হলেও টিকে আছে। আর বছরের পর বছর এভাবেই চলছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন!
এ তো গেলো আমার পারিবারিক ও শিক্ষা জীবনের কথা। একজন নাগরিক হিসেবে মনে হচ্ছে, আমার অবস্থান ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে আমাদের প্রত্যেকের জীবন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাই কেমন যেনো আতঙ্কিত। যদিও মাঝে মাঝে নিজেকে আশেপাশের মানুষদের থেকে নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু একটু পরেই মনে পড়ে আমার বাবা, ভাই, প্রিয় শিক্ষক ও আপনজনদের কথা; তারা নিরাপদে আছেন তো? সরকার, রাষ্ট্রের সমালোচনা করে—এমন পরিচিতজনদের নিয়ে সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকি। গুম, খুন, ধর্ষণ, জখম, ক্রসফায়ার, ভিন্ন মতকে নির্মমভাবে দমন আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার পরও সবাই যে ভয়ে থাকে, এমন নয়। কেউ কেউ ‘দুঃসাহস’ও দেখিয়ে ফেলে। তাদের নিয়ে শঙ্কা কেবল বাড়তেই থাকে; একটি বিষয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই, আরেকটি খুব সহজে আমাদের ভিতর ঢুকে যায়। দিন দিন এতো শঙ্কার মধ্যেও আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা ভুলে যাই আগেরটা! অর্থাৎ খুব সাবধানে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মনন-চিন্তাকে অন্যদিকে নেওয়া হয়। আর আমরাও খুব সচেতনভাবেই নিজেদের গা বাঁচাতে নির্দেশিত পথে হেঁটে চলি। এগুলোই হয়ে উঠছে আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবন!
কেমন জানি নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি আমরা। ‘আমরা এই আশা করতে করতে বাঁচি যে মরলে মরবে আর কেউ, আমি না। ভুলে যাই যে মরে গেছে সেও এমনটাই ভাবত।’৪ অন্যের কথা ভাবার যেনো কোনো সময়ই নেই। অন্য পথে হাঁটলে যদি ওই রকম বিপদ হয়? যদি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হই? কিন্তু এতো কিছুর পরও শঙ্কা আর কমে না; সঙ্গে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আমাকে কুঁকড়ে ছোটো করে দেয়।
আর এসব বিষয় নিয়ে প্রতিদিন চারপাশে যে চর্চা চলে, তা চিন্তার জগতকে দিন দিন মনে হয় অবশ করে ফেলছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র, টেলিভিশনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আতঙ্কিত করা ব্রেকিং নিউজ, টক-শো—একই সঙ্গে আমাকে বিচলিত, মানিয়ে চলতে সহায়তা করে। টক-শো’তে অনেকের আলোচনায় দেশের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে দল। টু অ্যান্ড টু-এ ক্লাসের সেই ‘সেরা’ শিক্ষার্থীদের মতো তারা সর্বজ্ঞানী হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। সত্য-মিথ্যা-বাস্তব সবকিছুকে প্রয়োজন মতো তারা একাকার করে ফেলে! অন্যদিকে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পছন্দ মতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার; সেটার ভিন্ন চর্চা আমাকে ভীত করে।
ভাবি, ব্যক্তি-নাগরিকের পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্য নেই এখানে। সবই চলছে বিশেষ ব্যক্তি, দলের পছন্দে। সর্বক্ষেত্রেই একধরনের নজরদারি। কাজকর্ম বিশেষ কোনো দল-মতের সঙ্গে মিলে না গেলেই যতো বিপদ। সবমিলিয়ে চারিদিকে কেমন জানি একটা ভীতিকর পরিবেশ!
তবে এই পরিবেশের মধ্যেও অনেকে অন্যায়কে অন্যায়ই মনে করছে। মনের ভিতর বপন করছে প্রতিবাদের বীজ। অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি করতে পারি না—ঠিক। কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো ভাই-বোন, চারপাশের দুই-একজনকে দেখি ঠিকই মাথা উঁচিয়ে কথা বলছে। ওই ‘বেয়াদব’ শিক্ষার্থীর বেয়াদবিতে হয়তো টিকে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়; অকুতোভয় চেনা মানুষটির বদৌলতে হয়তো টিকে যাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম; ‘সভ্য’ সমাজের ‘বখে’ যাওয়া কোনো তরুণের হাত ধরেই হয়তো অবসান হবে সব ভয়ের—এমন আশা মন করতেই চায়। মনে পড়ে টু অ্যান্ড টু-এর শেষ দৃশ্য, একেবারে শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীটি ২ + ২ = ৫ লিখে, পরক্ষণেই কেটে দিয়ে লেখে চার। তখন ভাবি, ‘একটি সমাজকে যখন সাপ্রেস করা হয়, প্রত্যেকটা ভিন্নমতকে যখন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরা হয় বা গুম করে দেয়া হয়, তখন ওই সমাজের ভিতরেই প্রতিচিন্তা জন্মাতে থাকে।’৫ আমরা হয়তো এখন সেই প্রতিচিন্তার অপেক্ষাতেই আছি।
লেখক : পপি সরদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।
popysarder@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. ‘স্কুলে পরীক্ষার ফি না দিতে পারায় শাস্তি : ছাত্রীর আত্মহত্যা’; প্রথম আলো, ৩০ আগস্ট ২০১৬।
২. নিউটন, সেলিম রেজা; ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার : প্রসঙ্গ শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি’; যোগাযোগ; সম্পাদনা : ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৯।
৩. প্রাগুক্ত; নিউটন (২০১১ : ৪৪)।
৪. আহমেদ, বখতিয়ার (২০১৫ : ৬৮); ‘গুম-খুন-আতঙ্ক : শাসন প্রণালী ও হত্যার কথকতা’; বাংলাদেশ পরিস্থিতি : নয়া উদারবাদী যুগে শাসনপ্রণালী ও কথকতা; সংকলন সম্পাদনা : বাধন অধিকারী; কাঠপেন্সিল, ঢাকা।
৫. প্রাগুক্ত; আহমেদ (২০১২ : ৬৯)।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন