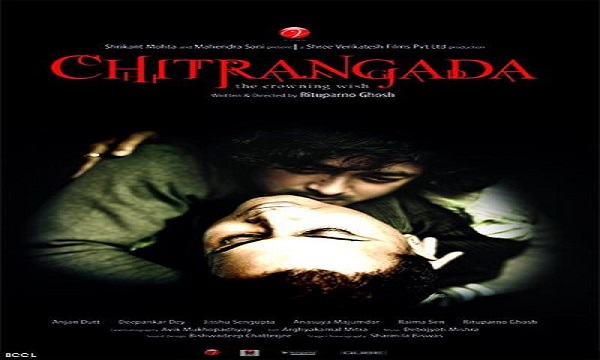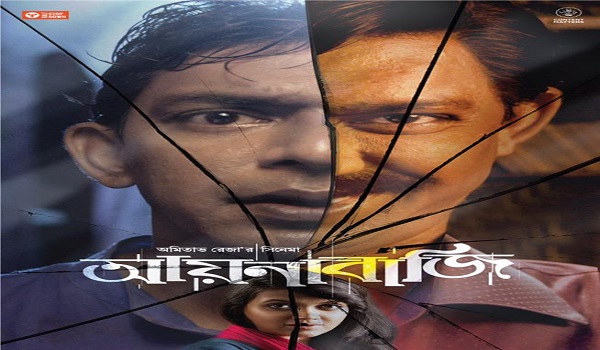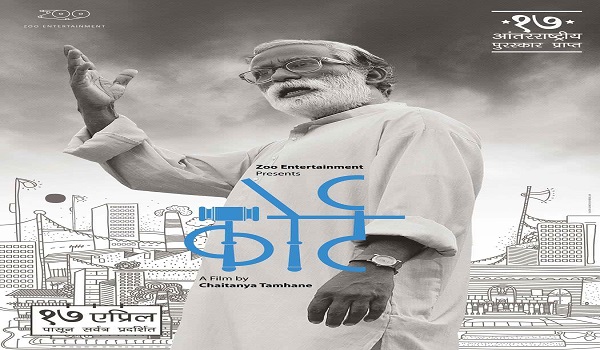আমিনুল ইসলাম
প্রকাশিত ০৯ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
‘অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড’ : যোগাযোগ বৈকল্য ও মানবিকতার রূপায়ণ
আমিনুল ইসলাম

মানবীয় চাহিদা/আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা/আকাঙ্ক্ষাটি হলো জগতের কোনো কিছু সঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং অন্যের নিকট নিজে বোধগম্য হওয়া। র্যাল্ফ নিকোলস
নিজেকে প্রকাশ করা এবং অন্যের প্রকাশকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারার ব্যাপারটি সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত মানবীয় চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি। জগতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সবচেয়ে সচেতন ও সক্রিয় সৃষ্টি হলো মানুষ। মানবজাতির জন্য সবচেয়ে তীব্র ও জোরালো আকাঙ্ক্ষাটি হলো পরিপার্শে¦র সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারা এবং জগতের সমস্ত উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দিতে পারা। কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো সময়ের জন্য তার জাগতিক ও সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলে সে উন্মাদ, পাগল ও পাশবিক হয়ে উঠবে। কাজেই কার্যকর যোগাযোগের সক্ষমতা ও সুযোগ একই সঙ্গে মানুষের জন্য উপহার ও অভিশাপস্বরূপ। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই মানুষ জাগতিক পরিমণ্ডল থেকে উৎসারিত সঙ্কেতগুলো উপলব্ধি করতে পারে। এসব সঙ্কেতে বৈচিত্র্যময় মিথস্ক্রিয়ামূলক অনুঘটক ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই সেসব সঙ্কেত হয়ে উঠতে পারে মানুষের জন্য আনন্দদায়ক; আবার যন্ত্রণাদায়কও।
যাহোক, মানুষ হিসেবে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রকাশ করার প্রশ্নে আমরা যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি। অর্থাৎ যেকোনো মূল্যে আমরা সমগোত্রীয় সৃষ্টিসত্ত্বার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে চাই। যোগাযোগের এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের জন্মগত। তবে এই যোগাযোগ সক্ষমতা সবার সমান থাকে না। নিজেকে প্রকাশ করা এবং অন্যের প্রকাশকে উপলব্ধি করার প্রশ্নে বহুমাত্রিক বাধা কাজ করে। এই বাধার ফলে ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ বৈকল্য (communication disorder) দেখা দেয়।
বর্তমান আলোচনায় ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড-এ মানবীয় যোগাযোগ বৈকল্যের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এই আলোচনা কোনোভাবেই চলচ্চিত্রটির সমালোচনা বা নান্দনিক রস আস্বাদন নয়। বরং এই চলচ্চিত্রের একটি চরিত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ বৈকল্য ধারণাটি উপলব্ধির প্রয়াস মাত্র। এই আলোচনায় মানবীয় যোগাযোগ বৈকল্যের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে সিজোফ্রেনিয়া ও যোগাযোগ বৈকল্যের বিভিন্ন মাত্রা। এজন্য চলচ্চিত্রটির কাহিনি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর চলচ্চিত্রের জন ন্যাশ চরিত্রটির যোগাযোগ বৈকল্যের বিভিন্ন মাত্রা উপলব্ধি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। এই আলোচনায় চলচ্চিত্র অধ্যয়নের কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোর আশ্রয় নেওয়া হয়নি। তবে সোশ্যাল কগনিটিভ থিওরি (Bandura, ১৯৯৯), কগনিটিভ ফিল্ম থিওরি (Allen, ২০০১) ও সাইকো অ্যানালাইটিক ফিল্ম থিওরি (ঈৎববফ, ১৯৯৮) চিন্তার চালিকাকাঠি হিসেবে কাজ করেছে।
যোগাযোগ বৈকল্য
ব্যক্তির কোনো চিন্তা কিংবা বাচনিক, অবাচনিক ও গ্রাফিক প্রতীক ব্যবস্থার বার্তা গ্রহণ, প্রেরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও উপলব্ধি করতে না পারাই হলো যোগাযোগ বৈকল্য।১ মোটাদাগে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যেসব যোগাযোগ বৈকল্য দেখা যায় তা হলো: ভাষিক বৈকল্য, বাচিক-শব্দ বৈকল্য, শ্রবণ বৈকল্য, উপলব্ধি বৈকল্য, শ্রবণেন্দ্রিয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সমস্যা, সিজোফ্রেনিয়া রোগ, কগনিটিভ যোগাযোগ বৈকল্য, শৈশবে তোতলানো বৈকল্য ও সামাজিক যোগাযোগ বৈকল্য ইত্যাদি। কোনো সরল শব্দের পুনরাবৃত্তি করা, শব্দের অর্থময়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারা, শব্দের পারস্পরিক বিন্যাসে বাক্য গঠন করে যোগাযোগ করতে না পারাও যোগাযোগ বৈকল্যের অন্তর্ভুক্ত।২ কাজেই যোগাযোগ বৈকল্য বলতে ব্যক্তির মধ্যে যেকোনো ধরনের বৈকল্যকে বুঝায় যা তার জাগতিক বাস্তবতা উপলব্ধিবোধ, চৈতন্যবোধ, চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা, অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নে ভাষার প্রয়োগ ও অন্যান্য বাচিক প্রকাশ ক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। যোগাযোগ বৈকল্যের বিষয়টি দৃশ্যমান হয় ব্যক্তির শ্রবণ, ভাষার প্রয়োগ কিংবা বাচিক যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে। যোগাযোগ বৈকল্য অতি স্বল্পমাত্রা থেকে অত্যন্ত জটিল মাত্রার হতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ বৈকল্য নতুন করে সৃষ্টি কিংবা পারিবারিক বংশ পরম্পরায় এই বৈকল্য সঞ্চারিত হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ বৈকল্য দেখা দিতে পারে। আর সেসব কারণের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া, স্নায়ু ইন্দ্রিয় বৈকল্য ও মস্তিষ্কে প্রদাহ।
সামগ্রিকভাবে মানুষের যোগাযোগ বৈকল্যকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা যায়। সেই বর্গগুলো হলো—অ্যাফাসিয়া (Aphasia), ডিসারথিয়া (Dysarthria), অ্যাপ্রাক্সিয়া (Apraxia), ডিসনোমিয়া (Dysnomia), ডিস্লেক্সিয়া (Dyslexia), ডিসক্যালকুলিয়া (Dyscalculia), পিউবারফোনিয়া (Puberphonia), স্পাসমোডিক ডিসফোনিয়া (Spasmodic Dysphonia), ডিসপ্রোসেডি (Dysprosodz), ডিমেনসিয়া (Dementia), ডিসফ্যাগিয়া (Dysphagia) আর্টিকুলেশন ডিজঅর্ডার বা যোগাযোগে ধীরগতি।৩ অ্যাফাসিয়া হলো মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে ব্যক্তির ভাষিক যোগাযোগ দক্ষতা হারিয়ে যাওয়া। এর ফলে ব্যক্তি কোনো ভাষা উপলব্ধি কিংবা প্রয়োগ করতে পারে না।৪ আর অ্যাপ্রাক্সিয়া মূলত মস্তিষ্কের নিউরনজনিত সমস্যা। এই সমস্যার ফলে ব্যক্তির বাচিক যোগাযোগ খুবই অবিন্যস্ত হয়। জটিল শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারে না এবং মনের ভাব প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ বেছে নিতে সমস্যা বোধ করে।
ডিসারথিয়া হলো ব্যক্তির কণ্ঠস্বরজনিত যোগাযোগ বৈকল্য। মূলত মস্তিষ্কে নিউরনজনিত সমস্যার—যেমন পারসকিনসন রোগ—কারণে ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ বৈকল্য দেখা দেয়। ডিসারথিয়ার ফলে কোনো কোনো ব্যক্তি খুব ধীরে, থেমে থেমে, কষ্ট করে কথা বলে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তি খুব দ্রুত গতিতে কথা বলে। ডিসারথিয়ায় আক্রান্ত হলে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে গেলে ব্যাহত হয়। ডিস্লেক্সিয়া মূলত ব্যক্তির পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর ফলে ব্যক্তি কোনো বর্ণের সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না। বিভিন্ন বর্ণের সঠিক সন্নিবেশে অর্থপূর্ণ শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না। এ ধরনের যোগাযোগ বৈকল্য ব্যক্তির জন্মগত হতে পারে আবার স্ট্রোক কিংবা মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত কারণেও হতে পারে।
যোগাযোগ বৈকল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধরনটি হলো ডিমেনসিয়া। মূলত আলঝেইমার্স রোগের কারণে ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের বৈকল্য দেখা যায়। এর ফলে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও ব্যক্তিত্বজনিত সমস্যা হয়। আর ডিসফ্যাগিয়া সেই অর্থে কোনো যোগাযোগ বৈকল্য নয়। এটি অন্যান্য যোগাযোগ বৈকল্যের সমষ্টি। এর ফলে ব্যক্তির ঢোক গিলতে সমস্যা হয়। গলায় কিংবা শ্বাসনালিতে কোনো কিছু আটকে যাওয়া ভাব হয়। ব্যক্তি কোনো কিছু খেতে পারে না। ফলে ব্যক্তির অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়।
ব্যক্তির বাচিক যোগাযোগ বৈকল্য৫ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন : আর্টিকুলেশন ডিজঅর্ডার, ফ্লুয়েন্সি ডিজঅর্ডার, ভয়েস ডিজঅর্ডার। আর্টিকুলেশন ডিজঅর্ডার মূলত ব্যক্তির বাচিক শব্দ উৎপাদন করতে পারা বা না পারার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ধরনের যোগাযোগ বৈকল্য থাকলে ব্যক্তি কোনো একটি শব্দের বদলে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারে না; কথা বলা বা লেখার সময় কোনো কোনো শব্দ বাদ পড়ে যায় কিংবা শব্দের বিকৃতি ঘটে। অন্যদিকে আর্টিকুলেশন ডিজঅর্ডারের কারণে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ ও শব্দবন্ধের উচ্চারণের গতি ও ছন্দ সুষম হয় না এবং পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফলে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও আচরণে সমস্যা দেখা দেয়। আর ভয়েস ডিজঅর্ডারের ফলে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ওঠানামা অস্বাভাবিক হয়; ব্যাহত হয় স্বাভাবিক যোগাযোগ।
ভাষিক বৈকল্যের৬ ফলে ব্যক্তি কোনো ভাষা পড়া, লেখা কিংবা অন্যান্য প্রতীক ব্যবস্থা উপলব্ধি করতে পারে না। ভাষার ব্যবহারে নিজস্ব চিন্তা, যুক্তি ও আবেগের সঠিক প্রকাশ করতে পারে না। এমনকি অনেক সময় মাতৃভাষাও বুঝতে ও কথা বলতে পারে না। মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যক্তির ভাষিক বৈকল্য দেখা যায়। এর ফলে সে ভাষা ব্যবহারে যোগাযোগ করতে পারে না।
অন্যদিকে কগনিটিভ বৈকল্যর৭ ফলে ব্যক্তির মস্তিষ্কের উপলব্ধিবোধ, চিন্তাশক্তি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা ব্যাহত হয়। এ ধরনের বৈকল্যের ফলে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা হলো—মনোযোগে ঘাটতি, স্মৃতিশক্তি লোপ; অনুধাবন ক্ষমতা ব্যাহত হওয়া; অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবোধ কমে যাওয়া; কোনো কিছুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশে সক্ষম না হওয়া; তথ্য প্রক্রিয়া করতে না পারা; যৌক্তিক চিন্তা করতে না পারা। যেসব ব্যক্তি কগনিটিভ যোগাযোগ বৈকল্যে ভুগছেন তারা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে মনোযোগ দিতে পারে না; তাদের চিন্তা-কথা-বিশ্বাস-বোধ একটি বিষয়েই নিবন্ধিত থাকে; কোনো তথ্য স্মরণ করতে পারে না; কোনো কিছুর প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে না; কোনো কোনো কৌতুক বা রসালাপ ও উপমার অর্থময়তা উপলব্ধি করতে পারে না কিংবা অনুসরণ করতে পারে না কোনো অনুরোধ আদেশ কিংবা দিকনির্দেশনা। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে কগনিটিভ বৈকল্য থাকলে শিক্ষা অর্জন, শিক্ষাদান ও গবেষণা সক্ষমতাও লোপ পায়। যেকোনো সময় আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কেননা তারা যেকোনো জরুরি মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারে না। নিজের কোনো কর্মের পরিণতি সম্পর্কেও অনুমান করতে পারে না।
যোগাযোগ বৈকল্য আছে এমন ব্যক্তি কারো সঙ্গে যোগাযোগে লিপ্ত হতে পারে না। যোগাযোগে নিজের দুর্বলতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না; স্মৃতিশক্তি, বিবেচনাবোধ, কার্যকরভাবে তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা হ্রাস পায়। দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না; কোনো কথা, কাজ বা বিষয়ের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অনুমান করতে পারে না। সেই পরিণতি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে বিচারবোধকে কাজে লাগাতে পারে না। কোনো সমস্যা সম্ভাব্য সমাধান বাতলাতে পারে না; যোগাযোগ দক্ষতা হ্রাস পায়; একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তারা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সামাজিক সম্পর্কের জগৎ থেকেও। তারা স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ বাহ্যিক জাগতিক উদ্দীপকের প্রতি তারা সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে না; চোখ সবসময় খোলা থাকলেও কোনো কিছুই ঠিকমতো দেখে না, অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না, কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারে না। কোনো কথা-বিষয়-ব্যক্তির প্রতি সঠিকভাবে মনোযোগ দিতে পারে না আদৌ। বলতে পারে না নিজের, স্ত্রী-স্বামী কিংবা তার সেবাকারীর নাম, ১০ পর্যন্তও গুণতে পারে না; নিজের কোনো চাহিদা পূরণ না হলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এদের যেকোনো সময় আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কেননা এরা যেকোনো জরুরি মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারে না। নিজের কোনো কর্মের পরিণতি সম্পর্কেও অনুমান করতে পারে না। ফলে তাদের সামাজিক যোগাযোগ একেবারেই সীমিত হয়ে পড়ে। নিজের মৌলিক চাহিদার কথাও ঠিকভাবে বলতে পারে না। তাদের যোগাযোগ সীমিত থাকে হ্যাঁ-না কিংবা কেবল মাথা ঝোঁকানোতে। পারস্পরিক যোগাযোগে তারা চোখ দিয়ে সংযোগ করে খুবই সীমিত মাত্রায় এবং শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণ জানাতে পারে না।
সিজোফ্রেনিয়া ও যোগাযোগ বৈকল্য
সিজোফ্রেনিয়া একধরনের জটিল ও মারাত্মক রোগ। এটি যোগাযোগ বৈকল্যের৮ অন্যতম কারণ। এই রোগে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির মধ্যে হ্যালুসিনেশন, ডিল্যুশন, ভাষিক দক্ষতায় অস্বাভাবিকতা এবং সামাজিক দক্ষতায় দুর্বলতা, চিন্তা, কথা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও উপলব্ধিবোধ ব্যাহত হয়; ভাষার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থময়তা সঞ্চারণ করতে পারে না। আবার আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে অর্থময়তা গ্রহণও করতে পারে না। ফলে সে অন্যের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগে লিপ্ত হতে পারে না। কাজেই এই রোগে আক্রান্ত হলে সমাজে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।
এটিও একধরনের মানসিক বৈকল্য। এর লক্ষণগুলো হলো—গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে না পারা, হ্যালুসিনেশনে থাকা, সঠিকভাবে অনুভূতির প্রকাশ করতে না পারা, অস্বাভাবিক চলাফেরা ও আচরণের প্রকাশ, অবিন্যস্ত চিন্তা, চিন্তার প্রকাশ খুব ধীর বা দ্রুত গতির কিংবা বিভ্রান্তিমূলক, কোনো কিছু বুঝতে না পারা, কোনো কিছুতে মনোযোগের ঘাটতি, দুর্বল স্মৃতিশক্তি, চিন্তা ও অনুভূতির সঠিক প্রকাশ করতে না পারা।
মোটাদাগে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক লক্ষণগুলো হলো ব্যক্তি স্বাভাবিক, কগনিটিভ ও আবেগীয় সাড়া প্রদানে সক্ষম হয় না। সামগ্রিকভাবে তার আবেগের প্রকাশ কমে যায়। একই সুরে কথা বলতে থাকে, কোনো একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, মুখভঙ্গির মাধ্যমে আদৌ যোগাযোগ ব্যবহার করতে পারে না এবং দুনিয়ার সবকিছুতে একধরনের উদাস ভাব দেখা যায়; সামাজিক যোগাযোগে অনাগ্রহ দেখা দেয়, কোনো কিছুতেই উৎসাহবোধ করে না, হারিয়ে যায় আনন্দবোধ। আর ইতিবাচক লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—ব্যক্তির মধ্যে একধরনের ভীতিবোধ কাজ করে, পঞ্চইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটি ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন কাজ করে, চিন্তন প্রণালি ও প্রকাশ খুবই অগোছালো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইতিবাচক লক্ষণগুলো ব্যক্তির মধ্যে শাব্দিক হ্যালুসিনেশন ও বিশৃঙ্খল চিন্তন।
সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিন্তন প্রণালি হয় খুবই বিশৃঙ্খল; মন অত্যন্ত ভঙ্গুর। তারা এক ভিন্ন জগতে বাস করে।৯ তাদের বাচিক প্রকাশ ও আচরণ খুবই অগোছালো। তারা মানবীয় সত্ত্বা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।১০ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সামাজিক দুনিয়া থেকেও।১১ তাদের কথাবার্তা, কণ্ঠস্বর, বিশ্বাসবোধ হয় অদ্ভুত কিসিমের; যা এই রোগে আক্রান্ত নয় এমন ব্যক্তির নিকট বোধগম্য হয় না।
অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড-এর গল্প
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। এক শীতের সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হন শিক্ষার্থী জন ন্যাশ। গণিতে বৃত্তি পেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তিনি সবসময় আনমনে নিজের মতো কী যেনো বলতে থাকে। মাথা ঝাঁকান ও মুখ বিড়বিড় করেন; আঙুলে কী যেনো গণনা করেন।
ক্যাম্পাসে ন্যাশের পরিচয় হয় মার্টিন হ্যানসেন, রিচার্ড সোল, এইনসেল, বেন্ডারসহ আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি রুমমেট হিসেবে পান সাহিত্যের শিক্ষার্থী চার্লস হারম্যান’কে। হারম্যান তার ভালো বন্ধু হয়। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে ন্যাশের তেমন সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তার সহপাঠীরা তাকে নিয়ে তামাশা ও কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হারম্যানকে ন্যাশ বলেন, তিনি মানুষের চেয়ে সংখ্যার সঙ্গে বেশি আরাম বোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে ন্যাশ মানুষের চেয়ে সংখ্যাকে বেশি ভালো বুঝতে পারেন। এ কারণেই পানশালায় কোনো এক নারীকে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত না হয়ে ন্যাশ গাণিতিক অর্থনীতির থিওরি গভর্নিং ইকোনোমিকসের ধারণা লাভের চেষ্টা করেন।
ব্যক্তি হিসেবে ন্যাশ খানিকটা অন্তর্মুখী স্বভাবের। তবে মৌলিক চিন্তার প্রশ্নে খুব অনড়। সবসময়ই অন্যমনস্ক। ক্লাসে তিনি সবসময় অমনোযোগী। হাজিরও থাকে না বেশিরভাগ সময়। কিন্তু তাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কমতি নেই। কারণ সবার মুখে তার মেধার খুব প্রশংসা। ন্যাশের ক্লাসের সবাই যখন গবেষণাপত্র প্রকাশনার জন্য আইডিয়া জমা দেয়, তখন ন্যাশ নিজ কক্ষে বসে ভেবেই চলেছেন। গবেষণা-আইডিয়া জমা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে আসে। কিন্তু সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সমস্ত চিন্তাজগৎ জুড়ে নিজের মতো নতুন সূত্র হাজিরের চেষ্টা তার।
চলাফেরা কাথাবার্তা সবকিছুতেই গাণিতিক সংজ্ঞা খোঁজেন ন্যাশ। এ নিয়ে সহপাঠীরা তাকে পাগল ভাবে। অবশ্য এ নিয়ে ভাবারও সময় নেই তার। বেশির ভাগ সময় একা থাকেন তিনি। একা থাকতে থাকতে তার জীবনে আগমন ঘটে কল্পনার কিছু মানুষের। প্রথমত, চার্লস হারম্যান। হারম্যান তার বোনের মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দেন ন্যাশের সঙ্গে। কারো সঙ্গে কথা না বললেও নিজের রুমমেট হারম্যানের সঙ্গে অনেক কথা বলেন তিনি। ঝগড়া করেন। সূত্র নিয়ে আলাপ করেন। অন্যদিকে, ন্যাশ কথা বলতে না চাইলেও হারম্যান যেচে এসে ন্যাশকে জালাতন করেন।
ন্যাশকে দেখা যায়, কবুতরের চরে বেড়ানোকে একটা অ্যালগোরিদমের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করতে; লাইব্রেরির জানালার সামনে বসে জানালার কাচকে বোর্ড বানিয়ে সমীকরণ তৈরি করতে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের আড্ডায় মেয়ে পটাতে গিয়ে ন্যাশ পেয়ে যান গেম থিউরি।
এম আই টি-তে ক্লাস নেওয়ার সময় অ্যালিসিয়া লার্দে নামের এক শিক্ষার্থীর প্রেমে পড়েন ন্যাশ। অ্যালিসিয়াকে বিয়েও করেন তিনি। কিন্তু তিনি নিজেকে ঘিরে এক কল্পজগৎ তৈরি করেন। সরকারি গোপন সব সমস্যা সমাধান করতে থাকেন তিনি; যদিও এর পুরোটাই তার কল্পনা। এই কল্পজগতেই ন্যাশ সোভিয়েতদের টেলিকমিউনিকেশনের কোড ভাঙার কাজ পান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে পার্কার নামের এক সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কিন্তু ন্যাশ বুঝতে পারেন, বড়ো ধরনের বিপদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যাচ্ছেন। পার্কারের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়ার সময় সোভিয়েত গোয়েন্দারা গুলি ছোড়ে তাদের দিকে। এর পরই মৃত্যু ভয় গ্রাস করে ন্যাশকে। সবসময়ই মনে হতে থাকে, কেউ তার পিছু নিয়েছে। সোভিয়েতরা তাকে বাঁচতে দেবে না।
প্রথমে বুঝতে না পারলেও, অ্যালিসিয়া একসময় ন্যাশের অস্বাভাবিক আচরণের বিষয়টি টের পান। তাকে নিয়ে যান চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক বলেন, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন ন্যাশ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুরু হয় চিকিৎসা। এবার সিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে ন্যাশের যুদ্ধ শুরু হয়। নিজের মনের ভিতরে তৈরি চরিত্রগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসকের দেওয়া উচ্চমাত্রার ওষুধ নেওয়া তিনি বন্ধ করে দেন। ফলে তিনি আবারও বন্দি হয়ে পড়েন নিজের কল্পনায় তৈরি চরিত্রগুলো কাছে। রুমমেট হারম্যান, সেনা কর্মকর্তা পার্কার সবাই আসলে ন্যাশের কল্পনায় তৈরি চরিত্র। ন্যাশ এ থেকে মুক্তি চান। ফিরে যেতে চান নিজের স্বাভাবিক জীবনে। তিনি গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান। ন্যাশের পাশে থাকেন স্ত্রী অ্যালিসিয়া। বন্ধু মার্টিন হ্যানসনের সহযোগিতায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে পড়ানো এবং গবেষণার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু তার ডিল্যুশন চলতে থাকে। তবে স্ত্রী ও বন্ধুদের সহযোগিতায় ন্যাশ আবারও ফিরে আসেন জীবনের কাছে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান।
ন্যাশ চরিত্রে যোগাযোগ বৈকল্যের রূপায়ণ
অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড-এ জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর প্রেক্ষাপটটি যথাযথ, সহজসরল ও মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রূপায়ণ করা হয়েছে হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তির জাগতিক অনুধাবন এবং বাস্তবতার ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কের জায়গাটিকে। এখানে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ন্যাশের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ন্যাশ চরিত্রটিতে সিজোফ্রেনিয়া রোগের অনেক লক্ষণ যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। সেই লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—হ্যালুসিনেশন, বিভ্রম, নিপীড়িত হওয়ার ভীতি এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতায় ঘাটতি।
জন ন্যাশের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ হয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। শুরুতে তিনি ছিলেন হ্যালুসিনেশনে। পরে তা ডিলুসিনেশনে পরিণত হয়। ক্রমেই লক্ষণগুলো প্রকট আকার ধারণ করে। এই চলচ্চিত্রে সিজোফ্রেনিয়ার শুরু, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া ও এর লক্ষণ, এই রোগের চিকিৎসা এবং ব্যক্তি জীবনের এই রোগের প্রভাব দারুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
ন্যাশ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। এই রোগের প্রকাশ ঘটে শ্রবণ ও দর্শন বিভ্রমের মাধ্যমে। এছাড়াও ন্যাশ স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারেন না, আবেগ অনুভূতির গঠন ও প্রকাশ সঠিকভাবে করতে পারেন না, কোনো সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নিতে পারেন না, বাস্তবে অস্তিত্ব নাই এমন ব্যক্তি বা বস্তু দেখতে পান; তার চারপাশে একটি কল্পিত জগৎ তৈরি করেন; বিভিন্ন শব্দ শুনতে পান, বাস্তবতা ও বিভ্রমের মধ্যে তফাৎ করতে পারেন না, হ্যালুসিনেশন হয়।
এই রোগটি আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন ন্যাশ তার অবস্থান নিয়ে প্রকটভাবে দুশ্চিন্তা করেন। ন্যাশের এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কারণে তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং বন্ধুদের ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তিনি কার্যকর যোগাযোগে সক্ষম না হওয়ায় বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে জটিল সমস্যায় পড়েন। এমনকি ন্যাশ তার সন্তানের জীবননাশের কারণও হয়ে ওঠেন। কেননা তিনি বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে তফাৎ করতে পারেন না।
অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড-এর সংলাপগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে নয় ধরনের উপলব্ধি বৈকল্যের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো—চিন্তার ক্রমবিন্যাস ও প্রকাশে লাইনচ্যুতি (derailment), খুব দ্রুত চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন (flight of ideas), শব্দ-বাক্য-ভাবনা-চিন্তাগুলোকে একে অন্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা (word salad), চিন্তাভাবনার প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া (blocking) অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দেওয়া (irrelevant answer), বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও প্রকাশ ব্যাহত হওয়া (retardation), এই কথা-চিন্তা-কাজের বারবার পুনরাবৃত্তি (perseveration), বাচিক বার্তার ওপর চাপ প্রয়োগ এবং কথা বলার সময় মূল বিষয়টি বলার ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করা (circumstantiality)।
উপসংহার
এই চলচ্চিত্রটি নোবেল বিজয়ী গণিতবিদ জন ন্যাশের জীবনের একটি দুর্দান্ত রূপায়ণ। জন ন্যাশ দৃশ্যগত, শ্রবণগত ও উপলব্ধিগত যোগাযোগ বৈকল্যে ভোগেন। এই চরিত্রের মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়া রোগের বিভিন্ন লক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। এসব লক্ষণের প্রধানতম লক্ষণটি হলো যোগাযোগ অক্ষমতা। যোগাযোগ বৈকল্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রশ্নে অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড দারুণ নজির হাজির করে। এই চলচ্চিত্রে ব্যক্তির মনোজগতে পীড়ন ও মানসিক অসুস্থতা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এটি জন ন্যাশের জীবনকে পুরোপুরি তুলে ধরে না। তবে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ মঞ্চে জন ন্যাশ তার স্ত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা কথাগুলো যোগাযোগ বৈকল্য ও সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমস্যা মোকাবেলা ও তাদের মানবীয় জীবনযাপনের মূল সূত্রটি ঠিকই প্রতিফলিত করে। তার সেই কথার মর্মার্থ ছেঁকে নিলে যা দাঁড়ায় তা হলো—পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের কেবল ভালোবাসা ও সহমর্মী আচরণই পারে যোগাযোগ বৈকল্যের কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক মানবীয় জীবনে ফিরিয়ে আনতে। যার সত্য স্বীকারোক্তি দিয়েছেন জন ন্যাশ। কাজেই ন্যাশ তার স্ত্রীর উদ্দেশে যে কথাগুলো উৎসর্গ করেন তা দিয়েই এই আলোচনার সমাপ্তি টানা যাক—
আমি সবসময় গাণিতিক সংখ্যায় বিশ্বাস করেছি। আমি বিশ্বাস করেছি বিভিন্ন সমীকরণ ও যুক্তিতে। এসব সংখ্যা, সমীকরণ ও যুক্তির মাধ্যেমে আমি সত্যের সন্ধান করেছি। সত্যকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছি। সারাজীবন এই চেষ্টার পর আজ আমি নিজেকে একটি প্রশ্নই করি, আর সেই প্রশ্নটি হলো সত্যিকারের যুক্তি কী? কোন বিষয়টি আমাদের সত্যবোধ নির্ধারণ করে। আমার এই প্রচেষ্টা আমাকে নিয়ে গেছে ভিন্ন জগতে। সেই জগত স্পর্শ করেছে আমার শারীরিক, অধিদর্শনগত ও ভ্রমাত্মক বাস্তবতাকে। আমাকে বারবার ফিরে যেতে হয়েছে পিছনের দিকে। হ্যাঁ, আমি আমার কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কার করেছি আমার সারাজীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর সেই আবিষ্কারটি নিহিত আছে ভালোবাসার এক রহস্যময় সমীকরণে। এই সমীকরণে যেকোনো যৌক্তিক সত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমি আজ রাতে এইখানে আসতে পেরেছি শুধু তোমার জন্য। আমার সমস্ত অস্তিত্বের কারণ তুমি। তুমিই আমার সব যুক্তি। ধন্যবাদ।
লেখক : আমিনুল ইসলাম, রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে পড়ান। সম্প্রতি তার প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মানবীয় যোগাযোগ’।
mukul.ru@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. American Speech-Language-Hearing Association. (1993). Definitions of communication disorders and variations [Relevant Paper]. Available fromww w.asha.org/policy. Docherty, Nancy M; `Cognitive impairments and disordered speech in schi“ophrenia: thought disorder, disorgani“ation, and communication failure perspectives'; Journal of abnormal psychology; Volume 114, Issue 2, 2005, p.269-278.
২. cÖv¸³; Docherty (2005: 269-278).
৩. Sims, Jordzn [not dated]; `Common Communication Disorders Defined: What are all these terms and what do they mean for everyday life?' [Available at: https://constanttherapy.com/blog/common-communication-disorders-defined-what-are-all-these-terms-and-what-do-they-mean-for-everyday-life/ ; retrieved on 13.12. 2016]
৪. Blom Johansson, M., M. Carlsson, and K. Sonnander; `Communication difficulties and use of communication strategies: from the perspective of individuals with aphasia'; International Journal of Language & Communication Disorders; Volume 47, Issue 2, 2012, p. 144-155.
৫. Titone, Debra; `Language, communication, & schi“ophrenia '; Journal of Neurolinguistics; Volume 23, Issue 3, 2010, p. 173-175.
৬. cÖv¸³; Titone (2010: 173-175).
৭. cÖv¸³; Docherty (2005: 269-278).
৮. Wible, Cynthia Gayle (2012: 1-12); `Schi“ophrenia as a Disorder of Social Communication'; Schi“ophrenia Research and Treatment; Volume 2012.
Niznikiewicy, M. A., M. Kubicki, C. Mulert and R. Condray (2013: 4); `Schi“ophrenia as a Disorder of Communication'; Schi“ophrenia Research and Treatment, Volume 2013. [ http://dx.doi.org/10.1155/2013/952034]
৯. cÖv¸³; Niznikiewicy, et. al (2013: 4).
১০. Henriksen, M. G., J. Nordgaard; `Schi“ophrenia as a disorder of the self'; Journal of Psychopathology; Volume 20, Issue 4, 2014, p. 435-441.
১১. cÖv¸³; Wible (2012: 1-12).
mnvqK cvV
Allen, R. (2001); Cognitive Film Theory, Wittgenstein, Theory and the Arts , Issue November. [DOI:10.1111/b.9780631206453.2003.00008.x]
Bandura, A.; Social cognitive theory : An agentic Albert Bandura, Asian Journal of Social Psychology, Volume 2, Issue 1, 1999.
Creed, B.; `Film and psychoanalysis' ; Film Studies: Critical Approaches, 2000. [DOI: 10.1080/01062301.1982.10592418]
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন