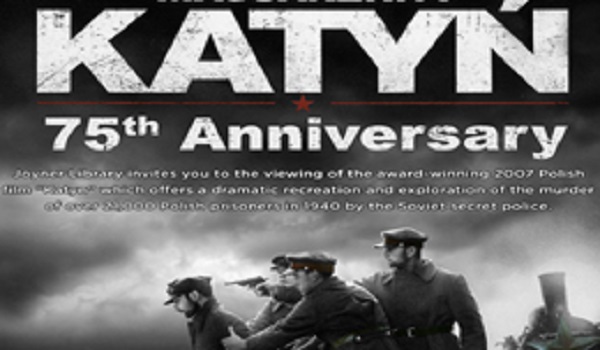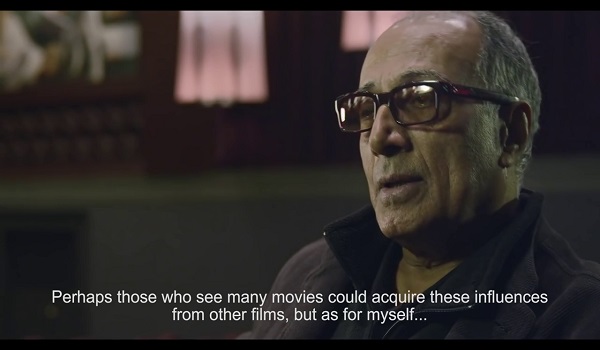কাওসার বকুল
প্রকাশিত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
ক্লোজ আপ-এ আব্বাসের অনন্যতা
কাওসার বকুল

সত্য, বাস্তবের মিশেল
হলিউডের চলচ্চিত্র যেমন বলিউডের মতো নয়, কোরিয়ান চলচ্চিত্রও ঠিক ইরানের চেয়ে আলাদা। একইভাবে সত্যজিৎ রায়, কিম কি দুক, আব্বাস কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র দেখেও নির্মাতাকে চেনা সম্ভব। এদের প্রত্যেকের চলচ্চিত্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে স্বকীয়তার জন্য সত্যজিৎ, কিম কিংবা আব্বাসের চলচ্চিত্র আর সবার মতো নয়। স্বকীয়তা থাকলে যে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, তার বড়ো প্রমাণ গুণী এই নির্মাতারা। ইরানের মতো প্রান্তিক একটা দেশের নির্মাতা হয়েও বিশ্ব দরবারে আব্বাসের নাম উচ্চারিত হচ্ছে, এর কারণ সম্ভবত তার চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা, শৈলী। আব্বাসের চলচ্চিত্রের কাহিনি সহজসরল গতিতে এগোলেও, একই সঙ্গে সেটা জটিলও। সেই জটিলতা থেকে রেহাই পেতে দর্শককে অপেক্ষা করতে হয় চলচ্চিত্রের শেষাবধি। দর্শক তখন চলচ্চিত্রের শুরুতে দেখা চরিত্রকে নতুনভাবে উপলব্ধি করে।
ক্লোজ আপ-এর কথাই ধরি। আব্বাস সেখানে গল্প বলেছেন সত্য, বাস্তব দুইয়ের মিশেলে। অর্থাৎ ঘটনার কিছু অংশ সরাসরি ধারণ করে, বাকিটা আগে যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেই ভাবেই আসল চরিত্রদের দিয়ে পুনর্নির্মাণ করে। সে কারণে ক্লোজ আপকে বলা যেতে পারে ‘প্রামাণ্য কাহিনিচিত্র’। এখানে সত্য বলতে বুঝানো হচ্ছে—প্রকৃত ঘটনার যে দৃশ্যগুলো সরাসরি ধারণ করা হয়েছে সেগুলোকে। আর যেসব ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, হুবহু তা ক্যামেরায় ধারণ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সত্যের আদলে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে—সে অংশকে বলছি বাস্তব। চলচ্চিত্রটিতে বাস্তব এবং সত্য এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে—গভীর মনোযোগ এবং আসল তথ্য জানা না থাকলে দর্শকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তারা এখন ঠিক কী দেখছেন।
ক্লোজ আপ-এর কাহিনি ছাপাখানার শ্রমিক হোসেন সাবজিয়ানকে ঘিরে। ছাপাখানার চাকরি চলে গেলে স্ত্রীও তাকে অকর্মণ্য ভেবে ছেড়ে যায়। এরপর চলচ্চিত্র-পাগল সাবজিয়ান ভবঘুরে জীবন যাপন করতে থাকেন। ইরানের বিখ্যাত নির্মাতা মহসিন মাখমালবাফের চলচ্চিত্রের ভক্ত তিনি। একদিন বাসে বসে দ্য সাইক্লিস্ট-এর চিত্রনাট্য পড়ার সময় পাশের আসনে বসা মিসেস আহনখের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মিসেস আহনখও নির্মাতা মাখমালবাফের দারুণ ভক্ত জেনে অগত্যা নিজেকেই মাখমালবাফ পরিচয় দেন সাবজিয়ান। এরপর মিসেস আহনখের বাড়িতে সাবজিয়ানের যাতায়াত শুরু হয়। এরই একপর্যায়ে মিসেস আহনখের ছেলেকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাদের বাড়িতেই শুটিংয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন সাবজিয়ান। কিন্তু বিপত্তি বাধে একটি ম্যাগাজিনে মাখমালবাফের ছবি প্রকাশের পর; মি. আহনখের সন্দেহ হয় সাবজিয়ানকে নিয়ে। পরে এক সাংবাদিক বন্ধুর সহায়তায় সাবজিয়ানের প্রতারণা ধরে ফেলেন তিনি। সাবজিয়ানকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে বিচারকার্য চলে। সাবজিয়ানের সরল স্বীকারোক্তিতে পরিবারটি বুঝতে পারে, তিনি নির্দোষ। পরিবার থেকে তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ তুলে নিলে সাবজিয়ান ছাড়া পান।
ভাঙাগড়ার খেলা
আব্বাস চলচ্চিত্রের ব্যাকরণটাই ভেঙে ফেলেছেন। ক্লোজ আপ-এ তিনি কাহিনিচিত্র আর প্রামাণ্যচিত্রের সীমানা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। ফিকশন আর নন-ফিকশনকে একসঙ্গে হাজির করেন পর্দায়। পুলিশের কাছে সাবজিয়ানের আটকের খবর নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে (৪৬ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড) তার বিচারকার্য পর্যন্ত চলচ্চিত্রে প্রামাণ্য তুলে ধরেন। আর এর আগের যে ঘটনাগুলো সরাসরি ক্যামেরায় ধারণ করা সম্ভব হয়নি; সেগুলো ঠিক রেখেই সাবজিয়ানকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেন নির্মাতা। এক্ষেত্রেও চিত্রায়ণ করা হয়েছে বাস্তবের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঠিক রেখে। এমনকি মহসিন মাখমালবাফের চরিত্রে নির্মাতা মাখমালবাফকে যেমন ঠিক রেখেছেন; একই সঙ্গে সাবজিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দৃশ্যে মাখমালবাফ ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে চলে গেলে নির্মাতা আব্বাস ও তার সঙ্গীর কথাবার্তাও (এক ঘণ্টা ২৩ মিনিট ২৯ সেকেন্ড) ক্লোজ আপ-এ উঠে এসেছে। কাহিনিচিত্র আর প্রামাণ্যচিত্রের সীমানা ভেঙেও যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়, আব্বাস সেটা করে দেখান। সাবজিয়ানের সত্য, বাস্তবতা, কল্পনা ও শিল্প সবকিছু মিলিয়ে নির্মিত ক্লোজ আপ-এ নতুন আঙ্গিকে হাজির হন আব্বাস।
ক্লোজ আপ-এ সেই অর্থে কোনো ন্যারেটিভ নেই। যে কারণে অনেক দর্শকের কাছেই চলচ্চিত্রটি একটু জটিল মনে হতে পারে। যদিও এই জটিলতার বিষয়টিকে আব্বাস নেতিবাচক হিসেবে দেখতে নারাজ। চলচ্চিত্রের বিষয় জটিল হলেই যে তা মন্দ হবে বিষয়টা তেমন নয়। বরং এক্ষেত্রে বিষয়টাকে তিনি জটিল কোনো কবিতার সঙ্গে তুলনা করার পক্ষপাতী।১ কারণ জটিল ওই কবিতার ভাষা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও কেউ সেটাকে মন্দ বলে না। দুর্বোধ্যতার এই বিষয়টাকে মজা করে আব্বাস অবশ্য ভিন্নভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন—‘আমার ছবি দেখতে দেখতে কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়ে কিছু মনে করব না। কারণ, আমি জানি খুব ভালো ছবিগুলো আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করতে পারে। এটাকে খারাপভাবে নেওয়ার কিছু নেই।’২ কিন্তু একজন নির্মাতার তো সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে দর্শকের কাছে যাওয়ার; আর, পছন্দমাফিক উপাদানের সন্ধান পেলে দর্শকও সেটা সাদরে গ্রহণ করে। কোনো চলচ্চিত্র যদি দর্শকের কাছে ঠিকঠাক না পৌঁছায়, তাহলে তো নির্মাতার উদ্দেশ্য সফল হয় না।
আব্বাস অবশ্য চান না তার চলচ্চিত্র দর্শক একাধিকবার দেখুক; তাতে নাকি নিজেকে তার অনেক স্বার্থপর মনে হয়। কারণ, জটিল কোনো কবিতা বোঝার খাতিরে পাঠক তা বারবার পড়লেও, নিজের চলচ্চিত্রের ভাষাগত কিংবা আধেয়ের জটিলতায় দর্শকের মূল্যবান সময় নষ্ট করার বিপক্ষে আব্বাসের অবস্থান। তবে তিনি এও মনে করেন,
অনেক দর্শক অতৃপ্তি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হয়ে আসতে পারে কিন্তু তার পরেও তাদের পক্ষে ছবিটা ভুলা সম্ভব নয়। আমি জানি তাদের খাবার টেবিলে তারা ওটা নিয়ে কথা বলবে। আমি আমার ছবির দ্বারা তাদের একটু অস্থির করে দিই; যাতে তারা নিজেদের মধ্যে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে। এইদিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা আমার ছবি একবারের বেশি দেখবে।৩
আসলে সব চলচ্চিত্র তো নিখাদ বিনোদনের জন্য নয়; কিছু দর্শককে প্রভাবিতও করে। তাছাড়া চলচ্চিত্রের যে ক্ষমতা—নানাধরনের চলচ্চিত্র ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা; ক্লোজ আপ-এ আব্বাস সেটা করেননি। শুরুর দৃশ্যে তিনি সাংবাদিক ফারাজমান্দের গাড়িতে ওঠা থেকে মি. আহনখের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার দৃশ্য পাক্কা ছয় মিনিট ৩০ সেকেন্ড ধরে দেখিয়েছেন। ফলে বাড়ি খুঁজে পেতে ফারাজমান্দকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে দর্শক তা চাক্ষুস করেছে। আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে ক্লোজ আপ-এ। তবে আব্বাসের বিরুদ্ধে বরাবরের অভিযোগ, তার চলচ্চিত্রে ঘটনার একটা সুষ্ঠু সমাপ্তি না দেখানো। তিনি ৯৮ মিনিটে থামিয়ে দিয়েছেন ক্লোজ আপকে; টেস্ট অব চেরিতেও তিনি গল্পটা শেষ করেননি। এ সম্পর্কে আব্বাসের বক্তব্য, ‘আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি দর্শকরা অনেক বেশী বুদ্ধিমান এবং নিশ্চয় এটাকে সুন্দর কিছু মনে করে না যে আমি দু’ঘণ্টা ধরে তাদের আমার গল্প বলে মুগ্ধ করে রাখি। আমি যেভাবে চাই সেটা সে ভাবে শেষ করে দিব, আমি এটা চাই না।’৪ তার মানে কি আব্বাস গল্প শেষ করেন না! অবশ্যই তার প্রত্যেকটা চলচ্চিত্রের গল্পই শেষ হয়। তার পরও আব্বাস দর্শককে তাদের কল্পনা মতো ভাবার সুযোগ দেন। এটাই হয়তো তার অনন্যতা।
ক্লোজ শটে দেখা জীবন
ক্লোজ আপ শেষাবধি না দেখলে যেকোনো দর্শক বিভ্রান্ত হতে পারে সাবজিয়ানকে নিয়ে। বেশিরভাগ দর্শকের মনে হতে পারে, সাবজিয়ান অপরাধী। কিন্তু কেনো সাবজিয়ান মিথ্যার আশ্রয় নেন, তা জানা যায় ঘটনার শেষ পর্যায়ে; নির্মাতা যে তথ্য বের করে এনেছেন সাবজিয়ানের জীবনের একেবারে কাছে গিয়ে। তিনি উন্মোচন করেছেন বাস্তবের ভিতরকার সত্যটাকে। চলচ্চিত্রের দৃশ্য ধারণেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্লোজ শট্ নেওয়া হয়েছে এবং সাবজিয়ানের বিচারের সময় ব্যবহার করা হয়েছে জুম লেন্স। ক্লোজ শটে যেহেতু খুব কাছ থেকে দৃশ্যবস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা যায়; সে কারণে ঘটনার গভীরে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে আব্বাস হয়তো এই শট্ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপারও রয়েছে, ক্লোজ শটের মাধ্যমে চরিত্রটির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করাটাও দুষ্কর হয়। ইরানে ধারণ করা চলচ্চিত্রকে তাই হয়তো যেকোনো অবস্থানের দর্শকের চোখে অপর বলে মনে হয় না।
এছাড়া ক্লোজ আপ-এর শুরুতে চালকের সঙ্গে সাংবাদিক ফারাজমান্দের কথোপকথন থেকে সাবজিয়ানের বিচার পর্যন্ত বিভিন্ন দৃশ্যে যাদের কথা শোনা যায়, সেই ব্যক্তিদের বদলে পর্দায় দেখা যায় অন্যদের। এই কৌশলকে বলা হয়, ‘প্রেজেন্স উইদাউট প্রেজেন্স’। আবার বেশিরভাগ শটে তিনি ফ্রেমে কেবল একজনকে রেখেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো আব্বাস একবারের জন্যও কর্তাকে (এখানে কর্তা বলতে, যারা মূলত ওই সব দৃশ্যে কথা বলেছেন তাদের বোঝানো হয়েছে) পর্দায় হাজির করেননি। তাছাড়া চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যে অস্পষ্টতা তো রয়েছেই। সাবজিয়ানকে পুলিশ আটক করতে আসার দৃশ্য কিংবা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মাখমালবাফের সঙ্গে তার সাক্ষাতের সময়ও এই অস্পষ্টতা ছিলো। ওই সময়ে ফ্রেমে মূল বিষয়কে ধরতে গিয়ে ক্যামেরার সামনে বারবার গাছ বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। এতে করে পর্দাজুড়ে মূল বিষয়ের বদলে দীর্ঘসময় ধরে বিশালাকার গাছের উপস্থিতি চলমান গল্পে একটা বাধা তৈরি করে।
এই অস্পষ্টতাকেও আব্বাস ইতিবাচকভাবেই দেখেন। তার ভাষায়, ‘সিনেমা তৈরিতে আমার লক্ষ্যই হচ্ছে, আমরা যা দেখি কতটুকু না দেখিয়ে বা না বলে করা যায়। আমরা দর্শকের কল্পনাকে কত বেশি ব্যবহার করতে পারি। বাহ্যিকভাবে আমরা যা দেখি তার বাইরেও তুমি কল্পনা করতে পারো, কারণ তুমি কোন এক বাস্তবতার মাত্র একটি অংশ দেখ।’৫ আবার যে বাস্তবতার অংশ দেখা যায়, প্রশ্ন উঠতে পারে সেই বাস্তবতা নিয়েও। আব্বাস দর্শককে নিজের কল্পিত বাস্তবতা দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখার বিপক্ষে; বরং তিনি চান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা চিন্তা করার সুযোগ পাক—সে কারণে হয়তো ক্লোজ আপ-এ তিনি দর্শকের কল্পনাকে কোনো ফ্রেমে আটকে রাখেননি।
অবশ্য ভালোভাবে খেয়াল করলে এই অস্পষ্টতার উত্তরও মেলে ক্লোজ আপ-এ। বাইকে করে মাখমালবাফের আসার দৃশ্য আড়াল থেকে ক্যামেরায় ধারণ করছিলেন আব্বাস। ক্যামেরা প্যান করে দৃশ্য ধারণের একপর্যায়ে মাখমালবাফ ফ্রেমের বাইরে চলে যান। এ সময় তাকে খুঁজতে (এক ঘণ্টা ১১ মিনিট ২৩ সেকেন্ড) গিয়ে ক্যামেরার সামনে বিশালাকার গাছ বাধা হয়ে দাঁড়ালে ওভার দ্য সাউন্ডে আব্বাসকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা তাকে (মহসিন মাখমালবাফ) হারিয়ে ফেলেছি। তিনি ঠিক জায়গায় থামেননি। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আবার আমরা দৃশ্যটা পুনরায় ধারণ করতেও পারবো না।’ দৃশ্যটা তিনি পুনরায় ধারণ করতে পারেননি ঠিকই; কিন্তু মাখমালবাফকে ফ্রেম থেকে হারিয়ে ফেলার পর নিজের বলা কথাগুলো ক্লোজ আপ-এ হুবহু তুলে ধরায় পরিস্থিতিটা আরো বেশি প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে। ফলে ক্যামেরার সামনে গাছের আড়াল হওয়াটা ‘দৃশ্যকটু’ লাগেনি।
দৃশ্য ধারণের সময়ও আব্বাস প্রাধান্য দিয়েছেন প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারে। অবশ্য অনেক আগেই আকিরা কুরোশাওয়া তার রাশোমন (১৯৫০) পুরোটাই প্রাকৃতিক আলোতে দৃশ্য ধারণ করেছিলেন। এর বাইরেও অনেক নির্মাতাকেই প্রাকৃতিক আলোয় দৃশ্যধারণ করতে দেখা যায়। ক্লোজ আপ-এ সাংবাদিক ফারাজমান্দ যখন গাড়িতে করে মি. আহনখের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন, সেই সময় গাড়ির চালক এবং ফারাজমান্দের মুখের একাংশে সূর্যালোক তীব্রভাবে পড়ে; আর পিছনের আসনে বসে থাকা পুলিশ সদস্যদের হালকা আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এক্ষেত্রে চলন্ত গাড়িতে দৃশ্য ধারণের সময় প্রাকৃতিক আলোর বাইরে নির্মাতা বাড়তি কোনো আলো ব্যবহার কিংবা তীব্রভাবে পড়া সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেননি। এমনকি ইনডোরের দৃশ্য ধারণেও ব্যবহার করা হয়নি বাড়তি কোনো আলো। মোদ্দা কথা, চলচ্চিত্রজুড়েই স্বাভাবিক আলোর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।
ক্লোজ আপ-এ আব্বাস অভিনেতাদের নির্মাতার দিকে ধাবিত করার চেয়ে নির্মাতাকেই তাদের দিকে ধাবিত করেছেন। আব্বাস মনে করেন, ‘সবকিছু অভিনেতাদেরই হয়—আমি শুধু পরিস্থিতিটা তৈরী করি। আমি মনে করি এই ধরনের পরিচালনা অনেকটা ফুটবল কোচের মত। তুমি তোমার খেলোয়াড়দের তৈরী করছো এবং ঠিক জায়গামতো তাদের বসিয়েছ কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়ে গেলো তখন তোমার আর করার কিছু থাকে না।’৬ সে কারণেই হয়তো সাবজিয়ানের সঙ্গে যা যা ঘটেছে, চলচ্চিত্রে সেই বিষয়গুলোই উঠে আসে। যদিও সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে কোন বিষয় থাকবে আর কোনটি থাকবে না, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণটাই নির্মাতার।
এক্ষেত্রে হয়তো অভিনেতা-অভিনেত্রীর পছন্দ কিছুটা থাকে আর বাকিটা নির্মাতার হাতে; আব্বাস অবশ্য বলছেন—‘আমার ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য থাকে না। আমার মনে চরিত্র ও ছবির সাধারণ কাঠামো থাকে। ... আমি যখন সেই চরিত্রটাকে পেয়ে যাই তখন তার সাথে সময় কাটাই এবং তাকে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি।’৭ সেক্ষেত্রেও নিজের কল্পনা মতো নোট না নিয়ে বাস্তবের আদলে সংলাপ রাখার চেষ্টা করেন তিনি। যে কারণে হয়তো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাবজিয়ানের গল্পটা তিনি বদলে দেননি; বিচারকার্যের সময় সাবজিয়ান নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অতীতের যে বর্ণনা হাজির করেছেন, আব্বাস সেটাই গ্রহণ করেন। সাবজিয়ানকে তাই ক্লোজ আপ-এর চিত্রনাট্যকার বললে বোধ হয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।
জীবনের কাছাকাছি পৌঁছাতে
শব্দ-নৈশব্দের খেলা
চলচ্চিত্র শুরুই হয় দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া একটি গাড়ির শব্দে। এরপর গাড়িতে মি. আহনখের বাড়ি যাওয়া থেকে শুরু করে, পানীয়র ক্যানে লাথি মেরে গড়িয়ে দেওয়া, ছাপাখানায় মেশিন চলা কিংবা মাখমালবাফের মোটরসাইকেলে করে সাবজিয়ানকে নিয়ে যাওয়া—সবখানেই ছিলো ঘটনা সংশ্লিষ্ট মূল শব্দের ব্যবহার। গাড়ি চলার সময় চালকের সঙ্গে ফারাজমান্দের কথোপকথন, তাদের গাড়ির শব্দ, হর্ন, অতিক্রম করে যাওয়া অন্য সব গাড়ির শব্দ, সেগুলোর হর্ন—সবমিলিয়ে একটা দ্যোতনা তৈরি হয়। অন্যদিকে আবার সাবজিয়ানকে আটকের সময় কিংবা তিনি যখন আদালতে নিজের অতীত তুলে ধরেন—এসব দৃশ্যে আব্বাস কোনো ধরনের শব্দেরই ব্যবহার করেননি। যদিও সচরাচর এসব দৃশ্যে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু আব্বাস তার চলচ্চিত্রজুড়েই কোনো ধরনের আবহসঙ্গীত কিংবা সঙ্গীতের ব্যবহার করেননি। সঙ্গীতকে তিনি অবশ্য আলাদাভাবেই শুদ্ধ একটা স্বতন্ত্র শিল্প মনে করেন; যা অত্যন্ত শক্তিশালী ও মুগ্ধকর।৮
সে কারণে সঙ্গীতের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতা করানোকে আব্বাস মোটেও সমীচীন মনে করেন না। তার মত, ‘সঙ্গীতের ব্যবহার অনেকটা আবেগী করে তোলে এবং আমি আমার দর্শকের উপর এমন নান্দনিক কোন বোঝা চাপাতে চাই না। সঙ্গীত দর্শকের উপর যে ভূমিকাটা পালন করে সেটা আবেগের, কখনও আনন্দে উত্তেজিত করে, আবার কখনও বেদনায় নিমজ্জিত করে এবং সঙ্গীতের উঠা নামায় দর্শকদের অনুভূতির উঠা নামা হয়।’৯ আব্বাস দর্শকের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করেন, আর সে কারণেই হয়তো তাদের আবেগ অনুভূতিকে সঙ্গীতের সাহায্যে ওঠানামা করাতে চাননি। এক্ষেত্রে কোনো চরিত্রকে হুবহু উপস্থাপনের জন্য তিনি বাইরে থেকে কিছু আরোপও করেননি। বরং তিনি দর্শককে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক বিচলন দেখাতে চেয়েছেন।
তিনি হয়তো জীবনের কাছাকাছি পৌঁছাতে চেয়েছেন। কিন্তু জীবনের হুবহু অনুকরণ তো আর শিল্প হতে পারে না। যেমনটা প্রায়ই বলতেন বিখ্যাত নির্মাতা গদার; তার ভাষায়, জীবনও একটি চলচ্চিত্র। তবে সেটা ভালোভাবে নির্মাণ করা হয়নি।১০ চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে সেটা ভালোভাবেই করতে হয়; সম্পাদনার টেবিলে নিয়ে যেতে হয়, সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়, এমনকি বাস্তবে যা আছে তার বাইরেও প্রয়োজনীয় সত্য নির্মাণ করতে হয়। সে কারণে হুবহু বাস্তবের অনুকরণে না গিয়ে নির্মাতারা চেষ্টা করেন চলচ্চিত্রে বাড়তি কিছু রাখার। প্রয়োজনীয় শব্দ সংযোজন থেকে ব্যবহার করেন আবহসঙ্গীত ও সঙ্গীত। কিন্তু আব্বাস ক্লোজ আপ-এ বাড়তি হিসেবে সঙ্গীত, আবহসঙ্গীতের ব্যবহার না করে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল শব্দ সংযোজন করেন। এদিক থেকে অবশ্য তিনি যথেষ্ট পটুও।
প্রাকৃতিক শব্দের মধ্যে যে দ্যোতনা, যে সুর লুক্কায়িত থাকে; চলচ্চিত্রটিতে তার যথার্থ্য ব্যবহার করেছেন তিনি। ক্লোজ আপ বার কয়েক দেখে মনে হয় গাড়ির শব্দ, হর্ন, মানুষের কোলাহল সবকিছু একেবারে সূক্ষ্মভাবে ধারণ করা। ফলে সাবজিয়ানের বিচারের সময়কার নীরবতা কিংবা গাড়ির হর্ন, মানুষের কোলাহল অনেকটাই অর্থবহ হয়ে ওঠে। যে কারণে সঙ্গীত না থাকলেও ক্লোজ আপ দেখা দর্শকের খারাপ না লাগারই কথা।
আব্বাস দায় নেন, কারণ খোঁজেন
ক্লোজ আপ-এ সাবজিয়ানকে আটকের পর ‘সোর্স ম্যাগাজিন’-এ শিরোনাম হয় ‘ভুয়া মাখমালবাফ আটক’। কিন্তু কাউকে মিথ্যে পরিচয় কেনো ধারণ করতে হয়, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আসলে আমরা যে সমাজ-রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করি, সেখানে ভুয়া মাখমালবাফ আটক হওয়ার খবর যতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; তার বিপরীতে কেনো একজন মানুষ নিজেকে মাখমালবাফ পরিচয় দেন, সেই প্রশ্নটা কিংবা সংবাদ নিয়ে কথা কমই হয়। বরং এর বিপরীতে মানুষজন ওই ব্যক্তি আটকের পর কী হলো তা নিয়েই বেশি আগ্রহী থাকে। বিপত্তি আরো বাধে, যখন সবাই ধরেই নেয়—ব্যক্তি-মানুষের এই পরিণতি ‘অদৃষ্টের লেখা’; তারা ভাবতে চায় না, এর পিছনে কারো দায় থাকতে পারে! ক্লোজ আপ-এ আব্বাস এই চিন্তাকে এতো সহজে ছেড়ে দেন না। তিনি কেবল আটক সাবজিয়ানকে দর্শকের সামনে হাজির করে ক্ষান্ত থাকেন না, তার ‘অপরাধী’ হওয়ার কারণও তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি এও বোঝান, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মানুষেরা সাবজিয়ানদের যে সীমানা বেঁধে দিয়েছে, সেটা অনেক আবদ্ধ; যার ফলে সাবজিয়ান কল্পনার রাজ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়।
আব্বাসের এই উদ্যোগকে যে রাষ্ট্রের কর্তারা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে, এমন নয়। যে কারণে সাবজিয়ানের বিচারের দৃশ্য হুবহু ধারণ করতে চাইলে, বিচারক তাতে আগ্রহ দেখান না। একইভাবে আগ্রহ দেখান না ওই চালকও; যার কাছে নির্মাতা মহসিন মাখমালবাফ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিষয়টা তিনি হেঁয়ালির সঙ্গে এড়িয়ে যান। তাছাড়া সাবজিয়ানের আটক হওয়াকে ফারাজমান্দ চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করলেও, তাতে চালকের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। চালকের এই অনীহার কারণ খুঁজে পেতে অবশ্য দর্শককে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।
এদিকে ক্লোজ আপ-এ সাবজিয়ান যে একাই বঞ্চিত হয়েছেন, বিষয়টা সে রকমও নয়। এর বেশিরভাগ চরিত্রকেই না পাওয়ার বেদনায় ভুগতে দেখা যায়। মি. আহনখের বড়ো ছেলে ছয় মাস আগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পরও কোনো চাকরি পাননি। বেকারের এই তালিকায় যে তিনি একা নন, সেটা তার কথাতেই বোঝা যায়। এক বছর আগে পাশ করা আমির, হোসেন, হুসাইনেরও চাকরি মেলেনি। একই সঙ্গে মি. আহনখের ছোটো ছেলের বাল্যকাল থেকেই শিল্প, সাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা; চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লেখা ছাড়াও তিনি ছবি আঁকতে পারেন। অথচ নিজের আগ্রহ, ভালোলাগা জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে পরিবারের ইচ্ছায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয়। নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও এখন তাকে বেচতে হয় রুটি।
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও পারিবারিক চাপের কারণে যেমন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর নিজের ভালোলাগার কোনো মূল্যায়ন হয় না; অন্যদিকে পরিবারের সমর্থন থাকলেও পছন্দমাফিক বিষয়ে ভর্তি হতে না পেরে বিকল্প খুঁজতে হয় তাদের। আবার পড়াশোনা শেষে দক্ষ ওই জনবলের যখন রাষ্ট্রকে দেওয়ার সময় আসে, তখনো তাদের কর্মসংস্থান করতে রাষ্ট্র আরেক দফা ব্যর্থ হয়। ফলে স্নাতকোত্তর শেষে কেউ যেমন পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, বাধ্য হয়ে কেউ আবার রুটি বিক্রি শুরু করে। আর রাষ্ট্রের ‘সফলতায়’ যে ‘সৌভাগ্যবান’দের কর্মসংস্থান হয়, তাদের অবস্থাও খুব একটা ভালো বলা চলে না। সাবজিয়ানকে আটক করতে যাওয়া এক পুলিশ সদস্য এখনো বিয়ে করেননি অভাবের কারণে; আরেকজন বিয়ে করার পরও পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারেন না। একইভাবে একসময়ের পাইলটকে দেখা যায় ট্যাক্সি চালাতে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যার প্রিয়জনের জন্য ফুল কেনারও সামর্থ্য নেই। যে কারণে হয়তো মি. আহনখের বাড়ির সামনের ডাস্টবিনে পড়ে থাকা ফুল তুলে নিতে হয় তাকে। অবশ্য এই দৃশ্যে আব্বাস অত্যন্ত অর্থবহ প্রতীকের ব্যবহার করেন। বিকট শব্দে ঊর্ধ্বমুখী রকেটের দিকে ওই চালকের চেয়ে থাকার দৃশ্যের পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছে ডাস্টবিন থেকে ফুল কুড়িয়ে নিতে দেখান তিনি। এরপর আবার ওই চালককে দিয়ে পানীয়র খালি ক্যানে লাথি মারান। খালি ওই ক্যানের গড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্য ৩৫ সেকেন্ড ধরে দেখা যায়; শেষ পর্যন্ত রাস্তার এক পাশে গিয়ে তা থামে।
প্রথম শটে ওই চালকের আকাশের দিকে চেয়ে থাকার মধ্যে আব্বাস হয়তো ব্যক্তি-মানুষের স্বপ্নের বিষয়টাকে বোঝান। সেই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বর্ণনা হাজির করতে এর পরের শটেই দেখান বিকট শব্দে ঊর্ধ্বমুখী রকেট; যার নীচের দিক রকেটেরই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। তৃতীয় শটে ওই চালককে দেখা যায় রকেটের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দু-চোখ মুছতে। স্বপ্নবান মানুষগুলোর স্বপ্নভঙ্গের পরের অবস্থা তুলে ধরতেই হয়তো এমন উপস্থাপন। স্বপ্নভঙ্গের পর যার অবস্থা পানীয়র ওই খালি ক্যানের মতো; গড়িয়ে গড়িয়ে যেটার একসময় নীচু কোনো স্থানে ঠাঁই হয়। ‘সাদামাটা’ এই শটগুলোর মধ্য দিয়ে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তুলে ধরেন আব্বাস; তার অনন্যতার জায়গাটাও সেখানেই।
এ জগতে হায় ...
চলচ্চিত্রজুড়ে সবারই অপূর্ণতা। সাবজিয়ান চাকরি হারিয়েছেন, পাইলট ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রুটি বেচেন, স্নাতকোত্তর শেষ করেও অনেকেরই চাকরি মিলছে না। কিন্তু মানুষ তো আসলে সবসময় নিজের দুঃখটা ভুলে সুখ পেতে চায়—ফ্রয়েডিয়ান ধারা অন্তত তা-ই বলে। এজন্য প্রয়োজনে কেউ কেউ যেকোনো উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। যেমনটা করেন সাবজিয়ান। স্ত্রী তাকে অকর্মণ্য ভেবে ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃখ ভুলে নিজেকে তিনি ক্ষমতাবান হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। সে কারণেই হয়তো মিসেস আহনখ তার পরিচয় জানতে চাইলে, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে নির্মাতা মাখমালবাফ হিসেবে পরিচয় দেন। অবশ্য সাবজিয়ানের দাবি, ‘মানুষজন মনে করে আমি সেই লোক (মহসিন মাখমালবাফ); কিন্তু আমি সেটা শুধরে দেওয়ার মতো কিছুই করি না।’ তাই চলচ্চিত্রে নিজেকে মাখমালবাফ হিসেবে জাহিরের জন্য বইয়ে অটোগ্রাফ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি মিসেস আহনখের ছেলেদের তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলেন।
এমনকি তাদের বাড়িতে যাওয়ার পর সাবজিয়ান সেখানে নতুন চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাতে অভিনয়ের প্রস্তাবও দেন মি. আহনখের ছেলেদের। তাদেরকে চলচ্চিত্র দেখাতে প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে তিনি অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক কথাবার্তা বলেন; ওই বাড়িতে রিহার্সেলেরও প্রস্তুতি নেন। মাখমালবাফরূপী সাবজিয়ান পুরো পরিস্থিতিকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আহনখের বাড়ির গাছ পর্যন্ত কেটে ফেলেন, দৃশ্য ধারণে অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কায়।
মাখমালবাফ হিসেবে সাবজিয়ান যা যা করেন, সেটা যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য; একইভাবে সেই কাজগুলো তার কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠারও পরিচয় দেয়। বিচারের সময় সাবজিয়ান নিজেই বলেছেন, ‘আমি শুধু মাখমালবাফ সেজে তাদেরকে আমার আদেশ মানতে বাধ্য করেছি।’ একদিকে সাবজিয়ানের নিজের অতীত ভুলে যাওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠা। সবমিলিয়ে সাবজিয়ানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের অনেক চরিত্রে এ রকম দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। যেখানে ঘটনার পরতে পরতে কোনো চরিত্রের ভিতরকার দ্বন্দ্ব নানা বাঁকে মোড় নেয়।
ক্লোজ আপ-এ একদিকে যেমন মি. আহনখের বাড়ির সবাই সাবজিয়ানকে মাখমালবাফ ভেবে সম্মান করে; অন্যদিকে সাবজিয়ানের মনে কিন্তু অপরাধবোধ, হীনমন্যতা কাজ করে। সাবজিয়ান নিজ থেকে মি. আহনখের পরিবারের কাছে সত্য ঘটনা খুলে না বললেও, নিজেকে সবসময় দুর্বল বলেই মনে করতেন। সাবজিয়ানের ভাষায়, ‘সবসময়ই ভাবতাম, আমি সেই ব্যক্তি যে নিজের পরিবারকে সাহায্য করতে পারে না।’ যে কারণে নির্মাতা মাখমালবাফ পরিচয়ে থাকার পরও মি. আহনখের ছেলের কাছ থেকে ধার হিসেবে টাকা নিতে হয় তাকে। এমনকি কেবল রাতের খাবারের জন্যও তাদের বাড়িতে সাবজিয়ানকে যেতে হয়।
অন্যের কাছে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাবজিয়ান মিথ্যা পরিচয় ধারণ করেন ঠিকই; কিন্তু মি. আহনখের বাড়িতে থাকা অবস্থায়ই তার মনে নিজের কৃতকর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কিন্তু তার পরেও তিনি মাখমালবাফ থেকে নিজেকে বাইরে নিতে পারেননি। বিচারকার্যের সময় তাই সাবজিয়ানের সরল স্বীকারোক্তি, ‘আমি জানি তাদের কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছি এবং সেখানে রাত কাটিয়েছি, এর জন্য আটক হতে পারি। কিন্তু তার পরেও কাজগুলো বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি।’ তিনি বাড়ি ফিরে না গেলেও নিজের নোটবুকে ‘দ্য লাস্ট ট্র্যাজেডি’ শিরোনামে মি. আহনখের বাড়িতে তার ঘটানো বিষয়ের বর্ণনা লিপিবদ্ধ রাখেন। সাবজিয়ানের ভাষায়, ‘আমি বুঝতে পারছিলাম এটার শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসছে। সে কারণেই ওটা লিখে রাখা।’ নোটবুকে লিখে রাখার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, মি. আহনখের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর আর সেখানে ফিরে আসবেন না। কিন্তু তার পরও তিনি মি. আহনখের বাড়িতে যান; শেষবার সেখানে গিয়ে আটক হন।
মি. আহনখের ছেলের অভিযোগ, সহানুভূতি পাওয়ার আশায় বিচারের সময়ও সাবজিয়ান নতুন চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছেন। কিন্তু সাবজিয়ানের সোজাসাপ্টা জবাব, ‘আমি শুধু নিজের ভোগান্তির কথা বলছি; এটা অভিনয় নয়। আমি সবকিছু মন থেকে বলছি।’ বাস্তবেও দক্ষ কোনো অভিনেতা চাইলে যেকোনো চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে তার নিজের চরিত্রে অভিনয় করার চেয়ে বেশি কঠিন আর কী হতে পারে। সাবজিয়ান মাখমালবাফ হিসেবে নিজের চরিত্র বদলে নির্মাতার মতো আচরণ করেছেন ঠিকই; কিন্তু তার পক্ষে এতো সহজে নিজের চরিত্রে অভিনয় করা সম্ভব নয়। সে কারণে বিচারের সময় সাবজিয়ান সবকিছু তুলে ধরেন নিজের মতো করে। মি. আহনখের পরিবারের সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে, তার জন্যও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি। এভাবে ক্লোজ আপ-এ ব্যক্তির ভিতরকার দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত দক্ষভাবে তুলে ধরেন আব্বাস।
অনন্যতা দিয়েই শেষ
আলোচনা শুরু করেছিলাম অনন্যতা দিয়ে। পুরো লেখায় ঘুরেফিরে উঠে এসেছে ক্লোজ আপ-এ আব্বাসের অনন্যতার প্রসঙ্গ। শেষ করার আগে চলচ্চিত্রের এক বলিষ্ঠ চরিত্র নিয়ে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছি। গণমাধ্যমে বিশেষ করে চলচ্চিত্রে যেখানে নারীদের সচরাচর সাজানোর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়; ক্লোজ আপ-এ দেখা যায় তার উল্টো। বড়ো ছেলে তার ভাইকে রুটি বিক্রেতা হিসেবে অভিহিত করলে, মিসেস আহনখ তার প্রতিবাদ জানান। ছেলেকে তিনি রুটি বিক্রেতার পরিবর্তে সেই দোকানের মালিক ভাবার পক্ষপাতী। ছেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও রুটি বিক্রি করাটাকে তিনি কোনোভাবেই খাটো করে দেখেন না। নারীর দৃষ্টিভঙ্গির যে উপস্থাপন আব্বাস করেন, তাও নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।
তাছাড়া, ক্লোজ আপ-এ কাহিনিচিত্র আর প্রামাণ্যচিত্রের সীমানা ভেঙে নতুন কিছু নির্মাণ, সত্য আর বাস্তবকে একসঙ্গে পর্দায় হাজির করা থেকে সাবজিয়ানের জীবনের একেবারে কাছে গিয়ে তার বিষয়গুলো তুলে আনতে ক্লোজ শটের ব্যবহার; চিত্রায়ণে সত্য ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যার যার অবস্থানে ঠিক রাখা; প্রামাণ্য দৃশ্য ধারণে নির্মাতা আব্বাস ও তার সঙ্গীর কথাবার্তা উঠে আসা; চলচ্চিত্রে সেই অর্থে কোনো ন্যারেটিভ না রাখা; ‘প্রেজেন্স উইদাউট প্রেজেন্স’ এর ব্যবহার; নৈশব্দ এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট মূল শব্দের ব্যবহার; সাবজিয়ানের নিজের মধ্যে চলা দ্বন্দ্ব; আর সব চরিত্রের অপূর্ণতা তুলে ধরে চলচ্চিত্রটিকে আব্বাস অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।
লেখক : কাওসার বকুল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী।
bokulmcj71@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. http://sangskriti.com/abbas-kiarostami/; retrieved on 30.09.2016
২. ‘বিদায় সেলুলয়েডের কবি’; কালের কণ্ঠ, ১৪ জুলাই ২০১৬।
৩. রফিক, মনিস (২০০৯ : ৩২); ক্যামেরার পেছনের সারথি; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।
৪. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ২৪)।
৫. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ২৪)।
৬. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ২৫)।
৭. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ২৫)।
৮. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ৩৮)।
৯. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ৩৮)।
১০. প্রাগুক্ত; রফিক (২০০৯ : ৩৭)।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন