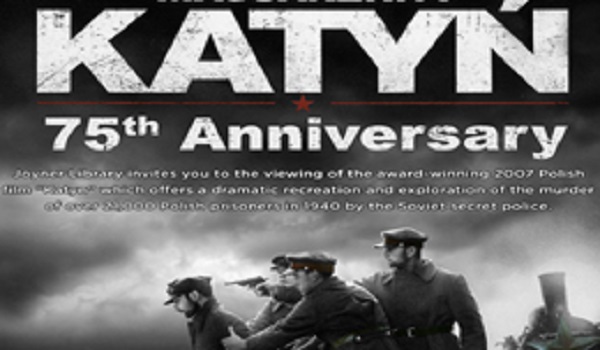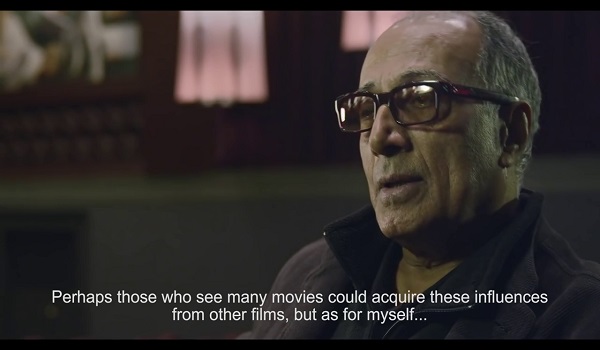মাসুদ পারভেজ
প্রকাশিত ০৭ আগস্ট ২০২৫ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
পালাবি কোথায় : গতানুগতিক খোকনের খানিক উল্টো দেখা
মাসুদ পারভেজ

‘চলচ্চিত্র সর্বকলা আত্মীকৃত এক শিল্প, যোগাযোগ ও প্রকাশ মাধ্যম।’১ এই কথার সূত্র ধরে যদি আলাপ শুরু করা যায় স্বভাবতই যে বিষয়টা আসে তা হলো, চলচ্চিত্র এমন একটা শিল্প যাতে শিল্পকলার অনেক মাধ্যমের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর তাই চলচ্চিত্রকে বিনোদন কিংবা গণযোগাযোগ যে মাধ্যম হিসেবেই দেখি না কেনো, পুরোপুরি এর স্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব কলার সংমিশ্রণে তা তৈরি, সেসবের ওপর ধারণা থাকা দরকার। এ তো গেলো দর্শকের ব্যাপার। আর চলচ্চিত্রনির্মাতার তো এসব বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞান থাকাই আবশ্যক। চলচ্চিত্রের অভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক উপাদানের সব বিষয় সম্পর্কে একজন নির্মাতাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হয়। তা না হলে একটি চলচ্চিত্র কখনোই নিখুঁতভাবে নির্মাণ সম্ভব হয় না।
তাহলে বিষয়টাকে এভাবে বলা যায়, চলচ্চিত্র অনেক কলার সংমিশ্রণ আর নির্মাতা সেই সব কলার সমন্বয়কারী। তো সেই সমন্বয়কারীর কথা দিয়ে শুরু করা যাক। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় যে যাত্রার শুরু করেন, তারপর থেকে নির্মাতা হিসেবে কতো মানুষের নাম যে যুক্ত হয়েছে তার হিসাব কোনো সহজ কর্ম নয়। তবে এর মধ্যেও কয়েকজন নির্মাতা বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে, তারা হয়তো রয়েও যাবে। আইজেনস্টাইন, আন্তোনিওনি, ওজু, কুরোশাওয়া, গদার, গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, ডি সিকা, তারকোভস্কি, পন্টিকভো, ফেলিনি, বার্গম্যান, বুনুয়েল, জ্যঁ রেঁনোয়া, আলফ্রেড জোসেফ হিচকক, মেহেরজুই, কিয়োরোস্তামি, শ্যাম বেনেগাল, উসমান সেমবেন, স্পিলবার্গ আরো কতো নাম এই তালিকায় জ্বলজ্বল করে। এইসব মানুষেরা বিভিন্ন ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, শুধু বাংলা ছাড়া। এই তালিকায় থাকা ঋত্বিক, সত্যজিৎ ও মৃণালই কেবল চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন বাংলা ভাষায়। তবে এখানেও একটা কথা থেকে যায়, এরা বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেও সীমানার সংজ্ঞায় (?) কেউই বাংলাদেশের নির্মাতা নন।
বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঘটলেও এর নিজস্ব সাহিত্যকে ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকেই ধরা হয়। সেই হিসেবে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও ১৯৪৭ থেকেই ধরা যেতে পারে। যদিও চলতি ইতিহাস হীরালাল সেনকে আমলে না নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাল ১৯৫৬-কেই ধরে। তো সেই হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রনির্মাতার খোঁজ করলে আবদুল জব্বার খান-এর নামটাই আগে আসে। এছাড়া ফতেহ লোহানী, সালাহউদ্দিন, জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, খান আতা, কাজী জহির, দিলীপ সোম, এহতেশাম, আমজাদ হোসেন, মিতা, চাষী নজরুল ইসলাম, প্রমোদকার, আলমগীর কুমকুম, আলমগীর কবির, কাজী হায়াৎ, এ জে মিন্টু, দারাশিকো, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, তারেক মাসুদ আরো কতো নাম। এইসব নামের সঙ্গে আরেকটা নাম চলে আসে—শহীদুল ইসলাম খোকন। এই নির্মাতাকে কেন্দ্র করেই এ লেখা।
২.
চলচ্চিত্র রচনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়—একদল রচয়িতা, তারা সমাজ-বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেয়; অন্যদল কল্পিত কোনো কিছুকে তাদের চলচ্চিত্রের বিষয় করে তোলে।২ এটা চলচ্চিত্রের গোড়ার দিককার কথা। তারপর সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের বিষয় ও আঙ্গিকে অনেক পরিবর্তন এসেছে, আর সেটা এখন পর্যন্ত চলছেও। বিশ্ব চলচ্চিত্রে কাহিনি কিংবা নির্মাণ কৌশল কিংবা শৈলী নিয়ে চলচ্চিত্র যতো এগিয়েছে বাংলাদেশে সেভাবে এগোয়নি। এটা কামনা করাও হয়তো যথার্থ হবে না। বিশেষ করে প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে কথাটা আরো প্রযোজ্য। তবে শুধু প্রাযুক্তিক অপর্যাপ্ততাই যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে পিছিয়ে রেখেছে তেমনও নয়। এক্ষেত্রে কাহিনি, নির্মাণশৈলী সর্বোপরি নির্মাতার চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পঠন-পাঠনের অভাবও আছে। প্রযুক্তিসহ নানা কিছুর অভাব থাকা সত্ত্বেও ইতালিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রে একদল স্বাধীন নির্মাতার আবির্ভাব হয়। যারা স্বল্প খরচে স্টুডিওর বাইরে পথে-ঘাটে বাস্তবতাকে ধারণ করার জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। আবার লাতিন আমেরিকার থার্ড সিনেমার কথা যদি ধরি, সেখানে ‘এই চলচ্চিত্র দর্শককে লড়াকু হতে উৎসাহী করে, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বাস্তবতাকে নিরীক্ষণ করে এবং প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক পরিকাঠামোকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে।’৩ তো বাংলাদেশে সময়ের নানা পরিক্রমায় এ ধরনের চলচ্চিত্র হয়নি বললেই চলে। প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে তাহলে হয়েছে কী কিংবা এর নিজস্বতা কোনটি?
এই প্রশ্নের উত্তরে চলচ্চিত্রের যে ভাগ কিংবা বিভাজন তৈরি হয়, তাতে চলচ্চিত্রের দর্শককে ঘিরেই প্রশ্নটার উত্তর তৈরি হয়—নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তের চলচ্চিত্র। এই দুইয়ের বাইরে যে শ্রেণি, তারা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দর্শক কোনো কালেই ছিলো না। তো নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তকে ধরেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে। যেমন গড়ে ওঠে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পও। আর বাংলাদেশের এই গার্মেন্ট শিল্প নিয়েই ২০ বছর আগে শহীদুল ইসলাম খোকন নির্মাণ করেন পালাবি কোথায় (১৯৯৬)। এর কাহিনি গড়ে উঠেছে গার্মেন্ট শিল্পের নারী শ্রমিকদের ঘিরে।
৩.
শহীদুল ইসলাম খোকন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্রে তার যাত্রা সোহেল রানার সহকারী পরিচালক হিসেবে মাসুদ রানা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।৪ এটা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। তার পর খোকন নিজেই পরিচালনায় আসেন রক্তের বন্দী (১৯৮৫) চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রটি অবশ্য ব্যবসায়িকভাবে সফলতা পায়নি। তারপর খোকন বাংলাদেশে এক নতুন ঘরানা নিয়ে হাজির হন—মার্শাল আর্টনির্ভর চলচ্চিত্র। নায়ক রুবেলকে নিয়ে খোকন নির্মাণ করেন লড়াকু (১৯৮৬)। যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে নতুন পর্ব যোগ করে। এরপর রুবেল আর হুমায়ুন ফরীদিকে নিয়ে খোকন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এখানে একটা বিষয় না বললেই নয়, কাজী হায়াৎ যেমন মান্না আর রাজীবকে নিয়ে নায়ক-ভিলেন জুটি করেন, খোকনও তার চলচ্চিত্রে রুবেল ও ফরীদিকে নিয়ে সেই জুটি বাঁধেন, যা দর্শকপ্রিয়তা পায়। হুমায়ুন ফরীদির নাম যখন চলেই এলো, তখন তাকে নিয়ে দু-একটি তথ্য দেওয়া জরুরি। চলচ্চিত্রে আসার আগে ফরীদি মূলত মঞ্চ আর টেলিভিশন নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন। খোকন তার চলচ্চিত্রে খলঅভিনেতার যে নতুন ফরমেট সাজান, তাতে ফরীদি অনেক ক্ষেত্রে নায়কের চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পান। সেই ফরীদিকে প্রধান চরিত্রে বসিয়ে খোকন নির্মাণ করেন পালাবি কোথায়।
কমেডিনির্ভর চলচ্চিত্র বাংলাদেশে সেভাবে নেই বললেই চলে। পালাবি কোথায়-এ খোকন হিউমার ব্যবহারের চমক দেখান। বিশেষ করে ফরীদির রূপ দান করা গার্মেন্ট ম্যানেজারের চরিত্রটিতে। এই ম্যানেজার নারীতে আসক্ত পুরুষ। ফলে ওই গার্মেন্টে কাজ করতে আসা নারী কর্মীরা প্রায়ই তার দ্বারা নানারকম হয়রানির শিকার হন। ম্যানেজারের অফিসে কম্পিউটার অপারেটর চরিত্রে রূপ দান করা শাবানা, টাইপিস্ট কাম পি এস চরিত্রে সুবর্ণা, ঝাড়ুদার চরিত্রের চম্পা থেকে গার্মেন্টের নারী শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে তার দ্বারা আক্রান্ত হন।
পুরুষ সহকর্মীর হাতে নারীদের যৌন হয়রানির ঘটনা বাংলাদেশে অহরহ ঘটে থাকে। এটা যতোটা ঘটে, তার চেয়ে প্রকাশ পায় কমই। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার নারীকেই নানাভাবে দোষারোপ করা হয়। খোকন পালাবি কোথায়-এ দৈনন্দিন অফিসিয়াল কর্মে একজন নারী কীভাবে তার অফিস প্রধান কিংবা পুরুষ সহকর্মী দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরেন। তবে এই বাস্তবতাকে নির্মাণ করতে গিয়ে খোকন চলচ্চিত্রের ডকুমেন্টারি, আর্টফিল্ম কিংবা বিকল্প ধারার কোনো বিষয় মাথায় রাখেননি বলে মনে হয়েছে। বঙ্কিম যেমন কমলাকান্তকে আফিম খাইয়ে সমাজের নানা অসঙ্গতিকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেন, তেমনই করেছেন খোকনও।
৪.
চলচ্চিত্রের শুরু কাট ওভার সাউন্ডে একটি বক্তব্য দিয়ে; তখন পর্দায় দেখানো হয় নারীদের বিভিন্ন রকম কাজ। এই নারীদের সবাই নিম্ন আয়ের নানা কর্মে যুক্ত। বক্তব্যটি এমন—
সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতা বিকাশের মূলে যুগ যুগ ধরে কাজ করে চলেছে মানবজাতি। এই কর্মকাণ্ডে নারী জাতির ভূমিকা গৌণ নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে চলেছে সমানতালে। একসময় আমাদের দেশে নারীরা শুধুই ঘর-সংসার নিয়ে জীবন কাটাতো। সময় বদলেছে, সাথে সাথে বদলেছে জীবন যাপন পদ্ধতি। নারীসমাজ আজ সক্রিয়ভাবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারাও প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের পোশাক শিল্পে নারীদের ভূমিকাই আজ প্রধান। সংসার ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের এই কর্মময় জীবনে প্রায়ই তাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেই প্রতিকূলতা যখন অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন তারাও হয়ে ওঠে সোচ্চার।
আজ থেকে ২০ বছর আগে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে যখন পালাবি কোথায় মুক্তি পায়, তখন বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প বর্তমানের মতো এতো বেশি বিস্তৃত হয়নি। তবে নারীদের যৌন হয়রানি তখনো ছিলো। আর তাই হয়তো খোকন চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে যৌন হয়রানিকে বেছে নিয়েছিলেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যৌন হয়রানি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এখন শুধু গার্মেন্টের মতো কর্মক্ষেত্রে নয়, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণপরিবহনে নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা আজো অপ্রকাশিতই থেকে যায়। আর যে দু-একটা প্রকাশ পায়, সেখানেও রয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি। ফলে অপরাধীরা আরো বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। যেমনটি পালাবি কোথায়-এ ঘটে ফরীদির বেলায়ও।
তবে পালাবি কোথায়-এ একটা সময় পর এর বিরুদ্ধে নারীরা জেগে ওঠে। নির্মাতা খোকন চলচ্চিত্রের শুরুতে যে বক্তব্যটি হাজির করেন তা ঢাকাই চলচ্চিত্রের দর্শককে খানিকটা ধাক্কা দেয়। কারণ যে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত দর্শক নিখাদ বিনোদন পাওয়ার আশায় সিনেমাহলে যায়, চলচ্চিত্রের শুরুতে এমন বক্তব্যে তারা বেশ নড়েচড়ে বসেন। একটু অন্যভাবে দেখলে, একজন নিম্ন আয়ের পুরুষ যে কিনা সংসারের প্রধান, তিনি যদি চলচ্চিত্রটির দর্শক হন, আর ওই ব্যক্তি যদি আগে তার স্ত্রীর কাজকে কোনোভাবে মূল্যায়ন না করে থাকেন, তাহলে তার মধ্যেও তো এটা সামান্য হলেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
যাহোক, কথা হচ্ছিলো পালাবি কোথায়-এর দর্শক নিয়ে। ধরা যাক, নিম্ন আয়ের গার্মেন্টকর্মীরা এই চলচ্চিত্রের দর্শক, যারা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে নিপীড়নের শিকার। তারপর যখন তারা সিনেমাহলে পালাবি কোথায় দেখছে, তখন তারা তো নিজেকেই দেখে। ফলে এই দর্শক নারীরা যারা গার্মেন্টকর্মী, তাদের মধ্যে তো এর প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকারের ইচ্ছা জাগতেই পারে। আর চলচ্চিত্রের শুরুর বক্তব্যের শেষ কথায় তো তার ইঙ্গিতও আছে—‘সেই প্রতিকূলতা যখন অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন তারাও হয়ে ওঠে সোচ্চার।’ আর এই সোচ্চার হওয়ার ব্যাপারটাই পালাবি কোথায়-এর মোটিফ। ঘুরেফিরে চলচ্চিত্র জুড়ে তা বারবার এসেছে। তাহলে পালাবি কোথায়-এ তো লাতিন থার্ড সিনেমার কিছুটা মেজাজ পাওয়া যায়।
চলচ্চিত্রের শুরুতে গার্মেন্ট ম্যানেজাররূপী ফরীদিকে তার স্ত্রীর কাছে আদর্শ স্বামী হিসেবে নিজের ফিরিস্তি দিতে দেখা যায়। কিন্তু অফিসে প্রবেশের পরপরই তার প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়ে। তাকে ইতর, লুচ্চা, হারামজাদা, শুয়োর, কুত্তা বলে গালি দিতে থাকে টাইপিস্ট কাম পি এস সুবর্ণা। একজন গার্মেন্টকর্মী তার ছেলের অসুস্থতার জন্য অফিসে আসতে কিছুটা দেরি করলে তাকে ম্যানেজার নিজ কক্ষে ডাকে। তারপর কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে দরজা বন্ধ করে দেন। নিয়মিত ঘটা এ ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যান্য কর্মীরা বুঝতে পারে, কক্ষে থাকা নারী কর্মীটির শ্লীলতাহানি ঘটতে পারে। আর তাই কৌশলে ওই কক্ষে আগে থেকে তারা এমনভাবে একটা কলিংবেলের সুইচ বসিয়ে রাখে, যাতে এই পরিস্থিতিতে সেই সুইচ টিপে ওই নারী তার অবস্থার কথা জানান দিতে পারে। আর তখনই কেউ না কেউ তার সাহায্যে ম্যানেজারের কক্ষে যেকোনো উছিলায় যেতে পারে।
যাহোক, কক্ষে থাকা সেই নারী শ্রমিকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দিতে থাকে ম্যানেজার। কিন্তু এইসব নারী কর্মী কোনো অভিযোগ করতে পারে না। প্রথমত, তাদের চাকরি যাওয়ার ভয়ে; দ্বিতীয়ত, তারা অভিযোগটা করবে কাকে কিংবা কোথায়? বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী গার্মেন্টকর্মী গ্রাম থেকে কাজের আশায় ঢাকায় আসেন। আর তাই তারা এসব যৌন হয়রানি নীরবে সয়ে যান, যাতে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে যেতে না হয়। তবে খোকন নারীদের এই হয়রানি নীরবে সয়ে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ফলে চলচ্চিত্রের শেষে গার্মেন্ট শ্রমিকরা ‘বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন’-এর ব্যানারে ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ স্লোগান দিতে দিতে নিপীড়ক ম্যানেজার ফরীদিকে ঘিরে ধরে।
খোকন এই চলচ্চিত্রে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আবার সমাধানও দিয়েছেন অনেক প্রশ্নের। তবে এইসব সমাধান আদৌ বাস্তবে সম্ভব কি না সেটা ভাবার বিষয়। তবে গার্মেন্ট সংক্রান্ত অনেকগুলো বিষয়ে তিনি ২০ বছর আগে নানা ইঙ্গিত দিয়েছেন। গার্মেন্ট মালিক চরিত্রে রূপদানকারী আফজাল হোসেনকে যেমন ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে সব দোষ পড়েছে ম্যানেজারের ঘাড়ে। যদিও বাস্তবচিত্র এমন নয়। এটা হলে প্রতিবছর ঈদের আগে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ, অনশনের মতো কর্মসূচিতে নামতে হতো না। আর এসব শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলাও এতো সহজ নয়। কয়েক বছর আগে ঢাকার সাভারে আমিনুল নামে এক গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা নিখোঁজ হন। ধারণা করা হয় শ্রমিকদের নানা দাবির পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন করাটাই তার নিখোঁজের অন্যতম কারণ। পরে তার মরদেহ পাওয়া গেলেও হত্যার আর বিচার হয়নি, হয়ও না। উল্টো গার্মেন্ট শ্রমিকরা যাতে তাদের অধিকার নিয়ে কোনো কথা বলতে না পারে, সেজন্য গঠন করা হয় শিল্প পুলিশ।
পালাবি কোথায়-এর একপর্যায়ে নারী শ্রমিকরা জোট বেঁধে ম্যানেজার ফরীদিকে কৌশলে অপহরণ করে আটকে রাখে। এই পরিবর্তন একেবারে একটা ভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। অনেকটা ব্যাটলশিপ পটেমকিন-এর মতো জাহাজের দখলটা শ্রমিকদের হাতে নিয়ে নেওয়া আর কি। এ সময় গার্মেন্টের কিছু গুণগত পরিবর্তন আনা হয়। কাজের সময় নারী শ্রমিকদের শিশুদের আলাদাভাবে যত্নে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। খানিক পরিবর্তন আনা হয় গার্মেন্টের অফিসের পরিবেশেও। খোকন ২০ বছর আগে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। যদিও এখনো বাংলাদেশের বেশিরভাগ গার্মেন্ট কারখানায় শিশুদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা নেই।
৫.
পালাবি কোথায়-এর নামকরণ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। ঢাকাই চলচ্চিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে নান্দনিকতার অভাব নতুন কিছু নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম দিয়েই দর্শক আন্দাজ করে চলচ্চিত্রের কাহিনি কী হতে পারে। আর খোকন মার্শাল আর্ট জাতীয় অ্যাকশনধর্মী যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করে জনপ্রিয় হন, সে অনুযায়ী ‘পালাবি কোথায়’ নামটা শুনে দর্শক হয়তো তেমনই ভাবেন। কিন্তু খোকন দর্শককে ধন্দে ফেলেন। গতানুগতিক খলচরিত্রের মতো ফরীদির চরিত্রটি এখানে মারপিটনির্ভর উদ্ভট নয়। সবমিলিয়ে চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে নারী গার্মেন্টকর্মীরা মিছিল নিয়ে যেভাবে চারপাশ থেকে হুমায়ুন ফরীদিকে ঘিরে ধরে, তখন তার পালানোর পথ থাকে না। আর তখনই পর্দায় ভেসে ওঠে পালাবি কোথায়।
পালাবি কোথায়-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ করা হয়েছে The Dirty Debauch। ইংরেজি শব্দদ্বয় চলচ্চিত্রের কাহিনিকে খোলসা করলেও ‘পালাবি কোথায়’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে কতোটা যথাযথ তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।
৬.
নির্মাতা খোকন প্রয়াত হন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল। তার নির্মিত অনেক চলচ্চিত্রের মধ্যে তাকে স্মরণ করার জন্য পালাবি কোথায় অনন্য। কিন্তু চলচ্চিত্রবোদ্ধারা নিশ্চয় সেটা আমলে নেবেন না। হাল আমলের থ্রি ইডিয়টস দেখে আমরা আপ্লুত হই। কারণ এই হিউমারের মাধ্যমে সেখানে শিক্ষাব্যবস্থার গলদ দেখানো হয়। পালাবি কোথায়-এ খোকনও একই কাজ করেন গার্মেন্টের নারী শ্রমিকদের নির্যাতন নিয়ে। কিন্তু পালাবি কোথায় নিয়ে কথা হয় না! কারণ এফ ডি সি’তে নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বললে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাত যাওয়ার ভয় থাকে!
পালাবি কোথায় জেন্ডার ইস্যুতেও প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ খোকন গার্মেন্টের নারী শ্রমিকদের যৌন নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচাতে কোনো পুরুষ-নায়ক হাজির করেননি, যিনি ত্রাতা হয়ে নারীর সম্ভ্রম বাঁচাবেন। বরং তিনি বাস্তবতার চরম রূপটি উন্মোচন করেছেন—নারী তোমার নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। পুরুষ প্রাধান্যশীলতায় নারীরা শুধু কর্মক্ষেত্রে ওপরওয়ালাদের হাতে হয়রানির শিকার হন তা নয়, সমপর্যায়ের কিংবা নীচের পুরুষ সহকর্মীটির কাছ থেকেও তিনি নিরাপদ নন। তাই সেই পুরুষের হাতে নারীর মুক্তি আশা করা নেহাতই বোকামি।
প্রথাবদ্ধ ঢাকাই চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে যখন খলচরিত্রকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়, তখন পুলিশ এসে বলে, আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। পালাবি কোথায়-এ খোকন এর বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। তাই দেখা যায়, নির্যাতিত সুবর্ণা-চম্পারা জুতা, ঝাড়ু দিয়ে ম্যানেজার ফরীদিকে পেটান আর শাবানা চাপাতির কোপ বসান। যা নতুন সম্ভাবনার কথা বলে। নির্মাতা খোকনও উতরে যান।
৭.
বিশ্ব চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ঘরানা তৈরি হলেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে তেমন একটা দেখা যায়নি, কিংবা বলা যায় বাংলাদেশের নির্মাতারা তেমনটা করতে পারেননি। হাতে-গোনা দু-একজন নির্মাতা পাওয়া যাবে যারা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য ধনী-গরিবের প্রেম কিংবা পিতৃহত্যার প্রতিশোধের বাইরে চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রয়াস দেখিয়েছেন। আলমগীর কবির, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল, আরো পরে তারেক মাসুদ তেমনই দু-একটি নাম। এদের বাইরে কয়েকজন নির্মাতা, বিশেষ করে হাল আমলের গরিবগুর্বার জীবন সঙ্কটকে আশ্রয় করে কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু তাতে চলচ্চিত্রিক উপাদান কিংবা এসবের দর্শক কারা এটা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে দর্শকের কথা আগে বলেছি, তারা নিজেরাই ইন্ডাস্ট্রির বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের কাহিনিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাই তারা চলচ্চিত্রে তাদের জীবন দেখতে চান, একই সঙ্গে তাদের প্রতিপক্ষকেও। এবং দিন শেষে প্রাণ খুলে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজের পক্ষের জয় দেখেন। পালাবি কোথায়-এ খোকন এর সবই করেন, তবে পার্থক্য কেবল এখানে উপস্থিত নেই কোনো অতি মানবীয় ক্ষমতার ত্রাতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যিনি পুরুষই হন। ফলে পালাবি কোথায় যে স্বপ্ন কিংবা ঘোর লাগায় তার একটা ইতিবাচক দিক থাকে, জীবন জয়ী হওয়ার রস ও রসদ থাকে। আর এখানেই শহীদুল ইসলাম খোকন নির্মাতা হিসেবে সবার মধ্যে থেকেও কিছুটা ভিন্নতা পান। যদিও বাড়ি বিক্রি করা টাকায় নির্মিত পালাবি কোথায় ব্যবসায়িকভাবে সফলতা পায় না, মানে দর্শক দেখে না। যেমনটা দেখে না আহমদ ছফার ‘ওঙ্কার’ উপন্যাস অবলম্বনে খোকন নির্মিত বাঙলাও।
লেখক : মাসুদ পারভেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়ান। তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম ‘ঘটন অঘটনের গল্প’ ও ‘বিচ্ছেদের মৌসুম’।
parvajm@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. আউয়াল, ড. সাজেদুল (২০১১ : ১৫); চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।
২. প্রাগুক্ত; আউয়াল, ড. সাজেদুল (২০১১ : ১৮)।
৩. প্রাগুক্ত; আউয়াল, ড. সাজেদুল (২০১১ : ৮৯)।
৪. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস (১৯৮৭) গ্রন্থে অনুপম হায়াৎ দস্যু বনহুর চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে শহীদুল ইসলাম খোকনের যাত্রা শুরুর কথা উল্লেখ করেছেন।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন