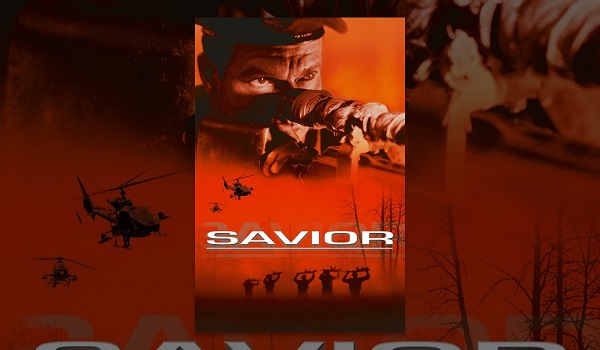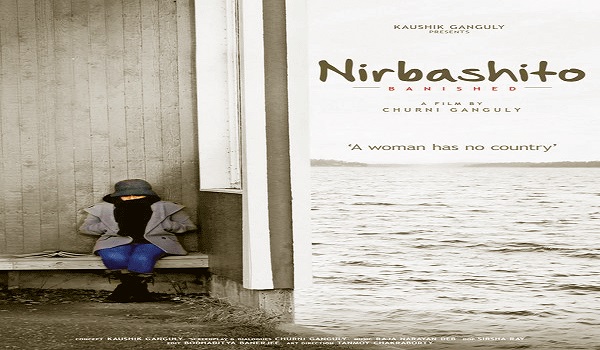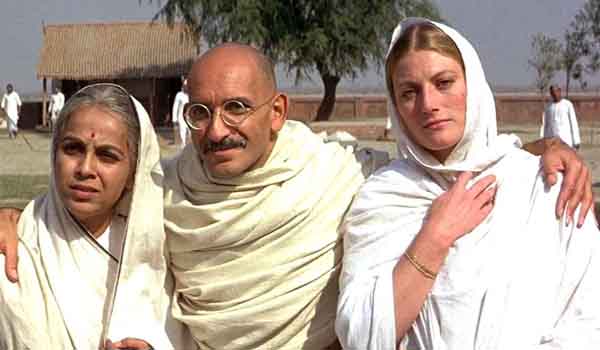তৌফিকুর রহমান
প্রকাশিত ২৬ মার্চ ২০২৪ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
’৭১-এর জীবনকে ছুঁতে পারেনি জীবনঢুলী
তৌফিকুর রহমান

কী হবেনে তা কবে কিডা!
৬০-এর দশকে আমার বাপ-চাচাদের হাতেখড়ি হয়েছিলো পাড়ার নারায়ণ কাকার কাছে, মদনমোহন তর্কালংকারের ‘শিশু শিক্ষা’র পাঠ নেওয়ার মাধ্যমে। আর কৈশোরে নাকি দুর্গাপূজার দশমীতে নৌকায় চড়ে আরতি দিতেন ছোটো চাচা। ওই চাচাই একবার নাকি তার হিন্দু এক বন্ধুকে পালিয়ে বিয়ে করতে সহযোগিতা করায় মামলায়ও জড়িয়েছিলেন। মায়ের মুখেও শুনতাম একই কথা। তিনিও ছোটোবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রসাদ নেওয়ার জন্য। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের এমন ভূরি ভূরি নজির মিলবে, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম এভাবেই বসবাস করেছে এই উপমহাদেশে।
আধুনিক যুগে যেখানে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের ধুয়া তুলে রাষ্ট্র ভাগ করা হয়, সেখানে দ্বাদশ শতকের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের অস্বিত্বই ছিলো না এই উপমহাদেশে। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের পর সুফি-সাধকদের হাত ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। মূলত সব ধর্মের প্রতি সুফিদের উদারনৈতিক মনোভাবই এই মানুষগুলোকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করেছিলো। তবে ইসলাম গ্রহণের পরও অনেক হিন্দু আচার পালন করতো তারা। ফলে বিদেশি ধর্ম ও দেশীয় ঐতিহ্য মিলেমিশে সৃষ্টি হয় অনন্য এক সংস্কৃতির, যেখানে হিন্দু-মুসলিমের আলাদা অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।
মূলত শাসন/ব্যবসা করতে আসা মুসলমানরা স্থানীয়দের ধর্ম-সংস্কৃতিতে হাত দিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চাননি। তাই হিন্দু-মুসলিমকে আলাদা করার পাঁয়তারা তো করেনইনি, বরং কোথাও এ রকম দেখলে শক্ত হাতে দমন করেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলিমের মধ্যযুগীয় এ সম্প্রীতি বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেয় ‘আধুনিক’ ইংরেজদের কাছে। ফলে ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতিতে পরবর্তী প্রায় দুশো বছর তারা উপমহাদেশ শাসন করেছে। তাদের দেখানো পথে স্বাধীন ভারতেও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ; তবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনো দিনই এই উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ সহ্য করেনি। ২০১৫’র দিল্লি লোকসভা নির্বাচনেও তার প্রমাণ মিলেছে। যেখানে বসে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন নরেন্দ্র মোদি, তার ৭০টি আসনের ৬৭টিতেই আম আদমিকে নির্বাচিত করে সাধারণ মানুষ কিন্তু ঠিকই জানান দিয়েছে তাদের অবস্থান।
হিন্দু-মুসলিমের চিরায়ত এই সম্পর্ক উপমহাদেশের ইতিহাসে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। ৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলায় সে প্রমাণ আরো স্পষ্ট। নিজের ভাষাকে অধিকারে রাখতে যেমন তারা (হিন্দু-মুসলিম) এক হয়েছিলো, তেমনই নিজ ভূখণ্ডে অন্যের শোষণও মেনে নেয়নি; নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বুকের রক্ত ঢেলে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা, সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচনা হয়েছে অনেক সাহিত্য, নির্মাণ হয়েছে চলচ্চিত্র। তেমনই একটি চলচ্চিত্র জীবনঢুলী, যার প্রধান চরিত্র গড়ে উঠেছে নিম্নবর্ণের হিন্দু ঢুলী জীবনকে নিয়ে। ঢুলী জীবনকে নিয়ে তানভীর মোকাম্মেলের মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণের স্বরূপ দেখাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।
জীবনের জীবনঢুলী
জীবনঢুলীর কাহিনি গড়ে উঠেছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধের উত্তাপ তখন শহর ছেড়ে ছড়িয়েছে গ্রামেও। এ নিয়ে গ্রামের শিক্ষিত-সচেতন মানুষের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বাড়তে থাকে অনিশ্চয়তা-উৎকণ্ঠা। এরই মধ্যে একদিন পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে জীবনের গ্রাম পরাণপুরে। কিন্তু নির্মম এই হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই স্পর্শ করে না শিল্পী জীবনকে। তার টনক নড়ে আরো দুই দিন পর, যখন মাস্টার মশাইয়ের লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে সে। একপর্যায়ে প্রাণ বাঁচাতে সপরিবারে ভারতের শরণার্থী শিবিরে রওনা দেয় জীবন। সবাই গেলেও দেশ ছাড়তে রাজি হন না জীবনের কাকি; মা দুর্গার নামে সবাইকে বিদায় দিয়ে একাই থেকে যান নিজ ভিটায়। এদিকে পথিমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মারা যায় জীবনের স্ত্রী, সন্তান ও কাকা।
সব হারিয়ে নিঃস্ব জীবন যখন নিজ গ্রামে ফিরে আসে, তখন পুরো গ্রাম রাজাকারদের দখলে। এ সময় রাজাকার বাহিনীতে ড্রাম বাদকের দরকার পড়লে তাদের ক্যাম্পে ডাক পড়ে ঢুলী জীবনের। একে একে রাজাকারদের সব অপকর্মের নীরব সাক্ষী হতে থাকে সে। তারপর একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন ঘটে জীবনের গ্রামে, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে তারা মুক্ত করে এলাকা। জীবনও রাজাকারের ড্রাম ফেলে তুলে নেয় তার ঢোল। এভাবে জীবনঢুলীর কাহিনি যতো এগিয়েছে, ততই কেনো জানি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে সামগ্রিকতার সম্পর্ক; সঙ্কট বাড়তে থাকে মানবিক বোধের। যুদ্ধের সঙ্গে যোদ্ধার, যোদ্ধার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কিংবা ধর্মের সঙ্গে ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো সরে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। তার পরও জীবনঢুলী শেষ হয়, তবে একটা অতৃপ্তি নিয়ে।
পরাণপুর পোড়ে, জীবন ঢাক বাজায়
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে অসাম্প্রদায়িক বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার গতানুগতিক যে ন্যারেটিভ তা জীবনঢুলীতেও পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। মতুয়াদের আসরে ঢাক বাজিয়ে ফিরছে জীবন, নদীর ধারে ছেলেছোকরাদের হা-ডু-ডু খেলা দেখে একটুখানি দাঁড়ায় সেখানে। দর্শক সারিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গ্রামের হিন্দু-মুসলিম উভয়েই উৎসাহ দিচ্ছে খেলোয়াড়দের। সীমানা অতিক্রম করলেই এক পক্ষের খেলোয়াড়কে জাপটে ধরছে আরেক পক্ষ। একহাঁটু কাদায় জাপটা-জাপটিতে হিন্দু-মুসলিম একাকার। সেখানে দাঁড়িয়েই ‘জয় বাংলা’ স্লোগান শুনতে পায় জীবন। পাশ ফিরতেই দেখে, বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে¾‘জয় বাংলা’, ‘ছয় দফার সংগ্রাম চলছে চলবে’। খেলা দেখে আবার হাঁটা দেয় জীবন। পথে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বজলুর সঙ্গে দেখা হয় তার। আসন্ন দুর্গাপূজায় ঢাকের বায়না নিয়ে কথা বলতে ঠাকুর দাস কাকার বাড়িতে যাওয়ার কথা বজলুকে জানায় সে।
কাহিনির একপর্যায়ে দত্তবাড়ির দুর্গাপূজায় জীবনকে ঢাক বাজাতে দেখা যায়। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরাও উপস্থিত যথারীতি। শুধু তাই নয়, নমশূদ্রদের সঙ্গে একই সারিতে বসে প্রসাদও গ্রহণ করছে তারা। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে আবহমান বাংলার সাম্প্রদায়িক এই সম্প্রীতিতে টান পড়ে, যখন পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করে জীবনের গ্রামে।
জীবনঢুলীর ২৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ড থেকে ২৬ মিনিট ছয় সেকেন্ড পর্যন্ত পরাণপুরে নৃশংস গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় পুরো গ্রাম। বাড়ির উঠানে, পুকুর পাড়ে, রাস্তাঘাটে যেদিকেই চোখ যায়, শুধু লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। গণহত্যার ভয়াবহ এ উপস্থাপন এবং পরের দৃশ্যে কেবল জীবনের পরিবারের লোকজনদের নিজ বাড়িতে ফিরে আসা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, ওই গ্রামে খুব বেশি লোক বেঁচে নেই। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাড়ি ফিরে জীবনের পরিবার নিজেদের জীবন রক্ষার উপায় খোঁজার পরিবর্তে কেনো জানি আঙ্গিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। পাড়া-প্রতিবেশী কারা কী অবস্থায় আছে কিংবা এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে গ্রামের অন্যদের অবস্থা কী¾এ নিয়ে কোনো ধরনের বিচলিত হতে দেখা যায়নি জীবন কিংবা তার কাকা, কাকি, স্ত্রীকে! কাকি ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে ব্যস্ত, জীবনের স্ত্রী ব্যস্ত উঠান ঝাড়ু দেওয়া নিয়ে। পারস্পরিক সম্প্রীতির এই বাংলার মানুষেরা গ্রামবাসী-প্রতিবেশীর প্রতি এতো উদাসীন¾এর আগে কোনো বাংলা চলচ্চিত্রে এসেছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
গণহত্যার পরের দিনটি শুরু হয় রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় পুকুর থেকে জীবনের কাকির কলসিতে করে পানি আনার মধ্য দিয়ে। পরের দৃশ্যে দেখা যায়, পরিষ্কার সাজানো-গোছানো উঠানে জীবনের ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে আর জীবন দাওয়ায় বসে ঢাকে পাউডার মাখছে। আগের দিনের ভয়াবহতার কোনো চিহ্নই সেখানে পাওয়া যায় না! বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয় জীবন ও তার স্ত্রীর কথোপকথনে।
জীবনের স্ত্রী : ছেলে-মেয়েগুলো কাল থেকে কিছু খায়নি। ঘরে তো কিছুই নাই, বাচ্চা দুটোরে তো খাতি দিতে হবে। চাল-ডাল-তেল কিছু তো আনা লাগবি।
জীবন : আইজ কি আর হাট বসপেনে, তবু দাও দেহি যাই।
এ সময় জীবন ঢাক সঙ্গে নিয়ে হাটে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরেক দফা কথোপকথন হয়,
জীবনের স্ত্রী : আরে ওডা (ঢাক) আবার নেচ্চ ক্যান?
জীবন : যাওয়ার পথে একবার ঠাউর দাস কাহার ওই হানে হইয়া যাই, কোনো বায়না-টায়না আছে কি না?
জীবনের স্ত্রী : এই যুদ্ধের মধ্যি তোমার ঢাক বাজানো শুনবি কিডা?
জীবন : আর তো কোনো কাম শিহিনি, যাই ঢাকটা নিয়েই যাই।
পুরো গ্রাম মৃত্যুপুরী, চিরপরিচিত মানুষগুলো লাশ হয়ে পড়ে আছে যত্রতত্র¾এ নিয়ে ভাবনার লেশমাত্র নেই জীবন কিংবা তার পরিবারের। বিপরীতে জীবন যুদ্ধের মধ্যে বায়নার খোঁজে যাচ্ছে। এমনকি যার কাছে বায়নার খোঁজে যাচ্ছে, সেই ঠাকুরদাস কাকা বেঁচে আছেন কি না তা নিয়েও কোনো উদ্বেগ নেই জীবনের। এ কোন ৭১ দেখাতে চান তানভীর! চলচ্চিত্রের শুরুতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বাংলা দেখান তানভীর, তা দুই দিনের মাথায় অন্যরূপে ধরা দেয় তারই ক্যামেরায়।
মৃত্যু যেখানে দুয়ারে দাঁড়িয়ে, সেখানে বাজার করতে রাজাকার ক্যাম্পের সামনে দিয়েই হাটে যায় জীবন। যে হানাদাররা কয়েক ঘণ্টা আগে পরাণপুরকে শশ্মানে পরিণত করেছে, তাদের দোসরদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে জীবনকে হাটে যেতে দেখা যায়! পরের দৃশ্যে রাস্তায় জীবনের সঙ্গে দেখা হয় গ্রামের মাস্টার মশাইসহ আরো তিন জনের। এরা সবাই সাইকেলে চড়ে বেতন তুলতে ফকিরহাটে যাচ্ছে বলে জীবনকে জানায়। এই ফকিরহাটেই আস্তানা গেড়েছে পাকিস্তানি বাহিনী; যারা মাত্র ১২ ঘণ্টা আগে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তাদেরই গ্রামে। ৭১-এ যুদ্ধের এই দামামার মধ্যে গ্রাম-বাংলার মতমোড়ল খ্যাত এই স্কুল শিক্ষকরা যখন গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, পরামর্শ দিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর প্রাণ বাঁচিয়েছে¾এখানে তাদের অবিবেচকের মতো আচরণ করতে দেখা যায়। অবশ্য কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এর ফলও পান ওই শিক্ষকরা। তাদের প্রাণ দিতে হয় হানাদার বাহিনীর গুলিতে।
হাটে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে কথা হয়, ফেরার পথে তাদেরই লাশ পড়ে থাকতে দেখে প্রথমবারের মতো শঙ্কিত হয় জীবন। অথচ ঠিক ১২ ঘণ্টা আগে হানাদার বাহিনী গ্রাম জুড়ে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা কেনো জানি জীবনকে সামান্যতম বিচলিত করে না।
চলচ্চিত্র সবসময়ই কোনো না কোনো সময়কে ধারণ করে তার ফ্রেমে। তানভীরের জীবনঢুলীও এর ব্যতিক্রম নয়। জীবনঢুলীর সময় মুক্তিযুদ্ধ, যে যুদ্ধ এই বাংলার মানুষকে স্মরণকালের মধ্যে এক কাতারে এনেছিলো, মানবিকতার অসাধারণ সব উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলো। সবকিছুকে উপেক্ষা করে সেলুলয়েডে তানভীরের এ সময় ধারণ দর্শক হিসেবে বিচলিত হওয়ার মতো।
কী ‘তানভীর’ দ্যাখলাম চাচা!
কী দুগ্গা দ্যাখলাম চাচা
ব্যাল পাতা বোজা বোজা
জোড়া ব্যাল বাইন্দা দিছে
তাতে দ্যাহ রঙ লাগাইছে
দেখতে লাগছে মচৎকার
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি তখনো, একটা চাপা উত্তেজনা চারদিকে। এর মধ্যেই দত্তবাড়িতে চলছে মা দুর্গার ভজন। সেখানে উপস্থিত গ্রামের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ; আগেই বলেছি, এদের একটা বড়ো অংশ মুসলমান। প্রসাদ গ্রহণের পাশাপাশি চলছে নিজেদের মধ্যে শেখ মুজিব, ছয় দফা, নির্বাচন, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা। মণ্ডপে অন্যদের সঙ্গে হাজির হয় পরাণপুরের গফুর পাগলও। দুর্গার সামনে পাঁঠা বলি দেখে কিছুটা ভয়-বিরক্তি নিয়ে ফেরার পথে ছন্দে ছন্দে গফুর উপরের পঙ্ক্তিগুলো আওড়াতে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গফুর যা বলছে তা দেবী দুর্গার শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। যে দেবী দুর্গা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবতা, সেই দুর্গাকে ঘিরেই এমন পঙ্ক্তি! দুর্গা মায়ের স্তনের আকার, রঙ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা আপাত কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ একজন মুসলমানের মুখ দিয়ে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়লো কেনো তা ঠিক বোঝা যায় না। এর পরের একটি পঙ্ক্তিতে না হয় দুর্গার অসুর বধের কথা বলা হয়, কিন্তু আবার ঘুরে ফিরে আসে দুর্গা ও দুর্গাপূজার কথা।
এর আগে জীবনঢুলীর ১৪ মিনিট ২৯ সেকেন্ড থেকে ১৪ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডে পূজার প্রসাদ বিতরণের সময় একটি মিড শটে দেবী দুর্গার ফোরগ্রাউন্ডে দত্তবাড়ির বউকে রেখে একবার ফোকাস, ডি-ফোকাসে পরিচালক যা দেখান, তাতে জীবন যে দুর্গামাতার মতোই শ্রদ্ধার চোখে দত্তবাড়ির বউকেও দেখে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। জীবন যেখানে দত্তবাড়ির বউকে দুর্গার সমান ভক্তিভরে প্রণাম জানাচ্ছে; ঠিক সেইখানে স্বয়ং দেবীকেই কামুক চোখে দেখছে এক মুসলমান! আবার এই মুসলমানই কিছু সময় পরে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার রূপে নিজেদের কাম চরিতার্থ করতে ধরে নিয়ে যায় ওই হিন্দু নারীদের।
তার মানে যে মুসলমান দুর্গার অবমাননা করছে, সেই মুসলমানই পরে হিন্দু নারীদের ভোগের জন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এ দিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চান নির্মাতা? পুরো চলচ্চিত্রে বজলু ছাড়া এমন কোনো মুসলমান চোখে পড়ে না, যাকে ‘ভালো মুসলমান’ বলা যায়। ৯/১১’র মুসলমানিত্বের যে ফাঁড়া মুসলমানের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আজ থেকে ৪৪ বছর আগের ঘটনা উপস্থাপন করে জায়েজ করার একটা চেষ্টা তানভীরের আছে বলে মনে হয়েছে। সে কারণেই হয়তো জীবনঢুলীতে হিন্দুদের উপস্থাপন অসাম্প্রদায়িক থাকলেও, সাম্প্রদায়িক হয়েছে মুসলমান।
এছাড়াও দত্তবাড়িতে পূজার উৎসবে পরাণপুরের যে মুসলমানদের দেখানো হয়, তার সংখ্যা নেহায়েতই কম নয়। পরে তাদের একসঙ্গে বসে প্রসাদ নিতেও দেখা যায়। অসাম্প্রদায়িক বাংলার এ দৃশ্যায়নের কিছু সময় পরই পাকিস্তানি বাহিনী যখন পরাণপুরে গণহত্যা চালায়, সেখানে শুধু হিন্দুদেরই মরতে দেখা যায়। প্রাণ বাঁচাতে ভারতের উদ্দেশে যারা যাত্রা করে, রাজাকার যাদের তুলে নিয়ে যায়, যে নারীরা ধর্ষিত হয়¾তাদের বেশিরভাগই হিন্দু। বিপরীতে মুসলমানদের দেখা যায়, হত্যাকারী আর ধর্ষক হিসেবে। এছাড়া ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাকবাহিনীর গণহত্যার পর কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে জীবন যখন এক মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, তখন গৃহকর্তা জীবনকে ‘মালাউন’ বলে গালি দেয়। পুরো চলচ্চিত্রে কেবলই হিন্দু উপস্থাপন!
কিন্তু ৭১-এ পাকিস্তানিরা এই দেশে কেবল হিন্দু নিধনে নামেনি; বাঙালি উচ্ছেদে নেমেছিলো তারা। হিন্দু-মুসলিম উভয়ের রক্তে স্বাধীন হয়েছে এদেশ। সবাই জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকার জন্য লড়েছে, জীবন দিয়েছে। এমনকি পাকি মুসলমানরা তাদের কাম চরিতার্থ করতে একচুলও ছাড় দেয়নি মুসলিম নারীদের। ইতিহাস ঘাঁটলে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। অথচ সে ইতিহাসের উপস্থাপন নেই জীবনঢুলীতে!
বজলু পারলেও, জীবন কিন্তু পারেনি
পরাণপুরে তখন বর্ষা। বৃষ্টিতে গ্রামের শান্ত নদীর স্রোত বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে রাজাকারদের নৃশংসতা। পাকবাহিনীর হামলা আর রাজাকারদের সেই নৃশংসতায় গ্রাম প্রায় জনশূন্য। এরই মধ্যে নদীতে জাল ফেলেছে বজলু; নদীর ধারের গাছতলায় বসে মাছ ধরা দেখছিলো জীবন। নদীতে ছইওয়ালা একটি নৌকা দেখে পাড় থেকে ডাক দেয় ওত পেতে থাকা রাজাকাররা। বন্দুক তাক করে নৌকা থামিয়ে যাত্রীদের বেরিয়ে আসতে বলে। এরপর ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার। ভীতসন্ত্রস্ত পরিবার-কর্তা রাজাকারদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বলতে থাকে¾‘ভাই আমরা কোনো দোষ করি নাই, আমরা ... শহরে ছোটোখাটো একটা চাকরি করি। এ্যাহন গিরামের বাড়ি যাইতেছি ভাই, আমরা গিরামের বাড়ি যাইতেছি।’ এরপর মেয়ে দুটোকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে তুলে নিয়ে যেতে চায় রাজাকাররা। সন্তানের সমূহ বিপদ দেখে পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে বাবা, অন্যদিকে বুকফাটা আর্তনাদে আহাজারি করতে থাকে মা। কিন্তু কিছুতেই মন গলে না রাজাকারের; বাপের বুকে লাথি মেরে মেয়ে দুটোকে নিয়ে যায় তারা।
চোখের সামনে এ অন্যায় মেনে নিতে পারে না বজলু; প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়। তখন জীবন তাকে বাধা দিয়ে বলে, ‘বজলু, যাইস না বজলু।’ কিন্তু ‘জীবন’কে উপেক্ষা করে রাজাকারদের চোখে চোখ রেখে চড়া গলায় বজলু বলে, ‘অগো যাতি দাও, অগো যাতি দাও কলাম।’ কিন্তু বজলুর এ প্রতিবাদ সহ্য করে না রাজাকাররা, বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় তার বুক। আর ‘ড্রামা’র জীবন তা দেখে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।
একপর্যায়ে তার এ আচরণে কেনো জানি রাজাকাররাই রেগে যায়, গলায় গামছা বেঁধে টেনে এনে বন্দুকের বাট দিয়ে জীবনকে পেটাতে পেটাতে বলতে থাকে, ‘শালা কাঁদিস না ক্যা, কাঁদিস না ক্যা! বউ বাচ্চা মইরা শ্যাষ, তোর চোখে এক ফোঁটা পানি দ্যাখলাম না। ... তুই মানুষ, না অমানুষ!’ রাজাকারদের মতো দর্শকদেরও প্রশ্ন জাগে জীবনের এ আচরণে। শুধু স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুই নয়, চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা আট মিনিট ২১ সেকেন্ড থেকে এক ঘণ্টা নয় মিনিট ৪৩ সেকেন্ড পর্যন্ত পর পর শটে জীবনের সামনে যৌন নিপীড়নের শিকার কিশোরীর মায়ের আর্তনাদ, জনশূন্য ঘরবাড়িতে রাজাকারদের লুটপাট, কিংবা আরো পরে দত্তবাড়ির ‘দেবীতুল্য’ বউকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জীবনের নির্লিপ্ততা দর্শক দেখে!
তাহলে এই জীবনকে দিয়ে কী বলতে চান তানভীর! স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে জীবন এক মুসলমানের বাড়িতে গিয়ে দেদারছে ভাত খায়, নিজ বাড়ি ফিরে এসেও কাকির দেওয়া ভাত খায়, রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়, ঢোল ছেড়ে ড্রাম বাজায়, চোখের সামনে একের পর এক নির্মমতা মেনে নেয়। আবার সবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় রাজাকার ক্যাম্পে ‘দেবীতুল্য’ সেই নারীকে না বাঁচিয়ে জীবন ঢোল আনতে বাড়ি যায়; যখন ফিরে আসে, ততক্ষণে ক্যাম্প পুড়ে দত্তবাড়ির সেই দেবী নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন¾তখন জীবন ঢোল বাজায়। জীবনঢুলীর প্রধান এই চরিত্রটি এর মধ্য দিয়ে ঠিক দাঁড়ায় কি! উল্টো একজন শিল্পীর এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তার শিল্পীসত্তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যে জীবন একজন বাদক, একজন শিল্পী¾শিল্পীর সেই দৃঢ়তা নিয়ে জীবন হাজির থাকে না কোথাও।
৭১-এ বাংলার বহু কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, অনেকে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না করলেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। কেউ কেউ রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে টাকা তুলেছেন শরণার্থীদের জন্য। আবার ‘বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’র শিল্পীরা তো ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে মনোবল জুগিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের। কিন্তু এতসব উদাহরণের বিপরীতে কেনো জানি শিল্পী জীবন ‘‘নপুংসক’ ভাব নিয়ে উপস্থাপিত হন!
রোগীর হিন্দু-মুসলমান না থাকলেও
তানভীরের আছে
জীবনের মতো শত শত পরিবার, হাজারো মানুষ প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে ভারতের শরণার্থী শিবিরে। সে যাত্রায় অন্য অনেকের সঙ্গে সামিল হয়েছেন ফকিরহাটের রতনলাল চক্রবর্তী। ডাক্তারি বিদ্যাটা জানা থাকায় দীর্ঘ যাত্রায় অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। পথে বেশ কয়েকবার রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার পরও প্রাণে বেঁচে যান তিনি। বিস্তীর্ণ প্রান্তর-নদী-মৃত্যুভয় সব ডিঙিয়ে অনিশ্চিত যাত্রা যখন প্রায় শেষ, ঠিক সেই সময় তাকে খুঁজতে আসা গ্রামের দুই যুবকের কাছে জানতে পারেন, ডাক্তারের অভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না তার গ্রামের মানুষ। সামনে ‘ইন্ডিয়া’ খচিত কংক্রিটের পিলারটুকু পেরোলেই নিরাপদ জীবনের হাতছানি, আর পিছনে মৃত্যুর বিভীষিকা। এ রকম পরিস্থিতিতে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নিজ গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা দিতে ফিরে যান রতনলাল। হয়তো রতনলালের অবস্থান থেকে এটিই তার মুক্তিযুদ্ধ।
কিন্তু এই রতনলালও তো হিন্দু। জীবনঢুলীতে যেভাবে একের পর এক মুসলমানের নেতিবাচক উপস্থাপনের বিপরীতে সব ভালো হিন্দুকে দেখানো হয়, ডাক্তারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটাননি নির্মাতা। এই ডাক্তার আবার এতটাই অসাম্প্রদায়িক, যার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনো তফাতই নেই। যে কারণে সহযাত্রীদের একজন ডাক্তারকে সতর্ক করে যখন বলে, ‘আপনার গিরামে মুসলমান ছাড়া তো আর কেউ নেই’; তার উত্তরে ডাক্তারকে বলতে শোনা যায়, ‘রোগীর আবার হিন্দু-মুসলমান কী?’
ফিরে যেতে উদ্যত হলে ডাক্তারকে উদ্দেশ করে একজন সহযাত্রী আবার বলে ওঠে, ‘ঠাউরের মরার স্বাদ অইছে।’ সহযাত্রীর কথায় স্পষ্ট হয়, গ্রামে মুসলমান রাজাকার থাকায় বিপাকে পড়েছে হিন্দুরা। এমনকি ডাক্তারের নিজের জীবনও নিরাপদ নয় সেখানে। অথচ, ‘‘বিপজ্জনক’ সেই মুসলমানদের চিকিৎসা দিতেই গ্রামে ফিরছেন ডাক্তার। অর্থাৎ, যে মুসলমান হিন্দুদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে, সেই মুসলমানেরই চিকিৎসা দিতে যাচ্ছে এক হিন্দু। হিন্দু এই ডাক্তারকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হিসেবে দেখালেও অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেননি তানভীর নিজে। যে কারণে জীবনঢুলীর মুক্তিযুদ্ধে ঘুরেফিরে কেবল অত্যাচারিত হিন্দুরাই হাজির হয়।
মুক্তিবাহিনী যেনো ফর্মুলা চলচ্চিত্রের নায়ক
ভারতের শরণার্থী শিবিরে যাত্রা করা কিছু মানুষকে নিয়ে রওনা দিয়েছে একটি নৌকা। অন্য অনেকের সঙ্গে দুই যুবককেও দেখা যায় সেখানে। জীবনঢুলীর ৪৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে নৌকার এক যাত্রীর সঙ্গে শার্ট-প্যান্ট পরা শহুরে ওই যুবকদের কথোপকথনে জানা যায়, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যাচ্ছে তারা। প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হয়। এর কিছু পরেই রাজাকারের হামলার শিকার হয় নৌকাটি। যাত্রীদের মারধর করে সর্বস্ব কেড়ে নেয় তারা, সেই সঙ্গে তুলে নিয়ে যায় যাত্রাদলের এক নারী শিল্পীকে। এ সময় যুবকদের একজন এর প্রতিবাদে উদ্যত হলে আরেকজন তাকে বাধা দিয়ে বলে, ‘আমাদের সময় এখনো আসেনি।’
এরপর এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ডে সূর্যাস্তের দৃশ্যকে রেখে প্রথমবারের মতো কয়েকজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। এক ঘণ্টা ২৯ মিনিট ২৩ সেকেন্ডের জীবনঢুলীতে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় বারের মতো দেখা যায় এক ঘণ্টা ১৮ মিনিট নয় সেকেন্ডে। চলচ্চিত্রের একদম শেষ পর্যায়ে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করতে পরাণপুরে আসে তারা। আক্রমণের জন্য নজর রাখতে থাকে ক্যাম্পের ওপর। চারদিক থেকে তারা ঘিরে ফেলে রাজাকার ক্যাম্প। একপর্যায়ে ‘সফল’ভাবে’ আক্রমণের মধ্য দিয়ে রাজাকারদের নির্মূল করে পরাণপুরকে মুক্ত করে তারা।
প্রথম কথা হলো, মুক্তিযুদ্ধ ছিলো একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। ২৫ মার্চ কালো রাতের মধ্য দিয়ে যার সশস্ত্র রূপ দেখা যায়। যুদ্ধের এই প্রক্রিয়া হঠাৎ করে শুরু হয়নি, পোড় খাওয়া নির্যাতিত আপামর জনসাধারণ নিজ থেকে সশস্ত্র এ সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। অনেকে সম্মুখ সমরে না থাকলেও খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, পথ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এই সংযোগ চোখে পড়ে না জীবনঢুলীতে। আবার মুক্তিযুদ্ধ তো সাধারণ কোনো যুদ্ধ ছিলো না, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এ যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো মানবিকতা। মানবিকতার সেই বোধ থেকেই হাজারো কৃষক-শ্রমিক-জনতা মা-মাটি-মানুষকে স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে। এমনকি সহযোদ্ধাকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার মত নজিরও আছে অসংখ্য। সেই মানবিকতার লেশমাত্র দেখা যায় না জীবনঢুলীতে।
সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা উপস্থাপনের দ্বিতীয় পর্বে চলচ্চিত্রের একেবারে শেষ মুহূর্তে যেভাবে তারা পর্দায় হাজির হন তাতে ফর্মুলা চলচ্চিত্রের সব শেষের মারপিটের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে শেষ মুহূর্তে ভিলেনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিপদগ্রস্তদের উদ্ধার করে ‘সুপারম্যান’ নায়ক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ তো তা ছিলো না। নায়ক ‘‘সুপারম্যান’ হয়ে আসলেন আর সব জয় করে নিলেন! একটা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে নয় মাস যুদ্ধ করেছে আমাদের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের সেই সামগ্রিকতা জীবনঢুলীতে অনুপস্থিত।
এছাড়া যে পরাণপুরকে পাকিস্তানি বাহিনী কয়েক ঘণ্টায় লাশের ভাগাড়ে পরিণত করেছিলো, সেই গ্রামের কাউকে যুদ্ধে যোগ দিতে দেখা যায় না। বিপরীতে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, দেখে মনে হয়, বজলু আর গফুর পাগল ছাড়া ওই গ্রামের সব মুসলমান রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে; আর হিন্দুরা সবাই পাড়ি জমাচ্ছে শরণার্থী শিবিরে। অথচ জীবনঢুলীর কাহিনি গড়েই উঠেছে ঢুলী জীবন ও তার গ্রাম পরাণপুরের নির্যাতিত ভাগ্যাহত মানুষকে কেন্দ্র করে। তানভীর সেই মানুষগুলোকে হিন্দু আর মুসলমানে ভাগ করে যুদ্ধে পাঠালেন কেবল শহুরে দুই যুবককে!
নির্মাণের অসাবধানতা ও অন্যান্য
বাড়ির আঙিনায় বসে মাছ কাটছে জীবনের স্ত্রী। কৈ মাছগুলো তখনো তাজা। এরই মধ্যে জীবনের গ্রামে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে সন্তানদের নিয়ে নিরাপদে আত্মগোপন করে জীবনের স্ত্রী। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পাক বাহিনী যখন চলে যায়, তখন গ্রাম জুড়ে পড়ে থাকে শত শত প্রাণহীন দেহ। জীবনেরাও বাড়ি ফিরে দেখে, তাদের আঙিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মরে পড়ে আছে সেই কৈ মাছগুলো। প্রতীকের এ ব্যবহার প্রশংসনীয়।
পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সময় পাড় থেকে লাফিয়ে পুকুরে আশ্রয় নেয় এক নারী। লাফিয়ে পড়ার এই দৃশ্য এতটাই জীবন্ত ছিলো যে, দর্শককে তা ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। কোনোভাবেই এটাকে অভিনয় বলে মনে হয়নি। তবে খটকা লাগে চলচ্চিত্র শুরুর ছয় মিনিটের মাথায় দেখানো ছয় দফার মিছিল নিয়ে। সেই মিছিলে অধিকাংশ মুসলমান হলেও হিন্দু ছিলো হাতেগোনা। অথচ, হিন্দু-প্রধান এলাকায় সংঘটিত এই মিছিলে মুসলমানের সংখ্যা বেশি থাকার কথা নয়।
হাট থেকে ফেরার পথে চলচ্চিত্রের ৩২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে জীবন যখন মাস্টার মশাইয়ের গুলিবিদ্ধ লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে, তখনো ঘুরতে থাকে তার পাশেই পড়ে থাকা সাইকেলের চাকা। অথচ মাস্টার মশাইয়ের মরে পড়ে থাকা দেখে মনে হয়, তাদেরকে গুলি করার ঘটনা আরো বেশকিছু আগের। এক্ষেত্রে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে¾হয় পরিচালক মুন্সিয়ানা দেখাতে সাইকেলের চাকা ঘুরতে দেখিয়েছেন। আর যদি মারা যাওয়াটা কিছুক্ষণ আগেরও হয়ে থাকে, তাহলেও তো জীবনের সেই গুলির আওয়াজ শোনার কথা। অথচ এখানে তার কিছুই বোঝা যায় না, কেবল সাইকেলের চাকা ঘোরে। সাইকেলের চাকা ঘোরা, গুলিবিদ্ধ হয়ে মাস্টারের মৃত্যু এবং দৃশ্যপটে জীবনের উপস্থিতি¾এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের বিষয়টি চলচ্চিত্রে আরো স্পষ্ট করলে ভালো হতো।
সঙ্কট আছে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থাপন নিয়েও। রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার শুরু থেকে শেষ অবধি মুক্তিযোদ্ধাদের যে দৃশ্যায়ন, সেখানে তাদেরকে দেখা যায় এলোমেলো গুলি চালিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে দৌড়াতে। অনেকটা ১৬ ডিসেম্বর কিংবা ২৬ মার্চসহ জাতীয় দিবসগুলোতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা যেমন মুক্তিযোদ্ধা সেজে ডিসপ্লেতে অংশ নেয়। জীবনঢুলীর মুক্তিযুদ্ধ তো ভিজ্যুয়াল ইতিহাস, শিশুদের ডিসপ্লে নয়।
এছাড়া শিল্পনির্দেশনারও কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। ভারতের শরণার্থী শিবিরে যাত্রাপথে প্রথম বিরতিতে সবার জিরিয়ে নেওয়ার দৃশ্য দেখানো হয় লঙ শটে, প্যান করে। এ সময় গাছের ডাল বেয়ে ক্যামেরা যখন টিল্ট ডাউন করে শরণার্থীদের কাছে যায়, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না গাছের ডালে পাতাগুলো কৃত্রিমভাবে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। কড়ই গাছের মূল কাণ্ডের প্রধান শাখায় যে পাতা থাকে না, সেটা হয়তো শিল্পনির্দেশক ভুলে গেছেন!
শুধুই দূরে সরে যাওয়া
সেলুলয়েডে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন নয়। সেই ওরা ১১ জন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে ফিকশনের শুরু তা আজ অবধি চলমান। ফলে অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের গ্রান্ড-ন্যারেটিভ তৈরিতে চলচ্চিত্রের ভূমিকাও অনেক। তাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র মূল্যায়নে, তৈরি হওয়া সেই গ্রান্ড-ন্যারেটিভ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পথ আগলে দাঁড়ায়। তাতে যে সমস্যা হয় না তা নয়, তবে শেষ পর্যন্ত উতরানো যায়। যদিও মেহেরজান তা পারেনি। মেহেরজান লাল ফিতায় না আটকিয়ে, একাকার হয়েছে সবুজ-হলুদে। ফলে এখন আর কেউ সাহস দেখানোর সাহস পান না। তাই গ্রান্ড-ন্যারেটিভের মধ্যেই বেশিরভাগ নির্মাতার নাচনকোঁদন। কিন্তু জীবনঢুলী কেনো জানি সেই গ্রান্ড-ন্যারেটিভ থেকেও বেশ খানিকটা দূরে অবস্থান করছে। ভাঙা তো দূরের কথা, গ্রান্ড-ন্যারেটিভকে ছুঁতেও পারেনি।
ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়তো এসেছে, সামগ্রিকতা আসেনি। তাতে জেঁকে বসেছে বিচ্ছিন্নতা ও অসামঞ্জস্যতা। এই বিচ্ছিন্নতা কখনো হিন্দু-মুসলিমের উপস্থাপন, সম্পর্ক ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত, আবার কখনো তাকে ভুগতে হয়েছে সাধারণ মানবিক দীনতায়। এই দেশটির সবচেয়ে বড়ো অর্জন নিয়ে তানভীর মোকাম্মেল কীভাবে জানি দেশের টাকাতেই (জীবনঢুলী সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত) সবচেয়ে বড়ো ফাজলামিটা করেন। ফলে সরকারের টাকায় একটা চলচ্চিত্র হয়তো হয়, কিন্তু তা জনগণের হয় না।
লেখক : তৌফিকুর রহমান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী।
taufiq19mcjru@gmail.com
বি. দ্র. প্রবন্ধটি ২০১৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত ম্যাজিক লণ্ঠনের ৯ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন