জাহাঙ্গীর আলম
প্রকাশিত ১৯ আগস্ট ২০২৩ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রের আকর গ্রন্থ : চলচ্চিত্রের অভিধান
জাহাঙ্গীর আলম

দর্শক-শ্রোতা নিজ নিজ শিক্ষা অভিজ্ঞতা দিয়ে যেকোনো বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ ও বোঝার চেষ্টা করেন। যেকোনো শিল্প (আর্ট) যেমন-চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তবে শিল্পরস আস্বাদনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতোটা দরকার তা একটি বিতর্কের বিষয়। সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকলেও যে একজন শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী হবেন একথা বলা যায় না। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষেরও শিল্পের প্রতি ঝোঁক থাকতে পারে। বাউল-ফকিরদের দর্শন, চর্চা ও সঙ্গীতসাধনা থেকে তা টের পাওয়া যায়।
স্থিরচিত্র থেকে চলমান চিত্রের উদ্ভব। সেকেন্ডে ২৪টি ফ্রেম চোখের সামনে দিয়ে গেলে তা আর আলাদা করা যায় না। তাই চলচ্চিত্রের উদ্ভব যেনো অনেকটাই ভ্রান্তি দিয়ে। তবে এ-তথ্য জানা না থাকলে যে চলচ্চিত্র উপভোগ করা যায় না, তা নয়। এ-তো গেলো চলচ্চিত্রের প্রযুক্তিগত দিকের একেবারে গোড়ার কথা। শিল্পের এ-নবীন শাখাটি মূলত প্রযুক্তি-নির্ভর। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চলচ্চিত্র বিকশিত হতে থাকে। ক্রমেই আলাদা শিল্পমাধ্যম হিসেবে তা জায়গা করে নিয়েছে। চলচ্চিত্রকে আগে পপুলার আর্ট হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর মাধ্যমে জীবনঘনিষ্ঠ, সূক্ষ্ম-মনস্তত্ত্ব ও জটিল চরিত্রেরও রূপায়ণ হয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে বিতর্ক হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সত্যজিৎ রায়ের মতো মহান চলচ্চিত্রকারদেরও কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্থবিনিয়োগ ও তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থেকে এ-মাধ্যমের অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয়েছে। এসব না জেনেই কেউ যদি সমালোচনা করেন তবে তা চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতি অনেকটাই অবিচার হবে। তবে শুধু সমালোচনা নয়, কোনো চলমান ছবি দেখে কারও এ-মাধ্যম সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হতে পারে। কেউ যদি এর বৈশিষ্ট্য, শিল্পের অন্যান্য শাখা থেকে পার্থক্য জানতে চান, তার জন্য ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত চলচ্চিত্রের অভিধান গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য।
চলচ্চিত্রের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত ৪২৬টি বর্ণানুক্রমিক প্রসঙ্গের এক সংকলন চলচ্চিত্রের অভিধান। এরমধ্যে সিনেমার পরিচয় নিয়ে ৭৯টি, সিনেমার ধরন নিয়ে ২৫টি, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখার ১৩টি, টেকনিক বিষয়ে ২৭টি, টেকনোলজিক্যাল প্রসঙ্গে ২৭টি, চিত্র প্রযোজনাকারী দেশ সম্পর্কে ২৪টি, চিত্রপরিচালক নিয়ে ১২৫টি, কলাকুশলী/শিল্পী/সমালোচক ইত্যাদি প্রসঙ্গে ৪৬টি এবং বিবিধ অনুষঙ্গ নিয়ে ২৯টি লেখা রয়েছে। এতে ৪০ জন সমালোচকের লেখা স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে ১৬ জন বিদেশিও রয়েছেন। এ হিসাবে অভিধানটি আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করেছে। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত এ-বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ ও মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিটি যুগ বা কালপর্বেরই একটি নির্দিষ্ট শিল্পমাধ্যম থাকে। মোটামুটিভাবে চলচ্চিত্রকে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর শিল্পমাধ্যম। এখন তা সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ। টেলিভিশন ও ভিডিওকে বলা যায়, চলচ্চিত্রেরই এক প্রকার প্রসারণ। চলচ্চিত্র মৌলিক মাধ্যম নয়, অন্য সব মাধ্যম থেকে অকৃপণভাবে আত্মসাৎ করে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। চলচ্চিত্রকে আলাদা শিল্প হিসেবে দাঁড় করাতে এর চিত্রপরিচালকরা রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চলচ্চিত্রের অভিধান-এ সংকলনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন পরিচালকরা।
চলচ্চিত্রের আদি প্রদর্শকদের মধ্যে আমেরিকান চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক ডেভিড ডব্লিউ গ্রিফিথ অন্যতম। ১৯০৮ সালে তিনি চলচ্চিত্রে মনোনিবেশ করলেও ১৯১৫-তে দি বার্থ অব এ নেশন-র মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা করেন। গ্রিফিথ বর্ণনা রীতিতে বিভিন্ন স্তরের প্রচলন করেন; কাহিনীকে ছোট-ছোট দৃশ্য ও পর্যায়ে ভাগ করে নেন, দৃশ্যাংশের সমবায় ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে গল্প, নাটকীয়তা ও বক্তব্যের ওপর গুরুত্ব দেন, অভিনয়কে চলচ্চিত্র-সুলভ করার চেষ্টা করেন। ক্যামেরার প্রয়োজন মতো স্থান পরিবর্তন তার ছবিকে চিত্রধর্মী করে তোলে। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আরেক দিকপাল সের্গেই আইজেনস্টাইন। তিনি শুধু চিত্রপরিচালকই নন, একই সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। তার ছবিতে মন্তাজের প্রয়োগ নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছে। মূলত চলচ্চিত্রের নতুন রীতি ও ভাষা দিয়ে এ-শিল্পের বাঁক বদল করেছেন বেশ কয়েকজন চিত্রপরিচালক। এ-ধারা প্রবাহমান রেখেছেন আরও অনেকে।
সাধারণভাবে বলা হয়, যদি বিশ শতকের ৫০-এর দশককে ইতালির নিওরিয়ালিজম, ৬০-এর দশককে ফ্রান্সের নুভেল ভাগ, ৭০-এর দশককে নতুন জার্মান চলচ্চিত্রের, ৮০-এর দশককে চীনা চলচ্চিত্রের বিশ্বজয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; তবে ৯০-এর দশক হবে ইরানসহ তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দশক। জাতিরাষ্ট্রের যুগে যেকোনো বর্গীকরণ বা আলোচনা দেশভিত্তিকভাবে এগিয়ে চলে। চলচ্চিত্রের অভিধানেও ২৪টি দেশের সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তি ও বিনিয়োগনির্ভর শিল্পমাধ্যম হিসেবে শিল্পায়িত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে চলচ্চিত্র বিকশিত হয়েছে বেশি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র বিশেষ সহায়তা পেয়েছে। এর বাইরে আফ্রিকা ও ইরানের চলচ্চিত্রও বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন কলোনিয়াল অঞ্চলে ইউরোপিয়রা তথ্যচিত্র তৈরি করে ইউরোপে দেখাতো। যুদ্ধের পর এ-ধরনের কাজ কমে গেলো। শুরু হলো টারজান ফিল্মের যুগ-যেখানে বন্য আফ্রিকাকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের খদ্দেরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। তাই আফ্রিকান চিত্রপরিচালকদের এ-প্রথাগত গৎবাঁধা চিত্রের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই প্রতিবাদ করতে হয়েছে। এ-কারণে সেনেগালের প্রখ্যাত পরিচালক উসমান সেমবেন একসময় বলেছিলেন, আফ্রিকাতে ছবি করাটাই একটা রাজনৈতিক কাজ।
সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও চলচ্চিত্র এবং এর আন্দোলন যে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হয় তা ইরানের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায়। ইরানি সমাজব্যবস্থায় শোষণ, নিপীড়ন, সংস্কার ও অবক্ষয়ের চেহারাটা প্রথম ফুটে ওঠে দারিয়ুস মেহেরজুই এর ছবিতে। শাহ সরকারের পতন ও ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর চলচ্চিত্রের অন্যতম বিষয় ছিলো প্রগতিশীলতা বনাম মৌলবাদের দ্বন্দ্ব। নব্বইয়ের দশক-কে ইরানি চলচ্চিত্রের নব জাগরণের যুগ বলা যায়। মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্কট-এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে নতুন পরিচালকদের অনেকের ছবিতে।
আগেই বলেছি, চলচ্চিত্র মূলত প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম। চলচ্চিত্রের অভিধান-এ টেকনিক ও টেকনোলজিক্যাল প্রসঙ্গে ২৭টি বিষয় সংযুক্তি রয়েছে। এতে ফিল্ম, লেন্স, ক্যামেরা থেকে শুরু করে এডিটিংয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডিজিটাল চিত্রনির্মাণ চলচ্চিত্রকারের হাতে তুলে দিয়েছে নতুন নতুন প্রাযুক্তিক সুবিধা এবং অভূতপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ। এ-বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রয়েছে আর্কাইভে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্ন কারিগরি দিক।
এ-গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে ৭৯টি চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ধীমান দাশগুপ্ত বলেছেন, ‘‘বাণিজ্যিক ও হলিউডের ছবির চেয়ে বেশি জোর পড়েছে ইউরোপীয় ও সিরিয়াস ফিল্মের ওপর।’ এর মধ্যে গ্রিফিথের বার্থ অব এ নেশন, ইনটলারেন্স; আইজেনস্টাইনের আইভান দ্য টেরিবল, আলেকজান্ডার নেভস্কি, ব্যাটলশিপ পটেমকিন উল্লেখযোগ্য। কুরোশাওয়ার রশোমন, সেভেন সামুরাই রয়েছে। এ-ছাড়া সায়েন্সফিকশন সিনেমা কুব্রিকের ২০০১-এ স্পেস ওডিসি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ও শ্যাম বেনেগালের সিনেমা রয়েছে। ব্যতিক্রমী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন উদয় শঙ্কর। ভারতীয় নৃত্যকে ভিত্তি করে তার কল্পনা ছবিটিকে একই সঙ্গে তথ্যচিত্র, শিল্পবিষয়ক চিত্র ও পরীক্ষামূলক চিত্র বলা যায়। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপু-ত্রয়ীর মধ্যে রয়েছে পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং অপুর সংসার। এরমধ্যে পথের পাঁচালী সত্যজিতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র। শৈল্পিকসাফল্য ও প্রভাব বিচারে এই ছবিটি ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রও বটে। তবে সম্পাদকের মতে, দৃশ্যগঠন, সঙ্গীত ও আবহধ্বনি, অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে চারুলতা সত্যজিতের শ্রেষ্ঠ ছবি। ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক ও সুবর্ণরেখা এ-সীমিত তালিকায় রয়েছে। অযান্ত্রিক-এ একটি মানুষ একটি গাড়িকে ভালোবেসেছে-এই সহজ কাহিনী শেষ পর্যন্ত দেখায় মানুষ ও যন্ত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক।
চলচ্চিত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গের অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৫টি আলোচনা। এতে চলচ্চিত্রের সঙ্গে কবিতা, চিত্রকলা, নাটক, সঙ্গীতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ-ছাড়া ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও নৃতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জর্জ গাবনারের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায়, চলচ্চিত্রে ক্রমেই সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র সমাজ জীবনে যে-প্রভাব ফেলছে বিভিন্ন গবেষণায় তা দেখা যায়। বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতির বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি। আর এই বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে পর্নোগ্রাফি। তা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে সিনেমার ধরন শাখায়।
চলচ্চিত্রের অভিধান গ্রন্থটিতে সূচিপত্রে প্রথমে বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর অক্ষর অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে। এরপরও নির্ঘণ্ট থাকলে যেকোনো বিষয় আরও সহজে খুঁজে পাওয়া যেতো। এ-অভিধানে পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সমালোচকদের অনেককে স্থান দেওয়া হলেও সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক ও সঙ্গীত-পরিচালকদের স্থান দেওয়া হয়নি। এ-ক্ষেত্রে সম্পাদকের কৈফিয়ত-‘পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা মনে রেখে এই গ্রন্থ একটি নির্দিষ্ট আকার ও মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।’ তবে অভিধান রচনার কাজটি চলমান প্রক্রিয়া। আগামীতে নতুন-নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হবে বলে আশা করা যায়।
বইয়ের নাম : চলচ্চিত্রের অভিধান
সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত
প্রকাশক : অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, কলকাতা
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮১
তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬
মূল্য : ৯০০ টাকা
লেখক : জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। বর্তমানে দৈনিক বণিক বার্তায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।
alam_rumc05@yahoo.com
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১২ সালের জুলাইয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন


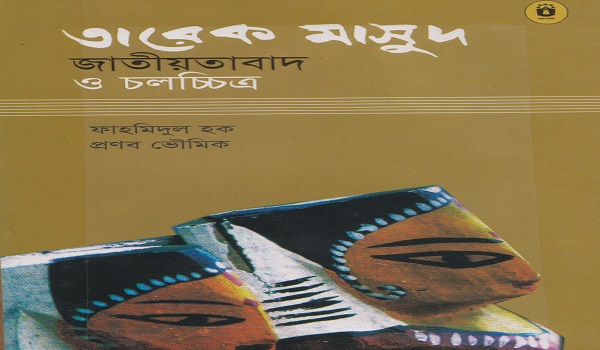
1735263359.jpg)



