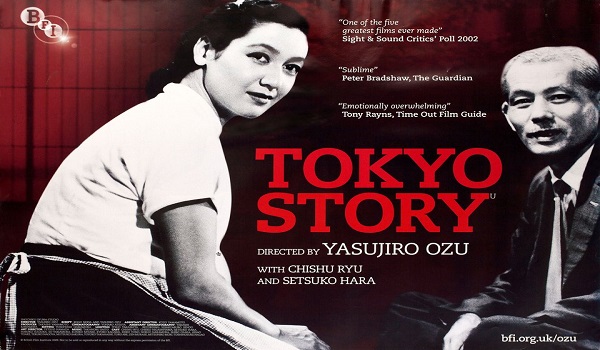হালিমা খুশি
প্রকাশিত ১৯ আগস্ট ২০২৩ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
ফ্ল্যাহার্টি : সেলুলয়েডের সংগ্রামী এক মানুষ
হালিমা খুশি

সালটি ১৮৯৫। পৃথিবী যেনো তার ইতিহাসের পাতাটি খুলে বসেছিলো কখন লিপিবদ্ধ করবে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের কথা। হ্যাঁ এই অষ্টম আশ্চর্যটি আর কিছু নয়, চলচ্চিত্র। আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি ১৯ মার্চ। ধারণা করা হয় এই দিনে প্রথম শ্যুট করা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে ৪৬ সেকেন্ডের একটি চলচ্চিত্র। সেই থেকে পথ চলা শুরু চলচ্চিত্রের। দুই বছরের মাথায় ১৮৯৭ সালে এই চলচ্চিত্রের পথযাত্রী হয় প্রামাণ্যচিত্র। আর এই প্রামাণ্যচিত্র যার হাত ধরে এসেছে তাকে নিয়েই আমাদের এবারের আলোচনা ।
না্ম : রবার্ট যোশেফ ফ্ল্যাহার্টি
জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪, যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের আইরন মাউন্টেন
প্রথম প্রামাণ্যচিত্র : নানুক অব দ্য নর্থ (১৯২২)
উপাধি : প্রামাণ্যচিত্রের জনক
অবদান : প্যানক্রোমাটিক ফিল্ম এর প্রবর্তক
মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ১৯৫১ সাল
প্রকৃতির চিরন্তন সজীবতায় বেড়ে ওঠা বালকটি ছোটবেলা থেকেই ছিলো প্রকৃতির মতোই প্রাণচঞ্চল। শীতের শীতলতায় পুরো এলাকায় বরফ জমতো তার বেড়ে ওঠা শহর আইরন মাউন্টেনে। সেই বরফের আস্তরণে দুরন্ত স্কিতে ছুটে বেড়াতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই দুরন্তপনার মাঝে লুকিয়ে ছিলো তার অনুসন্ধানী মন। তাইতো কিশোর বয়সেই খনিজ বিশেষজ্ঞ বাবার সঙ্গে উত্তর আমেরিকার হাডসন, বাফিন দ্বীপ এবং সুমেরু অঞ্চলের খনি অভিযানে যোগ দেন। যে-অভিযান তাকে করেছিলো সমৃদ্ধ; খুলে দিয়েছিলো সম্ভাবনার দ্বার। তিনি আর কেউ নন; প্রামাণ্যচিত্রের জনক রবার্ট যোশেফ ফ্ল্যাহার্টি।
পৃথিবীর অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের মতো তিনিও ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন। তার আগ্রহ ছিলো নতুন কিছুতে। আর ঠিক এ-কারণেই স্বাভাবিক সময়ের বেশ দেরিতে মিশিগান কলেজে খনিজ বিদ্যায় ভর্তি হন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, সেখানেও তিনি তার মন বসাতে পারেননি; পারেননি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে। কারণটি আর কিছু নয়, টানা অনুপস্থিতি। শাস্তিস্বরূপ তাকে মিশিগান কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি তার নতুন কিছুর সন্ধানে। নিরন্তরভাবে ছুটে চলেছেন তার মনের পথে। যার মন পড়ে রয় যতোসব দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের সন্ধানে, তিনি কী আর খনির সন্ধানে মগ্ন থাকতে পারেন। তাইতো খনির সন্ধান করতে করতে উত্তর মেরুতে বসবাসকারী এস্কিমোদের জীবন প্রণালী, রীতি-নীতি তার মনের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন, ক্যামেরায় বন্দি করবেন এমন সব বিষয় যেগুলোর দিকে অন্য কেউ ক্যামেরা তাক করতে পারেনি। তাইতো প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গে যুদ্ধ করা পাহাড়, জঙ্গল, বরফের মধ্যে বাস করা মানুষদের তুলে নিতে চেয়েছেন তার সেলুলয়েডের ফিতায়।
এই কথাটির প্রতিধ্বনি যেনো খুঁজে পাই ব্রিটিশ ফিল্ম একাডেমির প্রথম পরিচালক রজার ম্যানভেল এর বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘ফ্ল্যাহার্টি ছিলেন সাধারণ সাদামাটা মনুষ্য জগতের অভিজাত এক ধরনের কবি সুলভ নৃতাত্ত্বিক। এমন একজন মানুষ যার নিজস্ব প্রকৃতি তাকে তুষার, সমুদ্র, পাহাড় বা জলাভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশে নিঃসঙ্গ বসবাসকারী কোন সনাতন জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে বসবাস করতে করতে ছবি তৈরীতে অনুপ্রাণিত করতো।’১ আর এই অনুপ্রেরণা তাকে নিয়ে যায় নতুন এক উচ্চতায়। তিনি ১৯২০ সালের জুন মাসে কানাডায় রেভিলন ফার কোম্পানির (খনিজ অনুসন্ধান কোম্পানি) পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর মেরুর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত এস্কিমোদের জীবনচিত্র তুলে আনেন। নির্মাণ করেন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্যচিত্র নানুক অব দ্য নর্থ। তার এই সফল সৃষ্টি তাকে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে সম্মানিত করে।
আগেই বলেছি এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ এতোটা সহজ ছিলো না তার জন্য। অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াতে হয়েছে তাকে। ফ্ল্যাহার্টি এস্কিমোদের জীবন প্রণালীর ওপর একে একে ৭০ হাজার ফিট ছবি শ্যুট করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস নিজের সিগারেটের আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এই পুরো ফিল্ম। এ-যেনো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতো। যে-মানুষটির চিন্তার জগতের অধিবাসী সেই সব সংগ্রামী মানুষ, যাদের জীবনে প্রতিটি চাহিদা সংগ্রাম করে পূরণ করতে হয়; যার প্রাণের রসদ ওই মানুষগুলোর সংগ্রামী জীবন; সেই মানুষটিকে হতাশা বোধের শিকলে আটকে রাখবে এমন সাধ্য কারও কি আছে? তাইতো তিনি অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে পুঁজি করে আবারও বেরিয়ে পড়েন উত্তর মেরুতে; ধারণ করেন এস্কিমোদের জীবন-প্রণালী। এখানেই শেষ নয়, প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শনের জন্য তাকে ঘুরতে হয়েছে পরিবেশকদের দ্বারে দ্বারে। অবশেষে ফরাসি একটি সংস্থা এই ছবিটি পরিবেশনের দায়িত্ব নেয়। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, ছবিটি আমেরিকাতে প্রথমে তেমন কোনো সাড়া ফেলতে পারেনি। কিন্তু লন্ডন, প্যারিসে এবং পরে বার্লিন ও রোমে সমাদৃত হবার পর আমেরিকাতে এটি সমাদৃত হয়।
প্রথম প্রামাণ্যচিত্রের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২৬ সালে তিনি নির্মাণ করলেন মোয়ানা : এ রোমান্স অব দ্য গোল্ডেন এজ। ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ছবিটির নির্মাণ কাজ চলে।এই সময়ের মধ্যে তিনি দ্য পটারি মেকার (১৯২৫) নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। মোয়ানা তথ্যচিত্রে ফ্ল্যাহার্টি মোয়ানা দ্বীপের অপরূপ সৌন্দর্য এবং এখানে গড়ে ওঠা পলিনেশিয় সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন, জীবনাচরণ-এক কথায় পলিনেশিয় সংস্কৃতিকে তুলে আনেন। এই তথ্যচিত্রটিতে ফ্ল্যাহার্টি প্যানক্রোমাটিক নামে বিশেষ ধরনের ফিল্ম ব্যবহার করেন। যা মৃদু আলোতেও স্পষ্ট চিত্রধারণ করতে সক্ষম। মোয়ানা ছবিটি প্যানক্রোমাটিক ফিল্মে ধারণ করা প্রথম প্রামাণ্যচিত্র।
পরবর্তী সময়ে ১৯৩১ সালে ফ্ল্যাহার্টি নির্মাণ করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন। তার ক্যামেরার দৃষ্টি ছিলো সর্বদাই সংগ্রামী মেহনতি মানুষের দিকে। এই তথ্যচিত্রটিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার ফলে যন্ত্রের জয়গান তুলে যখন আকাশ-বাতাস ভারী করা হয়েছিলো, ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি সুউচ্চ কণ্ঠে গেয়েছেন শ্রমিকের জয়গান; দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন, ‘সুক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় পণ্য উৎপাদনে শ্রমিকের কোনো বিকল্প নেই।’
এর বছর দুয়েক পর ১৯৩৩ সালে এস্কিমোদের মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা আয়ারল্যান্ডের আরন দ্বীপের বাসিন্দাদের নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন ম্যান অব আরন। এখানে তিনি দেখালেন জীবন প্রসন্ন নয়, তাদের জন্মই হয়েছে সংগ্রাম করার জন্য। এরপর ১৯৩৭ সালে ভারতের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেন এলিফেন্ট বয়। কৃষি সমস্যা নিয়ে ১৯৪১ সালে ফ্ল্যাহার্টি নির্মাণ করেন দ্য ল্যান্ড প্রামাণ্যচিত্রটি। এখানে সেই সময়ে আমেরিকার কৃষিতে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তা থেকে কীভাবে উত্তরণ করা সম্ভব তা দেখানো হয়।
দীর্ঘ ছয় বছর পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ফ্ল্যাহার্টি নির্মাণ করেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি লুইজিয়ানা স্টোরি। একটি বালকের সঙ্গে একদল তৈল অনুসন্ধানকারীর গড়ে ওঠা বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে এর কাহিনী। এই ছবিটি নির্মাণের সময় তিনি চিন্তা করলেন কীভাবে এটাকে নতুন আঙ্গিক দেওয়া যায়। তাই এই চিন্তার ফসল হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম প্রামাণ্যচিত্রে সঙ্গীতের আবেশ ছড়ালেন ধারা বিবরণীর পরিবর্তে; যা পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রকাররা তাদের চলচ্চিত্রে সংযোজন করেন। এটিই ছিলো ফ্ল্যাহার্টির জীবনের শেষ তথ্যচিত্র।
সবাই যখন ব্যস্ত ছিলো আধুনিক সভ্যতার চিত্রায়ণে, ঠিক সেই সময় এই মানুষটি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন আদিম, সংগ্রামী, মেহনতি মানুষের সহজ-সরল জীবনগাঁথা সেলুলয়েডে তুলে ধরতে। নিজেকে পুঁজির কাছে বিকিয়ে না দিয়ে সততার সঙ্গে স্বাধীন শিল্পী সত্তাকে ধারণ করে চলচ্চিত্রের জন্য কাজ করে গেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ৬৭ বছর পাঁচ মাস সাত দিন পৃথিবীর বুক আলো করে বেঁচে ছিলেন ফ্ল্যাহার্টি; দাপটের সঙ্গে। ১৯৫১ সালে প্রামাণ্যচিত্রের এই মানুষটি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান অজানার দেশে।
প্রামাণ্যচিত্র ও নানুক অব দ্য নর্থ
প্রামাণ্যচিত্রের জগতে প্রবেশ করলে প্রথমে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হয় লুই লুমিয়ের ও অগাস্ট লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়কে। যাদের হাত ধরেই মূলত যাত্রা শুরু করে প্রামাণ্যচিত্র। তারা ১৮৯৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি ও ১৯০১ সালে তার শবযাত্রার দৃশ্য ধারণ করেন যা প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের আদি দলিল হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক প্রামাণ্যচিত্রের পথিকৃৎ হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার চিত্রনির্মাতা ডেনিস এ কফম্যান (১৮৯৬-১৯৫৬); যার ছদ্মনাম ঝিগা ভের্তভ। তিনি বাস্তবকে তুলে ধরার লক্ষ্যে কিনো-আই আন্দোলন শুরু করেন। এখানে তিনি ক্যামেরাকে কল্পনা করেছিলেন চোখ হিসেবে; যে-চোখ অনুভব এবং বর্ণনায় মানুষের চোখের চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হবে। এ বিষয়ে তার একটি মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ‘Camera means of making the invisible visible, the obscure clear, the hidden obvious, the disguised exposed.’2 তার বিবেচনায় অনুভবশীল ক্যামেরাকে হতে হবে যৌথ দায়িত্ববদ্ধ সত্যের পরিবেশক।
ঝিগা ভের্তভ ছাড়াও তথ্যচিত্রকে একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করানোর পিছনে যে-দুজনের অবদান অনস্বীকার্য তার একজন হলেন জন গিয়ারসন। আর অন্যজনের নাম আগেই বলেছি, রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। গিয়ারসন সেই তাত্ত্বিক, যিনি সর্বপ্রথম ডকুমেন্টারি শব্দটি ব্যবহার করেন। সালটি ১৯২৬। নিউইয়র্ক সান পত্রিকায় রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির মোয়ানার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথম এই ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্য শব্দটি ব্যবহার করেন। গিয়ারসন মনে করেন ডকুমেন্টারি হলো-The creative treatment of actuality বা বাস্তব অবস্থার সৃজনশীল পরিবেশনা। জন গিয়ারসন ১৯২৯ সালে নির্মাণ করেন তার বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র ড্রিফটার্স। উত্তর মহাসাগরের জেলেদের হেরিং মাছ ধরার ঘটনা এ-ছবিতে তুলে ধরা হয়। চলচ্চিত্রটিতে উত্তাল সাগরের কতিপয় সাহসী জেলের চোয়ালচাপা সংগ্রামী জীবন উঠে আসে।
ইতিহাস থেকে এবার ফিরে আসি প্রামাণ্যচিত্রের সংজ্ঞায়নে। ল্যাটিন শব্দ ‘ডকুমেন্টাম’ থেকে এসেছে ডকুমেন্টারি, যাকে আমরা বাংলায় বলছি প্রামাণ্যচিত্র। প্রামাণ্য শব্দটির মাঝেই আমরা এর একটি উত্তর খুঁজে পাই। আর তা হলো প্রমাণ, অর্থাৎ যেখানে তথ্য হবে ছলাকলা বর্জিত, যেখানে থাকবে না জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, শুধু থাকবে সত্য ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। অবশ্য সত্য ও বাস্তব শব্দ দুটিকে আমরা অনেক সময়ই এক ভেবে ভুল করি। কিন্তু শব্দ দুটির ব্যাখ্যা আসলে এক নয়। আমরা যদি কাহিনীচিত্রের কথা বলি, সেখানে আমরা গাড়ি ভাঙ্গতে দেখি, ঘর জ্বালিয়ে দিতে দেখি-এই বিষয়গুলি বাস্তবে ঘটাতে হয়। এখানে বলে রাখি বিষয়গুলি বাস্তবে ঘটতে পারে কিন্তু তা সত্য নয়, কাহিনীর প্রয়োজনে তা করতে হয়। প্রামাণ্যচিত্রের জগতে বাস্তববাদী শব্দটির প্রবেশ ঘটে হাউজিং প্রবলেমস নামে একটি তথ্যচিত্রের মধ্য দিয়ে।৩ এই ছবির নিষ্করুণ বাস্তবতা দর্শকদের মনে আঘাত করেছিলো। আর এটিই ছিলো সম্ভবত প্রথম ছবি যেখানে দর্শক প্রথম অস্বস্তিকর বাস্তবতার সম্মুখীন হন।
এবারে আমরা দেখবো প্রামাণ্যচিত্র নানুক অব দ্য নর্থ-এ কী আছে। প্রকৃতি তার নিবিড় ভালোবাসায় আগলে রেখেছে আমাদের। তাইতো আমরা হয়েছি প্রকৃতিপ্রেমী, করেছি প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি। প্রকৃতির সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের আবিষ্ট করে রেখেছে তার জগতে। যে-জগৎ আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে গোটা পৃথিবী। সমস্ত কিছু যেনো হাত দুখানি বাড়ালেই পেয়ে যাবো। এই পৃথিবীর মানুষ হয়েও একদল মানুষ আছে যারা সব আধুনিক সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। যেনো মনে হয় এই পৃথিবীর মানুষ হয়েও তারা এ-পৃথিবীর কেউ নয়। অন্য এক জগৎ, যেখানে প্রকৃতি সর্বদাই রুক্ষ, যেখানে নেই হেমন্ত, বসন্তের মতো ঋতু। আছে কেবল গ্রীষ্ম আর শীত। আর এই মানুষগুলোকে বাস করতে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে তারা উত্তর মেরুর এস্কিমো নামে পরিচিত। যেখানে আমাদের সকাল শুরু হয় পেস্ট আর ব্রাশ দিয়ে, সেখানে তাদের সকাল শুরু খাদ্যের সন্ধানে। তাদের খাদ্যের একমাত্র উৎস শিকার। খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য তারা শিল মাছ, স্যামন মাছ, সিন্ধুঘোটকের মতো শক্তিশালী প্রাণীকে শিকারে পরিণত করে। শিকারের এই কৌশলও তারা শিখেছে প্রকৃতির কাছে। জাল না থাকলেও মাছ শিকারের জন্য তাদের রয়েছে হার্পুন, সুতোয় বাঁধানো টোপ। এই মাছ তারা রেঁধে খায় না, কাঁচা খায়। আর এটাই যেনো তাদের কাছে অমৃত। পানির পিপাসা মেটানোর জন্য তারা ঘাস জাতীয় জ্বালানি ব্যবহার করে বরফকে পানি করে-এই তাদের খাদ্য প্রণালী।
প্রকৃতি তাদেরকে এক জায়গাতে থাকার অনুমতি দেয় না। তাইতো শীতে যেখানে তারা বাসা বাঁধে, গ্রীষ্মে সেখানে থাকে না। ঘর বাঁধার জন্য শক্ত দেখে বরফ অঞ্চলের সন্ধান করতে হয় এদের। এরপর আয়তাকার করে কাটা বরফ খণ্ড দিয়ে অর্ধচন্দ্রের মতো ঘর তৈরি করে। যাকে আমরা বলি ইগলু। এই ইগলুতে রয়েছে দিনের বেলা সূর্যের আলো ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা। ফলে দিনের বেলা উষ্ণ থাকে এই ঘর। আর রাতে উষ্ণ রাখার জন্য ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। তবে মজার বিষয় হলো, ইগলুতে যেমন দরজা কেটে ঢুকতে হয় ঠিক তেমনি আবার কেটে বাহির হতে হয়। সিনেমাটির সব জায়গাতেই সংগ্রামের একটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
তাদের এ-সংগ্রাম শুধু খাদ্যের জন্যই নয়, পোশাকের জন্যও। পোশাকের জন্য তাদেরকে শিয়াল, সিল এর মতো প্রাণীকে শিকার করে তাদের চামড়া রোদে শুকাতে হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্য তাদের ভরসা কেবলই সংগ্রাম। এই সংগ্রামী জীবনেও পরিবারের প্রতি, সন্তানের প্রতি তাদের মমত্ববোধ ছিলো পর্যাপ্ত, যেমনটি ছিলো নানুকের। নানুক অব দ্য নর্থ-এ সরাসরি জীবন থেকে তুলে আনা এসব নির্জন, নিঃসঙ্গ, প্রকৃতি ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামরত মানুষের জীবনগাঁথা সেলুলয়েডে ধারণ করে বর্তমানের দাম্ভিক সভ্যতার মানুষের সামনে হাজির করেছিলো ফ্ল্যাহার্টি। তাই প্রামাণ্যচিত্রের ইতিহাসে তাকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। যতোদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন অম্লান হয়ে থাকবেন ফ্ল্যাহার্টি।
লেখক : হালিমা খুশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। পাশাপাশি তিনি একজন বিতার্কিকও।
khushimcj@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৫ : ২৪); তথ্যচিত্রের আর্ট ও টেকনিক; বাণী শিল্প, ১৪এ টেমার লেক কলকাতা, ৭০০০০৯।
২. উদ্ধৃত, খান, ফৌজিয়া (মাঘ, ১৪১৮); ‘স্বাধীন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার পথচলা’; কালি ও কলম, সম্পাদক-আবুল হাসনাত; ৮ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মাঘ ১৪১৮, খিলক্ষেত, ঢাকা।
৩. প্রাগুক্ত; দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৫ : ২৮)।
সহায়ক গ্রন্থ
হোসেন, মাহমুদুল (২০১০); সিনেমা; ফ্ল্যাট ১/বি, বাড়ি ২৮, সড়ক ১৫ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।
হায়াৎ, অনুপম (২০০৪); চলচ্চিত্রবিদ্যা; বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, শান্তিনগর, ঢাকা, ১২১৭।
রফিক, মনিস (২০১০); চলচ্চিত্র বিশ্বের সারথি; রোদেলা প্রকাশনী।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন