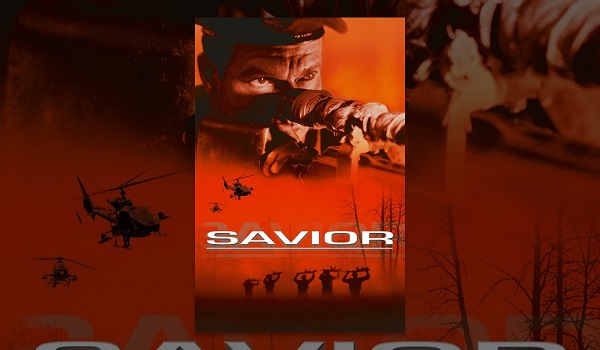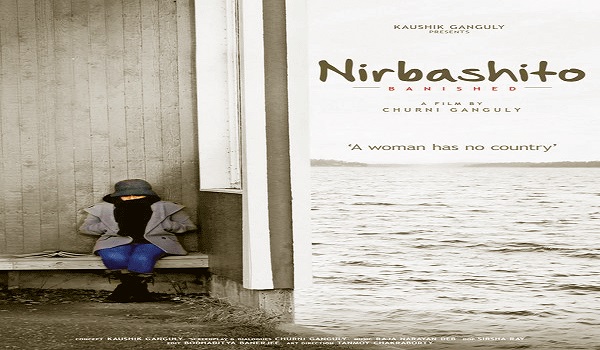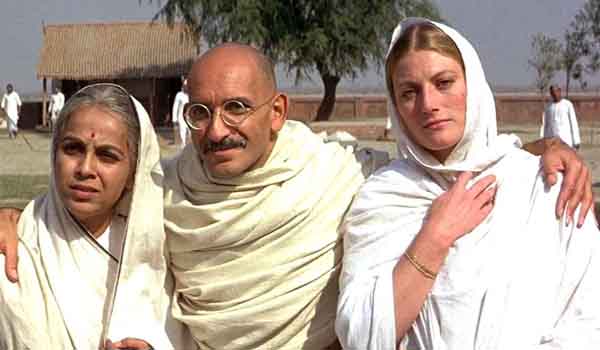রুবেল পারভেজ
প্রকাশিত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ
ডানা লাগালেই যায় না ওড়া
রুবেল পারভেজ

প্রতিদানের পুরস্কার নোবেল আর অস্কার
চে গুয়েভারা। সারাবিশ্বের মানুষের শান্তির জন্য, সমতার জন্য লড়াই করেছেন আমৃত্যু। আর এই ‘অপকর্মের’ জন্য ‘বিশ্ব কর্তৃপক্ষ’ তার শরীরকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলো ‘মাত্র’ নয়টি গুলি করে। সঙ্গে কেটে নিয়েছিলো দুটি হাত। তারিখ ৯ অক্টোবর ১৯৬৭।
বারাক ওবামা। অগাধ সম্পদের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম রাষ্ট্রপতি। যিনি ওই বিপন্ন মানুষগুলোর পক্ষে সম্মুখ সমরে যাননি। মুখের বুলি দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি এনেছেন, আনবেন—এই প্রত্যাশায় তার দুই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার। তারিখ ৯ অক্টোবর ২০০৯। মিলের মধ্যে মিল হলো, যেদিন সারাবিশ্বের লাখো মানুষ চে’র মৃত্যুতে শোক পালন করে; ঠিক সেই দিনই মার্কিন দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পান শান্তিতে নোবেল পুরস্কার। তারিখটি অপরিবর্তিত; পার্থক্য কেবল ৪২ বছরের।
অন্যদিকে ওবামার নোবেল জয়ের ঠিক এক বছর আগে ২০০৮ সালে হলিউড নির্মিত ‘হার্ট লকার’১ চলচ্চিত্রে মার্কিন সেনারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ‘মানবতা’ রক্ষা করে, ‘শান্তি’ ফিরিয়ে এনে অস্কার পুরস্কার পায়। এভাবে নোবেল দিয়ে দুনিয়ার ভৌগোলিক রাজনীতি আর অস্কার দিয়ে শিল্পজগতের রাজনীতি চলে। আর এই দুই মিলিয়ে হয় ‘আমরাই শ্রেষ্ঠ’ মতবাদ।
আসলে ভালোর জন্য পুরস্কার, মন্দের জন্য তিরস্কার—কর্তৃপক্ষের পুরস্কার-তিরস্কারের এই ঘোষণা চলছে অনাদিকাল। পরকাল বিষয়ক কর্তৃপক্ষের জন্য বিষয়টি যেমন সব কথার শেষ কথা, তেমনই ইহকাল বিষয়ক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষ আসলে এই পুরস্কারের জন্যই লড়াই করে। এজন্য সে চেষ্টা করে পুরস্কার পাওয়ার যতো শর্ত আছে তা পালনের। আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃত পুরস্কারটির নাম নোবেল। বলা হয়, মানবের উন্নতিতে, বিশ্বের উন্নতিতে সৃষ্টিশীল ও অনবদ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সবচেয়ে দামি যে পুরস্কারটি দেওয়া হয়, সেটি অস্কার। দুটি পুরস্কারেরই বয়স শত বছরের কাছাকাছি। দীর্ঘ সময়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অসংখ্য মানুষ। মানবসেবার জন্য যেমন ‘মাদার তেরেসা’২, তেমনই মানবশত্রু বলে পরিচিত যুদ্ধবাজ হেনরি কিসিঞ্জারও পেয়েছেন এই পুরস্কার। হয়তো নোবেল কমিটির দৃষ্টিতে মাদার তেরেসা আর কিসিঞ্জারের মধ্যে আদতে কোনো পার্থক্য নেই!
সময় গেলে সাধন মেলে
অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। সময়ের নিয়মতান্ত্রিক এই শ্রেণিবিন্যাসেই মানুষের পথ চলা। কিন্তু এর মধ্যে অতীত নিয়ে এই মানুষের আগ্রহ চিরকাল। কারণ যা ঘটে গেছে এমন বিষয় মানুষ জানতে চায়, কেনো ঘটলো উত্তর পেতে চায়। আর অন্য দুটির ওপর আগ্রহের মাত্রা এতটা না হওয়ার সম্ভাব্য কারণ-মানুষ নিজেই বর্তমানের সাক্ষী, স্রষ্টা; এই সময় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা মানুষের নাগালের বাইরে থাকায় সে চাইলেও তা নিয়ে খুব বেশি কিছু করতে পারে না।
অতীতের গুরুত্ব আছে বলেই খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম অব্দ থেকে আজও লেখা হচ্ছে মানুষের ইতিহাস, তার কর্মের ইতিহাস। ঐতিহাসিকতাবাদ আছে বলেই চার্লস ডারউইন জীবনের জন্ম ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে অবারিত করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিকতাবাদ আছে বলেই মার্কসবাদ আজ মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পেরেছে।
এখন দেখা যাক, ইতিহাস কথাটির ব্যাকরণিক অর্থ। প্রত্যয়টি বিভক্তি করলে দাঁড়ায়, ইতিহ + আস অর্থাৎ এমনটিই ছিলো বা এমনটি ঘটেছিলো। মানে, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিলো তার অনুসন্ধান ও বিবরণই ইতিহাস। এখন এই প্রকৃত বা আসল শব্দটি নিয়েই যতো গণ্ডগোল। কেননা সব পক্ষই বলতে চায় তার রচিত ইতিহাস ঠিক। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তি যেহেতু বিজয়ীর পক্ষে ধায়, সেহেতু বিজিত পক্ষের দিকেই বেশি ঝোঁক, বিশ্বস্ততা। আর বিজয়ের সঙ্গে যেহেতু ক্ষমতার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি, সেহেতু ইতিহাস রচনায় বিজয়ীও ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরাজিত পক্ষকে যেমন খুশি তেমনভাবে উপস্থাপন করবে এটিই স্বাভাবিক। ইতিহাস রচয়িতাদের তাই দেখা যায়, পাল্টাপাল্টি রচনা লিখতে। সবার চেষ্টা একটাই, ‘আমার লেখা ইতিহাস শ্রেষ্ঠ, নির্ভেজাল।’
ঐতিহাসিক পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর দাসসমাজ। এই দাসসমাজ নিয়েও রয়েছে অসংখ্য মানুষের অজস্র ইতিহাস। যে যার জায়গা থেকে এই সময়কে, এই সময়ের দাসপ্রভুদের কথা তুলে ধরেছে তার নিজস্ব বয়ানে। আর সেই ইতিহাস জানতে আমরাও মুখিয়ে থাকি, অনুসন্ধান করি। কারণ, ‘ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকে বিচার করতে পারি।’৩ সুতরাং শত শত বছর আগে ঘটে যাওয়া দাসপ্রথা নিয়ে এখন এই সময়ে যদি কিছু রচনা হয় বা নির্মাণ করা হয়, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে সবার নিকট ধরা দেবে। কেননা, কারণ ছাড়া ইতিহাস রচনা হয় না। যে কারণে ইতোমধ্যে রচিত ইতিহাসের পুনর্নির্মাণেরও মাজেজা না থাকার কথা নয়।
এমনিভাবে সলোমন নামের এক ব্যক্তির ১২ বছরের দাসজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা একটি ইতিহাস ‘টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ’। শত শত বছর ধরে টিকিয়ে রাখা দাসপ্রথার ইতিহাসে ১২ বছরের এই ইতিহাস খুবই খণ্ডিত কিন্তু ‘তাৎপর্যমণ্ডিত’। আর তা থেকেই মার্কিন চলচ্চিত্রনির্মাতা স্টিভ ম্যাককুইন ২০১৩ সালে নির্মাণ করেন টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ নামের চলচ্চিত্র। আর এর মধ্য দিয়েই ‘কালো মানুষ’ হিসেবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য প্রথম অস্কার পাওয়া স্টিভ ম্যাককুইনের নাম উঠে আসে ইতিহাসের পাতায়।
চলচ্চিত্রের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে ‘দিস ফিল্ম ইজ বেজ্ড অন অ্যা ট্রু স্টোরি’। অর্থাৎ সত্য কাহিনি অবলম্বনে এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত। তার মানে দাঁড়ায়, দাসদের নিয়ে ইতোমধ্যে যতো নাটক-চলচ্চিত্র রচনা হয়েছে তাতে বিতর্ক আছে, আছে মিথ্যার সম্ভাবনা। এজন্য দর্শক যেনো ভুল না বোঝে, তাই পুরো একটি শটে বাক্যটি তুলে ধরে দর্শকের চোখের ঠুলিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন জানতাম, কাল্পনিক ঘটনা বা গল্প দ্বারা কোনো নাটক, চলচ্চিত্র-নির্মাণের বিপরীতে নিরেট বাস্তব ঘটনা নিয়ে কিছু নির্মাণ করলে সেক্ষেত্রে লিখে দেওয়া হয়, ‘সত্য কাহিনি অবলম্বনে এটি নির্মিত’। এদিক দিয়ে হিসাব করলে, চলচ্চিত্রটি শুরুতেই ইঙ্গিত দিলো, দাসদের নিয়ে তৈরি এই ধরনের বেশিরভাগ গল্পই মিথ্যা-বানোয়াট-কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করে নির্মাণ করা হয়েছে বা হতেও পারে। এখন দেখা যাক, কী আছে এই সত্য ঘটনায়।
টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর গল্প
শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত শহর নিউইয়র্কে পরিবার নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ সলোমন। মনোমুগ্ধকর বেহালা বাজিয়ে তিনি সবার প্রিয়মুখ হয়ে উঠেছিলেন; বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের কাছে। কিন্তু একদিন তার সব সুখ হারিয়ে যায় দুজন শ্বেতাঙ্গ প্রতারকের কারণে। ফাঁদ পেতে সলোমনকে তারা বিক্রি করে দেয় দাস হিসেবে। অমানবিক অত্যাচারের শিকার সলোমন একের পর এক দাস ব্যবসায়ীর হাত বদল হন। এভাবে একদিন তাকে বিক্রির জন্য নেওয়া হলে দাসপ্রভু মি. ফোর্ড তাকে কিনে নেয়। নিখুঁত কাজ আর ‘দায়িত্বশীল’ আচরণ করে প্রভুর বাহবা পায় সলোমন। তবে শ্বেতাঙ্গ এক কর্মচারীর সঙ্গে একদিন তার মারামারি হয়। একপর্যায়ে তার সাঙ্গপাঙ্গরা সলোমনকে নির্মমভাবে মারধর করে। এই ঘটনায় শঙ্কিত মি. ফোর্ড তাকে মি. এপ্স নামের আরেক দাসপ্রভুর কাছে বিক্রি করে দেন।
এখানে এসে অন্যান্য অনেক দাসের সঙ্গে সলোমন পান পাতসি নামের পরিশ্রমী এক নারীকে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও সামান্য কারণে পাতসি’কে নির্মম নির্যাতন, ধর্ষণ করে মি. এপ্স। সব দেখেও সলোমন কিছু করতে পারেন না। দিন যতো যায়, ততোই বাড়তে থাকে অত্যাচারের মাত্রা। একদিন এক শ্বেতাঙ্গ কাজ করতে আসে মি. এপ্সের বাড়িতে। সেখানে সলোমন তাকে তার দুর্দশার কথা খুলে বলেন। তারপর জাজ টারনার নামের ওই শ্বেতাঙ্গের সাহায্যে খবর পায় সলোমনের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্বেতাঙ্গ আইনজীবীরা; মুক্তি পান সলোমন। ১২ বছরের দাসত্ব থেকে ফিরে যান পরিবারের কাছে।
মানুষ দাস হলো মানুষেরই ভুলে
কাকও পাখি, কোকিলও পাখি। কিন্তু কী বিস্ময়, নিজ দক্ষতায়-মননে বানানো কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে, সেখানেই তার বাচ্চা হয়। আর এই বাসা বাঁধা থেকে শুরু করে ছানাটি বড়ো হওয়া পর্যন্ত কাকই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা কোকিলের কোনো ভূমিকা নেই। কারণ তারা যে বাসাই বানাতে পারে না। ফলে বংশ টিকিয়ে রাখতে তাকে সবসময় অন্যের ওপরই ভরসা করতে হয়। ত্যাগ করতে হয় নিজ সন্তান আর পরিবারের প্রতি অধিকারের আশা। এমতাবস্থায় আশঙ্কা করা যেতে পারে, কখনো যদি কাক পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, সঙ্গে কোকিলকেও নিতে হবে। কেননা তার অস্তিত্বও যে পুরোপুরি কাকের ওপর নির্ভরশীল। আবার কাক যদি কখনো বুঝে ফেলে ডিমটি সত্যিই কোকিলের, তাহলেও যে কোকিলের বংশ ধ্বংস হবে, নয়তো কাকের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তাই কাক এক্ষেত্রে কোকিলের প্রভু, কোকিল দাস। যদিও কোকিল এর বিনিময়ে কাকের কোন্ আদেশ পালন করে তা নিয়ে গবেষণা প্রাসঙ্গিক।
আমরা জানি না, ঠিক কোন্ কারণে কাকের প্রতি কোকিলের এই নির্ভরতা, আর কেনোই বা সে নিজের বাসা বানানো শিখলো না। ঠিক যেমনটি চাক্ষুষ জানি না, স্বাধীন মানুষও কীভাবে দাস হলো, কীভাবে তারই স্বজাতির হাতে সে বন্দি হলো। তবে ইতিহাস ধারণা দেয়, কোকিলের মতোই এই মানুষগুলো একদিন নীড়হারা হয়েছিলো। দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমায় আদিম সাম্যবাদী চেতনা ভাঙতে শুরু করেছিলো; মানুষ ভাগ হয়ে পড়েছিলো দুই দিকে—শিকারী জীবন ও পশু পালন। এ সময় ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রবণতা বাড়তে থাকে আর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এই মানুষেরই একটি পক্ষ। ঘটনাক্রমে তা তাদের লোভে পরিণত হয়; দখল করতে থাকে অন্যের জিনিস। নিজেদের স্বার্থ হাসিলে একপর্যায়ে মানুষ স্বাধীন স্বজাতিকেই বন্দি করে ব্যবহার করতে থাকে। স্বজাতির আরেক মানুষের হাতে এভাবেই দাসে পরিণত হয় মানুষ।
এর পরের ঘটনা সবার জানা। অর্থশালীরা সব হারানো মানুষদের তালুবন্দি করে ব্যবহার করেছে ইচ্ছেমতো। এদের দিয়েই তারা গড়ে তুলেছে রোমান আর গ্রিকের মতো বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য। এই সুযোগেই গড়ে উঠতে থাকে রাষ্ট্র। এদিকে দাসদের দিয়ে রাষ্ট্রের ভিত আরো মজবুত করতে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরাও দাসপ্রথাকে আইনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ‘মহান’ অ্যারিস্টটলও তাই যুক্তি তুলে ধরেন,
অজীব যন্ত্র প্রভুর আদেশ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না; কিন্তু সজীব দাস প্রভুর আদেশ এবং ইচ্ছা ইশারামাত্র বুঝতে পারে এবং তা কার্যকর করতে পারে। কিন্তু দাস কখনো শাসক হতে পারে না। দাসের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর জন্য শ্রম করা। এবং প্রভুর কাজ হচ্ছে দাসের শ্রমের ফলে জীবিকার চিন্তামুক্ত যে অবকাশ সে লাভ করছে সে অবকাশকে শাসনকার্যে ব্যয়িত করা।৪
ফলে বোঝা যায়, আদেশদাতারাই রাষ্ট্র; দাস নামক শ্রমিকটিই যে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখে, সে বিনিময়ে হয় সজীব দাস। অর্থাৎ প্রভুর প্রভুত্ব বজায় রাখতে নিজেকে তাদের পায়ের তলায় সমর্পণ করাই হলো দাসের একমাত্র কাজ।
কে বলে মানুষ তারে ...
মুখ থেকে থুথু মাটিতে ফেলে তা আবার মুখে তুলে নিলে ‘জাত’ যায় মানুষের। আত্মসম্মান ও জাত সম্পর্কে সচেতন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ অবাক হতে হয়, যে রাষ্ট্র প্রতিক্ষণ মানুষ, মানবতার কথা চিৎকার দিয়ে হুঙ্কার তুলে সর্বত্র শোরগোল তোলে সেই যুক্তরাষ্ট্রই প্রতিনিয়ত এই ফেলে দেওয়া ‘থুথু’ পুনরায় চাটতে অভ্যস্ত। দেখা যায়, আজ যে তার শত্রু, কাল সে তার বন্ধু। আজ যাকে সে গালাগাল করে তিরস্কার করলো, কাল তাকে আবার হোয়াইট হাউজ বলে খ্যাত ‘শ্বেতাঙ্গ প্রাসাদে’ (ধরে নিতে হবে, ব্ল্যাক হাউজ বলে কোনো হাউজ থাকা যাবে না) সেই রকম আদর-আপ্যায়ন করা হয়। মনে আছে, যে নরেন্দ্র মোদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র তার ভিসা বাতিল করেছিলো, সেই যুক্তরাষ্ট্রই তাকে লাল গালিচার অভ্যর্থনা দিয়েছে।
বর্ণবাদ বিরোধী কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে এই যুক্তরাষ্ট্রই সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো। সেই যুক্তরাষ্ট্র ১০ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তোড়জোড় করে পাঠিয়েছিলো বারাক ওবামাসহ পূর্বসূরি তিন প্রেসিডেন্টকে। সেখানে তারা তাকে বীর, শান্তিকামী বলে গলা ফাটিয়ে এসেছিলো। বিষয়টিকে তখন স্বাভাবিক-অসাধারণ সিদ্ধান্ত মনে হলেও ভুল ভেঙে যায়, ঠিক সাত মাস ছয় দিন বাদে। ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ৪ থেকে ৬ আগস্ট ওয়াশিংটনে আফ্রিকান নেতাদের সঙ্গে বিশাল আকারের সম্মেলন করে আফ্রিকায় বাণিজ্য করার বার্তা দিলেন বিশ্ববাসীকে।’৫ আর আফ্রিকার বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের চোখ দেওয়ার কারণ হলো, ‘এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির ১০টি দেশের মধ্যে ছয়টিরই অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশে।’৬ এতেই বোঝা যায়, ফেলে দেওয়া ‘থুথু’ পুনরায় মুখে নেওয়ার মাজেজা।
এবার আসি টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এ। চলচ্চিত্রটি দেখে দর্শকের মনে হতে পারে, কেনো ‘শ্বেতাঙ্গ প্রাসাদের’ লোকেরা নিজেদের অতীতের ভুল নিজেরাই তুলে ধরছে। তাছাড়া সবাই তো জানে, শ্বেতাঙ্গরা কালোদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং একই সঙ্গে অস্কার দেওয়ার ব্যাপারটি কেনো ঘটছে? উত্তর উপরের ওই থুথু চাটার কারণের মধ্যেই পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী যে শাসকেরা এই বিশ্ব চালায় তাদের অধিকাংশই সাদাচামড়ার অধিকারী। উনারা সারাবিশ্ব বিশেষ করে কালো মানুষের মহাদেশ আফ্রিকাকে দুঃশাসনের চরমে নিয়ে গিয়েছিলেন; শ্রমিকের শ্রমকে আখের ছোবড়ার মতো পিষে বের করে নিয়েছিলেন। আর তা করতে গিয়েই কালো মানুষেরা হয়ে ওঠে তাদের দাস। তবে অত্যাচার আর অনাচারের নির্মম কাহিনি তারা চেপে রাখতে পারেননি। বিশ্বময় নিপীড়িত এই মানুষগুলোর আর্তনাদ ধেয়ে গেছে, সঙ্গে নিপীড়কের নৃশংসতাও। প্রমাণ হয়েছে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাই দাসপ্রথাকে মজবুত করেছে।
কিন্তু সময় পাল্টেছে। কালোরা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছে এগিয়ে যাওয়ার। শ্রম-মেধা-সাহস দিয়ে তারা আজ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আর তাতেই অবাক হয়েছে তাদের পুরনো বর্ণশত্রুরা। কিন্তু এরা চাইলেই আজ আর আগের মতো কালো মানুষগুলোর ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না; চাইলেই সহজে পারে না তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে। কেননা শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ভয়ঙ্কর মুখোশগুলো আজ সবারই চেনা। তাই তাদের প্রয়োজন হয় অভিনয়ের, নতুন ইতিহাস নির্মাণের, আর প্রমাণের—দেখো আমরা তোমাদের শত্রু নই। যা হওয়ার হয়ে গেছে; এসো আবার গলাগলি করে হাঁটি (যেনো গলা টিপে ধরতে সুবিধা হয়)।
ঘটনা-১
প্রদীপের নির্মল আলোয় জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যা। বেশ কয়েক জোড়া ধনাঢ্য ধবধবে সাদা আমেরিকান যুগল সলোমনের বেহালার ছন্দে আনন্দ করছে; উপচে পড়ে হাসির ঝলক। নাচানাচি শেষ হওয়ার পর তারা সবাই মিলে কালো সলোমনকে বাহবা দেয়, তিনি গর্ব বোধ করেন। ছয় মিনিট দুই সেকেন্ড থেকে সাত মিনিট পাঁচ সেকেন্ড, মোট এক মিনিট তিন সেকেন্ডের এই দৃশ্য দিয়ে শুরু হয় টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর কাহিনি। আর এই সময়ের মধ্যে দর্শক ভাবতে বাধ্য হয়, ন্যায্যতার মানদণ্ডে সাদারা আসলেই সব জাতির চেয়ে সেরা। সলোমন দেখতে কালো, ‘কুৎসিত’ হলেও তার যোগ্যতার প্রবল বাতাসে নিমিষেই সব উবে যায় সাদাদের চোখে। কেননা অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর রুচিশীল সাদাদের যে মনোরঞ্জন করতে পারে সে-ই তো প্রকৃত যোগ্য মানুষ!
এর পরের শটেই সলোমন তার সন্তানদের সঙ্গে প্রফুল্ল চিত্তে খুনসুটি করে তাদের ঘুম পাড়িয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। এই দৃশ্যে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কালো, কুৎসিত যে যাই হোন না কেনো, আপনি যদি আপনার যোগ্যতাবলে সাদাদের খুশি রাখতে পারেন, তার বিনিময়ে আপনিও সলোমনদের মতো সুখে থাকবেন, তা সে যতোই দুর্দশাগ্রস্ত নির্মম সময়ের মধ্যে থাকুন না কেনো। সাদাদের তুষ্টি দিতে আপনার সমগোত্রীয়রা ব্যর্থ বলেই তারা দাস হয়ে আবর্জনাময় জীবন কাটায়। এদের যোগ্যতাহীনতার জন্য তো সাদারা দায়ী নয়! সাদারা উদার বলেই তো তাদের সিংহাসনে বারাক ওবামা বসেন, অপরাহ উইনফ্রে হন বিশ্বের সবচাইতে দামি-প্রভাবশালী তারকা, ভেনাস-সেরেনা দুই বোন হন পৃথিবীর অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড়, মোহাম্মদ আলি ঠুসোঠুসি (বক্সিং) করে হন বিশ্বখ্যাত! এদের দেখে বোঝেন না, সাদারা কতো ভালো, কতো উদার!
ঘটনা-২
রোদ ঝলমলে মিষ্টি সকাল। স্ত্রী-সন্তানকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে সলোমন বুক ফুলিয়ে হেঁটে আসছেন; চারিদিকে খোশগল্পে মুখরিত চকচকে পোশাক পরিহিত ধনাঢ্য সাদা মানুষের জটলা। শিশুদের হাসিতে শুভ্র পুরো এলাকা। গির্জায় বাজছে পবিত্র ঘণ্টাধ্বনি। এমন আহ্লাদিত কোলাহলের মধ্যে সলোমনকে কেউ কিছু বললে তিনিও গাম্ভীর্য দেখিয়ে ইশারায় উত্তর দেন। এরপর তার আরেক শ্বেতাঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষী হাসিমুখে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সলোমনও বেশ আত্মবিশ্বাসী হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটি সলোমনের মঙ্গলের কথা ভেবে, তার ভালো রোজগারের সন্ধানে দুজন সার্কাস সদস্যের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। পরিষ্কার হয়, সাদারা সলোমনদের শুধু খ্যাতিই দেয় না, আর্থিক উন্নতির জন্য, পিছিয়ে পড়াদের টেনে তুলতেও প্রাণপণ চেষ্টা করেন।
ঘটনা-১ + ঘটনা-২ = ইতিহাস কী বলে
আলোচিত ঘটনা দুটির বয়ান নিউইয়র্কে; সময় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হতে বাকি আড়াই দশক। উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গরা ততোক্ষণে গিলে ফেলেছে আমেরিকার অধিকাংশ জায়গা। একে একে তারা নিঃশেষ করে দিচ্ছিলো আমেরিকার প্রকৃত অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ান আর কালো মানুষদের যাবতীয় ইতিহাস। হত্যা, লুণ্ঠন, ভূমি দখল, ধর্ষণ আর মানুষ বিক্রিই ছিলো এই শ্বেতাঙ্গদের একমাত্র কাজ (আজও তারা করে তবে একটু ভিন্নভাবে)। চেরোকি জাতিসহ অসংখ্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে মূল্যবান পণ্যের লোভে প্রকৃতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলো এরা। এ সময় ‘... জীবন্ত গাছপালা, বনভূমি, তার পশুপাখি জীবজন্তু, আচ্ছাদিত তৃণভূমি, পানি, মাটি এবং খোদ তার বাতাসকেও’৭ তারা শত্রুপক্ষ বানিয়ে নিধন করেছিলো।
যদিও এই অবস্থা ঠেকাতে ঔপনিবেশিক আরেকটি পক্ষ (সম্পদ ভাগাভাগির সম্পর্কে) দখল করে নেয় ইন্ডিয়ান অধিবাসী অধ্যুষিত মেক্সিকোর বিস্তীর্ণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, টেক্সাস থেকে শুরু করে পুরো ক্যালিফোর্নিয়া। সবচেয়ে খেয়াল করার বিষয়, ওয়াশিংটন এই সময় যাবতীয় দখলদারিত্বের বৈধতা দিতে ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি বা নিয়তির বিধান ঘোষণা করে। বলা হলো, ‘ইউরোপীয় এবং তাদের বংশধররাই গোটা আমেরিকা শাসন করবে এটাই নিয়তির লিখন। তারাই দুনিয়ার সেরা জাতি এবং সেই হেতু তাদের ঘাড়েই দায়িত্ব বর্তেছে ... ভালমন্দ দেখাশুনা করার।’৮ আর এই যুক্তির দোহাই দিয়েই তারা অবশিষ্ট রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করেছিলো, কালোদের দাস হিসেবে বিক্রি, হত্যা, ধর্ষণের মতো যাবতীয় নির্যাতন চালিয়েছিলো। মুনাফার লোভে, যখন যা খুশি তা করতে এতটুকু মানবিকতার পরিচয় দেয়নি এই শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা।
অথচ টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর আমেরিকাতে সলোমনসহ আরো যে কয়েকজনকে ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এ দেখা যায়, তাদের কারো সঙ্গেই এমন আচরণ করে না কোনো শ্বেতাঙ্গ। কিংবা দেখা যায় না কোনো যুদ্ধাবস্থা, হত্যা, লুণ্ঠন, জ্বালাও, পোড়াও। বরঞ্চ প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গকেই দেখা যায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে। সেই সঙ্গে সলোমনদের তোষামোদ করতে করতে সব সাদাদের কুঁজো হয়ে পড়া তো ছিলোই। তাহলে সেই সময়ের বাস্তব ইতিহাসের ভোল উল্টে দিয়ে চলচ্চিত্রটি ঠিক কোন্ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এমন অসাম্প্রদায়িক-বর্ণবৈষম্যহীন আর শান্তিপূর্ণ দৃশ্যের আয়োজন করলো?
নাকি সময়ের প্রয়োজনে সত্য আপনা-আপনিই পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন করতে হয়, সত্যকে সাজাতে হয়, বানাতে হয়! ক্ষমতাবানরা সত্যের ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে এটিই তাহলে স্বাভাবিক। এই না-হলে আমেরিকা, এই না-হলে অস্কারের জন্মদাতা হলিউড!
বিধাতাকে সত্যিই দেখা যায়!
বিধাতার অস্তিত্ব নিয়ে যে বিতর্ক—সে বিতর্কের সমাধান আজও কোনো পক্ষ পুরোপুরি দিতে পারেনি। যদিও বিশ্বকর্মা বিধাতাকে খুঁজে বের করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাদের কথায় এই দুনিয়া চলে তারা কোথায়, তারা কেমন? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর দুনিয়া ঘুরে আসা যাক। এই দুনিয়ায় মানুষের সম্পর্ক দাস-প্রভুর।
পণ্য কেনা-বেচার মতো দাস ব্যবসাকে ঘিরে এখানেও রয়েছে হরেক রকম পক্ষ। ধাপে ধাপে এই কাজটি সম্পন্ন করতে দালালচক্র, পাইকারি ব্যবসায়ী (আমদানিকারক, রপ্তানিকারক), খুচরা ব্যবসায়ীসহ জড়িত মোটামুটি ৩৯ জন। ফাঁদ পেতে মানুষ ধরে এনে দাস বানিয়ে ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচিত্র সব আচরণ চোখে পড়ে। এদের মধ্যে কয়েকজন মিথ্যা প্রলোভন আর মিষ্টি কথা বলে সাধারণ মানুষদের ফাঁদে ফেলে দাস বানায়। কয়েকজন প্রচণ্ড প্রহার করে; এমনকি হত্যার পর ছুঁড়ে ফেলে সমুদ্রের পানিতে। কেউ ধর্ষক, কেউ হিংসুটে, কেউ বা আবার টাকার নেশায় মানবিক বোধশূন্য।
দাসপ্রথা নিয়ে আগে যতো ইতিহাস নির্মাণ হয়েছে সেগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই দাস ব্যবসায়ীদের এমন উপস্থাপনের দেখা মেলে। চলচ্চিত্রটির এই ভিজ্যুয়াল ইতিহাসে দাসপ্রথার বর্বরতা দেখে আমরা সবাই আঁতকে উঠি। আশ্বস্ত হই শ্বেতাঙ্গ প্রধান হলিউডের এই সাহস ও সততা দেখে; শেষ পর্যন্ত তারাও নিজেদের ভুল নিজেরা স্বীকার করলো ভেবে।
কেনা-বেচার এই পর্যায়ে আগমন ঘটে সাত জনের আরেকটি পক্ষের, তারা হলো ক্রেতা। ইনারাই হলো উল্লিখিত ৩৯ জনের পরম কাঙ্ক্ষিত দাসপ্রভু। এতক্ষণ ধরে ইনাদের জন্যই ছিলো তাদের এতো যজ্ঞ। বিক্রেতার শো-রুমে একালের মডেলদের মতো দাঁড় করানো উলঙ্গ দাসদের কিনতে এসেছেন তারা। হাসিমাখা তাদের মুখগুলো যেনো শুদ্ধতায় ভরা, নেই এতটুকু হিংস্রতা, ধর্ষকামিতা। কোনো রকম বাকবিতণ্ডা তারা পছন্দ করে না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কেনে যে যার দাস।
এদের মধ্যে মি. ফোর্ড অন্যতম, যিনি এই মাত্র কিনেছেন সলোমন ও এজরা নামের দুজন দাসকে। এ সময় সন্তানদের নিজের সঙ্গে নেওয়ার জন্য বুকফাটা আহাজারি করছিলো এজরা। এই দৃশ্য দেখে মি. ফোর্ড আঁতকে ওঠেন; চোখ-মুখ বলে দেয় হৃদয়ে তার মানবিকতার ঝড় বইছে। তিনি মায়ের বুকে সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে মেয়েটিকে কিনতে চান; কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় আর পারেন না! সন্তানকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হলেও দাস ব্যবসায়ীকে ধিক্কার দিয়ে এই অমানবিকতার প্রতিবাদ করে আসেন।
এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সলোমনকেও একদিন শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। একপর্যায়ে মঙ্গলের কথা ভেবে সলোমনকে অন্যত্র বিক্রি করে দেন। বোঝা যায়, সব দাসপ্রভু খারাপ নয়, ছিঁচকে সন্ত্রাসী আর দাসব্যবসায়ীরাই যতো নষ্টের গোড়া। তার মানে, যদিও তাদের প্রয়োজনেই এই দাসব্যবসা টিকে আছে, থাকতে হয়; তার পরও দাসদের নির্যাতিত জীবনের যে নির্মম ইতিহাস বিশ্বময়, তার জন্য তারা দায়ী নয়। এজন্যই হয়তো টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর নির্যাতিত, নিপীড়িত দাসরা সমস্বরে গেয়ে উঠে দাসপ্রভুদের বেঁধে দেওয়া গান, ‘... মাই লর্ড সানশাইন, মাই লর্ড-লর্ড লর্ড, ইজ লেট, ইন হাই।’
এক্সেপশন ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল
আঁধার ঘনিয়ে এলে রাত, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে দিন। ডানা মেলে কিচিরমিচির শব্দ করে যে প্রাণী আকাশে ওড়ে সেটি পাখি। ঘেউ ঘেউ করলে কুকুর, মিউ মিউ করলে বিড়াল। না বলে কারো জিনিস চুপিচুপি নিলে চুরি, ডাক দিয়ে নিলে ডাকাতি। সমাজ নির্মিত এমন বিধির বলেই আমরা এর একটি বুঝালে অন্যটি বুঝি, একটিকে চেনালে অন্যটি চিনি। ঠিক যেভাবে চিনি পাগলকে, উন্মাদকে। আর এই নিয়ম ধরে হাজার হাজার ‘সুস্থ’ মানুষের মধ্য থেকে একজন পাগলকে খুঁজে বের করা মোটেও কষ্টকর হয় না। কেননা, সামাজিক সত্তার বাইরে চলা এই পাগল নিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে যে চর্চিত চিত্র আঁকা আছে, তাতে পাগল চিনতে না পারাটাই পাগলের কাজ।
‘প্রকৃতিগত’ পাগলকে অপর করে, তার বক্তব্য যুক্তিহীন হিসেবে অস্বীকার করে, সামাজিকভাবে তাকে মূল্যহীন করে তুলে, তার বিরুদ্ধে ‘যথাযথ ব্যবস্থা’ নিয়ে রাষ্ট্র সমাজে ‘স্বাভাবিক’ পরিবেশ বজায় রাখে—এটা প্রমাণিত। তবে এর বিপরীতে বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র কেনো নিজে নিজেই পাগল-উন্মাদ সৃষ্টি করে তা নিয়ে কথা বলা জরুরি। রাষ্ট্রসৃষ্ট এমনই এক উন্মাদের নাম এডউইন এপ্স। যিনি টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর দুনিয়ায় একমাত্র হিংস্র দাসপ্রভু। হয়তো এজন্য চলচ্চিত্রের দুই-তৃতীয়াংশ সময় জুড়েই তাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে পুরো কাহিনি। হিসাব করে ৫৩ মিনিট ছয় সেকেন্ড থেকে দুই ঘণ্টা তিন মিনিট ২৬ সেকেন্ড পর্যন্ত, দীর্ঘ এই এক ঘণ্টা ১০ মিনিট ২০ সেকেন্ড ধরে তার একটাই কাজ ছিলো—সলোমন-পাতসিসহ অন্যান্য দাসদের মারধর, ধর্ষণ করা। যা দেখে দর্শককুলের মোটামুটি সবার মনেই দাসপ্রভু হিসেবে এপ্সের প্রতি ধিক্কার জাগে।
তবে লক্ষণীয় ব্যাপার, টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর নির্যাতিত শত শত দাস কিংবা শুধু এর দর্শক, ঘৃণ্য এই ব্যক্তিটিকে ধিক্কার জানায়নি, তার স্বজাতি শ্বেতাঙ্গ এমনকি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত তাকে তুলাধুনা করেছে। দেখা যায়, মি. ফোর্ড সলোমনকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে এপ্স-এর কাছে পাঠানোর সময়ই বলে দেয়, ‘সে খুবই একরোখা। দাস মেরে নিজেকে সে গর্বিত মনে করে।’ তার স্ত্রীও তাকে কয়েকবার রাগান্বিত স্বরে বলেন, ‘তুমি একটা অমানুষ, দূষিত, নোংরা, অসভ্য, অধার্মিক কিংবা তুমি আমার বিছানায় উঠলে তা অপবিত্র হয়ে যায়।’ সবশেষে দাসদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গে একজন বলেন, ‘মি. এপ্স এগুলো অসুস্থতা। এই (শ্বেতাঙ্গ দাসপ্রভু) জাতির মধ্যে এসব কাজ আসলেই অতি ভয়ঙ্কর অসুস্থতার লক্ষণ।’ এতে বোঝা যায়, শ্বেতাঙ্গরা তাকে অমানুষ, পাগল, অসুস্থ বলে স্বীকার করে নিয়ে কালো দাসদের কাছে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত বলে স্বীকার করে।
শুধু তা-ই নয়, এপ্সের নেশাগ্রস্ত আচার-আচরণ, ছেঁড়া-জীর্ণ পোশাক, মুখের ভিতর থেকে লালা পড়া, এক পায়ের গোটানো প্যান্ট, আবোলতাবোল বকা, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, যাকে খুশি মারধর করা—এমনকি পাতসি’কে রাতের আঁধারে ধর্ষণের সময় বিষণ্ণ মুখ, চোখে কান্নার অবারিত ধারা, হতাশা নজরে পড়ে। যা দেখে সত্যিই মনে হয়, এপ্স পাগল-মাতাল-উন্মাদ-মানসিক রোগী। কেননা, ‘প্রকৃতিগত’ পাগলও কিন্তু মানসিক বোধগম্যতা হারিয়ে কখনো কখনো এই ধরনের জীবন যাপন করে। এখন প্রশ্ন, যে ব্যক্তি দাসদের ওপর এমন নির্মম আচরণ করলো, যিনি টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর একমাত্র নিপীড়ক দাসপ্রভু, সেই এপ্স’কে কেনো অপরাধী, ধর্ষক না বলে পাগল আর মানসিক বিকারগ্রস্ত চরিত্রে উপস্থাপন করা হলো?
সন্দেহের এই পর্যায়ে তাদের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের আইন-আদালত কি বলে তা দেখে নেওয়া যাক। ৪৭৭, ইউ এস, ৩৯৯ (১৯৮৬) এর ধারা মতে, ‘আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এই ঘোষণা দেয় যে, পাগলামি বা মানসিক বিকারগ্রস্ততা হলো মানসিক অসুস্থতার সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়। ... বাস্তব অনুভূতির বাইরে থাকার কারণে তারা খারাপ থেকে ভালোকে আলাদা করতে পারে না। এবং এর ফলে সংগঠিত অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও সে কোনো কিছু অনুধাবন করতে পারে না। যে কারণে তাকে শাস্তি পাওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।’৯ একইভাবে এপ্স’কে পাগল ও মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে তার স্বজাতি, স্ত্রী কিংবা টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর লেখক মানে স্বয়ং সলোমনই যেহেতু সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছে সেহেতু তাকেও উল্লিখিত আইন অনুযায়ী এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। তাহলে বোঝা গেলো, দাসদের ওপর অমানুষিক-অমানবিক নির্যাতনের দায়ে কোনো শ্বেতাঙ্গকে দায়ী করা যাবে না। কেননা অত্যাচারী দাসপ্রভুরা তো এপ্সের মতোই মানসিক রোগী। সুতরাং নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে দাস পেটাও ‘মানসিক রোগে’ আচ্ছাদিত এপ্সরা!
মানবতা, মানবতা? মানবতা!
‘... তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। এইরূপে তোমার দান যেন গোপনে হয়; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।’১০ সম্ভবত পিতার (যিশু প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যের প্রায় সব ইতিহাসই বলে তিনি শ্বেতাঙ্গ) প্রস্তাবিত ও ঘোষিত এই ফল লাভের আশা না করেই তার ‘ধার্মিক পুত্র’ যুক্তরাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের ‘যোগ্য সন্তান’ হলিউড নিজেরাই নিজেদের দানশীলতার একটি খবর টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ মারফত, দক্ষিণ হস্ত থেকে বাম হস্তে নয় পুরো বিশ্ববাসীকেই জানিয়ে দিয়েছে। চোখ রাখুন, চলচ্চিত্রটির ঘড়ির ঠিক ২৫ মিনিটের কাঁটায়; ক্লোজআপ শটে হাজির হন দাসপ্রভু মিস্টার জোনাস রায়। চিন্তিত-বিমর্ষ তার মুখখানি কেবলই খুঁজে ফেরে লুণ্ঠিত দাস ক্লেমনস রায়কে। অবশ্য, এই দাসের নামের শেষে রায় পদবি দেখে অনুমিত হয় তাদের ভিতর আসলেই বুঝি রক্তের সম্পর্ক। যাহোক, প্রভুকে দেখতে পেয়ে ক্লেমনস-এর সমস্ত শরীর জুড়ে শিহরণ দোলা দিতে থাকে। মনে হয়, কোনো দাস এই মাত্র মুক্তির দেখা পেলো।
এর পর, ক্লেমনস যে মিস্টার জোনাস-এরই লাইসেন্স করা দাস তা প্রমাণ করে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। অবশেষে মুক্তি ও প্রাপ্তির এই আবেগে উল্লসিত হয়ে দাস ক্লেমনস ও প্রভু জোনাস পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। বোঝা যায়, চলতি নিষ্ঠুর জীবনের হাত থেকে এক দাসকে ‘রক্ষা’ করে শ্বেতাঙ্গ এই দাসপ্রভু নতুন জীবন দান করেছেন; রক্ষা করেছেন মানবতা!
দর্শক, ভাববেন না এখানেই শেষ, মানবতা রক্ষায় শ্বেতাঙ্গদের মূল অভিযান এখনো ঢের বাকি। দুই ঘণ্টা ১৪ মিনিট ১০ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ-এর এক ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডেই দেখা মেলে আরেক শ্বেতাঙ্গ রক্ষাকর্তার—মিস্টার বাস (Bass)। যিনি কাজ করতে এসেছেন মি. এপ্সের বাড়িতে। প্রথম দর্শনেই দায়িত্বশীল, কর্মঠ আর সৎ হিসেবে নিজেকে তিনি জাহির করেন। তারপর দাস নির্যাতনের দু-একটি অভিযোগ করেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্বয়ং এপ্সের বিরুদ্ধেই। সঙ্গে শুনিয়ে দেন সাম্যের, সমতার, মানবতার কথা; সাদা-কালো, সর্বজনীন সত্য আর সত্য-মিথ্যার কথা। অবশ্য এসব তার নিজের কথা নয় বলে দাবি করে তিনি বলেন, ‘আমি শুধু ঈশ্বরের চোখ দিয়েই এসব কথা বলছি ...।’ বোঝা যায়, অসত্য যেখানে জেঁকে বসে, মিথ্যা যেখানে ফুলবাবু সাজে, মানবতা যেখানে নিঃশেষ হয়-সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে, বিধাতাপ্রেরিত মহামানবরা যুগে যুগে যেমনটি মানবতা রক্ষা করতে এসেছেন, সত্য বাণী প্রচার করেছেন ঠিক তেমনই মি. বাস-ও এসেছেন দাসদের রক্ষা করতে।
যাহোক, এর পর তিনি সলোমনের আর্জি শোনেন; প্রতিশ্রুতি দেন মুক্তির ব্যবস্থা করার। পরে সলোমনের পরিচিত ক্ষমতাধর একজন শেতাঙ্গকে বিষয়টি জানান তিনি এবং মুক্তি পান সলোমন। এমনকি তার সংসার-সন্তানদের কোলেও তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন তারা। আর এই পুণ্যের কাজ করতে পারার যে প্রশান্ত নির্বাক আনন্দধারা তা-ও ফুটে উঠে সলোমনের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকা শ্বেতাঙ্গ এক রক্ষাকর্তার আপাদমস্তকে। একপর্যায়ে সলোমন-পরিবারের আসন্ন আবেগঘন মুহূর্তের মধ্য থেকে তিনি কোনো কথা না বলে, নিঃস্বার্থ-নিশ্চুপ মানবতাবাদী হিসেবে বাইরে চলে যান।
আবারও প্রমাণ হয়, দাস সলোমনরা কখনো নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন হতে পারে না, শ্বেতাঙ্গ মার্কিনিদের কাছে স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইতে হয়; তারপর তারা এগিয়ে আসেন, রক্ষা করেন, দাসত্ব ঘুচিয়ে ফিরিয়ে দেন পরিবারের কাছে; বিনিময়ে তারা কিছুই চায় না। এ কারণেই হয়তো মানবতা-প্রভু যুক্তরাষ্ট্র চুপি চুপি হাজির হয় ইউক্রেন-রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ সুদান-উত্তর সুদান, সোমালিয়া-ইথিওপিয়া সীমান্তে; শিয়া-কুর্দি-সুন্নি, ইহুদি-মুসলমানদের ‘সাম্প্রদায়িক’ কোন্দলের মধ্যে; কিংবা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমারে—লক্ষ্য একটাই, যেকোনো মূল্যে ‘মানবতা’ রক্ষা। কিন্তু তাদের সেই ‘প্রচেষ্টা’ অর্জিত হয়েছে কি? তাহলে শত শত বছর ধরে চলা মানবতা রক্ষার এই টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ প্রজেক্ট কি চলতেই থাকবে?
স্পার্টাকাসদের দেখা আর মিলবে না!
চলচ্চিত্রটি তখন পার করছে কেবল ২১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড। ঠিক তখনই দেখা মেলে মুখ আটকে রাখা এক দাসের—যার অপরাধ সবাইকে সাহসী হতে বলা, অন্যায়ের বিরদ্ধে লড়াই করতে বলা। একসময় মুখ খুলে দেওয়া হলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সলোমন (মধ্যমনি) ও আরেক দাসের—
দৃঢ়চেতা ওই দাস বলেন : আমি বলছি, আমাদের যুদ্ধ করা উচিৎ।
সলোমন : নাবিকরা সংখ্যায় অনেক কম। যে কারণে এটা একটা ভালো পরিকল্পনাও বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত।
দ্বিতীয় দাস : তাদের সবার বিরুদ্ধে তিন জনের কিছু করা সম্ভব নয়। আর খুদভাত খাওয়া পেট নিয়ে জীর্ণ এই দাসদের যুদ্ধ করার মতো অবস্থা নেই ...।
দৃঢ়চেতা দাস : আমি তো এসবের সবই জানি। দেখো, আমরা যদি মনে করি, এখানে আমরা ভ্রমণ করতে এসেছি, তাহলে মনে রাখতে হবে, মরে যাওয়ার জন্যই আমরা চেষ্টা করছি।
দ্বিতীয় দাস : অর্থহীনভাবে বাঁচতে চাওয়া শুধু মৃত্যুর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, এর সঙ্গে তোমার মাথা নত হওয়ার বিষয়টিও জড়িত (দৃঢ়চেতা দাসকে উদ্দেশ্য করে)।
দাসত্বের চেয়ে লড়াই করে মরে যাওয়াও ভালো—প্রথম দাস যখন এই বিষয়টিই বোঝাতে চাচ্ছেন সলোমনদের, ঠিক তখনই সলোমন কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে ওঠেন, ‘কিছুদিন আগেও আমি আমার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ছিলাম, এখন তোমরা বলছো, সবকিছু শেষ। কেউ আমাকে বলছে না, আমি কে? আর এটাই কি বেঁচে থাকার উপায়? ভালো, কিন্তু আমি এভাবে বাঁচতে চাই না, অর্থপূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।’ দীর্ঘ এই আলাপচারিতার পর আর কোনো কথা না বললেও চলবে, বিপ্লবী ওই দাসের লড়াইকে অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেন সলোমন ও আরেক দাস! এছাড়া সাহসী ওই দাস যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সব দাসদের একত্রিত হওয়ার কথা বলছেন, তখন সলোমন আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, প্রকারান্তরে শুধু নিজের ভালো থাকার কথাই ভাবছেন। তার কাছে সামাজিক যূথবদ্ধ জীবনের চেয়ে ব্যক্তিগত সুখই অর্থপূর্ণ। আর এ কথা তিনি ভাববেন নাই বা কেনো? তিনি তো নিজেকে আর দাস, মানে পরাধীন মানুষ মনে করেন না। তিনি তো নিজেকে দাবি করেন, ‘ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদী’ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক বলে।
দাস হিসেবে বন্দি হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত সলোমন, ‘আমি স্বাধীন মানুষ’ কথাটি প্রায় পাঁচ বার বলেছেন, এছাড়া ‘আমি দাস নই’, ‘আমি নিউইয়র্কের সারাটোগার বাসিন্দা’, ‘আমার জীবন আসলে এ রকম নয়’, ‘আমার স্ত্রী, পরিবারে ছিলো সীমাহীন সুখ’—এমন কথাও অসংখ্যবার তিনি উচ্চারণ করেছেন। একই সঙ্গে এজরা, পাতসি ও অন্যান্য দাসরা যখনই কোনো প্রতিবাদ করতে চেয়েছে, তিনি তাতে বাধা দিয়েছেন। এমনকি শ্বেতাঙ্গ এক দাসপ্রভুকে পর্যন্ত তিনি শালীন, ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
আর এসব কথা প্রমাণের শেষ পেরেকটি মারেন, যখন উদ্ধারকারী শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাকে ছাড়িয়ে নিতে আসে তখন। তার পরই তিনি দুঃখের দিনের সঙ্গী ওই দাসদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে দ্রুত গিয়ে চড়ে বসেন ‘প্রভুদের’ গাড়িতে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ইতিহাসবিদ সলোমন বুঝিয়ে দেন, এক দাস স্পার্টাকাস গ্রিস রাজ্যের সিংহাসনের খুঁটি নাড়িয়ে দিলেও, তিয়েনমেন স্কয়ারে এক ‘ট্যাঙ্ক ম্যান’১১ কামানের সামনে গণমানুষের অধিকার আদায়ে বুক পেতে দিলেও, আজ আর সে বাস্তবতা নেই। এখন সলোমনের ভাষায়, ‘স্ট্রং-আর্মড’ শ্বেতাঙ্গরা আরো বেশি স্ট্রং। সুতরাং কালো-দাস-বন্দি-অসহায় সাবধান! সলোমনদের মতো সমঝোতা ও মানিয়ে চলা নীতি গ্রহণ করো, তাহলে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাই তোমাকে তোমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সুখে রাখবে। স্পার্টাকাসদের মতো মরে গিয়ে কী লাভ!
আসিবে দিন সুদিন
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে
সমালোচনা শব্দটির মানে সম্ভাব্য সব পক্ষকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি বিষয়ে আলোচনা করা। টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ নিয়েও সেরকম একটি আলোচনার ঔচিত্যবোধ-প্রত্যাশা-ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। অনেকের কাছে হয়তো এই আলোচনাটিকে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী-হলিউডবিরোধী মনে হলেও হতে পারে। কেননা দর্শক-আবেগের এই সিদ্ধান্তের ওপরই জায়েজ হয় অস্কার প্রাপ্তি-প্রদানের যৌক্তিকতা। হয়তো এ কারণেই মাত্র ১২ বছরের দাসত্ব তুলে ধরে এই চলচ্চিত্রটি তার ইচ্ছাপূরণ করতে পেরেছে। আর সত্য নির্মাণে এই মাজেজাটুকু বজায় না রাখলে যে অস্কারেরই মাহাত্ম্য থাকে না। তাই টুয়েলভ ইয়ারস অ্যা স্লেভ নিয়ে আলোচনার সময় একজন সমালোচক হিসেবে ‘পক্ষপাতদুষ্টতার দায়ে দায়ী হতে পারি’ এই আশঙ্কা মাথায় রেখেই একটু ঝুঁকি নিয়েছি। আর এতে যদি দণ্ডিত বলে প্রমাণিত হই, তাহলে অপরাধের সাজা মেনে নেবো।
লেখক : রুবেল পারভেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়েছেন।
rubelmcj@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. বিস্তারিত জানতে পড়ুন : পারভেজ, রুবেল; ‘লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন : চলচ্চিত্র-ময়দানে যুদ্ধ’; ম্যাজিক লণ্ঠন; সম্পাদনা : কাজী মামুন হায়দার; বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬, জানুয়ারি ২০১৪, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২. মানবসেবার এক অনন্য নজির সৃষ্টিকারী এই নারী মূলত পাশ্চাত্যের। সেখান থেকে এই ভারতবর্ষে এসে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসা মানুষদের সেবা শুশ্রূষা করে নতুন জীবন দান করেছেন—এমন কথা সারাবিশ্বে বর্তমান। মূলত তার এই মহত্ত্ব তুলে ধরে ইউরোপিয় মানবতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। সেই অর্থে মাদার তেরেসাকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ভিন্ন কারণ থাকতে পারে।
৩. চক্রবর্তী, ড. রতন লাল ও ড. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ (২০১০ : ২); ‘ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাসের উপাদান ও প্রয়োজনীয়তা’; বাংলাদেশ ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস (নবম-দশম শ্রেণি); সম্পাদনা : ড. সিরাজুল ইসলাম; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪. করিম, সরদার ফজলুল (২০০৬ : ৩৫১); ‘দাস ব্যবস্থা’; দর্শনকোষ; প্যাপিরাস, ঢাকা।
৫. ‘আফ্রিকার বাণিজ্যে চোখ ওবামার’; প্রথম আলোর শুক্রবারের বিশেষ ক্রোড়পত্র ‘চলতি বিশ্ব’, ১৫ আগস্ট ২০১৪।
৬. প্রাগুক্ত; প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০১৪।
৭. ব্রাউন, ডি. (২০০৭ : ৩১); ‘তাদের আচার-আচরণ ছিল প্রশংসাযোগ্য’; আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙ্গার বাঁকে; অনুবাদ : দাউদ হোসেন; সংঘ প্রকাশন, ঢাকা।
৮. প্রাগুক্ত; ব্রাউন, ডি. (২০০৭ : ৩২)।
৯. http://www.deathpenaltyinfo.org/mental-illness-and-death-penalty#reduction
১০. ঢাকার ‘দ্য বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি’ প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল নূতন নিয়ম-এর (২০০১, পৃ. ৮) ‘দান, প্রার্থনা ও ধর্মকর্মের কথা’ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।
১১. চিনের তিয়েনমেন স্কয়ারে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালে সংগঠিত হয়েছিলো গণঅভ্যুত্থান। সেখানে অজ্ঞাত এক আন্দোলনকারী মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অভূতপূর্ব সাহসী এই প্রতিবাদের জন্য সবার নিকট তিনি ‘ট্যাঙ্ক ম্যান’ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৫ সালের জানুয়ারির ম্যাজিক লণ্ঠনের অষ্টম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন