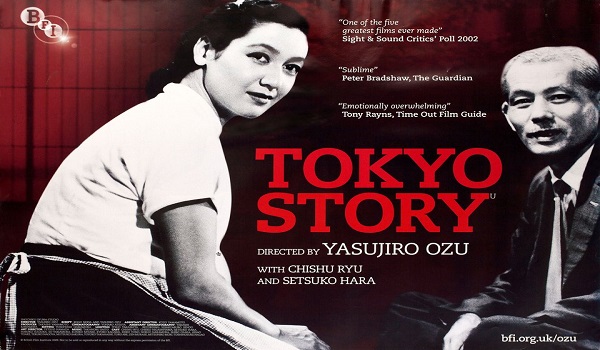প্রদীপ দাস
প্রকাশিত ২৩ জানুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
মনের সঙ্গে বাস্তবের সাযুজ্য রূপায়ণে ভিনের অভিব্যক্তি
প্রদীপ দাস

পুরো নাম : রবার্ট ভিনে
জন্ম : ২৭ এপ্রিল ১৮৭৩, সাইলিজা, জার্মানি
চলচ্চিত্রে অবদান : অভিব্যক্তিবাদ ধারার পথিকৃৎ
মৃত্যু : ১৯৩৮ সালের ১৭ জুলাই, প্যারিস
চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তির চলচ্চিত্র
চলচ্চিত্র নিজ গুণেই বাস্তবতাকে তার মধ্যে ধারণ করে—এটা স্পষ্ট হয়েছে ১৮৯৫ সালে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনীতেই; যখন লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের ধারণ করা ‘স্টেশনে ট্রেন থামা’র দৃশ্য দেখে দর্শক ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। আসলে চলচ্চিত্রে বাস্তবতাকে হুবহু তুলে ধরার এই প্রবণতাকে চলচ্চিত্র-তাত্ত্বিকগণ ১৯ শতকের মধ্যভাগে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন; নাম দেওয়া হয় বাস্তববাদী চলচ্চিত্র ধারা। কিন্তু এই ধারায় সমাজের বাস্তবতাকে হুবহু তুলে ধরলেও সাধারণ মানুষের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণি বা রাষ্ট্রের শাসন, শোষণ, গুম, হত্যার প্রকৃত চিত্র বা কারণ কখনোই উঠে আসতো না। তবে এর নেপথ্যের কারণ বা চিত্র যে কেউ তুলে ধরেনি বা আনেনি, তা নয়। জীবনে ঠেকে লাতিন আমেরিকার নির্মাতারা এমনই এক ধারার শুরু করেন, নাম দেন থার্ড সিনেমা বা তৃতীয় চলচ্চিত্র। যাতে উঠে আসতে শুরু করে উপনিবেশ উত্তর জীবনের দুঃসহনীয় বাস্তবতা।
তৃতীয় চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন-এর মন্তাজ তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কিছুর দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনের মাধ্যমে মন্তব্য জুড়ে মূল খোঁজার চেষ্টা করে মন্তাজ তত্ত্ব। নির্মাতারা মন্তাজের মতো করে অন্যান্য আঙ্গিকবাদী চলচ্চিত্রেও চিন্তা, জ্ঞান, দক্ষতা, আদর্শ, দর্শন ইত্যাদি তুলে ধরতে থাকেন। আর দর্শক শুধু তার পাঠ উদ্ধার করেন। অন্যদিকে, সমাজের বাস্তবতা থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, উপাদান নিয়ে নির্মাতা নির্মাণ করেন বাস্তববাদী চলচ্চিত্র। দর্শক সেই প্রতিফলিত বাস্তবতাকে নিজের মধ্যে পুনঃসজ্জিত করে এবং তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এই বাস্তববাদী চলচ্চিত্র ধারার ঠিক ‘বিপরীত মেরুতে’১ যার অবস্থান, সেটিই হলো অভিব্যক্তিবাদ বা এক্সপ্রেশনিজম।
অভিব্যক্তিবাদে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতরের নির্যাস নিংড়ে বের করে তা দৃশ্যমান করা হয়।২ মানুষের ভিতরের আদিমতা, পাগলামো, আবেগ-অনুভূতি, বোধ, যৌনতা, আত্ম-সমালোচনা ও প্রাণনাশের ভীতির মতো বিষয়গুলো প্রাকৃতিক হওয়ায় তা প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা তার শিল্পকর্মে, চলচ্চিত্রনির্মাতা তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ শুরু করেন। মনোজগতের এই বিষয়গুলো চলচ্চিত্রে তুলে ধরার জন্য আলো-আঁধারের ব্যবহার, সেট নির্মাণ, ছায়ার প্রয়োগ, ক্যামেরার কোণ নির্বাচন এমনভাবে করা হয় যেনো একটা ভয়ানক ও ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যেগুলো পরে নির্মাতারা ক্যামেরার অবজেক্টিভ ব্যবহারের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলেন।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প আন্দোলনের ফলে ইউরোপ-আমেরিকায় পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ গড়ে ওঠে। ফলে ওই সমাজে শ্রমিক, সাধারণ মানুষ ও নিম্নশ্রেণির ওপর চলতে থাকে শাসন, শোষণ ও নির্যাতন। তাদের এই শোষণের চিত্র ২০ শতকের শূন্য দশকে চিত্রকলা, চারুকলা, স্থাপত্য ও নাট্যকলায় উঠে আসা শুরু হয়। শিল্পীরা ব্যক্তির রাগ-ক্ষোভকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলো বলে শিল্পকলায় অভিব্যক্তিবাদ অনেকটা অ্যান্টি-ন্যাচারালিস্টিক শিল্প আন্দোলন হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এই আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে অ্যাডওয়ার্ড মান্চ (Edward Munch) ও ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্ (Vincent Van Gogh) অন্যতম। মানুষের ভিতরের অনুভূতিকে শিল্পকর্মে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য শিল্পীরা ব্যবহার করতেন চড়া রঙ, স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ-এর মতো বিষয়গুলো। এর কিছুটা প্রভাব চলচ্চিত্রেও পড়ে। এ কারণে অনেক চলচ্চিত্রবিদের ধারণা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই জার্মান চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তিবাদের ক্ষীণ ধারা বিদ্যমান ছিলো।
মূলত জার্মান চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তিবাদের অনুপ্রয়োগ ঘটে ১৯১৮ সালের দিকে। তবে এটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২০ সালে রবার্ট ভিনে’র দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারির মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র; যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ক্ষুধা, দরিদ্রতা ছিলো মানুষের নিত্যসঙ্গী। সহিংসতা, যৌনতা, ভয়-ভীতি, হাহাকার, হতাশার মতো বিষয়গুলো গ্রাস করে পুরো সমাজকে। একই সঙ্গে হিটলারের ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিকাশও প্রভাব বিস্তার করে। সেই নিরাপত্তাহীনতা, যৌনতা, অস্থিরতা, পাগলামো, দুঃস্বপ্নতাড়িত আবহের চিত্রই উঠে আসে দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারিতে।
জার্মান সমাজের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক সত্তাকে তুলে ধরার জন্য নির্মাতাদের ভিন্ন ধরনের আঙ্গিকের এই ব্যবহারকে কোনো আন্দোলন না বলে ‘চলচ্চৈত্রিক শৈলী’৩ বলাই শ্রেয়। কারণ ব্যক্তির এই সত্তাকে তুলে ধরার জন্য ‘স্বাভাবিক ইমেজকে ভেঙ্গে ক্যামেরার চোখ দিয়ে নৈর্ব্যত্তিক উপায়ে তাকে’৪ তুলে ধরা শুরু হয়। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর ও ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করতে ‘...ক্যামেরাম্যান শরীরের সঙ্গে ক্যামেরা বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছেন—তাতে মনে হয়েছে ক্যামেরাই যেন হাঁটছে।’৫ শুরু হয় ক্যামেরার সাবজেক্টিভ ব্যবহার। নির্মাতা মুরনাউ-ই প্রথম কাট্ না করে মিড লঙ্ থেকে ক্লোজ আপ ও ট্রলি শট্ ব্যবহার শুরু করেন এই ধারায়। ট্র্যাক শট্, ফ্লাশব্যাক, ডিজল্ভ, স্লো-মোশন ও নেগেটিভের ব্যবহারও এতে লক্ষ করা যায়। ওই সময়টাতে শব্দের ব্যবহার না থাকলেও দৃশ্যমাত্রাগত দিকটাতে জোর দেওয়ার জন্য সাব-টাইটেলের ব্যবহারও এড়িয়ে চলা হতো।
অভিব্যক্তিবাদ ধারায় অভিনয়শিল্পীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, নির্মাতারা এখানে মানুষের ‘মনের মধ্যে জগতের যে প্রতিরূপ রয়েছে, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জগতের এক প্রতিরূপ রচনা’৬ করে। এই রচনায় অভিনেতা সক্রিয় না থাকলে তা ফুটিয়ে তোলা সহজ হয় না। তাই শিল্পীর ভিতরের বোঝাপড়া, প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
মজার ব্যাপার হলো, হিংসার বিরুদ্ধ অবস্থান থেকে উঠে আসা অভিব্যক্তিবাদ চলচ্চিত্রগুলো জার্মান সমাজকে আরো বেশি হিংসাত্মক করে তোলে। এ সুযোগে হিটলার তার নাৎসি পার্টির মুখপাত্র হিসেবে এই শৈলীকে ব্যবহার শুরু করেন। শুধু যে নাৎসি পার্টির ‘বক্তব্য বিধৃত’৭ কিংবা ‘বুর্জোয়া বাস্তবতাকে ভেঙ্গে চলচ্চিত্রকারদের নিজ নিজ মনোজগতের আলোকে সমাজবাস্তবতাকে দেখার ইচ্ছা’৮ থেকেই জার্মান চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তিবাদ জায়গা করে নিয়েছিলো বিষয়টা মোটেই এমন নয়। এর পিছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিলো ইউরোপ, আমেরিকায় এসব চলচ্চিত্রের বাজার। ফলে প্রযোজকরা টাকা দিতে কুণ্ঠা বোধ করতো না।
১৯২৪ সালের দিকে অভিব্যক্তিবাদ স্তিমিত হতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে এই ধারার মন্দার ফলে হাত-গুটিয়ে নিতে থাকে প্রযোজকরা। অন্যদিকে নির্মাতারা বুঝে ফেলেন, এই চলচ্চিত্র নির্মাণে জার্মানির চেয়ে আমেরিকা তাদের জন্য বেশি নিরাপদ। ফলে অভিব্যক্তিবাদের বেশিরভাগ নির্মাতাই আমেরিকায় পাড়ি জমান। সেখানে তাদের হাতে শুরু হয় ফিল্ম নয়ার (Film Noir) নামে লোমহর্ষক এক চলচ্চিত্র ধারার। তবে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আলফ্রেড হিচকক্, ওরসন ওয়েলস্’সহ বেশ কয়েকজন নির্মাতার চলচ্চিত্রে অভিব্যক্তিবাদের উপাদান লক্ষ করা যায়।
নির্মাতা ভিনে’র জীবন-পাণ্ডুলি
জার্মানির সাইলিজা (Silesia) প্রদেশের রাজধানী ব্রেসলো (সাইলিজা বর্তমানে পোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত)। ১৮৭৩ সালের ২৭ এপ্রিল এ শহরেই জন্ম রবার্ট ভিনে’র। বাবা কার্ল ভিনে আর মা পলিন লভি’র (Paulin Loevy) দুই সন্তানের মধ্যে ভিনে ছিলেন বড়ো। বাবা নাট্যশালায় জড়িত থাকায় ভিনে বেড়ে ওঠেন অনেকটা সাংস্কৃতিক পরিবেশেই। ভাই কনর্যাড ভিনেও ছিলেন একাধারে অভিনেতা, পরিচালক ও সংস্কৃতিকর্মী। ভিনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি স্টুটগার্ট (Stuttgart) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে; মাধ্যমিক শেষ করেন ড্রেসডেন (Dresden) উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। এরপর ভিনে ১৮৯৪ সালে বার্লিনের হামবোল্ড (Humboldt) বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তবে একই বছরের ২০ অক্টোবর চলে আসেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে অবশ্য তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে ৪৫ বছর বয়সে ভিনে তার চেয়ে ২১ বছরের ছোটো হেনরিয়েট’কে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনে তারা ছিলেন নিঃসন্তান।
১৯০১ সালে ওয়াইমার-এ (Weimar) আইন চর্র্চা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন রবার্ট ভিনে। ১৯০২-০৩ সালের দিকে ভিনে’র নামের সঙ্গে ‘জুরিস্ট’ (অ্যাটর্নি) শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এদিকে ভিনে যেনো তার পরিবার থেকে পাওয়া শিল্প-সংস্কৃতির পিছুটান কিছুতেই ছাড়তে পারছিলেন না। সেই টানেই ১৯০৩ সালে তিনি যোগ দেন অপেরায়, আটকে পড়েন নাট্যাঙ্গনের মায়ার বাঁধনে। বাবার খ্যাতির সুবাদে তারও পরিচয় ঘটে লেখক, নাট্যকর্মী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে। তাদের সংস্পর্শে এসে, তাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে আইনজীবী ভিনে হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন। এভাবে তিনি জীবন-নদীর এক পাড়ে আইন পেশা, অন্য পাড়ে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে সমান তালে বয়ে নিয়ে চলছিলেন।
১৯০৮ সালে ভিনে চলে আসেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে; এসেই নাটকে অভিনয় শুরু করেন। সে বছরেই Kleines Schauspielhous নাট্যশালার প্রধান নির্বাচিত হন, কিন্তু বেশিদিন সে দায়িত্ব পালন করেননি তিনি। ওই বছরেরই ৩১ অক্টোবর অ্যাডল্ফ স্টেইনার্ট-এর (Adolf Steinert) সঙ্গে যৌথ মালিকানায় Neue Wiener Buhne নামে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু হয় এই নাট্যশালার। কিন্তু অংশীদারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ১৯০৯ সালের ৫ মে নাট্যশালাটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন ভিনে। অবশ্য নাট্যশালাটি পরে বেশ নামডাক কুড়িয়েছিলো। আসলে এই দুটি নাট্যশালাই নাটককে ভিনে’র পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিলো।
২০ শতকের শূন্য দশকে শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার আগ্রহ ভিনে’র আরো বেড়ে যায়। কারণ তখন নতুন শিল্প-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র কেবল পথ চলতে শুরু করেছে। চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতাও তখন ব্যাপক। মানুষের এই আগ্রহের বিষয়টি ভিনে’কে আকৃষ্ট করে। তাই তিনি নাটক ছেড়ে চলচ্চিত্রের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কলম হাতে স্ক্রিপ্ট লিখলেন, ক্যামেরা কাঁধে নির্মাণ করলেন প্রথম চলচ্চিত্র Die Waffen der Jugend (১৯১২)। ১৯১৩ সালের দিকে জার্মানিতে নাট্যশিল্পীরা দলে দলে চলচ্চিত্রে যোগ দিতে শুরু করলে জার্মান চলচ্চিত্র শক্ত একটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়।
১৯১৪-১৯ সালের এই সময়টাতে ভিনে চিত্রনাট্য লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেন। বিশেষ করে সেই সময়ের জার্মান চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা হেনি পর্টেন-এর (Henny Porten) জন্য তিনি চিত্রনাট্য লেখেন; পরে ভিনে’র তিনটি চলচ্চিত্রে পর্টেন অবশ্য অভিনয়ও করেন। ভিনে’র চিত্রনাট্য লেখার পটুতার কথা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিলো।
ক্যালিগারি নির্মাণের আগে ভিনে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেন। এর মধ্যে মেস্টার (Messter) ফিল্ম, বার্লিনের ডয়চে বায়োস্কোপ (Deutsche Bioscop) ও ভিয়েনার সাসকা ফিল্ম কোম্পানি উল্লেখযোগ্য। এসব কোম্পানির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সবসময় মুনাফার কথা মাথায় রাখতে হতো ভিনে’কে। তাই তার অনেক চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছিলো সমাজের বিভিন্ন হাস্য-রসাত্মক ঘটনা, পারিবারিক মেলোড্রামা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক উপাদান। তাই বলে এটা ভাবা ঠিক হবে না, স্বদেশ-ভাষার প্রতি প্রাণের আকুতি কিংবা সমাজের অসঙ্গতি ভিনে’র চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এর পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের সমাজে বিরাজমান অবস্থাও চলচ্চিত্রে তুলে ধরেন ভিনে। তার অনুরোধেই জার্মান চলচ্চিত্রের উন্নতি, রক্ষা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মেস্টার ও সাসকা ফিল্ম কোম্পানি যৌথভাবে সাসকা-মেস্টার ফিল্মফেব্রিক (Sascha-Messter Filmfabrik) প্রতিষ্ঠা করে। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের চলচ্চিত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
ভিনে’র জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হলো দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি। চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ তিনি এমন একসময় শুরু করেন, যখন কিনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র; কিন্তু মানব-মনে সেই যুদ্ধের ভয়াবহতার রেশ একটুও কাটেনি। এমন সময় হ্যান্স জানোভিজ ও কার্ল মায়ার নামে দুই ব্যক্তি বার্লিনে মিলিত হন। যৌগিক মাধ্যম চলচ্চিত্র তাদেরও আকৃষ্ট করে। তারা এক মেলায় ‘মানুষ ও মেশিন’ নামে প্রদর্শনী দেখেন। ওই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়, এক লোক সম্মোহিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারছে। এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জানোভিজ ও মায়ার একটি চিত্রনাট্য লিখে ফেললেন। যা থেকে পরে নির্মাণ করা হয় দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি। এই চিত্রনাট্যটি তারা বার্লিন ফিল্ম কোম্পানির প্রযোজক এরিখ পমার-এর (জার্মান চলচ্চিত্র প্রযোজক; ১৮৮৯-১৯৬৬) কাছে নিয়ে গেলে, তিনি প্রথমে সেটি নিতে না চাইলেও পরে গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। পমার প্রথমে এটি বিখ্যাত জার্মান পরিচালক ফিৎজ’কে নির্মাণ করতে বলেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত থাকায় এটি পরিচালনার দায়িত্ব পান ভিনে। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বার্লিনে কাজের শুরুতেই একটি পরীক্ষামূলক শট্ নেন ভিনে; সেই শট্ দেখে পমার খুশি হয়ে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেন।৯
১৯২০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বার্লিন মার্মোরাস-এ (Marmorhous) চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রদর্শন হয়। এতে চারদিকে সমালোচনার পাশাপাশি দারুণভাবে প্রশংসাও হতে থাকে। ক্যালিগারির অকল্পনীয় সফলতা ভিনে’র জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। অন্য নির্মাতাদের জন্য চিত্রনাট্য লেখা কমিয়ে দিয়ে তিনি পরিচালনার কাজে মনোযোগ দেন। তিনি একে একে The Night of Queen Isabeau,Genuine,The Three Dances of Mary WilfordIPanic in The House of Ardon নির্মাণ করেন।
ভিনে’র প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলো ছিলো বেশ ব্যয়বহুল ও দুঃসাহসিক। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ক্যালিগারির সফলতাই পরের কাজগুলোতে ভিনে’কে আরো সাহসী করে তোলে। এ সময় বড়ো বড়ো তারকারাও তার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যিশু খ্রিস্টের জীবনী নিয়ে নির্মিত I.N.R.I (১৯২৩) চলচ্চিত্রে হেনি পোর্টার, অ্যাস্টা নেলসন (Asta Nielsen) ও ওয়ের্নার ক্রাব-এর (Werner Kraub) মতো বিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেখা যায়। ভিনে ক্যালিগারি নির্মাণের পর প্রায় একই ধরনের জেনুইন (১৯২০) নামে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু জেনুইন সফলতার মুখ দেখেনি। তবে পরবর্তী সময়ে নির্মিত রাসকোলনিকো (Raskolnikov, ১৯২৩) চলচ্চিত্রটি জার্মান চলচ্চিত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো।
ভিনে’র জীবনে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯২৪ সালে আবার ভিয়েনায় ফিরে যাওয়া। সেখানে ফিরে তিনি ‘পান ফিল্ম কোম্পানি’র (Pan Film Company) সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের জন্য Orlacs Hande(1924), Boading House Groonen(1925),The Guardsman(1925), Der Rosenkavalier (১৯২৫-২৬) চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করেন। এর মধ্যে Orlacs Hande ও Der Rosenkavalier আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়।
ভিনে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যেমন বুঝতে পারতেন, সঙ্গে তার শৈল্পিক দক্ষতাও ছিলো চমৎকার। এ প্রসঙ্গে Orlacs Hande -এর অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা সরিনা (Alexandra Sorina) ভেনিসের জনপ্রিয় এক জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘রবার্ট ভিনে সেই পরিচালক, যার রুচিসম্পন্ন শৈল্পিক বোধ আছে। সবসময় তিনি নতুন শৈল্পিক প্রতিবন্ধকতাকে অন্বেষণ করতেন। শিল্পীদের মানসিক গভীরতাটা ভিনে জানতেন, তাই কাজ করার সময় তাদের নিয়ে তৈরি করতেন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ।’১০
নির্বাক যুগের শেষের কয়েকটি বছর ভিনে বার্লিনেই কাটান। এখানে এসে চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি তিনি জোহান স্ট্রস-এর (Johann Strauss) ওপর আত্মজীবনীমূলক একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ সময় নির্মাণ করা তার অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে Die Konigin van Moulin Rouge(1926),Die Geliete(1927),Die beruhmte Frau(1927),Die Frau auf der Falter(1928) IDie grosse Abenteuerun (1928)। রম্য ও হাস্য-রসাত্মক বিষয়ে নির্মাণ করা এ চলচ্চিত্রগুলো ছিলো মূলত নারী প্রধান।
বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হলো ১৯২৯। এ বছরই চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে প্রবেশ করে সবাক যুগে, সঙ্গে জার্মান চলচ্চিত্রও। ভিনে অবশ্য এই বছর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি। ১৯৩০ সালে তিনি নির্মাণ করেন প্রথম সবাক চলচ্চিত্র Der Andere। পরবর্তী সময়ে তিনি Der Liebesexpress(১৯৩১),Panik in Chicago(১৯৩১) ITaifun (১৯৩৩) নামে তিনটি সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। পরে ভিনে দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি পুনর্নির্মাণ করে সবাক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তার নির্মিত অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হলো—He This Way,She That Way(১৯১৫), The Canned Bride(১৯১৫),The Queen's Secretary(১৯১৬),Lehmann's Honeymoon(১৯১৬), Steadfast Benjamin(১৯১৬), The Infernal Power(১৯২২),The Doll Maker of Kiang-Ning(১৯২৩) ইত্যাদি।
১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ক্ষমতায় আসেন হিটলার; শুরু হয় দমন-পীড়ন। বাদ যায় না চলচ্চিত্রশিল্পও। চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ, সেন্সরে আটকানোসহ নানাধরনের উৎপাত শুরু হয় চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর। হিটলারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চলচ্চিত্রনির্মাতাসহ দেশের শিল্পপ্রেমী মানুষেরা পাড়ি জমাতে থাকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। ১৯৩৩ সালে টাইফান-ই ছিলো জার্মানিতে নির্মিত ভিনে’র সর্বশেষ চলচ্চিত্র। জার্মান সরকার ওই বছরের ৩ মে চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করলে তা আর প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি হাঙ্গেরিতে চলে আসেন। হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল ‘ফিল্মকুলটুরা’(Filmkultura) মারফত জানা যায়, ভিনে ১৯৩৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বুদাপেস্টে এসে Eine Nacht in Venedig -এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। অবশ্য পরে ভিনে আর জার্মানিতে ফিরেননি।
ভিনে তার নির্বাসিত জীবনের কিছু সময় (১৯৩৫-৩৬) লন্ডনে কাটিয়েছিলেন। এখানেও তিনি চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ ফিল্ম ক্যাটালগে প্রযোজক হিসেবে নিবন্ধিতও হন। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে প্যারিসে বসবাস শুরু করেন ভিনে; সেখানেই ১৯৩৮ সালের ১৭ জুলাই ৬৫ বছর বয়সে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমান পরপারে।
চলচ্চিত্র দ্য কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি
ফ্রান্সিস ও এলান দুই বন্ধু। একবার তারা হোলস্টেনওয়াল-এ (Holstenwall) তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে। সেখানে তারা এক মেলায় ঘুরতে যায়। দুই বন্ধুর পরিচয় হয় হাতুড়ে চিকিৎসক ক্যালিগারির সঙ্গে। ক্যালিগারি মেলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ক্যালিগারি সেখানে সিজার নামের এক ব্যক্তিকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সিজার আসলে ২৫ বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে এবং ওই অবস্থাতেই সে হাঁটাচলা করে।
সিজারের আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো—সে সম্মোহিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতো। এলান কবে মারা যাবে জানতে চাইলে সিজার জানায়, তার মৃত্যু আসন্ন। আর ঘটেও তাই। বন্ধুর এমন পরিণতির কারণ উদ্ঘাটন করতে ফ্রান্সিস সবকিছু পুলিশকে জানায় এবং ক্যালিগারি ও সিজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে।
এদিকে ফ্রান্সিসের বাগদত্তা জেন তার বাবার খোঁজ-খবর না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। সে বাবার খোঁজে বের হলে হঠাৎ একদিন ক্যালিগারির সঙ্গে দেখা হয়। জেনকে হত্যার জন্য সিজারকে নির্দেশ দেয় ক্যালিগারি। কিন্তু সিজার জেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আর খুন করতে পারে না। জেনকে নিয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে এবং একপর্যায়ে এলাকাবাসী তাকে ধরে ফেলে।
এখানে এসে ঘটনা নতুন দিকে মোড় নেয়। ফ্রান্সিস আবিষ্কার করে ক্যালিগারি একটি পাগলা গারদের প্রধান। সে সবাইকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সিজারকে তৈরি করেছে। ১০৯৩ সালে উত্তর ইতালির এক লোক ছিলো, সে ঘুমের ঘোরে হাঁটে—এমন লোক দিয়ে মানুষ খুন করাতো। ওই লোক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্যালিগারি এমন কাজ করে। পরে অবশ্য সিজারকে মুমূর্ষু অবস্থায় ক্যালিগারির কাছে আনা হলে সে অনুতপ্ত হয়। ঘটনা জানাজানি হলে ক্যালিগারিকে আটক করে রাখা হয় পাগলা গারদে।
আসলে পুরো ঘটনাটি ফ্রান্সিস এতক্ষণ বর্ণনা করছিলো। তার বর্ণনা শেষ হলে ঘটনা নতুন মোড় নেয়। জানা যায়, ক্যালিগারি ও জেনকে নিয়ে মূলত ফ্রান্সিস এমন গল্প ফেঁদেছে। ক্যালিগারি আসলে ওই পাগলা গারদেরই চিকিৎসক, যার ওপর দায়িত্ব ছিলো ফ্রান্সিসকে সুস্থ করার।
লেখক : প্রদীপ দাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
pradipru03@gmail.com
তথ্যসূত্র
১. আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৪); ‘চলচ্চিত্র ধারাসমূহের অন্তর্গত পাঠ’; চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।
২. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৪)।
৩. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৪)।
৪. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৬)।
৫. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৭)।
৬. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৪)।
৭. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৭)।
৮. প্রাগুক্ত; আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৬৭)।
৯. রহমান, মুম (২০১১ : ১৩); বিশ্বসেরা আরো ৫০ চলচ্চিত্র; আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।
১০. http://www.jstor.org/stable/3815107?
পাঠ সহায়িকা
আউয়াল, সাজেদুল (২০১১); চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।
https://mubi.com/cast_members/15075
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
http://www.jstor.org/stable/3815107?
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন