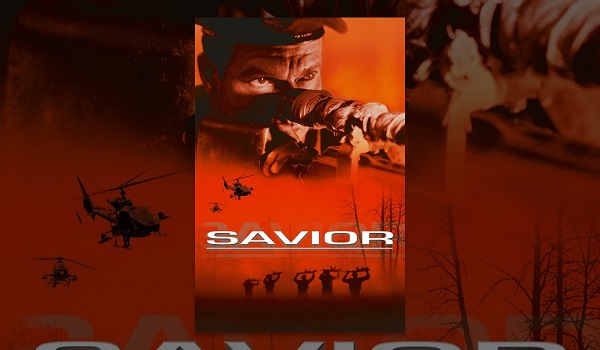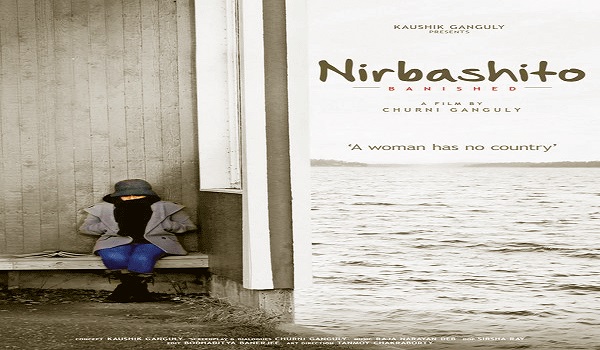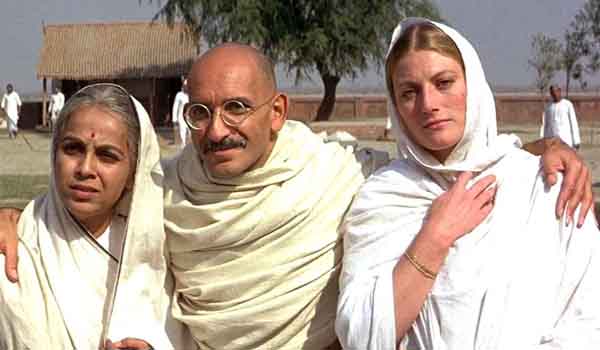আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির ও সাবরিয়া সাবেরিন বাঁধন
প্রকাশিত ১৭ জানুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
জল ফুরালে ফুলের হিসাব
অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের ছবি কামার আহমাদ সাইমনের `শুনতে কি পাও!'
আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির ও সাবরিয়া সাবেরিন বাঁধন
1673955474.jpg)
আমাদের এই দুনিয়াটার ধরণই এমন—বিচিত্র, অজস্র, অসীম সবকিছু ছড়িয়ে আছে এর সবখানে। আর এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরকাল এক রকম থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই নানা পরিবর্তন, পরিমার্জন, বিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, বিভাজন ইত্যাদি চলে যুগের পর যুগ। এই হয়তো সর্বকালের, সর্বস্থানের সত্যতম স্বাভাবিকতা। কিন্তু মানুষ আজীবন কারণে-অকারণে, জেনে/না-জেনে অস্বাভাবিকের জন্য অপেক্ষা করে। অসুন্দর বা ভয়ানকের সঙ্গে একটানা বহুদিনের দেখা না হওয়াটা, মানুষ তার একান্ত স্বভাবের কারণেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যদি চিরকাল শান্ত-সৌম্য-ভদ্র হয়ে থাকে, ঝড়-খরা-ঢল কিছুই যদি না ঘটে, তবে দুনিয়া আর দুনিয়া থাকে না।
এখন প্রশ্ন হলো, এই স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক ঝড়-ঝঞ্ঝার সমস্তই কি বিধ্বংসী, সবটাই কি ক্ষতিকর? দুর্যোগের সময়টাতে প্রকৃতি নিষ্ঠুর ঘাতক হয়ে ওঠে—এ তো স্পষ্ট সত্য। কিন্তু একে কি একক সত্য বলা যাবে? এই দুর্যোগ বা দুর্যোগাক্রান্ত এলাকা, সময় বা মানুষগুলো সুন্দর নাকি অনাকর্ষণীয়? ঝড়ে গাছেরা নুয়ে পড়ছে, টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট সবকিছু, এখানে কতোখানি সুন্দরের বাস? অথবা ‘সুন্দর’ আসলে কী? ‘যার নয়নে যারে লাগে ভালো’—এই ধরনের একটা প্রবাদ আছে। সুন্দর চিরকালই আপেক্ষিক। একেকজনের একেক রঙ, একেক গন্ধ ভালো লাগে। কারো কারো মতে, সৌন্দর্যবোধ তৈরি হয় মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিপাশ থেকে। একেকটা সংস্কৃতি তাদের মতন করে সুন্দর, অসুন্দরের প্রভেদ করে নিয়েছে।
‘...সময়ের সাথে সাথে, সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে সৌন্দর্যের ধারণা বদল হয়। উন্নত বক্ষের মেরিলিন মনরো ১৯৫০ এর দশকের মার্কিন মুল্লুকে ছিলেন সুন্দরের প্রতীক, পরবর্তীতে তাঁর জায়গায় এসেছেন শীর্ণকায় টুইগি। চীনে পুতুলের মতোন মসৃন চামড়ার যেমন কদর, তেমনি আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় চামড়া পুড়িয়ে, খোদাই করে সুন্দর করা হয়।’১
এ সম্পর্কে ডারউইন অনুসারীদের মত অন্য। তাদের ধারণা, সৌন্দর্যবোধ বিবর্তনের ফল, জিনগতভাবে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে থাকে। ‘...এরপর কখনও যদি কোন গয়নার দোকান আপনার সামনে পড়ে, কোন জলকণার মতোন জ্বলজ্বলে পাথর যদি আপনার ভালো লেগে যায়, মনে করবেন না কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক পরিপাশ, বিকাশের কারণেই আপনার এই ভালোলাগা। আপনার বহুকালের পূর্বপুরুষ/নারী নিশ্চয়ই এই ধরনের জলকণা-রত্ন ভালোবাসত।’২ মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের নানা রকমফের হয়। সবচেয়ে বেশি বদলে যায় বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। কামার আহমাদ সাইমন দুর্যোগ আর মানুষের এই সম্পর্ককে তুলে এনেছেন শুনতে কি পাও! (২০১৪) চলচ্চিত্রে। ২০০৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আইলা নামের এক ভয়াল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। সাইমন ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে দুর্গত এলাকাগুলোতে ভ্রমণ শুরু করেন।৩ মানুষের দুর্গত, অসহায় অবস্থার মধ্যেই আবিষ্কার করেন এক অকল্পনীয়, অনন্য সৌন্দর্য; যা দুর্যোগহীন, শান্ত দুনিয়ায় কোনোভাবেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব না।
আ.
চিত্রকলায় অভাব, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, খুন, ধর্ষণ এসব অজস্রবার বিচিত্র রকমে এসেছে। ফ্রান্সিসকো গয়া, ফ্রিদা কাহলো, জয়নুল আবেদিন, এস এম সুলতানসহ বহু শিল্পী সংগ্রাম, দুর্যোগ, নিষ্ঠুরতা, অস্ত্র, রক্ত, অনাহারকে তাদের ছবির বিষয়বস্তু করে বিখ্যাত, জনপ্রিয় হয়েছেন। আর মার্শেল ডুচাম্প-এর ‘দ্য ফাউন্টেইন’-এর কথাও এখানে উল্লেখ করার মতন। তিনি এবং অন্যান্য দাদাবাদী শিল্পীরা দেখিয়েছেন, যেকোনো সময়, যেকোনোভাবে, যেকোনো বস্তু শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে। ঝড়ের মতন ভয়াল, খুনের মতন নিদারুণ, দুর্ভিক্ষের মতন অনাকাক্সিক্ষত বিষয়ও দর্শকের মনে একধরনের আনন্দানুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম।
সাইমন তার চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন, কীভাবে আইলা-আক্রান্ত, বিধ্বস্ত একটা গ্রাম শত অভাব-অভিযোগ, দুরাবস্থার পরও হয়ে উঠতে পারে মানুষের আদিম সৌন্দর্যের প্রতীক; প্রকৃতির সঙ্গে হার-জিতের খেলা না। আমরা বরং দেখি কী করে মানুষ প্রকৃতিকে জেনে বুঝে, প্রকৃতির রাগ/শাস্তি মেনে নিয়ে, অপার সাহস, বুদ্ধি আর শক্তিতে আবারো জীবন শুরু করে, তাও আবার এই প্রকৃতির কোলেই।
শুনতে কি পাও!-এর গল্প রাখি (২৭), সৌমেন (৩২) ও তাদের একমাত্র সন্তান রাহুলকে (৬) ঘিরে আবর্তিত। আইলাবাহিত জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি হারিয়ে খুলনা জেলার সুতারখালি গ্রামের মানুষ আশ্রয় নেয় গ্রামের উঁচু বাঁধে। রাখি, সৌমেন আর রাহুল তাদেরই তিনজন। পুরো চলচ্চিত্রে এই বাঁধবাসীদের জীবনের নানান মুহূর্ত উঠে এসেছে। অভাব, উৎসব, কান্না, হাসি—এভাবে গল্প এগোতে থাকে। একটা পর্যায়ে গিয়ে সব মানুষ একত্র হয়, নিজেদের বাড়ি ফিরে পাবে এই আশায়। নির্মাণ হয় প্লাবনের লোনা জল থেকে উদ্ধারকারী একটা বাঁধ। শুরু হয় ঘরে ফেরা।
গয়া’র বিখ্যাত ছাপচিত্রগুলো মনে পড়ে, ‘ক্যাপ্রিকোস’ (১৭৯৭-৯৮) আর ‘দ্য ডিজাস্টারস অব ওয়ারস’ (১৮১০-২০)। এই ছবিগুলো যুগের পর যুগ টিকে আছে, বহুকাল ধরে মানুষের মনে ভয়ের অনুভূতি আর সংগ্রামের আবেদন রচনা করে আসছে। যেসব বাস্তবতা প্রতিদিন দুঃস্বপ্নের মতন ঘনিয়ে আসে, যেসব অপ্রত্যাশিতকে সকাল-বিকাল মোকাবেলা করতে হয়, সেসবই গয়া’র ছবিতে একের পর এক তুলে আনা। ‘ক্যাপ্রিকোস’-এ যেমন একটা ছবি আছে, ‘দ্য স্লিপ অব রিজন প্রোডিউসেস মনস্টারস’। একটা লোক তার ছবি আঁকার টেবিলে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে গেছে। শরীরের চারপাশে উড়ছে বেশকিছু বাদুড় আর পেঁচা জাতীয় প্রাণী। ‘অ্যান্ড দেই স্টিল ডোন্ট গো’ নামের আরেক ছবিতে দেখা যায়, আধমরা কিছু মানুষের গায়ের ওপর একটা দেয়াল ভেঙে পড়তে যাচ্ছে আর ভীত-সন্ত্রস্ত একজন নারী চোখ বড়ো করে সেই দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য একজন লোক তার সমস্ত শক্তি একত্র করে চেষ্টা করছে দেয়ালটাকে থামাতে। শুনতে কি পাও!-এ আমরা দেখি হাঁটু সমান কাদাপানিতে কয়েকজন লোক নৌকা ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে; আরেকটা দৃশ্যে কয়েকজন নারী একটা মাটির বস্তা কাদা-জল পার করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। গয়া বা সাইমন দুজনই সংগ্রাম আর চেষ্টার মধ্যকার অসামান্য সুন্দরকে ধরতে পেরেছেন, আর মমতায় তুলে এনেছেন ক্যানভাসে বা পর্দায়।
চলে আসে ফ্রিদা কাহলো’র ছবির প্রসঙ্গ। তার ছবিতে আমরা একধরনের গাঢ় বেদনার গন্ধ পাই। ঘন হয়ে আসা দুঃখবোধ তার ছবির অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যখন আমরা ছবিগুলো দেখি, কেনো জানি এতকিছুর পরেও একধরনের ভালোলাগা, অদেখাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ বা তৃপ্তির অনুভূতি কাজ করে। যেমন ‘ব্রোকেন কলাম’ নামের ছবিটা। এই ছবিটা আপাত দৃষ্টিতে কেবল একজন নারীর দুঃখভারাক্রান্ত ভাঙা শরীর, যে শরীরের আর কোনো আবেদন, অনুভূতি নেই। কিন্তু মেয়েটার চোখ একধরনের ভিন্ন গল্প বলে। যেনো একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন এখনো তার চোখে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।
সংগ্রামে ভেঙে পড়ার মধ্যেও অনেক সময় এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়, যার আর কোনো তুলনা হয় না। কাহলো’র অন্য আরেকটা ছবি, ‘উন্ডেড ডিয়ার’-এর বিষয় আর সাইমনের ছবির চরিত্র রাখির মধ্যে বেশ মিল আছে। ‘উন্ডেড ডিয়ার’-এ আমরা দেখি এক নারীমুখী হরিণ, গায়ে অনেকগুলো তির বিঁধে আছে। রক্ত ঝরছে অথচ চোখে জীবনের ছবি এখনো স্পষ্ট, পায়ে সামনে চলার ঢঙ এখনো বিদ্যমান। তিরের বিষে ঢলে পড়েনি, এখনো সোজা দাঁড়িয়ে। রাখিও তেমন। মুসলিম দেশে হিন্দু, পুরুষের দুনিয়ায় নারী, ধনীর রাজ্যে সহায়সম্বলহীন রাখি। বহু বৈষম্যের তির উপেক্ষা করেও মুখে অবিচল হাসি বজায় রেখে, জীবনের গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে। মুগ্ধ চোখে দেখার মতো আকর্ষণীয় আর কী হতে পারে?
জয়নুলের ছবির সঙ্গেও অনেকখানি যায় শুনতে কি পাও!; ৪৩-এর (বঙ্গাব্দ) দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঁকা স্কেচগুলো, ৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় অবলম্বনে ‘মনপুরা ৭০’—এই ছবিগুলোতে তিনি জীবন, মৃত্যু, মানুষ, শকুন, কুকুর, কাক, হাহাকারকে তুলে এনেছেন এক জমিনে। মৃতপ্রায় মানুষগুলো শহরের ডাস্টবিনের পাশে পড়ে আছে শেষবারের মতন বাঁচার আকুতি নিয়ে। কাক, কুকুর অপেক্ষায় আছে মানুষগুলোর মৃত্যুর। তাদের অপেক্ষারও অন্য নাম আরো খানিক বেঁচে থাকা। সুতরাং মরণ-গন্ধ নিয়ে আঁকা ছবিগুলোর পরতে পরতে আছে জীবনের ঘ্রাণ। ‘মনপুরা ৭০’-এ দেখা যায়, এক স্তূপ মৃত মানুষের পাশে বসে মাথা গুঁজে কাঁদছে একজন। পুরো দ্বীপ হয়তো জনশূন্য হয়ে গেছে ঝড়ে। একলা একজন বসে বিলাপ করছে। এই যে একজন তবু বেঁচে আছে, এর মানে জীবন একেবারে থেমে যায়নি। এখানে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। এই একজনের নির্বাক বিলাপ, পাশে অসংখ্য মৃতদেহ—বোঝা যায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন সবচেয়ে প্রিয় হয়ে যায়, শত মৃতের পাশে জীবন্ত একজন তাই অনন্য এক ভালোলাগা জাগিয়ে তোলে মনে।
বাড়ির জন্য, ভিটামাটির জন্য মানুষের সহজাত দুর্নিবার আকর্ষণের কথাও আছে শুনতে কি পাও! চলচ্চিত্রে। আইলার মতন প্রলয় মানেই ঘরছাড়া সহস্র মানুষ। এরা নিজের ঘর থেকে দূরে কোথাও দিন কাটায়, রাত কাটায়। গায়ে গা লাগিয়ে, অল্প জায়গায় নতুন ঘর বাঁধে। এই যে অস্বাভাবিক কিন্তু মনোরম মানুষের পাশাপাশি অবস্থান, এর মধ্যেই আছে দেখে ভালো লাগে এমন কিছু। শুনতে কি পাও! বার বার এস এম সুলতানের ছবির সেই পেশীবহুল মানুষগুলো, তাদের একত্র সংগ্রাম আর সমান জীবনযাপনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ‘জলোচ্ছ্বাস’ (১৯৮৬) চিত্রে দেখা যায়, পেশীসমৃদ্ধ, গৃহহারা এক ঝাঁক মানুষ ধানের ক্ষেতে পড়ে আছে। এর মধ্যে হাহাকারের অনেক কিছু থাকলেও, এই যে কাছাকাছি অবস্থান মানুষগুলোর, ছবির রঙের ব্যবহার, এসব কেমন যেনো পছন্দের ব্যাপার হয়ে যায়। ‘ঝড়ের পরে’ (১৯৯০) নামের ছবিতে দেখা যায়, একের পর এক গাছ ঝড়ে উপড়ে গেছে। লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া গ্রামে তবুও জীবনের আয়োজন চলছে। আবারো সবকিছু শুরুর আয়োজন। আবারো পাশাপাশি ঘুরে দাঁড়ানো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ধ্বংসলীলার পাশাপাশি জীবনের আসল রূপ, সত্যিকারের জীবনসংগ্রাম, মানুষের অদম্য এক শক্তিকে চোখের সামনে তুলে আনে সুলতানের ছবিগুলো।
ই.
সংগ্রামের রং শাদা
সংগ্রাম জীবন, সত্য; এই কথা ঠিক!
...আর কিছু নাই হোক প্রতিদিন ভোর হয়। ঠিক।৪
দূর থেকে তোলা গ্রামের ছবি দিয়ে শুরু হয় শুনতে কি পাও! এরপরই পর্দায় ভেসে ওঠে মা আর ছেলের ছবি। বিছানায় শুয়ে রাখি আর রাহুল পুরনো দিন, ফেলে আসা বাড়ি, গাছপালাকে—অন্তত ভাষায়—ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।
—পেয়ারা গাছে কেডা উঠতো?
মায়ের প্রশ্নে রাহুলের অম্লান উত্তর,
—আমি
যেনো স্মৃতির জাল বুনে সেই সমৃদ্ধ অতীতকে আবারো তুলে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা। অন্য এক দৃশ্যেও যেমন রাখি বলে,
—তিনজনে বেড় পাবো না, এত্তো বড়ো গাছ।
যতোই মনে পড়ে কী তাদের ছিলো, ঝড়ের আগে কীভাবে কাটতো দিন, যতোই তারা বুঝতে পারে তাদের প্রিয় সবকিছু থেকে এখন তারা আলাদা হয়ে পড়ে আছে, এই নতুন জীবনের কষ্ট ততোই বাড়ে; হারানোর বেদনা গাঢ় হয়। আবার একই সঙ্গে পুরনো দিনের স্মৃতি তাদের মধ্যে একধরনের প্রাণশক্তির সঞ্চার করে। আবারো সেই জীবনে ফিরে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। সমস্ত অতীত, অতীতের সবকিছু যেনো সেই পিছুটান, সেই ঘরমুখী টান যা না থাকলে এই মানুষগুলো একত্র হয়ে বাঁধের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তো না।
একটা দৃশ্যে দেখা যায়, গ্রামের নারীদের খাবার পানির জন্য দীর্ঘ সারি। একটা সময় পানি আসে নৌকায় করে। নৌকা চলে জলের উপর, আবার নৌকার উপর জল। অদ্ভুত, অসাধারণ এই দৃশ্য যেমন খাবার জলের তীব্র সঙ্কট নির্দেশ করে, তেমনই আবার একধরনের দৃষ্টিমাধুর্যের জন্ম দেয়। অপলক তাকিয়ে দেখার মতন একটা দৃশ্যের অবতারণা করে। অপেক্ষায় ক্লান্তদের একজন, বিরক্তিভরে বলে ফেলে—‘জল যদি না দাও, এক বোতল বিষ কিনি দাও।’ এই বিরাগ উক্তি থেকে এইটা অন্তত নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই অপেক্ষাবহুল, অভাবসঙ্কুল জীবন তাদের কাছে মোটামুটি দুর্বিষহ। কিন্তু সব কথার অর্থ আসলে একাধিক। এই নারী আসলে সাহসী, প্রতিবাদী। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক নারী যখন জীবনের মৌলিক চাহিদার দাবিতে দৃঢ় হয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করে, আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না।
আরো বেশি অবাক লাগে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে ‘দৃষ্টিকটু’ দৃশ্য দেখেও যখন একধরনের ভালোলাগা কাজ করে। সৌমেন ঝরা পাতা আর কাদায় মাখামাখি হয়ে পায়খানা বসাচ্ছে তাদের অস্থায়ী বাঁধ-ঘরের পিছনে। রাখি বসে আছে, চোখে মুখে আনন্দ। সৌমেনকে প্রশ্ন করে, গলায় কৌতুকের রেশ—‘স্বাস্থ্যসম্মত না অস্বাস্থ্যসম্মত এইডা?’ পর্দায় আমরা বিপরীতের সহাবস্থান দেখি, অন্যরকম ভালো লাগে। সৌমেনের কড়া শ্রম-ঘাম, নোংরা কাদায় বসানো পায়খানা, অন্যদিকে রাখির নির্মল হাসি, কৌতুকপূর্ণ সংলাপ।
এই দুর্গত জীবনেও আছে সঙ্গীত। কেউ একজন রেডিওতে শুনছে, ‘চেও না সুনয়না আর চেও না এ নয়ন পানে।’ তবে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে দুর্গাপূজার দৃশ্যগুলো। এই প্লাবন, প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেই চলে পূজার সর্বাত্মক আয়োজন। ভোরে আলো ফুটতে না ফুটতেই রাখি প্রসাদের ডালা হাতে ঘর থেকে বের হয়। আবছা আলোয় হাতের সাদা শাঁখাজোড়া জ্বলতে থাকে যেনো। এরপর মণ্ডপমুখী যাত্রা। সোনালি শাড়ি পরে বের হয় রাখি, সঙ্গে যথাসাধ্য ভালো পোশাকে রাহুল। ‘মধুমতিতে বান ডেকেছে’—গানের সুরে ভেসে চলে নৌকা। ঢাকের শব্দ, রঙিন পূজাস্থল। পাশে মেলা বসেছে। সেই মেলা থেকে দরদাম করে রাখি কাঠের ফ্রেম বসানো আয়না কেনে। ফিরতি পথে আনন্দভরা চোখ পড়ে জলে। আশ্বিনের চাঁদ ভাসছে পূজার সমান উজ্জ্বল হয়ে।
আরেক সময় বসে ফুটবল উৎসব। তখন সম্ভবত ফুটবল বিশ্বকাপের হাওয়া বইছে দুনিয়াজোড়া। আইলায় জর্জরিত এই জনপদও সেই হাওয়ায় ভাসতে থাকে। কর্দমাক্ত মাঠে বসে ফুটবলের বিশাল আয়োজন। মাইকে ঘোষণা চলছে; মাঠ ঘিরে আছে অজস্র দর্শক। খেলা শেষ হয়। বিজয়ী দল তাদের পুরস্কার—টিভি সেট মাথায় করে মাঠময় নেচে বেড়ায়। অতি আনন্দে ঘোষক লোকটা বলে বসেন, ‘এই সময় আমরা বিশ্ববিখ্যাত শাকিরার গানটা এক মিনিট শুনি।’ নিমেষেই বেজে ওঠে—‘ওয়াকা ওয়াকা’। এই রঙ, এই সুর আর ছন্দ, ঝড়ে নুয়ে পড়া একটা জনপদে আমরা আশা করিনি। তাই অপ্রত্যাশিত রঙ লাগে মনে, অবাক করা সুরে মন ভরে যায়।
গ্রামের স্কুলটার কথা ভুলে যাওয়াও অসম্ভব। একপাশে শিমুল গাছ, একটা দোচালা ঘর, বাঁশ-চাটাইয়ের বেড়া। প্রথম দর্শনে কখনোই মনে হয় না, এটা কোনো স্কুল হতে পারে। একটা ঘরেই সব—একপাশে স্কুলের দাপ্তরিক কাজকর্ম চলেছে, অন্যপাশে ক্লাস। কিন্তু এতো অসুবিধার পরও কেনো যেনো স্কুলজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো কমতি নাই। ছেলেমেয়েরা কচি গলা মিলিয়ে গেয়ে যাচ্ছে দেশপ্রেমের গান—‘আমরা তোমাদের ভুলবো না’; আঁকছে জাতীয় ফুলের ছবি। রাখি এখানে শিক্ষক। সেই প্রাণরসে ভরপুর চাহনি। শিশুদের আঁকানো ছবিগুলো দেখতে গিয়ে তার কৌতুকাবেশী, ক্লেশহীন বাক্য—‘জাতীয় ফুলের মাথায় কি পরগাছা হয়েছে নাকি?’ এমনই এক প্রাণবন্ত রাখিকে আমরা দেখি সন্তান নিয়ে যাচ্ছে বাঁধের উপর বসানো ঘিঞ্জি বাজারে। জল থেকে উঠে আসা মৃদু হাওয়ায় দোকানগুলো ঘিরে থাকা নীল পলিথিন মৃদু উড়ছে।
পরস্পর বিপরীত দুটো বৃষ্টিদৃশ্যের উল্লেখ করলে বোঝা যাবে, এই উদ্বাস্তু জীবনও কতোখানি বিচিত্র হতে পারে। ঘোর বৃষ্টির এক রাত। কোনো রকমে তৈরি করা ঘরের চাল গলে পানি পড়ছে ভিতরে। রাখি আর সৌমেন সেই পানি যথাসাধ্য ঠেকাতে চাইছে। আরেক দিনের বৃষ্টি একেবারে আলাদা। রাখি ঘরের সামনের পথ ধরে মনভরে ভিজছে জলে, আবারো সেই হাসিমুখ।
হয়তো এসবের চেয়েও মুগ্ধকর কিছু ছড়িয়ে আছে শুনতে কি পাও!-এর নানা জায়গায়। যেমন হ্যাজাকের শুভ্র আলোয় গ্রামবাসী বসে আছে। নিজেদের বহু সমস্যা, অভাব নিয়ে চলছে আলোচনা। কে কতোখানি ত্রাণ পাবে তার তালিকাও তৈরি হচ্ছে এই বৈঠকে। এর মধ্যেই একজন আত্মসন্ধানীর মতন বলে বসেন, ‘ত্রাণ মানে তো ভিক্ষা। অসহায় অবস্থা দেখে মানুষ আমাদের ভিক্ষা দিচ্ছে।’ অর্থাৎ তাদের আত্মসম্মানবোধ এখনো বজায় আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তারা প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে, দুর্যোগ আর অভাবের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শিখছে। এখনো আছে আলো জ্বালানোর শক্তি আর সাহস।
‘যেন গ্রিক পুরাণের আদিম মানুষ এক নাজুক প্রাণী হিসেবে রুদ্র প্রকৃতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যার প্রকাণ্ড থাবা নেই, বিশাল দাঁত নেই, তীক্ষ্ম নখ নেই, ওড়ার পাখা নেই। দুর্বল সেই প্রাণী প্রমিথিউসের চুরি করা আগুন দিয়ে ক্রমেই বশ করে ক্ষমতাধর এই প্রকৃতিকে এবং নিজেই তৈরি করে এক দ্বিতীয় প্রকৃতি। আইলাবিধ্বস্ত ছবির মানুষগুলো যেনো প্রমিথিউসের আগুন লাগা একেকজন আদিম মানুষ। সর্বস্ব হারিয়ে যৌথ উদ্যোগে তারা তৈরি করছে তাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি।’৫
উ.
শুনতে কি পাও! একই সঙ্গে প্রামাণ্যচিত্র আবার কাহিনিচিত্র। প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে সফল; কারণ, বাস্তব ছবিটার সর্বস্ব জুড়ে আছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অন্য কারো চরিত্র করছে না। হয়তো নিজের চরিত্রে নিজে অভিনয় করাটা আরো কঠিন, তবু এরা বেশ সাবলীল থেকে তা করেছে। কাহিনিচিত্র হিসেবে একে সফল বলা যায়, কারণ একটা গল্প, দুঃস্বপ্ন-সুস্বপ্নের একটা প্রবাহ বয়ে গেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে না-কাহিনি/না-প্রামাণ্যতা, এই যে যা খুশি ধরে নেওয়ার দুর্লভ স্বাধীনতা, এখানেই লুকিয়ে আছে সুন্দর, ভালো লাগার এক অনন্য উৎস।
চলচ্চিত্রে আছে আরো একটা দ্বন্দ্ব—আশা আর নিরাশা। যদিও চলচ্চিত্রটা মূলত এক বিধ্বস্ত জনপদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প বলে, মানুষের অপরিসীম স্বপ্নক্ষমতার নজির উপস্থাপন করে; প্রকৃতি আর মানুষের আবহমান সম্পর্কের জয়গান গায়; তবু এখানে ওখানে, নানান দৃশ্যে আছে সব হারানোর দুঃখ, অকাল মৃত্যুর সংবাদ, অভাব আর পরিশ্রমের জ্বালা, শোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি। গয়া, কাহলো, জয়নুল, সুলতান যেমন জীবন-মৃত্যু, সুন্দর-অসুন্দর, আলো আর অন্ধকার, রঙ-মলিনতাকে এক ক্যানভাসে তুলে এনেছেন, সাইমনও তেমনি একই সঙ্গে দুর্যোগ, সংগ্রাম আর মানুষের কালো অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন। রাজনীতির অন্ধকার, দুর্নীতির স্বরূপ, বিশ্বায়নের ধোঁয়াশাকে তুলে ধরেছেন। চায়ের দোকানের একটা দৃশ্যের উল্লেখ এখানে না করলেই নয়।
চায়ের চুলায় আগুন জ্বলছে। শীতের রাত। গ্রামের সাধারণ লোকজন আর তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বসে আছে। আলোচনার বিষয় তাদের বহুকাক্সিক্ষত, বহু প্রতীক্ষার বাঁধ। আলোচনার একপর্যায়ে এই অপেক্ষা-ক্লান্ত, সর্বস্বান্ত মানুষেরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে অভিযোগে উদ্ধত সৌমেনের উচ্চারণ,
—গ্লাস ভাইঙ্গে ফেলতি পারেন না?
এই অস্বচ্ছ ‘গ্লাস’ ব্যবহার করেই ক্ষমতাবানেরা—যাদের শ্রেণিগত বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান বহু উপরে—অসহায়, দুর্গত মানুষের দুরাবস্থা আড়াল করে রাখে, শুনেও শোনে না, দেখেও দেখে না। দুনিয়াজোড়া এই কদাকার বৈষম্য এড়িয়ে যাওয়া কোনো লেখক, পরিচালক, শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই গৌরবগাথা লিখতে গেলে; মানুষ ও প্রকৃতির মায়া আঁকতে গেলে; স্বপ্ন, রোদ, জোছনা নিয়ে ছবি বানাতে গেলে; চলে আসে জীবন আর পৃথিবীর আলোহীন অংশ, মানুষের মনের যতো ছায়া, অন্ধকার।
শুনতে কি পাও!-এর প্রায় শেষে, প্রকৃতিকে যখন জয় করা হয়ে গেলো, বাঁধ বানানোর পরে রাখি অন্যান্য সবার মতন ঘরে ফিরছে মুক্তির আনন্দ নিয়ে। নিজের ভিটায় আবারো নিজের ঘর বাঁধা চলছে। মাঝপথে আবারো রোদ নিভে আকাশ কালো; আবারো ঝোড়ো বাতাস। সদ্য তোলা ঘরের নীল পলিথিন উড়ে যেতে চায়। ঘন বৃষ্টি। রাখি আর সৌমেন কাজের ভারে ক্লান্ত, তবু আপ্রাণ চেষ্টা করে বৃষ্টির জল থেকে জিনিসপত্র বাঁচাতে। এতকিছুর মধ্যেও রাখির হাসিমুখের এক ঝলক পর্দায় ভেসে ওঠে।
যেনো জীবনের চিরসত্য এখানেই। ঝড়ের মতন দুর্যোগ আবার আসবেই। যেকোনো সময় আবার জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে পারে সবকিছু। কিন্তু মানুষকে তবু বাঁচতে হয়। ধ্বংস আর মরণকে সঙ্গী করেই জীবন চিরকাল বহমান। আমাদের দুনিয়ায় সবাই থাকবে, একই আকাশের নীচে দোয়েল, ফড়িং, নদীর উদাস তীর, চায়ের দোকান, অজস্র গান, বাঘের থাবা, খুন, যুদ্ধ। তাই সুতারখালি একটা গ্রাম, আবার একটা বিশ্ব।
‘দিনের শেষে আলো নিভে এলে পরে এখানে এখনও ‘সন্ধ্যা’ দেয়া হয়; সস্তা সিগারেট, হারিকেনের আলো আর কেরোসিনের গন্ধে চায়ের দোকানে রাত হয় গভীর, রসালো। অমাবস্যার রাতে এখানে পথিকের পেছন লাগে ‘পুরো’ (অতৃপ্ত আত্মা), শিকার খুঁজে না পাওয়া বুড়ো বাঘের থাবায় উড়ে যায় এক খাবলা মাংস। আমার পৃথিবী থেকে এই বহুদূর দেশে নতুন মানুষ আমাকে ‘মানুষের’ সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়... রুপালি চিকচিক নদীর তীরে আমি ছুটে বেড়াই এক গাছা দড়ি হাতে, ফড়িং আর দোয়েলের খোঁজে।’৬
লেখক : আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির ও সাবরিয়া সাবেরিন বাঁধন, চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন।
muktadir137@gmail.com
sabriasaberin@yahoo.com
তথ্যসূত্র
১. Frith, Katherine, Shaw, P., & Cheng, H. (2005 : 1); ‘The Construction of Beauty : a Cross-cultural Analysis of Women's Magazine Advertising’; Journal of Communication, Los Angeles.
২. Dutton, Denis (2010); ‘A Darwinian Theory of Beauty’; http://www.ted.com/talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beauty
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You_Listening!.
৪. রফিক, মোহাম্মদ (২০০১ : ১৩০-৩১); ত্রয়ী : কীর্তিনাশা, গাওদিয়া, কপিলা; ঐতিহ্য, ঢাকা।
৫. শাহাদুজ্জামান; ‘শুনতে কি পাও!: এক টুকরো ভাবনা’; প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
৬. সাইমন, কামার আহমাদ; ‘শুটিং এক্সার্প্টস্ : শুনতে কি পাও!’; আলোকিত বাংলাদেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩।
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন