জাহাঙ্গীর আলম
প্রকাশিত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
সিনেমার প্রেমে পড়া অতঃপর একটি বই
জাহাঙ্গীর আলম

কৈশোরের প্রেম কি ভোলা যায়? ভোলা না গেলেও জীবন তো চলে যায়, চালিয়ে নিতে হয়। স্মৃতির বালুচরে পলি জমে, সেই প্রেম চাপা পড়ে। আবার তা ফিরে আসে। এমন করেই মাহমুদুল হোসেন তার কৈশোরের প্রেম চলচ্চিত্র নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন চার দশক। পেশায় সিস্টেম অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি চলচ্চিত্র বানাননি, তবে একনিষ্ঠ দর্শক, কখনও কখনও সংগঠনের নেপথ্যকর্মীও।
চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে মাহমুদুল হোসেন কিছু লেখালেখিও করেছেন; কখনও চলচ্চিত্র সংসদের প্রকাশনায়, লিটল ম্যাগাজিনে কখনও সংবাদপত্র-সাময়িকীতে। আবার কিছু লেখা রয়েছে অপ্রকাশিত। এসব লেখা নিয়ে তার বই ‘সিনেমা’। রচনাকালের দিক দিয়ে এ-বইয়ে সবচেয়ে পুরনো লেখা ১৯৮৯ সালের ‘আলমগীর কবিরের ছবিতে সমাজ চেতনা’, শেষটা ২০০৭ সালে তারেক মাসুদের অন্তর্যাত্রা নিয়ে।
গ্রন্থটিতে চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রনির্মাতা, তথ্যচিত্র, এ-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর বিভিন্ন লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্মাতাদের মধ্যে রয়েছেন ইতালির ফেদেরিকো ফেলিনি ও বাংলাদেশের আলমগীর কবির। চলচ্চিত্রের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তারেক মাসুদের অন্তর্যাত্রা নিয়ে দু’টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র রোকেয়া নিয়ে রয়েছে একটি লেখা। চলচ্চিত্রের তত্ত্বীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র : পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা’ এবং ‘চলচ্চিত্রের মতানৈক্যের কণ্ঠস্বর : বিকল্প চলচ্চিত্র’ প্রবন্ধে। এছাড়া ‘প্রসঙ্গ : ডিজিটাল সিনেমা’য় তিনি প্রযুক্তিগত দিক, এর সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।
ফেদেরিকো ফেলিনি, ইতালির অস্কারজয়ী নির্মাতা। ১৯৯৩ সালে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের আজীবন সম্মাননা লাভ করেন। এর আগে তিনি আরও চারবার অস্কার পুরস্কারে ভূষিত হন। এই বরেণ্য চলচ্চিত্রকার স্মরণে রয়েছে ‘ফেদেরিকো ফেলিনি : একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। এতে ফেলিনির একাধিক চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তিনি কীভাবে মানুষের স্বপ্ন, সম্ভাবনা, প্রেরণা-হতাশা, কাম-ক্রোধ, ঈশ্বর চেতনা, পুরাণ সর্বোপরি সমকালের রাজনীতিকে খতিয়ে দেখেছেন, তা ব্যাখ্যা করেছেন। মাহমুদুল হোসেনের মতে, চলচ্চিত্রে এসব বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করায় ফেলিনির চলচ্চিত্র সাবজেক্টিভ হতে বাধ্য। তার চলচ্চিত্রকে যারা ইচ্ছাপূরণের যেমন খুশি কর্মকাণ্ড মনে করেন, তাদের সঙ্গেও তার যেমন দ্বিমত, আবার যারা এক দীর্ঘ আত্মজৈবনিক প্রবাহ হিসেবে বিবেচনা করেন সেটাও অতিসরলীকরণ বলে তার ধারণা।
ফেদেরিকো ফেলিনি নিওরিয়ালিজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তবে ১৯৫১ ও ’৫২ সালে নির্মিত ভ্যারাইটি লাইট ও দ্য হোয়াইট সেইথ-এ তার নিওরিয়ালিজম থেকে দূরবর্তী হওয়ার নিশানা পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালে লা স্ত্রাদা নির্মাণ করে সমালোচকদের নজর কাড়েন ফেলিনি। ১৯৬০ সালে লা দোলসে ভিতা শ্রেষ্ঠ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র হিসেবে অ্যাকাডেমি পুরস্কার পায়। এরপর ফেলিনির অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ এইট অ্যান্ড হাফ। আঙ্গিকের দিক দিয়ে এটি জটিল একটি চলচ্চিত্র।
বহু মানুষের শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে নির্মাণ হয় চলচ্চিত্র। আবার বিনিয়োগ নির্ভর হওয়ায় এ-শিল্পমাধ্যম থেকে অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য দর্শকদের দিকটিও সবসময় মাথায় রাখতে হয়। এ-কারণে ভৌত ও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণে চলচ্চিত্র জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক। ‘সিনেমা’য় অকাল প্রয়াত পরিচালক আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্রে সমাজচেতনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক শেষে ইংল্যান্ডে যান আলমগীর কবির। সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার সময়ই তিনি চলচ্চিত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আধুনিকবোধে সঞ্জীবিত হয়ে ১৯৬৬ সালে আলমগীর ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকাই চলচ্চিত্রের বয়স ততোদিনে ১০ বছর পেরিয়ে গেছে। বছরে তখন গড়ে ২০-২৫টি চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। তবে এসব চলচ্চিত্রে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছিলো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।
এ-সময় আলমগীর কবির নামলেন চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, দেশে সুস্থ চলচ্চিত্র রুচি গড়ে তোলার জন্য। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছিলেন আলমগীর। যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে ১৯৭৩ সালে তিনি নির্মাণ করলেন প্রথম কাহিনীচিত্র ধীরে বহে মেঘনা। ১৯৮৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সাতটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন। তার চলচ্চিত্রে এ-দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রবলভাবে উপস্থিত। প্রতিটি চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যবিত্তের জীবন, বিদ্রোহ ও সংস্কৃতি।
সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিলো মূলত সংলাপপ্রধান। এ-জন্য সমালোচকদের অনেকেই এর শিল্পগুণ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে মাহমুদুল হোসেনের ভাষায়, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা আনন্দ দেয় সার্থক কবিতার মতোই।’ কবিতার অমীমাংসিত রহস্য অবয়বহীন এক উপত্যকায় আমাদের হাজির করে-অতঃপর আমরা অনিশ্চিত বোধ করি; কোথাও আদৌ গন্তব্য আছে কি না- এ সেই অনুভূতি।
এ-চলচ্চিত্রে ইন্দ্রনাথ চৌধুরীকে সবাই অতিক্রম করে যায় প্রকৃতির অনুপ্রেরণায়। এখানে অশোক, নগরের কোনো হিরো নয়, মনীষাও সম্ভবত নগরে অন্য মনীষা। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার অশোক বা মনীষা হতে গেলে আগে চাই দার্জিলিং। এ-চলচ্চিত্র ব্যস্ত নাগরিকদের প্রকৃতির শুদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়-প্রজন্মের সংঘাতে নতুন মানুষদের বিজয়ী হওয়ার কথা বলে, নতুন ভাবনার বিজয়ের কথা বলে। শ্রেণির সংঘাতকে নিরাকরণ করতে চায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে; জীবনকে ভিন্ন রকম হতে অনুপ্রাণিত করে।
আধুনিক মানুষ যখন বাইরের হিসাব মেলাতে পারে না, তখন অন্তর বা ভিতরের দিকে যাত্রা করে। অন্তর্যাত্রা হতে পারে তার চেতন বা অচেতন আকাঙ্ক্ষা। তারেক মাসুদের অন্তর্যাত্রা চলচ্চিত্রেও এসব বিষয় ফুটে উঠেছে। মাহমুদুল হোসেনের মতে, এ-চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নির্মাতা পশ্চিমা আধুনিকতার মাত্রা, উত্তরাধুনিকতা, সমকাল ও বিষয়বস্তুর এক চিরকালীন সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেছেন। চলচ্চিত্রটির শেষ ফ্রেম পার হয়ে যাওয়ার পরও ভাবনা ছেড়ে যায় না দর্শকদের।
সোহেলের মাতৃভূমি দর্শনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের শুরু। তার মা শিরিনের নিঃসঙ্গতা এ-চলচ্চিত্রের কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা নির্মাণ করে। তার অন্তর্যাত্রার সঙ্গে যোগ হয় আরও কয়েকজনের অন্তর্যাত্রা। তবে এ-চলচ্চিত্রে সংস্কৃতির বিনিময় বিষয়ে কোনো দ্বান্দ্বিক আলোচনা বা ইঙ্গিত নেই। মাহমুদুল হোসেন মনে করেন, সোহেলদের মতো প্রাচ্যের সন্তানেরা নানা জটিল কারণে বিভিন্ন ধরনের অন্তর্যাত্রায় জড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও তা ভীষণ সহিংস ও অন্ধকার যাত্রা হয়। এ-চলচ্চিত্রে তা সযতেœ এড়িয়ে গেছেন নির্মাতা।
বইটিতে মানজারেহাসীন মুরাদ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র রোকেয়া নিয়ে আলোচনা আছে। বেগম রোকেয়া বিষয়ে তথ্য অপ্রতুল নয়; তার বেশিরভাগ গ্রন্থ বা সাময়িকীতে পাওয়া যায়। এ-অবস্থায় তাকে নিয়ে আগ্রহোদ্দীপক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা কঠিন। লেখকের মতে, রোকেয়া মন্তব্যধর্মী জীবনী-চলচ্চিত্র। বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মের নির্মোহ সন্নিবেশ নির্মাতার লক্ষ্য নয়, বরং তার সেক্যুলার, আধুনিক সমাজের জন্য সংগ্রাম ও সাধনা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক এ-কারণে যে, আমাদের শিল্প ও সমাজকর্মে আজও তা আরাধ্য হয়ে রয়েছে।
আরেকটি প্রবন্ধে লেখক প্রামাণ্যচিত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উত্তরাধুনিক তত্ত্বের কল্যাণে এ-কথা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- সত্য বা বাস্তবতা নির্মিত। কীভাবে নির্মাণ হচ্ছে, কার স্বার্থে কাজ করছে- সেটাই দেখার বিষয়। তার মানে কাহিনীচিত্রে গল্পের রূপায়ণ হয় এবং প্রামাণ্যচিত্রে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে-বিষয়টা এতো সরল নয়। এজন্য মাহমুদুল হোসেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার ‘টার্মস অব রেফারেন্স’ বুঝতে চান এবং এর আওতায় সত্য ও বাস্তবতার সমীকরণ মেলাতে চেষ্টা করেন।
বিশ্বায়নের যুগে ‘জাতীয়তা’ জনপ্রিয় শব্দ নয়। পরিস্থিতি এমন যে, কোনো কোনো মহলে জাতীয়তা আর গ্রাম্যতা এক অর্থে গণ্য করা হচ্ছে। তবে বিশ্বায়ন যে ‘গ্লোবাল ভিলেজ’-এর কথা বলে, তা নিয়েও অনেকে সন্দিহান। প্রযুক্তি ব্যবহার ও মালিকানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নয়া উপনিবেশবাদ। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। তার মতে, জাতীয়তার ধারণা সঙ্কটহীন, শুদ্ধ গ্রন্থনা নয়। একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ যৌথায়নে ব্যক্তি-মানুষ গঠিত হয়, তৈরি হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের। এভাবেই জাতীয়তার সৃষ্টি।
বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস থেকে জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। সের্গেই আইজেনস্টাইন, পুদভকিন রুশ চলচ্চিত্রের ভিত্তি গড়েছেন। একে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তারকোভস্কি, মিখাইল রোম, দভঝেঙ্কো প্রমুখ। যদিও এসব নির্মাতাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারপরও রুশ চলচ্চিত্রের ধারা গড়ে উঠেছে। একই কথা প্রযোজ্য জাপান, ইতালি, ইরান প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে।
এ-প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে কেনো জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারা গড়ে ওঠেনি, তা একটি কাঠামোর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে দ্বিখণ্ডিত জাতিসত্তা জাতীয় চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে। তার মতে, মূলধারার চলচ্চিত্রে যা ঘটছে তা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ-জন্য তিনি বিকল্প ধারাতেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জাতীয়তার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করেছেন।
বইয়ের নাম : সিনেমা
লেখক : মাহমুদুল হোসেন
প্রকাশক : মাহমুদুল হোসেন, ফ্ল্যাট ১/বি, বাড়ি ২৮, সড়ক ১৫ (নতুন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০
মূল্য : ৮০ টাকা
লেখক : জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। বর্তমানে দৈনিক বণিক বার্তায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।
alam_rum05@yahoo.com
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৩ সালের জানুয়ারির ম্যাজিক লণ্ঠনের চতুর্থ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন


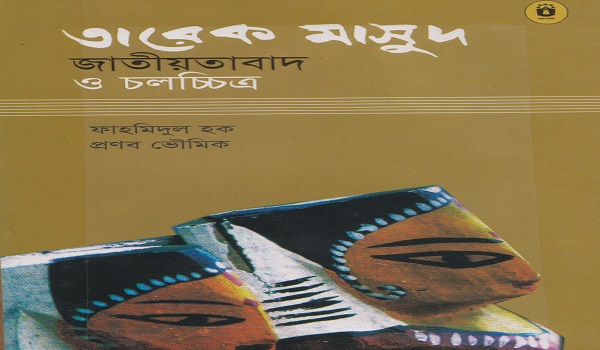
1735263359.jpg)




