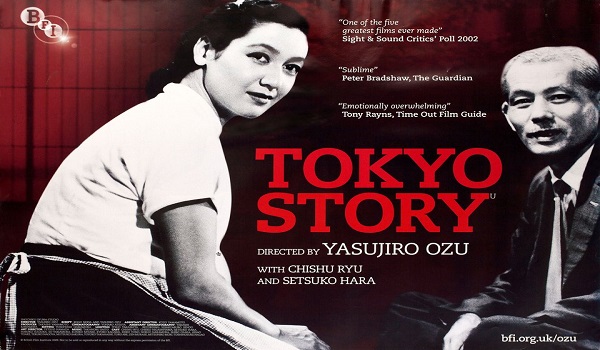সাবিহা তমা
প্রকাশিত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:০০ মিনিট
অন্যকে জানাতে পারেন:
ভিত্তোরিও,‘বাস্তবতা’ দিয়ে পরিবর্তন শুরুর নায়ক
সাবিহা তমা

পুরো নাম : ভিত্তোরিও ডি সিকা
জন্ম : ৭ জুলাই ১৯০১,সোরা,ইতালি
চলচ্চিত্রে অবদান : নিওরিয়ালিজম ধারার পথিকৃৎ
মৃত্যু : ১৩ নভেম্বর ১৯৭৪, নিউলি-সুর-সেইন, ইউস-ডি-সেইন, ফ্রান্স
চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা বহুমাত্রিক শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তাই এই মাধ্যমটিতে শিল্পের নানা রূপের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করে থাকেন শিল্পীরা। এই প্রয়োগে সফলও হয়েছেন অনেকে। আবার শুধু যে শিল্পরূপের ব্যবহার হয়েছে এমন নয়;বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্রকে সামনে এগিয়ে নিতে কাজও করতে হয়েছে তাদের। নির্মাতা,তাত্ত্বিক,দর্শক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নেমে এসেছে এই কাজে।আর তাতে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের নানান ধারা;শিল্প-আন্দোলন।
মানুষ সবসময়ই চেয়েছে বাস্তবের কাছাকাছি যেতে; আবার এও সত্য,সে কল্পনাকেও ভালোবেসেছে।সে সবসময় সেই কল্পনাকে দেখতে চেয়েছে তার জীবনে,সমাজে-বাস্তবের আদলে। এমন করেই সব শিল্পী,সাহিত্যিক,লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বাস্তব জগতকে তুলে ধরতে চেয়েছে তাদের সৃষ্টিকর্মে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলো না শিল্পের নবীনতম সদস্য চলচ্চিত্র ও এর রূপকাররা। তারা বাস্তবকে ধরতে চাইলেন সেলুলয়েডে,জন্ম নিলো চলচ্চিত্রমাধ্যমে শিল্পের এক অনন্য ধারা। ইতালিতে শুরু হওয়া চলচ্চিত্রের এই নতুন শিল্পধারা পরিচিত হলো নিওরিয়ালিজম বা নয়াবাস্তববাদ আন্দোলন নামে।
'Take the camera out into the street'-এই মূলমন্ত্র নিয়ে ইতালির চলচ্চিত্রে যে নিওরিয়ালিজম বা নয়াবাস্তববাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিলো,সময়ের পরিবর্তনে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইতালির সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে,নিজেদের সঙ্কটাপন্ন চলচ্চিত্রকে বাঁচাতেই মূলত এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন নির্মাতারা।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ সময়ে অর্থাৎ ১৯১৯ সালে মুসোলিনি ইতালিতে গঠন করেন ফ্যাসিস্ট দল। ১৯২২ সালে দেশটির ক্ষমতায় আসেন মুসোলিনি;শুরু হয় ফ্যাসিবাদী শাসন।দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও বাদ যায়নি মুসোলিনির বলয় থেকে।এই বলয়ের অন্যতম টার্গেট ছিলো চলচ্চিত্রনির্মাতারা।তাই প্রবল ইচ্ছা ও যথেষ্ট উপাদান থাকার পরও নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্রে বলতে পারেননি দেশের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা।
এই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে সময়। ইতালির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কান্নার সুর একটু করে কমতে থাকে।তারা চেষ্টা করতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি সামলে উঠবার। মুসোলিনি সরকার নজর দেয় সবধরনের কাঠামো-অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে।কিন্তু বিশ্ব যেনো শান্তি চায় না।আর তাই রণহুঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ইতালির বেশকিছু অংশ জুড়ে জার্মানদের তাণ্ডবলীলা পুরোদমে চলতে থাকে। চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলো তখন ভেঙে চুরমার; দেখা দেয় কাঁচা ফিল্মের সঙ্কট।এ অবস্থায় অনেক পরিচালক দেশ ছাড়তে একরকম বাধ্য হন। নির্মাতাদের বেশিরভাগই হলিউডে চলে গেলেও কেউ কেউ থেকে যান ইতালির ধ্বংসস্তুপের মধ্যে।এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কয়েকজন পরিচালক চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিতে কাজ করতে থাকেন,চিন্তা করেন নতুন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের।এদের মধ্যে অন্যতম হলেন উমবার্ত বারবারা,লুচিনো ভিসকন্তি,ভিত্তোরিও ডি সিকা,রবার্তো রোসেলিনি,আলদো ভেরগানো,আলফ্রেদো গুসারিনি’র মতো নির্মাতারা। দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে রোমের ভিয়া দেল্ ত্রাফোরো’র একটি বাড়িতে বসে গোপন বৈঠক। একদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভঙ্গুর অবস্থা,অন্যদিকে মার্কিন চলচ্চিত্রের প্রকোপ; কিভাবে এ থেকে চলচ্চিত্রকে বাঁচানো যায় বা দেশিয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ কী হবে-তা নিয়ে আলোচনার জন্যই ছিলো মূলত এই বৈঠক।
১৯৪৩ সালের আগ পর্যন্ত ইতালিতে যে চলচ্চিত্রগুলো হয়েছিলো সেগুলোতে মূলত দেশটির সুন্দর ইমেজই উঠে আসে।কিন্তু সেবছরই অর্থাৎ ১৯৪৩-এ অবসান ঘটে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি সরকারের।একদিকে মুসোলিনি হারায় ফ্যাসিস্ট কাউন্সিলের সমর্থন,অন্যদিকে স্বদেশি যোদ্ধাদের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট সমর্থকদের বিরোধ।১৯৪৪-এ ইতালি চলে যায় মিত্রবাহিনীর দখলে।ইতালি ছাড়েন মুসোলিনি।এ ধরনের একটা সময়ে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্তরালে জন্ম নেয় চলচ্চিত্রের মহান সেই শিল্পমন্ত্র-নিওরিয়ালিজম।এই ধারার শিল্পীরা স্টুডিওগুলোর কৃত্রিম চত্বর ছেড়ে সবরকম মেকি ফ্যাশন পরিত্যাগ করে পথে নেমে আসেন।কৃত্রিম লোকেশন নয়,শুটিং করা শুরু হয় রাস্তায়,দোকানে,ক্যাফে,বস্তি ও ঘরে;যেখানে বাস্তব-জীবনের বাস্তব মানুষেরা থাকে,বিশেষ করে দরিদ্র মানুষেরা।
নয়াবাস্তববাদ বা নিওরিয়ালিজম শব্দটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহার শুরু করেছিলেন ঔপন্যাসিক,নাট্যকার ও পরিচালক উমবার্তো বারবারা।বারবারা মূলত ১৯৪২ সালে ভিসকন্তি নির্মিত ওসেসিয়োনে (Ossessione)চলচ্চিত্রকে ধরেই নিওরিয়ালিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে অনেকে এই ধারার প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে রোজেলিনি’র রোম ওপেন সিটিকে (১৯৪৫) ধরে। কারণ ওসেসিয়োনে ১৯৪২ সালে নির্মাণ হলেও জনসম্মুখে এর প্রদর্শন করা হয় ১৯৪৬ সালে। তবে এই আন্দোলনের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্র বলা হয় ভিত্তোরিও ডি সিকা’র দ্য বাইসাইকেল থিভস্কে।আমাদের এবারের আলোচনা ভিত্তোরিও ডি সিকা এবং তার দ্য বাইসাইকেল থিভস্ নিয়ে।
নিওরিয়ালিজম ধারার অন্যতম পথিকৃৎ ভিত্তোরিও ডি সিকা'র জন্মসাল নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। কেউ বলছেন,১৯০১ সালের ৭ জুলাই তার জন্ম;কারো মতে সেটা ১৯০২ সালের ৭ জুলাই। ইতালির সোরা শহরের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে ভিত্তোরিও ডি সিকা’র জন্ম। কিন্তু তিনি বেড়ে ওঠেন নেপলেস শহরে।বাবা ম্যানুয়েল ডি সিকা ও মা ক্রিস্টিয়ান ডি সিকা’র অভাবী সংসারে একটু ভালোভাবে বাঁচার জন্য ছোটবেলাতেই কাজের সন্ধানে নামতে হয় ভিত্তোরিও’কে।একটু বড়ো হয়ে ভিত্তোরিও কেরানির কাজ নেন স্থানীয় একটি অফিসে।স্বপ্ন যার রঙিন দুনিয়া ঘিরে সে কি আর কেরানির চাকরি করতে পারে? তাই ভিত্তোরিও’কে কেউই ধরে রাখতে পারেনি সেভাবে। ১৯২০ সালের দিকে ভিত্তোরিও চাকরির পাশাপাশি স্থানীয় থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেন।একপর্যায়ে কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অভিনয়ে নিয়মিত হন।
থিয়েটার কোম্পানি ‘তাতিয়ানা পাভলোভা’র সঙ্গে যুক্ত হন ১৯২৩ সালে। সেখানে তিনি অভিনয় করতেন মূলত কমেডি চরিত্রে।আর একজন কমেডিয়ান হিসেবে তার নামডাকও ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।তাই একসময় নিজেই একটি থিয়েটার কোম্পানি খোলার চিন্তা করেন।সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেন ১৯৩৩ সালে। প্রথম স্ত্রী জুদিত্তা রিসোনি (১৯৩৭-১৯৫৪) এবং সারজিও টোফানোর সঙ্গে খুলে বসেন নিজের থিয়েটার কোম্পানি। সেখানে তিনি নিজে অভিনয় করতেন কমেডিয়ান হিসেবে। এতো কিছু করার পরও ভিত্তোরিও মনে যেনো শান্তি পাচ্ছিলেন না। কারণ,মঞ্চের আলো আসলে ভিত্তোরিও’কে সন্তুষ্ট করতে পারছিলো না।
শেষপর্যন্ত ১৯৪০ সালে মান্দালিনা,জিরো ফর কনডাক্ট দিয়ে ভিত্তোরিও'র চলচ্চিত্রযাত্রা শুরু।এর আগে একই বছর অবশ্য অন্য একজনের সঙ্গে মিলে রজ স্কারলাতে নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। একপর্যায়ে পরিচয় হয় নয়াবাস্তববাদ ধারার আরেক সারথি সিজার জাভাত্তিনি’র সঙ্গে। মূলত জাভাত্তিনি’র সঙ্গে পরিচয় ভিত্তোরিও ডি সিকা’র জীবনে একটা অন্যতম ঘটনা।শুরু হয় চলচ্চিত্রনির্মাণের মহাযজ্ঞ,নাম দ্য চিলড্রেন আর ওয়াচিং আস (১৯৪৪)।এখানে ভিত্তোরিও এক অবহেলিত শিশুর চোখ দিয়ে দেখান তার মা-বাবার দাম্পত্য জীবনের টানাপড়েন। তবে এই ছবি শুধু যে পারিবারিক টানাপড়েনের কথা তুলে ধরেছে তা নয়। আসলে এর মধ্য দিয়ে ভিত্তোরিও তুলে ধরলেন বুর্জোয়া সমাজে প্রলেপ দিয়ে ঢাকা মানুষের জীবনের ক্ষতগুলোকে;মানুষের জীবন-বাস্তবতাকে।এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই ভিত্তোরিও নয়াবাস্তববাদ ধারাকে প্রাথমিকভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের জীবনকে এভাবে পর্দায় দেখতে অভ্যস্থ না হওয়ায় চলচ্চিত্রটি তেমন ব্যবসা করতে পারে না। কিন্তু তাতে কী,দমবার পাত্র নন ভিত্তোরিও।পরের বছরই নির্মাণ করলেন দ্য গেইট অব হ্যাভেন (১৯৪৫)।
এদিকে একই বছর (১৯৪৫)রোসেলিনি কাজ শুরু করেন রোম ওপেন সিটির। ক্যামেরা হাতে রোসেলিনি নেমে পড়লেন একেবারে রাস্তায়।পুরনো বন্ধু চিত্রনাট্যকার সের্জিয়ো আমিদেই এবং আরেক যুবক ফেদেরিকো ফেলিনির সহায়তায় নির্মাণ করলেন রোম ওপেন সিটি।সমালোচকরা এই চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করলেন নয়াবাস্তববাদের আদর্শ হিসেবে।রোম ওপেন সিটির সাফল্যে ভিত্তোরিও ডি সিকা অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করলেন নতুন চলচ্চিত্র সুসাইন (১৯৪৬)এর কাজ।এবারো সেই সাধারণ মানুষের কথা বললেন চলচ্চিত্রে।রোম ওপেন সিটি ও সুসাইন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়।অস্কারে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার পায় সুসাইন।শুরু হয় নয়াবাস্তববাদ ধারার নতুন এক অধ্যায়।
ইতালির নয়াবাস্তববাদের উৎকৃষ্ট ফসলের বীজ যেনো বোনা ছিলো ভিত্তোরিও’র দ্য বাইসাইকেল থিভস্-এ।সবার মুখে তখন নয়াবাস্তববাদ চলচ্চিত্রের কথা। তারপরও প্রযোজকের কাছে টাকা পেতে নানা শর্ত।আর কয়েকজন টাকা দিতে চাইলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় সরকার।অন্যদিকে অন্যরকম উদ্দেশ্য নিয়ে ভিড় বাড়তে থাকে আমেরিকান প্রযোজকদের।শেষপর্যন্ত ভিত্তোরিও’কে অর্থ দিতে রাজি হন ডেভিড ও সোলানাজ নামে দুই প্রযোজক।তবে শর্ত জুড়ে দেন,প্রধান চরিত্রে অভিনেতা হিসেবে নিতে হবে জনপ্রিয় অভিনেতা ক্যারি গ্রান্ট’কে।তবে ভিত্তোরিও’র সেই এককথা,তিনি সাধারণ মানুষকে দিয়েই চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন।
তাই সেই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিলেন ভিত্তোরিও। টাকার জোগাড় করতে ফিরে গেলেন আবার সেই থিয়েটারে।শুরু করলেন অভিনয়।জোগাড় হলো টাকা। ফিরে এলেন চলচ্চিত্র নির্মাণে।এবার নিজের ইচ্ছামতো প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেছে নিলেন কারখানার এক মামুলি শ্রমিককে।আর ছেলের ভূমিকায় নিলেন এক শিশু শ্রমিককে,যে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাগজ বিক্রি করতো।ভিত্তোরিও মূলত যুদ্ধপরবর্তী ইতালির বাস্তব অবস্থাটা ধরতে চেয়েছিলেন।তাই ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায়,কারখানায়,বাজার,পতিতালয়-সব জায়গায় করলেন বাইসাইকেল থিভস্-এর শুটিং;তুলে ধরলেন ইতালির সাধারণ মানুষের জীবন।
অবশেষে ১৯৪৮ সালে মুক্তি পেলো সিকার বহু কষ্টের দ্য বাইসাইকেল থিভস্।চলচ্চিত্রটি সাড়া ফেলে দিলো ইতালিসহ সারাবিশ্বে। আবার জিতে নিলো অস্কারের বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার।বাইসাইকেল থিভস্-এ বাস্তবতাকে ধরার জন্য ভিত্তোরিও এমন কোনো দৃশ্য তুলে ধরেননি,যা বাস্তব নয়।মোটকথা এর জন্য তিনি কোনো সেট নির্মাণ করেননি।অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেশিরভাগই ছিলো চলচ্চিত্রটির নানা চরিত্রের মতোই বাস্তবে শ্রমিক।
জনপ্রিয়তার এমন সময়ে জাভাত্তিনি’র সঙ্গে কাজ শুরু করেন ভিত্তোরিও।১৯৫০ সাল।জাভাত্তিনি চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেন ভিত্তোরিও’র জন্য।তার সহযোগিতায় এবার ভিত্তোরিও নির্মাণ করলেন মিরাকল ইন মিলান।ধনী-দরিদ্রের আধা-কাল্পনিক ও আধা-বাস্তব গল্পের একটি বিদ্রূপাত্মক উপস্থাপন হলো চলচ্চিত্রে।যদিও নিওরিয়ালিজম ধারার বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্রটিতে কিছু স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছিলো;তারপরও এটি শিল্প-সমাজে থাকা দরিদ্র-শ্রেণির আশা ও প্রাপ্তির মধ্যে একটা দোদুল্যমান অবস্থা প্রকাশ করেছিলো।১৯৫২-তে ভিত্তোরিও নির্মাণ করলেন উমবার্ত ডি।এখানে ভিত্তোরিও একজন বয়স্ক ব্যক্তির একাকিত্ব তুলে ধরলেন। যেখানে ব্যক্তিটির জীবন-যন্ত্রণা,ক্ষোভ ও তার জীবনের শূন্যতা ফুটে ওঠে। এই চলচ্চিত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মনস্তাত্বিক বিষয়। এই উমবার্ত ডিকেই নিওরিয়ালিজম ধারার শেষ চলচ্চিত্র মনে করেন তাত্ত্বিকরা। তবে এই সীমিত সময়ে নির্মিত অন্যান্য পরিচালকের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো ছিলো-ডি স্যান্টিসের ট্রাজিক হান্ট;লুইজি জাম্পার টু লিভ ইন পিস,অ্যাঞ্জেলিনা;ভিসকন্তির দ্য আর্থ ট্রিম্বলস;রোসেলিনির ইউরোপা ফিফটি ওয়ান।
নিওরিয়ালিজম আন্দোলনটি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে টিকে ছিলো মাত্র ছয়-সাত বছর। ভিত্তোরিও ডি সিকা পরবর্তী সময়ে এ ধারার বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। ভিত্তোরিও'র উল্লেখযোগ্য অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ডু ইউ লাইক উইমেন (১৯৪১),হার্ট,হার্ট অ্যান্ড সোল (১৯৪৮),ইট হ্যাপেন্ড ইন দ্য পার্ক (১৯৫৩),দ্য গোল্ড অব ন্যাপেলস (১৯৫৪),দ্য রুফ (১৯৫৬),টু উইমেন (১৯৬১),দ্য লাস্ট জাজমেন্ট (১৯৬১),ইয়েস্টারডে,টুডে অ্যান্ড টুমরো (১৯৬৩),আ প্লেস ফর লাভার্স (১৯৬৮),সানফ্লাওয়ার (১৯৭০),দ্য গার্ডেন অব দ্য ফিনজি-কনটিনিস (১৯৭০),দ্য নাইটস অব মালটা (প্রামাণ্যচিত্র, ১৯৭১),আ ব্রিফ ভ্যাকেশন (১৯৭৩),দ্য ভয়েজ (১৯৭৪)। ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো (১৯৬৩)ও দ্য গার্ডেন অব দ্য ফিনজি-কনটিনিস (১৯৭০)চলচ্চিত্র দুটি অস্কারে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার পায়। শুধু পরিচালনা করেই ক্ষান্ত দেননি ভিত্তোরিও ডি সিকা,অভিনয়ও করেছেন চলচ্চিত্রে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকান পরিচালক চার্লস ভিদর নির্মাণ করেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’ অবলম্বনে চলচ্চিত্র আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস।এই চলচ্চিত্রে একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন ভিত্তোরিও।মজার ব্যাপার হলো-এই চরিত্রের জন্য সেই বছর অস্কারে সেরা পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কারও পান তিনি। চলচ্চিত্রটি সমালোচকদের কাছে বেশ প্রশংসা পেলেও বক্সঅফিসে ব্যবসা করতে পারেনি। তবে কেবল ভিত্তোরিও অভিনয় করায় তা খুবই আলোচিত হয়েছিলো।
ভিত্তোরিও’র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দু-একটি কথা না বললেই নয়। বিখ্যাত এ পরিচালকের কিন্তু অসম্ভব রকমের জুয়াখেলার নেশা ছিলো। জুয়া খেলে তিনি খুইয়েছিলেন অনেক টাকা। যদিও এটাকে তিনি খোলামেলা বিষয় মনে করতেন।প্রথম স্ত্রী জুদিত্তা রিসোনি (১৯৩৭-১৯৫৪)এর সঙ্গে সিকা’র ছাড়াছাড়ি হয় ১৯৫৪ সালে।মূলত ১৯৪২ সালে আ গেরিবালডিয়ান ইন দ্য কনভেন্ট চলচ্চিত্রটি করতে গিয়ে স্পেনিশ অভিনেত্রী মারিয়া মারসেডার-এর সঙ্গে ভিত্তোরিও’র সম্পর্ক হয়।১৯৫৯ সালে তিনি মারিয়াকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ে নিয়ে আইনি কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভিত্তোরিও ইতালি ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।এবং ১৯৬৮ সালে পুনরায় মারিয়াকে বিয়ে করেন।দুই পক্ষে ভিত্তোরিও’র এক মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে।বিচ্ছেদ হলেও জুদিত্তা রিসোনি’র সঙ্গে কিন্তু ভিত্তোরিও’র একধরনের সম্পর্ক ছিলো।
শেষ জীবনটা ভিত্তোরিও ফ্রান্সেই কাটান।একপর্যায়ে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হন তিনি।১৯৭৪ সালের ১৩ নভেম্বর প্যারিসে একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর আমাদের ছেড়ে চলে যান বিখ্যাত এই চলচ্চিত্রনির্মাতা।
চলচ্চিত্র দ্য বাইসাইকেল থিভস্
লুইজি বার্তোলিনি’র গল্প অবলম্বনে নির্মিত বাইসাইকেল থিভস্-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালির প্রেক্ষাপটে।কাজের সন্ধানে তখন হাজারো মানুষ ইতালির রাস্তায়।তাদেরই একজন আন্তোনিও রিচি। চাকরির সন্ধানে পথে পথে ঘুরে অনেক চেষ্টায় একটি কাজ পায় সে;চলচ্চিত্রের পোস্টার লাগানো।কিন্তু সমস্যা হলো এ কাজে বাইসাইকেল থাকতে হবে। আন্তোনিও বাইসাইকেলের কথা স্ত্রী মারিয়া’কে জানালে অনেক কষ্টে তার একটা ব্যবস্থা হয়। মারিয়া মূলত বাসার বিছানা-চাদর মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে সেই টাকায় বাইসাইকেল কেনে আন্তোনিও’র জন্য।পরের দিন সকালে বাইসাইকেল নিয়ে কাজে বের হয় আন্তোনিও। সাইকেল রেখে উঁচু জায়গায় পোস্টার লাগাতে উঠলে সেই ফাঁকে চুরি হয় সেটি। চোরের পিছে প্রাণপণ দৌড়েও তাকে ধরতে পারে না আন্তোনিও। একপর্যায়ে পুলিশের শরণাপন্ন হয়।কিন্তু ‘সামান্য’ সাইকেল উদ্ধারে তেমন তৎপরতা দেখায় না পুলিশ। বাধ্য হয়ে আন্তোনিও ছেলে ব্রুনো’কে নিয়ে রোমের পথে পথে সাইকেল খুঁজতে থাকে।
একপর্যায়ে আন্তোনিও হারানো সাইকেলের সন্ধানে চার্চে যায়,তাতেও কোনো ফল হয় না।তখন একদিকে সাইকেলের চিন্তা অন্যদিকে কাজ হারানোর ভয়;বেপরোয়া হয়ে ওঠে আন্তোনিও।একসময় চোরকে হাতের নাগালে পেয়েও সে কিছুই করতে পারে না;উপরন্তু নিজেই বিপদে পড়ে। চোরটি অসুস্থতার ভান করলে আন্তোনিও’কে ঘিরে ধরে চোরের প্রতিবেশীরা। তারা ‘অসহায়’ বালকটির এই অবস্থার জন্য আন্তোনিওনিকে অভিযুক্ত করে। পুলিশ এসে আন্তোনিও’কে জানায়,যেহেতু তার কাছে কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নেই,সেহেতু বালকটির বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার নেই। আন্তোনিও’কে ফিরে যেতে হয়।
শেষ পর্যন্ত আন্তোনিও নিজেই সাইকেল চুরির সিদ্ধান্ত নেয়। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরাও পড়ে। উপস্থিত লোকজন আন্তোনিও’কে মারধর করে ছেলের সামনে। তাকে পুলিশে দিতে চায়,কিন্তু অসহায় ব্রুনো’কে দেখে সাইকেল মালিকের দয়া হয়। সে পুলিশের কাছে আন্তোনিও’কে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে।
শেষ দৃশ্যে লোকভর্তি রাস্তায় বেচারা আন্তোনিও ছেলে ব্রুনো’র হাত ধরে বিষন্ন মনে ফিরে যায়। এই হলো সিকা’র দ্য বাইসাইকেল থিভস্। যতোদিন পৃথিবীতে চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমটি থাকবে,ততোদিন চলচ্চিত্রপিপাসু মানুষের কাছে তা অনন্য হয়ে থাকবে।
লেখক : সাবিহা তমা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
sabihatoma@gmail.com
পাঠ সহায়িকা
দাশগুপ্ত,ধীমান (২০০৬); চলচ্চিত্রের অভিধান; বাণীশিল্প,কলকাতা।
আউয়াল,সাজেদুল (২০১১); চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্য প্রকাশ,ঢাকা।
http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_DeSica
বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৩ সালের জানুয়ারির ম্যাজিক লণ্ঠনের ৫ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন